ভূমিকা:
ভারত উপমহাদেশে দুই’শ বছরের বৃটিশ শাসনামলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সভ্যতা। সর্বাধিক নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার হয়েছে মুসলিম জনগোষ্ঠী। আর অঞ্চল হিসাবে অধিক পরিমাণে শোষিত হয়েছে মুসলিম প্রধান পূর্ববাংলা। এ সময়ে দখলদার জালিম ইংরেজ শাসকদেরকে বিতাড়নের জন্য অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। বহু প্রাণহানী ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোন আন্দোলনই এ অঞ্চলের মুসলমানদেরকে এতোটা ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করতে পারেনি, যতটা পেরেছিল ‘খিলাফত আন্দোলন নামে’ পরিচিতি এক উম্মাহ্ কন্সেপ্ট থেকে উৎসারিত ঐতিহাসিক একটি আন্দোলন। অবশ্য ১৯২৪ সালে তুরস্কে উসমানী খিলাফত পতনের পর এ আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। মুসলিম নেতারা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পরিবর্তে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। আর এই সুযোগে চতুর ইংরেজরা স্বাধীনতার প্রশ্নে মুসলানদের মাঝে দ্বিজাতি তত্ত্ব আর অবিভক্ত ভারতের দাবীতে এক বিরাট বিভক্তি সৃষ্টি করে দেয়। ফলে গতিহারা হয়ে যায় মুসলমানদের আন্দোলন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূল দাবী হারিয়ে যায় সাময়িক ইস্যুতে আন্দোলনের ডামাডোলে। যার ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো এখনও বহন করে চলছে।
এই নিবন্ধে আমি পুরো বিষয়টিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে আলিম-উলামাদের সীমাহীন অবদান আছে। তবে এই নিবন্ধে সেই বিষয়ে আলোকপাত না করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রসঙ্গকেই এর আলোচ্য বিষয় বনানো হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রবন্ধটিকে মোট ৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হলো।
এক : ১৯৪৭ পূর্ববর্তী খিলাফত আন্দোলন।
দুই : ১৯৪৭ পরবর্তী পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলের ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা।
তিন : ১৯৭১ এরপর থেকে বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর অবস্থান এবং
চার : ফলাফল বিশ্লেষণ।
উপমহাদেশে খিলাফত আন্দোলন
১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বৃটেন তাদের বৃহত্তম উপনিবেশ ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথ খোলা রাখার জন্য আরব দেশগুলোকে উসমানী খিলাফত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জোর চক্রান্ত চালাতে থাকে। এতদুদ্দেশ্যে খিলাফত বিরোধী মনোভাব উস্কে দেয়ার জন্য তারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের দক্ষ গুপ্তচরদেরকে নিয়োগ করে। বৃটিশদের হয়ে আরব এলাকায় খিলাফত বিরোধী চেতনা ও আরব জাতীয়তাবাদী ধারণা ছড়ানোর গোয়েন্দাবৃত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী কর্ণেল টি.ই. লরেন্স এর প্রচেষ্টায় গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে তারা উত্তপ্ত ও বিভক্ত করে ফেলে। ভারত উপমহাদেশের উলামাগণ খিলাফতের এই বিপদ দেখে ভীষণভাবে আতংকিত হয়ে উঠেন। যে কোন মূল্যে খিলাফত শাসন বহাল রাখার জন্য তারা জোর তৎপরতা শুরু করেন। খিলাফত রক্ষার জন্য ভারতীয় উলামাদের সেই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকেই ইতিহাসে ‘খিলাফত আন্দোলন’ নামে অবিহিত করা হয়।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের মুসলমানরা ব্রিটিশকে এই শর্তে সমর্থন দিয়েছিল যে, ব্রিটিশরা তুরস্কের খলীফার কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু এই যুদ্ধে তুরস্ক ও জার্মানি মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি তুর্কী খিলাফতকে বিভক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পবিত্র মক্কা ও মদীনা খ্রিষ্টানদের করতলগত হবার আশস্কায় ভারতের মুসলমানরা ১৯১৯ সালের ৭ অক্টোবর খিলাফত দিবস পালন করে। খিলাফত রক্ষাকল্পে ভারতীয় মুসলমানগণ দেশব্যাপী গড়ে তোলে তীব্র আন্দোলন।
এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন-ভারতের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ এর তৎকালীন মুহতামিম শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.), মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার এবং মাওলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ড. মুক্তার আহমদ আনসারী প্রমুখ।
খিলাফত আন্দোলন হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার এবং মাওলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয় ১৯১৯ সালে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ড. মুক্তার আহমদ আনসারী প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে খিলাফত আন্দোলন নামের এই সংগঠনটির কাজ শুরু করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল : তুর্কী খিলাফতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। এই একটি মাত্র সংগঠন ভারতের সকল ঘরানার উলামা ও সাধারণ মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে যে, খিলাফতই হচ্ছে এক উম্মাহ্র ঐক্যের প্রতীক। এখানে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী ছিলেন একজন উচ্চতর হানাফী। অথচ তার সাথে এই আন্দোলনে ঘনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তিনি ছিলেন একজন গায়ের মুকাল্লিদ। এভাবে সকল মাসলাক, মাশরাফ ও মাযহাবের উলামাগণ খিলাফত ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।
১৯২০ সালে বঙ্গ প্রদেশের আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত খিলাফত কন্ফারেন্সের সভাপতির ভাষণে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ খিলাফতের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছিলেন : এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপরে চালানোর জন্য সংগঠিত করা এবং দুনিয়াতে আল্লাহ্’র কালামকে বুলন্দ করা। এর জন্য জরুরী হচ্ছে খলীফার হাতে যথাযথ কর্তৃত্ব থাকা। মাওলানা আজাদ বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের খলীফা বিহীন জীবনই হচ্ছে ইসলাম বিহীন জীবন। খিলাফত বিহনে বসবাস করলে মুসলমানদেরকে আখেরাতে জবাব দিতে হবে। ‘মাসআলায়ে খিলাফত’ নামে এক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন : “খিলাফত বিহীন ইসলামের অস্তিত্ব অসম্ভব। ভারত বর্ষের মুসলমানদের উচিত সর্বশক্তি দিয়ে খিলাফতের জন্য কাজ করা।” মাওলানা শওকত আলী কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা জারী করেছিলেন যে আমরা আশা করি ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ মুসলিমগণ ভারতবর্ষে অবস্থান করে বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেবে। তা অসম্ভব হয়ে উঠলে খিলাফত রাষ্ট্রে হিজরত করার চিন্তা করবে। ভারতবর্ষের বিশিষ্ট উলামাগণ এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী জোর দিয়ে বলতেন মুসলমানদের জন্য একজন খলীফা থাকা ফরয। ১৯২০ সালে মাওলানা মুহম্মাদ আলী জাওহারের সঙ্গে এক প্রেস কন্ফারেন্সে উপস্থিত তার সঙ্গী সাইয়েদ হুসাইন বলেছিলেন যদি দুনিয়াতে ইসলামের অস্তিত্ত্ব বজায় রাখতে হয়, তাহলে মুসলমানদের একজন খলীফার উপস্থিতি অপরিহার্য্য।
শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান কঠিন পরিশ্রম করে খিলাফতের অধীনে যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে খলীফার নিকট প্রেরণ করতেন। তিনি রাশিয়া এবং তুরস্কের যুদ্ধে উসমানী খিলাফতকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করেছিলেন। খিলাফতের সাহায্যার্থে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করেন। ছাত্রদের একটি বিশাল বাহিনীকে তুরস্কে প্রেরণ করে অপর আরেকটি বাহিনী নিয়ে নিজে তুরস্ক চলে যান। তিনি জানতেন সমগ্র ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে খিলাফত ধ্বংসের মাধ্যমে ইসলামের প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারত বর্ষের মসজিদগুলোতে খুতবার মাঝে খিলাফতের কথা উল্লেখ করা হতো এবং নামাজে মুসলমানদের বিজয় ও কাফেরদের পরাজয়ের জন্য দোয়া করা হতো। খিলাফত আন্দোলনের আরেক মহান ব্যক্তিত্ব মওলানা শওকত আলীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কেন খুতবায় তুর্কী সুলতানের নাম অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি জবাবে বলেছিলেন, কারণ তুর্কী সুলতান এই মূহুর্তে মুসলমানদের খলীফা। বৃটিশ সামাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র থেকে খিলাফত রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য মাওলানা মাহমুদুল হাসান তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এই জন্য তিনি হিজাজ সফর করেন। গভর্নরের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য পত্র মারফত এই অনুরোধ নিয়ে এসেছিলেন যে তারা যেন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এই চিঠি ইতিহাসে গালিব নামা নামে খ্যাত। খিলাফতের পক্ষে এই ধরণের তৎপরতার দরুন নিষ্ঠুর ইংরেজ শাসকরা মাওলানা মাহমুদুল হাসানের উপর কঠিন চাপ সৃষ্টি করে। সত্য ভাষণ থেকে নিবৃত করা এবং ইংরেজ সরকারের বিপক্ষে গিয়ে উসমানী খিলাফতকে সমর্থন দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁর উপর অনেক অত্যাচার করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুদূর মাল্টাদ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ইংরেজরা দাবী করেছিল তিনি যেন মক্কার বিশ্বাসঘাতক গভর্নর শরীফ হোসেনকে ইংরেজদের স্বার্থে সমর্থন দিয়ে খিলাফতের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করেন। এ জঘণ্য অন্যায় কাজটি করতে অস্বীকার করায় গাদ্দার শরীফ হোসেন তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে মক্কায় গ্রেফতার করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়।
অন্য সব বিষয় নিয়ে কম-বেশী মতভেদ থাকলেও খিলাফত আন্দোলন নিয়ে মুসলিম শিক্ষাবিদদের মাঝে কোন প্রকার অনৈক্য ছিল না। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার বিখ্যাত পত্রিকা “আল হেলাল”-এ ১৯১২ সালের ২রা নভেম্বর সংখ্যায় নিজের অভিমত এভাবে ব্যক্ত করেছেন : “শুধু উসমানী খিলাফতের হাতেই এখন সেই তলোয়ার আছে যা মুসলিমদেরকে রক্ষা করতে পারে। খিলাফতই হচ্ছে শরীয়তের একমাত্র কর্তৃপক্ষ। এই ব্যবস্থা ওহির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করা আল্লাহ্’র নির্দেশ। খিলাফতের বিধি-বিধান মেনে চলা ফরয।”
এভাবে খিলাফত রক্ষার আন্দোলন ভারতময় ছরিয়ে পড়লেও ১৯২৪ সালে তুরস্কে উসমানী খিলাফতের পতনের পর এর ধারাবাহিকতায় এক প্রকার ভাটা পড়ে। তাছাড়া বৃটিশ শাসনের শেষের দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং দেশভাগের প্রশ্নে মতানৈক্য সৃষ্টির ফলে খিলাফতের চেতনা অনেকটাই হ্রাস পেয়ে যায়। যার কুপ্রভাবে উম্মাহ্ আজও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি।
পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলে ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা
বৃটিশদের কারসাজি এবং মুসলিম লীগের অপরিনামদর্শী তৎপরতার দরুন ভারত বিভক্তির পর পূর্ব-পাকিস্তান নামক অঞ্চলটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। একই রাষ্ট্রভূক্ত দুই অংশের দূরত্ব হয়ে যায় প্রায় ১৯৩২ কিলোমিটার। মাঝখানে থেকে যায় শত্রু রাষ্ট্র ভারত। ভৌগলিকভাবে শুধুমাত্র দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের বাকী তিন দিকই রয়ে যায় ভারতের বেষ্টনীতে। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনতা, অর্থনৈতিকভাবে শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণ, রাষ্ট্রের মূল নেতৃত্বের সাথে ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈপরিত্য ইত্যাদি সমস্যা ছাড়াও তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ইসলামী নেতৃবৃন্দের জন্য আরো অনেক সংকট দেখা দেয়। প্রথমত, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আশায় পাকিস্তান সৃষ্টির যুক্তি কোনভাবেই তাদের অনুকূলে যায়নি। কারণ শাসকরা প্রথম দিন থেকেই বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে পাকিস্তানকে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি ইসলামী দলেরই মূল নেতৃত্ব ও কেন্দ্র পড়ে যায় পশ্চিম-পাকিস্তানে। ফলে তাদের কর্ম চেতনায় বড় ধরণের ছন্দপতন ঘটে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির সময় এ অঞ্চলে মুসলিম লীগই ছিল প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল। আরও যে কয়টি দল তখন ইসলামী দল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী এবং নিখিল ভারত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম যা পরবর্তীতে নেজামে ইসলাম পার্টি নামে পুণঃর্গঠিত হয়। তাছাড়া পরবর্তীতে খেলাফতে রব্বানী নামের একটি দলও এখানে বেশ তৎপর ছিল। বর্তমানে অবশ্য এর অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই।
পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে এ বৈষম্যের ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। দিনে দিনে পুঞ্জীভূত এ বৈষম্যের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে ওঠে কতগুলো বড় বড় আন্দোলন। এগুলোর মধ্যে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ এর ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ এর মুক্তিসংগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব আন্দোলনের সময় পাকিস্তানপন্থী ইসলামী দলগুলোর নেতিবাচক আচরণে গণমানুষের অধিকার আদায়ে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে জনমনে তৈরী হয় বিভ্রান্তিকর আবহ। এই প্রসঙ্গে আমি ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ এর অভ্যুত্থান পর্যন্ত তৎপর কয়েকটি ইসলামী দলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।
মুসলিম লীগ
১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। প্রধানতঃ ইংরেজ শাসকদের অনুগ্রহ ভাজন উপমহাদেশীয় তথাকথিত প্রগতিশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দের সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নবাব ভিকারুলমূলক। সভায় নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাব অনুসারে সর্বসম্মতিক্রমে এই দলটির নাম রাখা হয় ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’। ভারতবর্ষে মুসলমানদের নিয়ে ইংরেজদের নীল-নকশা বাস্তবায়নের সহযোগী শক্তি হিসাবেই এ দলটি কাজ শুরু করে। বাহ্যত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও এ দলের প্রধান ভূমিকা ছিল জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদের চেতনাকে সংগঠিত করা।
কংগ্রেসের মত মুসলিম লীগেরও প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম ঘোষিত লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা। নওয়াব সলিমুল্লাহ নিজে ছিলেন ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার পক্ষপাতী। মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতারাও দাবী-দাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন জানানোর বাইরে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের কথা চিন্তা করেননি। ১৯০৬ সালের যে সম্মেলনে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েও সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ব্যারিষ্টার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তাঁর বক্তব্য ছিল কংগ্রেসের বাইরে নতুন আরেকটি সংগঠন সৃষ্টি করা হলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য বাড়বে। তাঁকে বলা হত হিন্দ-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত। পরে অবশ্য ব্যারিষ্টার জিন্নাহ কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দেন। শুধু তাই নয়, একজন ইসমাঈলী শীয়া হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুসলিম লীগের সভাপতির পদ লাভ করেন এবং তার সভাপতিত্বেই মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন করে।
বৃটিশ শাসনের শেষের দিকে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাবকে সর্বস্তরের মুসলিমদের নিকট গ্রহণযোগ্য করার জন্য এই দলের তৎকালীন নেতারা বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচার-পত্রের সাহায্যে ইসলামের বিজয়কে পাকিস্তান কায়েমের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। ‘পাকিস্তানের লক্ষ্য কি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’- এ ধরণের শ্লোগান তারা জনসম্মুখে তুলে ধরেন। তদানিন্তন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ স্বাক্ষরিত একটি প্রচারপত্রে ‘হুকুমতে ইলাহিয়া’ প্রতিষ্ঠাকে পাকিস্তান কায়েমের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়। এভাবে তারা মানুষকে বুঝায় যে, পাকিস্তান কায়েম হলেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে।
কিন্তু দেশ ভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে ইসলাম কয়েমের ধারে কাছেও হাঁটেনি। ক্ষমতা রক্ষা করাই হয়ে যায় তাদের একমাত্র আদর্শ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের শ্লোগানে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাই গঠিত হয় হিন্দু ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মন্ত্রীদের সমন্বয়ে।
ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের কান্ড দেখে দলটির স্বাধীনচেতা লোকেরা বেজায় ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠে। অনেকেই নবাব-জমিদারদের মুসলিম লীগ ছেড়ে একটি ‘জনগণের মুসলিম লীগ’ গঠনে উদ্যোগী হয়। সে অনুসারে আসাম থেকে আগত মুসলিম লীগ নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও টাঙ্গাইলের জনাব শামসুল হককে যথাক্রমে সভাপতি ও সেক্রেটারী করে ১৯৪৯ সনের ২৪ জুন ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ নামে নতুন আরেকটি দল গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী এই দলের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং তার অনুসারী শেখ মুজিবুর রহমান নিযুক্ত হন এর অন্যতম জয়েন্ট সেক্রেটারী। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ, এডভোকেট আতাউর রহমান খান প্রমুখ ব্যক্তিত্বও এই দলের সাথে সম্পৃক্ত হন। এ দলটির মাধ্যমেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে অঞ্চল-ভিত্তিক রাজনীতির এক নতুন ধারা সূচিত হয়। কিন্তু এর দ্বারা ইসলামের তো কোন উপকার হয়ইনি বরং এক সময় দলটির নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটিকেই উচ্ছেদ করে (১৯৫৫সালে) সম্পূর্ণ সেক্যুলার আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। এভাবেই মুসলিম লীগ সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনা থেকে বিরত রাখা হয়। ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আটশ’ বছর শাসন করার সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও হিন্দুদের হাতে ভবিষ্যতে মুসলমানদের স্বার্থ ভুলুন্ঠিত হওয়ার কাল্পনিক ভয় দেখিয়ে উম্মাহ্র মধ্যে জন্ম দেয়া হয় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের এক কূটিল চিন্তা। হুকুমতে ইলাহিয়ার নামে মনোমুগ্ধকর শ্লোগানের আবরণে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় বিশাল মুসলিম শক্তিকে। এদের ভুল রাজনীতি চর্চার পরিণতিস্বরূপ গোটা পরিস্থিতিই চলে যায় সেক্যুলারদের হাতের মুঠোয়।
অবশ্য ইসলামের নামে প্রতারণার দায়ে মুসলিম লীগও এ ভূখন্ডে জনগণের প্রচন্ড ক্ষোভের মুখে পড়ে। এতো জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসার মাত্র সাত বছরের মাথায় তারা একেবারে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে নির্বাচিত হয়। এতে মুসলিম লীগ শুধু ক্ষমতাচ্যুতই হয়নি বরং পূব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকেই উৎখাত হয়ে যায়।
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম
এটি মূলতঃ ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবী উলামাদের একটি দল ছিল। যারা ছিলেন শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এর ভাবশিষ্য। জেহাদে আযাদী নামে দীর্ঘ সংগ্রামের শেষের দিকে ১৯১৯ সালে এই দলটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। প্রথমে এর নামকরণ করা হয় ‘জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ’। শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীকে এই দলের সদর বা প্রধান নিযুক্ত করা হলেও তিনি তখন মাল্টা দ্বীপে বৃটিশদের হাতে বন্দী থাকায় মুফতী কেফায়েতুল্লাহকে ভারপ্রাপ্ত সদর ঘোষণা করে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। ইংরেজ শাসনের শেষপ্রান্তে এসে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বৃটিশ খেদাও আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলমান ও ইসলামের স্বার্থে ভারতকে অখন্ড রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পর এ অঞ্চলে জমিয়তের রাজনৈতিক তৎপরতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় তখন পূর্ব-পাকিস্তানে জমিয়তের শক্ত কোন সাংগঠনিক অবস্থানও ছিলনা। দলের প্রধান সারির নেতারা হয় ভারতের নাহয় পশ্চিম-পাকিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন। এর পাশাপাশি আরো দুটি কারণে জমিয়ত এখানে দুর্বল ছিল। এক, বৃটিশ শাসন অবসানের পর এই উপমহাদেশে পুর্ণাঙ্গ ইসলাম বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাদের কোন পরিকল্পিত কর্মসূচী ছিলনা। দুই, এই অঞ্চলে মুসলিম লীগের প্রাধান্য থাকার কারণে সাধারণভাবে জনমত গড়ে উঠেছিল ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান হওয়ার পক্ষে। ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী শক্তি হিসাবে জমিয়তের জনসম্পৃক্ততাও ছিল কম। পূর্ব-পাকিস্তানে এই দলটি অনেকটা সিলেটেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো এ দলটি শুধুমাত্র উলামা ও মাদরাসা ছাত্র-নির্ভর। জনসম্পৃক্ততা না থাকায় ‘৪৭ পরবর্তী সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানে জমিয়ত কেবল কিছু ধর্মীয় ইস্যুতে মিটিং-মিছিল ছাড়া সার্বিক রাজনীতি ও জাতীয় ইস্যুতে প্রভাব ফেলার মত কোন ভুমিকাই পালন করতে পারেনি।
নেজামে ইসলাম পার্টি
১৯৪৫ সালের ২৮ ও ২৯ অক্টোবর কলিকাতার মুহাম্মদ আলী পার্কে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সমর্থনে একটি উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম’ নামে একটি নতুন সংগঠন। এই নতুন জমিয়ত পাকিস্তান প্রশ্নে মুসলিম লীগের পক্ষ নেয়। কিন্তু দেশভাগের পর মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দের ওয়াদা ভঙ্গের ফলে নবগঠিত পাকিস্তানে ‘নেজামে ইসলাম’ তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুদূর পরাহত দেখে তারা নিরাশ হয়ে পড়েন। এক প্রকার প্রতারিত হয়েই ১৯৫২ সালে নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের সঙ্গ ত্যাগ করে ‘নেজামে ইসলাম পাটি’ নামে পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে ‘৫২ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার হযরত নগরে দলটির কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনেই মাওলানা আতহার আলী (রহ.) কে সভাপতি, মাওলানা সৈয়দ মুসলেহ উদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক এবং মাওলানা আশরাফ আলী ধর্মন্ডলীকে সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত করে ‘নেজামে ইসলাম পার্টি’র কার্যক্রম শুরু হয়। যে কোন মূল্যে পাকিস্তানে নেজামে ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে এই পার্টির প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়। এই একটি মাত্র কথার আকর্ষণ এবং মুসলিম লীগের তুলনায় এই দলের নেতৃতে বড় বড় উলামা থাকায় অল্পদিনেই নেজামে ইসলাম পার্টি একটি শক্তিশালী বৃহৎ দলে পরিণত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে প্রচলিত ধারায় রাজনীতি করা এবং সেক্যুলার রাজনীতির সহযোগী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হওয়ায় এই দল নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। এর প্রতিষ্ঠাতা নেতাগণ যথেষ্ঠ যোগ্য এবং ক্ষমতা সম্পন্ন আলিম হওয়া সত্বেও পশ্চিমা ধারার গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ বিহীন সংবিধান দ্বারা পরিচালিত সরকারে অংশ নিয়েছেন। অথচ এমনটি না করে গোটা পশ্চিমা ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবার মত জনসমর্থন এক সময় তাদের ছিল। কিন্তু এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি তারা পরিহার করেছেন। যার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এটি একটি নামে মাত্র দলে পরিণত হয়েছে।
যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচিত সরকারে নেজামে ইসলামের অংশ গ্রহণ
পশ্চিমা ধারার গণতান্ত্রিক নির্বাচন নেজামে ইসলাম বা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি না হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫৪ সালে নেজামে ইসলাম পার্টি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়। শুধু তাই নয়, এই নির্বাচনে তাদের এককালের পৃষ্ঠপোষক ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে অপরাপর বিরোধী দলগুলোর সমন্বয়ে একটি যুক্তফ্রন্টও গঠন করা হয়। এই ফ্রন্টে নেজামে ইসলাম পার্টি ছাড়া আরও যে সব দল ছিল সেগুলো হলো আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টি। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল ‘নৌকা’। যা বর্তমানে আওয়ামী লীগের পরিচয় চিহ্নে পরিণত হয়েছে। ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ২১-দফা দাবি সম্বলিত একটি নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। এর ভূমিকায় শুধু বলা হয় : ‘কুরআন ও সুন্নাহ-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না।’ ব্যাস এই নেতিবাচক কথাটুকু ছাড়া পুরো ইশতেহারে ইসলামের সপক্ষে কোন ইতিবাচক বক্তব্য ছিল না। এতেই প্রমাণ হয়ে যায় যে এই নির্বাচন নেজামে ইসলাম কায়েমের নির্বাচন ছিলনা। তবু নির্বাচন পরবর্তী কুরআন-সুন্নাহ বিহীন সংবিধান দ্বারা পরিচালিত সরকারে নেজামে ইসলাম পার্টি অংশ নেয় এবং মন্ত্রিত্ব লাভের সুবাদে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারনী ভূমিকা পালন করে। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে দলটির ৩৬ জন নেতা নির্বাচিত হন। জাতীয় পরিষদে সংসদীয় দলের নেতা ছিলেন দলীয় সভাপতি মাওলানা আতহার আলী (রহ.)। এডভোকেট মৌলভী ফরিদ ছিলেন কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী। প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকার ছিলেন আব্দুল ওহাব খান। এছাড়া আইন, ভূমি ও শিক্ষা মন্ত্রনালয়ও ছিল নেজামে ইসলাম পার্টির মন্ত্রীদের দায়িত্বে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী পরবর্তীতে নেজামে ইসলাম পার্টিতে যোগ দিলে তাকে দলের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়।
যুক্তফ্রন্টের সরকার ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী, দুর্বল এবং অন্তর্কলহে জর্জরিত। মাত্র ৫৭ দিনের মাথায় এসে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে এই সরকারের মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা হয়। এ ধরণের জোট ও সরকারে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নেজামে ইসলাম পার্টি তাদের মূল দাবী তো পূরণ করতে পারেইনি বরং এর পর থেকে তারা দ্রুত জনগণের আস্থা হারাতে শুরু করে। তবুও পরবর্তীতে ইসলামী দলগুলোর জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করা এবং সেক্যুলার সংবিধান দ্বারা পরিচালিত সরকারে অংশ নেওয়ার জন্য এসব ঘটনাবলী দলীল হয়ে দেখা দেয়।
জামায়াতে ইসলামী
এ দলটি গঠন করা হয় ১৯৪১ সালের ২৫ আগষ্ট। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী মাওলানা আবুল আলা মওদুদী। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জায়গায় ইসলামী হুকুমত বা আল্লাহ্’র আইনের কথা থাকলেও জামায়াতে ইসলামী তাদের ইতিহাসে কখনও ইসলামের একমাত্র শাসন ব্যবস্থা খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেনি। উল্টো তারা খিলাফতের দাবীকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে বিভিন্নভাবে। তাদের বই-পত্রে শিয়াদের মতো করে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তী খলীফাদের অনেকের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর সমালোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, খিলাফত আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করার জন্য খিলাফত শাসন ব্যবস্থা নিয়েও তারা অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করেছে এবং এখনও করছে।
১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের আগে পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী’র কোন সংগঠন ছিলনা। শুধু তাই নয় মাওলানা মওদুদীর পুস্তিকাদি উর্দূ ভাষায় লিখিত হওয়ায় এ অঞ্চলে তখন জামায়াতে ইসলামীর কোন পরিচিতিই ছিল না। আইডিএল ও ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুর রহীমই প্রথম ব্যক্তি, যিনি জামায়াতে যোগদান করে এই অঞ্চলে দলটির ভিত্তি স্থাপনে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নেন। তার প্রচেষ্টায় ১৯৪৬ সনে এই ভূখন্ডে জামায়াতের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর তিনি জীবনের যাবতীয় শক্তি একত্রিত করে জামায়াতকে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য এক পর্যায়ে তিনি জামায়াতের সাথে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।
রাজনৈতিক দল হিসাবে জামায়াত প্রথম থেকেই অন্যান্য ইসলামী দলের তুলনায় একটি মজবুত সংগঠন। কিন্তু ইসলামী চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতির দিক থেকে এর কোন স্থায়ী অবস্থান তৈরী হয়নি। দলটির আদর্শিক অস্থিতিশীলতা এবং পক্ষ পরিবর্তনের ধরণ বুঝার জন্য এতোটুকু জানাই যথেষ্ঠ যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপলাভের স্বার্থে এ পর্যন্ত জামায়াত মোট তেরবার গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করেছে। সর্বশেষ অক্টোবর ২০০৮ এ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন শর্ত রক্ষা করতে গিয়ে গঠনতন্ত্র থেকে তারা اقيمواالدين এবং ‘আল্লাহু আকবার’ খঁচিত মনোগ্রামটি প্রত্যাহার করে। শুধু তাই নয়, যে শ্লোগান দিয়ে এদেশের বহু তরুণকে তারা জীবন দিতে উৎসাহিত করেছিল, সেই ‘আল্লাহর আইন চাই’ কথাটিও নিবন্ধন লাভের জন্য তাদের গঠনতন্ত্র থেকে বাদ দেয়া হয়।
পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এ অঞ্চলে যে ধরণের ইসলামী দল আশা করে জামায়াত সব সময় নিজেকে সেই রঙে সাজাবার চেষ্টা করেছে। ইসলামী রাজনীতিকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মোড়ক লাগিয়ে পরিবেশন করা এবং সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার শাসকগোষ্ঠীর সাথে আঁতাতের মাধ্যমে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থাকে দীর্ঘায়ু করতে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এ দল। এ প্রসঙ্গে আমি তাদের ইতিহাস থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি।
১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করেন। এর মাত্র ২০ দিন পর সেনাপতি আইউব খান অস্ত্রের মুখে ইস্কান্দার মির্জাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে নিজে প্রেসিডেন্টের পদটি দখল করে নেন। শুরু হয় কঠোর দমন নীতি। দেশ জুড়ে নেমে আসে রাজনৈতিক নিস্তব্ধতা। ১৯৬২ সালের ১মার্চ আইউব খান আরেকটি নতুন সংবিধান জারী করে কয়েক মাসের মধ্যে সামরিক আইন তুলে নেয়। নতুন সংবিধানে দেশকে ‘ইসলামী প্রজাতন্ত্র’ বলা হলেও কুরআন-সুন্নাহ মুতাবেক আইন রচনার কোন অঙ্গীকার তাতে ছিলনা। ফলে দেশ জুড়ে ইসলামী সংবিধানের দাবীতে আইউব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু জামায়াত এই আন্দোলনের পরিবর্তে ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের’ নামে এক উদ্ভট আন্দোলন শুরু করে। এমনকি, এই ক্ষেত্রে সোহ্রাওয়ার্দীসহ দেশের ধর্মবিমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দলগুলোর সাথেও ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলে। এটিই ছিল জামায়াতের পক্ষ থেকে ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের’ প্রথম আন্দোলন এবং এভাবেই ইসলামী দাওয়াতের পরিবর্তে ‘গণতন্ত্র উদ্ধার’ করা জামায়াতের প্রধান কাজ হয়ে দেখা দেয়।
১৯৬২ সনে ডিক্টেটর আইয়ুব খান নতুন সংবিধানের মাধ্যমে ‘মৌলিক গণতন্ত্র’ (Basic Democracy) নামে দেশে এক আজব ‘গণতান্ত্রিক’ পদ্ধতি চালু করে। এর অধীনে ১৯৬৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দেশে একটা প্রহসনের নির্বাচন ডাকা হয়। জামায়াতসহ অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলো আইয়ুবের পাতা এই ফাঁদে সহজেই পা দেয়। শুধু তাই নয় এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রভৃতি দলের সমন্বয়ে সম্মিলিত বিরোধী দল COP নামে একটি মোর্চা গঠন করে। এই মোর্চা থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ’র বোন ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহের একমাত্র প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দেয়া হয়। উপমহাদেশে নারী নেতৃত্বের প্রতি এই প্রথমবারের মতো জামায়াতসহ কয়েকটি ইসলামী দলের সমর্থন ইসলামী রাজনীতিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এই ঐতিহাসিক ভুলটিকেই বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক ইসলামী দল নারী নেতৃত্বের অধীনে নির্বাচনী জোট ও সরকারে অংশ গ্রহণের দলীল হিসাবে ব্যাবহার করে থাকে। যদিও ইসলামে নারী নেতৃত্বের কোন অবকাশ নেই। সেদিনের সেই হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে জামায়াত ও তার শরীক দলগুলোর ইসলামী আন্দোলন যে কি তা মানুষের কাছে ম্পষ্ট হয়ে উঠে। তাই ১৯৬৫ সনের নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ’র চরম পরাজয় ঘটে। এর মাধ্যমে জামায়াত এক প্রকার কোনঠাসা হয়ে পড়ে।
এই পর্যায়ে এসে দলটি নতুন রূপ ধারণ করে। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট’ (PDM) নামে পুনরায় একটি জোট গঠন করে। জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবার আট-দফা দাবির ভিত্তিতে নতুন করে আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে যখন ৬ দফার ভিত্তিতে আইয়ুবের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে প্রচন্ড গণআন্দোলন শুরু হয়, তখন জামায়াত ৫ দফার নামে আরেকটি আন্দোলন শুরু করে প্রকারান্তরে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে ব্যহত করার চেষ্টা করে। তারা বার বার অন্যায়ভাবে ইসলামকে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। পশ্চিম পাকিস্তানের জালিম শাসকদের অনুকুলে চলে যায় তাদের অবস্থান। এটিই ছিল জামায়াতের জন্যে একটি গুরুতর রাজনৈতিক বিপর্যয়। এ থেকেই জামায়াত জনস্বার্থ বিরোধী একটি বিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হয়। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে তোলে।
১৯৭০ সনে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামী দল যৌথভাবে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বীতা করে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে একেবারে শূন্যের কোটায় নেমে আসে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) দলটির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়।
১৯৭১ সনে স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে জামায়াত নেতাদের ভুমিকার দরুণ এ অঞ্চলে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের যে ক্ষতি হয়েছে তা আজও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তারা পূর্বের সুবিধাবাদী আন্দোলনের ধারা বর্জন করেনি। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের পর বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জামায়াত বেগম খালেদা জিয়াকে সমর্থন দেয়। এরপর ১৯৯৫ সালে আরেক মহিলা নেত্রী আওয়ামীলীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঐক্য গড়ে তাদেরই সমর্থনে গড়া খালেদা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এভাবেই বরাবর অস্বচ্ছ ও ভুল পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছে যে, মুখে ইসলামের কথা বললেও রাজনৈতিক সুবিধার বিপরীতে ইসলামী স্বার্থ কখনই তাদের কাছে মূখ্য ছিল না।
এখানে একটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৬৪ সনের ৬ জানুয়ারী জামায়াতকে নিষিদ্ধ দল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এর আগে ১৯৫৭ সালে জামায়াত প্রথম বারের মত ভাঙ্গনের সন্মুখীন হয়। দলের অভ্যন্তরে এক তীব্র আদর্শিক সংকট মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ফলে মওলানা মওদূদী পদত্যাগ করেন। পরে অবশ্য তাকে পদে ফিরতে হয়। তবে ঐ সময় অনেকেই জামায়াত ছেড়ে চলে যায়।
১৯৭১ এর পর থেকে বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর অবস্থান
১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী সংগঠনগুলোর ইতিহাস যেমন গৌরবের নয়, তেমনি ১৯৭১ পরবর্তী বাংলাদেশের ইসলামী সংগঠনগুলোও গণ-আকাঙ্খার যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। মাঝখানে শুধুমাত্র মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর আহবানে ‘খেলাফত আন্দোলন’ নামে স্বল্প সময়ের জোয়ার ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া আর কোন আশার আলো দেখা যায়নি এ সময়ের ইসলামী দলগুলোর আচরণ থেকে। খেলাফত আন্দোলন ভাঙ্গনের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও স্বতন্ত্র কোন গতিপথ সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এসময়ে ইসলামী দলগুলোর মাঝে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পুঁজিবাদী শাসনের অংশীদার হওয়ার প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে সবচেয়ে বেশী। এমপি-মন্ত্রী হওয়ার লোভে নিজ আদর্শ ছেড়ে দিয়ে বড় দলের পিছনে চলার নীতি চালু হয়েছে ব্যাপকভাবে। ইসলামী ইস্যুকে ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাসক শ্রেণীর সাথে দর কষাকষি প্রকাশ্য রূপ লাভ করেছে। এইসব আচরণে ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত চেহারা আজ সকলের কাছে অপরিচিত হয়ে গেছে। অথচ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বৈরী পরিবেশে ইসলামী দলগুলো ভিন্ন এক অঙ্গীকার নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল। আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের সহযাত্রী হিসাবে বাংলাদেশে তৎপর ইসলামী দলগুলো সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো।
বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান ও ইসলামী রাজনীতি
১৯৭২ সনে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা হয়। সম্পূর্ণ সেক্যুলার দৃষ্টি ভঙ্গিতে রচিত এই সংবিধানের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার পরিকল্পিতভাবে এদেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করে। যদিও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামী’র ভূমিকা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল, তবুও এই অজুহাতকে ব্যবহার করে প্রথম থেকেই বাংলাদেশকে একটি ইসলামশূন্য রাষ্ট্রে পরিণত করার বিদেশী চক্রান্তের অংশ ছিল এই সংবিধান। সমাজতন্ত্রের তল্পীবাহক ডক্টর কামাল হোসেন ছিলেন এর অন্যতম রচয়িতা। মুজিব সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে ১৯৭২ সালের ৩০শে মার্চ এক বিবৃতিতে ডক্টর কামাল বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ন্যায় মৌলিক নীতিসমূহ বিদ্যমান থাকিবে।’ মূলতঃ এই চার নীতিমালার ভিত্তিতেই তৈরী হয় বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান। যার মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন মুসলিম প্রধান এই দেশটিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজনীতি করার পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।
সংবিধান পরিবর্তন ও বিসমিল্লাহ’র রাজনীতি
ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বাংলাদেশকে ইসলামী সভ্যতাশূন্য করার আওয়ামী দুঃসাহস ১৯৭৫ সালে এসে আরও ভয়াবহ রূপ লাভ করে। এক তরফা নির্যাতন চালাবার প্রয়াসে সব দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে চালু করা হয় এক দলীয় বাকশালী শাসন। এই জুলুম বেশী দিন টিকেনি। ‘৭৫ এর ১৫ আগষ্ট পট পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতারও পরিবর্তন হয়। দৃশ্যপটে আসেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বারের মত চালু করা হয় সামরিক শাসন। এরপর ১৯৭৭ সনের শুরুতে জিয়াউর রহমান সংবিধানে একটি সংশোধনী আনেন। যার মধ্যে থাকে বিসমিল্লাহ’র সংযোজন। আর উল্লেখ থাকে ‘আল্লাহ্’র উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থাই হবে সংবিধানের মূল ভিত্তি।’ এতেই তৎকালীন ইসলামী দলগুলো জিয়াউর রহমান এবং তার জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে ইসলামের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এরপর থেকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী আদর্শের বিপরীত অবস্থানে থাকা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাঁবেদার হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র একটি কুফুরী সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহ’ জড়াবার রাজনীতি দিয়েই জিয়া ও তার বিএনপি এদেশের ইসলামী শক্তির অভিভাবকের মর্যাদা দখল করে নেয়। আর কিছু কিছু ইসলামী দল হয়ে যায় বার বার বিএনপিকে ক্ষমতায় আনার বাহন। যেন এ দলগুলোর আদর্শই হচ্ছে ইসলামী রাজনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে বিএনপির জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সেবা করা।
জামায়াত যেভাবে পুনর্বাসিত হয়
একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, জেনারেল জিয়াউর রহমান ইসলামী রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ইসলামী দলগুলোর জন্য কিছুটা অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই জামায়াত নেতারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হওয়ার চেষ্টা শুরু করে। তবে মাওলানা আবদুর রহীম এবার আগের মতো পুরাতন দলের নামে কাজ করতে রাজী ছিলেন না। তাই তিনি আগের দলগুলোর সমন্বয়ে একটি সম্মিলিত ইসলামী দল গঠনের উদ্যোগ নিলেন। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে জামায়াতসহ তৎকালীন কয়েকটি ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে এই ভাষায় অঙ্গিকার করেন যে, “আমরা অধুনালুপ্ত কতিপয় ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ আল্লাহ্’কে হাজির নাজির জেনে এই অঙ্গীকার করছি যে, আমরা অতীতের পরিচিতি ভুলে সম্পূর্ণ নতুন নামে একটিমাত্র ইসলামী দল গঠন করব।” এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সাবেক জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, খেলাফতে রব্বানী, পিডিপি, বিডিপি, আইডিপি ও ইমারত পার্টিসহ মোট সাতটি দল নিয়ে ‘ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ’ (IDL) নামে একটি নতুন দল গঠন করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পর রাজনৈতিক দূর্দিন কেটে গেলে জামায়াত নেতারা আল্লাহ্’র নামে নেয়া শপথ ভঙ্গ করে পুনরায় জামায়াতে ইসলামী দলের নামে এ দেশে রাজনীতি শুরু করে। এভাবেই জামায়াত স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ইসলামী রাজনীতিতে অনৈক্যের সূচনা করে এবং ১৯৮০ সনে আইডিএল ভেঙ্গে পূর্বনামে পুনুরুজ্জীবিত হয়।
মাওলানা আবদুর রহীম এবার আর জামায়াতের রাজনীতির সাথে একাত্ম হননি। তিনি ১৯৮৪ সালের ৩০ শে নভেম্বর আইডিএলকে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন নাম দিয়ে নতুন গতিতে রাজনীতি শুরু করেন।
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
১৯৮১ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রবীণ আলেম মওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন ব্যক্তিত্ব রূপে আবির্ভুত হন। তাঁর ‘তওবার রাজনীতি’র ডাক দেশের রাজনীতি বিমূখ ইসলামী মহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ তার ছাত্র-শিষ্যদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ এ ডাকে সাড়া দিয়ে অচিরেই সামনে এগিয়ে আসেন। তাদেরকে নিয়েই তিনি ১৯৮১ সনের ২৯ নভেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক শায়েস্তা খান হলে ‘খেলাফত আন্দোলন’ নামে একটি সংগঠনের কার্যক্রম ঘোষণা করেন। প্রায় ৫০ বছর পর খেলাফত আন্দোলনের নামে এ অঞ্চলে আবার সৃষ্টি হয় এক অভাবনীয় ঐক্যের জোয়ার। স্বাধীনতার পর এই প্রথম উলামাদের মাঝে তৈরী হয় নতুন প্রাণচাঞ্চল্য। ইতি পূর্বে অনেকের মাঝে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, ইসলামে কোন রাজনীতি নেই। তাছাড়া পাকিস্তান হওয়ার পর খিলাফত কায়েমের সুনির্দিষ্ট দাবীতে এ অঞ্চলে কোন আন্দোলন না থাকায় জাতিগতভাবে সকলেই এই গুরুত্বপূর্ণ ফরযটি তরক করার গুনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। হজরত হাফেজ্জী হুজুর এ জন্য জাতিগত ভাবে সকলের প্রতি তওবার আহ্বান জানান। মূলতঃ গায়রুল্লাহর প্রবর্তিত প্রতারণার রাজনীতি থেকে আল্লাহ্’র প্রবর্তিত সততার রাজনীতিতে প্রবর্তনের নাম দেয়া হয়েছিল তওবার রাজনীতি।
খেলাফত আন্দোলনের গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছ, খেলাফত আন্দোলন কোন পার্টি নয়, এটি একটি আন্দোলন। দল-মত ও দেশকালের উর্ধ্বে থেকে গোটা মানব মন্ডলীকে আল্লাহ্’র যমীনে আল্লাহ্’র খেলাফত কায়েমের ডাক দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।
কয়েক বছরের মাথায় হযরত হাফেজ্জী হুজুরের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তার বিবেচনায় তাঁকে কেন্দ্র করেই দেশের ছোট বড় এগারটি সংগঠন ও কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিককে নিয়ে ‘খিলাফত কায়েমের লক্ষ্যে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ’ নামে একটি বৃহত্তর মোর্চা গড়ে উঠে। হাফেজ্জী হুজুরের বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, মাওলানা আব্দুর রহীমের ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, মেজর (অব.) এম এ জলীলের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি সংগঠন এ মোর্চাকে জনগণের আশা-আকাঙ্খার কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত করার লক্ষ্যে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন।
১৯৮২ সনের মার্চে সেনাপ্রধান এরশাদ বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখল করলে হাফেজ্জী হুজুর তার বিরুদ্ধে প্রচন্ড আন্দোলন গড়ে তোলেন। তবে জামায়াত এ সময় স্বৈরাচারের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। ১৯৮৬ সনে এরশাদ যখন তার স্বৈরশাসন দীর্ঘায়িত করতে পাতানো নির্বাচনের ব্যবস্থা করে, তখন এ নির্বাচনকে বৈধতা দেয়ার জন্য জামায়াত বিএনপির সঙ্গ ত্যাগ করে আওয়ামী লীগের অনুসরণে নির্বাচনে অংশ নেয়।
বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টিকরে খিলাফত কায়েমের লক্ষ্যে গঠিত ‘সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ’ তাদের ঐক্য বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি। ফলে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে বাংলাদেশে খিলাফতের রাজনীতি যে আশার আলো ফুটিয়েছিল তাও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। ১৯৮৫ সনে হযরত হাফেজ্জী হুজুরের জীবদ্দশায় তারই শিষ্য শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক হাফেজ্জীর নেতৃত্বাধীন দল থেকে বের হয়ে নিজ নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন (আ-গা) নামে আরেকটি দল গঠন করেন। এ দলটিই ১৯৮৯-এর ১২ অক্টোবর যুব শিবিরের সাথে একাকার হয়ে খেলাফত মজলিস নামে নতুন দল হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। উল্লেখ্য ১৯৮২ সনে অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদেরের নেতেৃত্বে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির থেকে বের হয়ে আসা একটি অংশ যুব শিবির নামে কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল।
ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
এই দলটি একক কোন রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করেনি। বরং অনেকগুলো ইসলামী দলের সমন্বয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরে অবশ্য এই ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এটি একটি একক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।
১৯৮৭ সনে তদানিন্তন সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট আলিম, পীর-মাশায়েখ এবং ইসলামী রাজনীতিবিদ অনুভব করলেন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – চরমোনাই’র পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম, শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক, ঐক্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুর রহীম, জামায়াতের মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, ব্যারিস্টার মাওলানা কোরবান আলী, আওলাদে রাসূল মাওলানা আবদুল আহাদ মাদানী, তৎকালীন যুব শিবিরের সভাপতি অধ্যাপক আহম্মদ আব্দুল কাদের প্রমূখ। ঐক্যের জন্য পবিত্র কুরআন ছুঁয়ে তারা কঠিন শপথ করলেন। সিদ্ধান্ত হলো ১৯৮৭ সালের ৩ মার্চ, সকলের উপস্থিতিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হবে এবং এই ঐক্য প্রক্রিয়ার অন্যতম উদ্যোক্তা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ঘোষণাপত্র পাঠ করবেন। কিন্তু সেদিন সম্মেলনস্থলে গিয়ে জানা গেল ঐক্যবদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের উদ্যোক্তা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী দেশ ছেড়ে উধাও হয়ে গেছেন। তিনি নাকি নিজ দল জামায়াতের চাপে ইতিমধ্যেই পাড়ি জমিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যে। কারণ জামায়াতে ইসলামীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে আরো কোন শক্তিশালী ইসলামী ব্লক গড়ে উঠুক, এটা নাকি জামায়াত নেতারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। যাই হোক নির্ধারিত দিনেই ঢাকাস্থ মতিঝিলের হোটেল ‘শরীফস ইনে’ অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন পীর সাহেব চরমোনাই। ১৩ মার্চ ১৯৮৭ ছিল জনসম্মুখে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আত্মপ্রকাশের দিন। এ উপলক্ষে আয়োজিত শাপলা চত্বরের সমাবেশে এরশাদ সরকারের পুলিশী আক্রমণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চেতনাকে আরো শানিত করে। কিন্তু কিছুদিন পর এরও একই পরিণতি ঘটে। অনৈক্য। ভাঙ্গন। হতাশা।
১৯৮৭ সনের ১ অক্টোবর মাওলানা আব্দুর রহীম ইন্তেকাল করেন (ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এরপর ‘৯১এর জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়া না নেয়ার প্রশ্নে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্যারিস্টার মাওলানা কোরবান আলীর নেতৃত্বে একটি অংশ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে থেকে যায়, আর হাফেজ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকটি অংশ এ ঐক্য থেকে বের হয়ে যায়। অন্য দিকে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হকের নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলন (আ-গা) এবং ইসলামী যুব শিবিরও এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ১৯৮৯-এর ১২ অক্টোবর খেলাফত আন্দোলন (আ-গা) ও যুব শিবিরের এক যৌথ বৈঠকে খেলাফত মজলিস নামে নতুন দল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন চরমোনাইর পীর সাহেবের নেতৃত্বাধীন একটি একক দলে পরিণত হয়।
২০০১ এর নির্বাচনে জাতীয় স্বার্থের ঠুনকো দোহাই দিয়ে যখন অনেক ওলামা ও ইসলামী দল নারী নেতৃত্বের অধীনে জোটবদ্ধ নির্বাচনে অংশ নেয়, তখন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন জামায়াত-বিএনপি’র সাথে না হলেও এরশাদের সাথে ঠিকই নির্বাচনী জোট বাঁধে। এ দলটি অন্য ইসলামী দলের তুলনায় কিছুটা স্বকীয় অবস্থানে থাকলেও প্রচলিত পদ্ধতির গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বাহিরে থেকে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করতে পারেনি। অবশেষে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন লাভের জন্য ২০০৮ এর অক্টোবরে বহু ঘটনার জন্ম দিয়ে তৈরী হওয়া ‘ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন’ তাদের নাম পরিবর্তন করে ‘ইসলামী আন্দোলন’ নাম ধারণ করে।
ইসলামী ঐক্যজোট
১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর একটি স্মরনীয় গণআন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে ৷ এরপর ১৯৯১ সনের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসলামী ঘরানায় চালু হয়ে যায় ভিন্ন রকম হিসাব-নিকাশ। নতুন করে তৎপর হয়ে ওঠেন ইসলামী জগতের ঐ সকল কুশীলবগণও যারা সদ্য হযরত হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলন থেকে বের হয়ে এসেছেন। এর মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হাফেজ্জী হুযুরের জামাতা মুফতী ফজলুল হক আমিনী। যিনি হাফেজ্জীর ইন্তেকালের পর (১৯৮৭) খেলাফত আন্দোলন ত্যাগ করে ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হন। খিলাফত ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গঠন ও গণবিপ্লব সৃষ্টির পরিবর্তে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের উচ্চাভিলাষ থেকে তিনি এবং অন্যান্য কয়েকটি ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ মিলে একটি ইসলামী ঐক্যজোট গঠন করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, তখন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া তো সম্ভব হয়ই নি, বরং নির্বাচন চলাকালেই এই ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য অনেকেই নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, দেশের মাদরাসাগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করা এবং ক্ষমতাসীনদের সাথে দর কষাকষির হাতিয়ার হিসাবে এই নামটিকে ব্যবহার করেছেন। এই প্রবণতা বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতিতে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি ধারার জন্ম দেয়, তা হলো ইসলামী আদর্শের তোয়াক্কা না করে প্রচলিত পুঁজিবাদী রাজনীতির সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এর ফলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বতন্ত্র ভাবধারা এবং সঠিক রাজনীতি ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়।
১৯৯১ সনে গঠিত বিএনপি সরকারের দলীয় করণ ও দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার ফলে ১৯৯৬ এর নির্বাচনে ইসলাম বিদ্বেষী আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসে। এরপর ইসলামের উপর একের পর এক আঘাত আসতে থাকে। আওয়ামী সরকারের দুঃশাসন, ইসলাম ও ওলামা বিদ্বেষী আচরণ ইসলামী দলগুলোকে আবারও ঐক্যবদ্ধ করার পরিবেশ তৈরী করে দেয়। কিন্তু কিছু কিছু নেতার অতীত ভূমিকা অভিজ্ঞজনদেরকে এই ঐক্যে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। তদুপরি ২০০১ সনে মহিলা নেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপির অধীনে চারদলীয় জোটে থাকা না থাকাকে কেন্দ্র করে ইসলামী ঐক্যজোটে আরেক দফা ভাঙন দেখা দেয়। শাইখুল হাদীস ও আমিনীর নেতৃত্বে খেলাফত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী মোর্চা প্রভৃতি দল বিএনপি ও জামায়াতের সাথে চার দলীয় জোটভূক্ত হয়ে নির্বানে অংশ নেয়। আর ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন জোট বাঁধে এক কালের স্বৈরশাসক এরশাদের সাথে। নির্বাচনোত্তর খালেদা জিয়ার সরকারে মন্ত্রিত্ব পাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে ঐক্যজোটের ঘনিষ্টতা একেবারে খানখান হয়ে যায়। মুফতী ফজলুল হক আমিনী শাইখুল হাদীস আজীজুল হকের পরিবর্তে নিজেকে ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ঘোষণা করলে শাইখুল হাদীস খেলাফত মজলিস নিয়ে ঐক্যজোট থেকে বের হয়ে আসেন। এরপর থেকে এই দলটি একাই নিজেদেরকে ইসলামী ঐক্যজোট বলে দাবী করতে থাকে। এদিকে সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রতিযোগীতার দ্বন্দে ঐক্যজোট আমিনী অংশের নতুন মহাসচিব নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরীকে জোট থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ নিয়ে ভেঙ্গে যায় নেজামে ইসলাম পার্টি। নতুন নেজামে ইসলাম পার্টি ঘোষণা করে মুফতী ইজহারুল ইসলামও নিজেকে ঐক্যজোটের নেতা বলে দাবী করেন। মিসবাহুর রহমান নামে এক হকার নেতাকে মহাসচিব নিযুক্ত করার কয়েকদিন যেতে না যেতে সেও বিদ্রোহ করে মুফতী ইজহারের সাথে। ইজহারের জোট ভেঙে সে তার দলের নাম দেয় বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট। অন্যদিকে নেতৃত্বের কোন্দলে পড়ে ভেঙে যায় খেলাফত মজলিস। ২০০৫ সনের ২২ মে শাইখুল হাদীসের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে আহমদ আব্দুল কাদির তার পুরাতন যুব শিবিরের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আরেকটি খেলাফত মজলিসের জন্ম দেয়।
এমতাবস্থায় মুফতী আমিনী চারদলীয় জোটে ইসলামী ঐক্যজোটের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই নব গঠিত খেলাফত মজলিসের নামই ব্যবহার করতে থাকেন। এরই মধ্যে ঘটে যায় আরেক ভয়াবহ ঘটনা। স্মরণ কালের সকল ইতিহাস ব্রেক করে মুফতী ইজহার ফুলের তোড়া দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বরণ করে নেন। আর ২০০৬ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর শাইখুল হাদীস নেতৃত্বাধীন খেলাফত মজলিস পাঁচ দফা চুক্তির ভিত্তিতে চির শত্রু আওয়ামীলীগের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দেয়। এভাবে ক্ষণিকের ক্ষমতা লোভী কতিপয় নেতার আচরণ বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনকে ভাবগাম্ভীর্যহীন একটি ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত করে।
ফলাফল বিশ্লেষণ
গত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস একথা প্রমাণ করেছে যে, এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমান্বেয়ে জোরদার হওয়ার পরিবর্তে অধঃগতির দিকেই ধাবিত হয়েছে বেশী। গণবিপ্লবের মাধ্যমে বস্তুবাদী রাজনীতির পশ্চিমা ধারার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবার যাবতীয় উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলন এখানে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে পারে নি। এর কারণ হিসেবে যে সব বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে তা নিন্মরূপ:-
ক. চিন্তাগত দুর্বলতার দরুন ইসলামকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে তুলে ধরতে না পারা। আভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক এবং বিশ্ব রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য পূর্ববর্তী উলামাগণ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করাকে যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, গত ৫০ বছরের রাজনীতিতে সামগ্রিকভাবে বিষয়টির সে ধরণের গুরুত্ব বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়া।
খ. পদ্ধতিগত ভুলের দরুন বার বার পুঁজিবাদী শত্রুর ছকে তৈরী করা তথা কথিত গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতির স্রোতে গা ভাসিয়ে আপোষমূলক প্রবণতায় জড়িয়ে যাওয়া।
গ. রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে খিলাফত শাসনের প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতার চিন্তার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়া।
ঘ. ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে ইসলামের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার পরিবর্তে একটি বিশেষ শ্রেণীর মাঝে এর আংশিক চর্চা করা এবং প্রকৃত সংগঠন বলতে যা বুঝায় তা গঠন না করে শুধুমাত্র মাদরাসার ছাত্র দিয়ে অনিয়মিত আন্দোলন করা।
ঙ. একদিকে নিজেরা বিশ্ব রাজনীতির গতিবিধি লক্ষ্য রেখে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া অন্যদিকে এ ধরণের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ ও ভিশন তুলে ধরতে না পারা।
চ. ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ না করে ব্যক্তি কেন্দ্রীক দল গঠনের প্রবণতা এবং ব্যক্তির ইমেজ দিয়ে আবেগময়ীতার জন্ম দেয়া। পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার শক্তিগুলোর বিপরীতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে তাদের রাজনীতি অনুসরণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া।
ছ. গণমুখী ও ইতিবাচক রাজনীতি দিয়ে জনস্বার্থের পক্ষে শক্ত ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জনের পরিবর্তে বিশেষ ঘটনাবলী ও ইস্যুর মাঝে ইসলামী রাজনীতিকে সীমাবদ্ধ রাখা।
জ. সর্বোপরি লক্ষ্যহীন পথ চলা, অপরিনামদর্শী বাগাড়ম্বর, ক্ষণিকের সুবিধাভোগের লোভে আদর্শ বিবর্জিত হয়ে সেক্যুলার দলগুলোর সাথে গাঁটছড়া বাধা ইত্যাদি কারণে জনসমর্থন হারানো।
এই ছিল গত অর্ধ শতাব্দী ধরে চলা এ অঞ্চলের ইসলামী রাজনীতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা’আলা আমাদেরকে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন
মাওলানা মামুনুর রশীদ
২০০৮

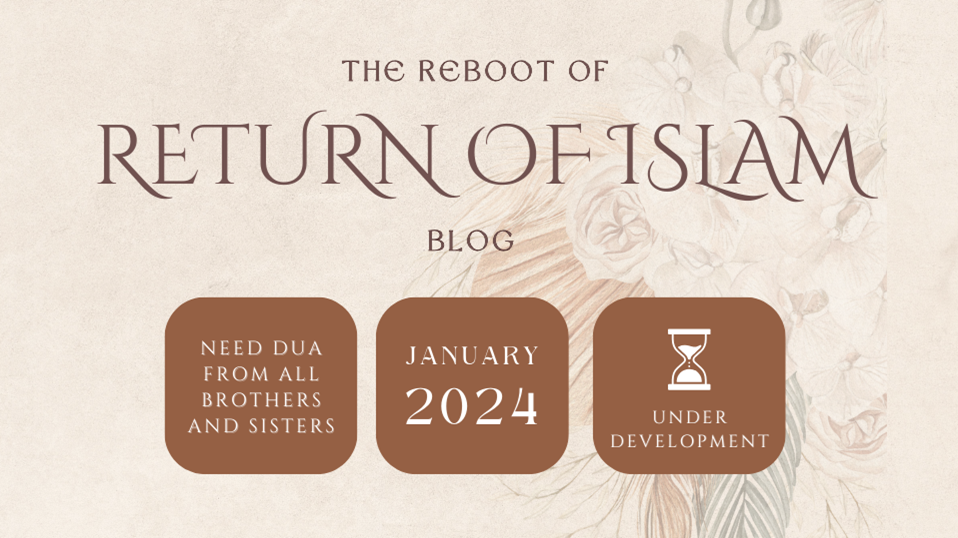















 Users Today : 25
Users Today : 25 Total Users : 18411
Total Users : 18411 Total views : 91811
Total views : 91811