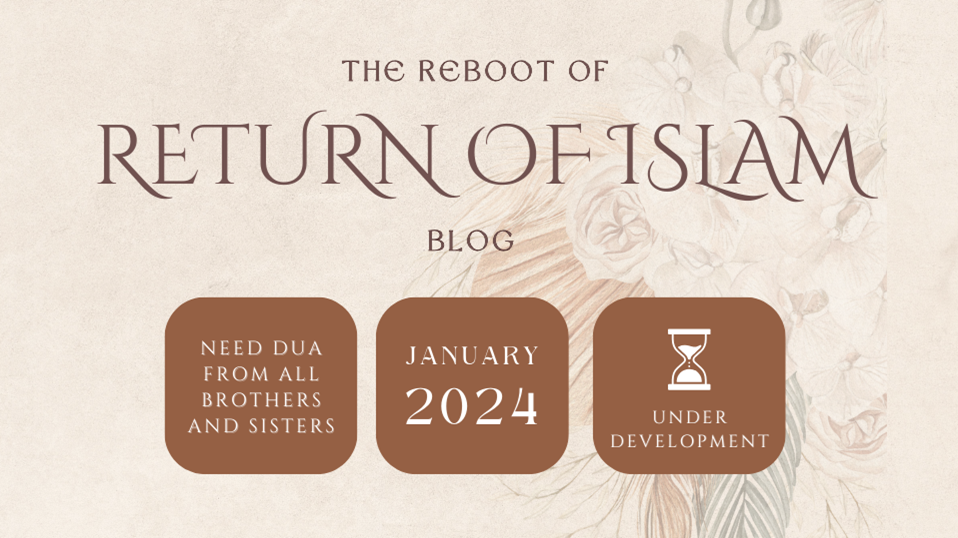ফিকহ এর সংজ্ঞা:
প্রখ্যাত অভিধান বিশারদ আল্লামা আবুল ফযল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ আল মিসরী (রহ) বলেন,
“ফিকহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কোন কিছু সম্বন্ধে জানা ও বুঝা।” [লিসানুল আরব]
‘ফিকহ’ শব্দটি আল কুরআনে বিশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। (ফাতাওয়া ও মাসাইল. ১ম খন্ড, ইফাবা প্রকাশিত) যেমন,
“তাদের (মুমিনদের) প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বহির্গত হয় না যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে ফিকহ হাসিল করতে পারে (লি ইয়াতাফাক্বাহু ফিদ-দ্বীন) এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে- যাতে তারা সতর্ক হয়”। (সূরাই তওবা : ১২২)
হাদীসেও এই শব্দটি বহুল ব্যবহৃত যেমন-
“আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের ফিকহ (তাফাক্কুহ ফিদ-দ্বীন) দান করেন”। (বুখারী, মুসলিম)
“একজন ফকীহ শয়তানের জন্য হাজার (মূর্খ) আবেদ অপেক্ষা ভয়ংকর” (তিরমিযি) ইত্যাদি।
অতএব, আভিধানিক অর্থে ‘ফিকহ’ বলতে যে কোন বিষয়ের গভীর জ্ঞানকে বোঝালেও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ও বিভিন্ন হাদীসে ‘ফিকহ’ বলতে সুনির্দিষ্ট ভাবে দ্বীনের গভীর জ্ঞানকেই বোঝানো হয়েছে। প্রথম যুগে ‘ফিকহ’ বলতে তাই ইসলামী জ্ঞানের বিশেষ কোন শাখাকে বোঝানো হতো না বরং সামগ্রিকভাবে গোটা দ্বীন সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানকে বোঝানো হতো। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বীনের প্রতিটি শাখা স্বতন্ত্র ভাবে বিস্তৃত ও বিকশিত হতে থাকলে ‘ফিকহ’ শব্দটি কুরআন-সুন্নাহ থেকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের হুকুম আগরনের যে বিজ্ঞান কেবল তার জন্যই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। অতএব, ইসলামী শরীয়াই’র পরিভাষায় ‘ফিকহ’ হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের সেই বিশেষ শাখা যা শরীয়াহ’র প্রামান্য উৎস থেকে শরীয়াহ’র শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত বিধি বিধান আহরন বা ইস্তিম্বাত (إستنباط) করে। তাই ইমাম শাফিঈ (রহ) ফিকহের সংজ্ঞায় বলেন,
“শরীয়াহ’র বিস্তারিত প্রামাণাদি থেকে ব্যবহারিক শরীয়াহ’র বিধি-বিধান সম্পন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়” [আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু]
সংক্ষেপে বলা যায় ‘ফিকহ’ হচ্ছে ইসলামী আইন কানুন এবং এ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। এই হচ্ছে ফিকহের সংজ্ঞা। আর এ ইলমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যা তা হলো দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সাফল্য অর্জন। এ অর্থেই ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেছেন,
“ফিকহ হচ্ছে নফস এর পরিচয় লাভ করা তথা কি কি তার অনুকূলে (কল্যাণকর) এবং কি কি তার প্রতিকূল (ক্ষতিকর) সে সম্বন্ধে জ্ঞান”।
এখানে জ্ঞানীগণ নফসের অনুকূলে ও প্রতিকূলের অর্থ করেছেন “যার সাহায্যে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ অর্জন করে আর যার কারণে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। [ঐ]
শীর্ষস্থানীয় ইমামদের মতে এই হলো ’ফিকহ’ এর সংজ্ঞা আর এই হলো তার উদ্দেশ্য। ফিকহ এর আলোচ্য বিষয়গুলোকে নিম্নোক্ত বিভাগগুলোর অধীনে বিবেচনা করা যায়:
ইবাদত : যা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের নিয়ম কানুন বলে দেয়। যেমন- সালাত, সওম, হজ্জ্ব ইত্যাদি।
মু’আমালাত : সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিবিধান। যেমন- কেনাবেচা, ঋণ, ভাড়া, আমানত, জামানত ইত্যাদি।
মানাকিহাত : মানবের বংশ রক্ষা সংক্রান্ত বিধিবিধান। যেমন- বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।
উকুবাত : বিভিন্ন অপরাধ। যেমন- চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তি, যেমন- মৃত্যুদন্ড, রক্তপণ ইত্যাদি।
মুখাসামাত : আদালতি বিষয়ে। যেমন- অভিযোগ, বিচারবিধি, স্বাক্ষ্য প্রমাণ ইত্যাদি।
হুকুমাত ও খিলাফত : শাসক নির্বাচন, বিদ্রোহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জিহাদ, সন্ধি, চুক্তি, কর আরোপ ইত্যাদি।
যেহেতু ‘ফিকহ’ এর মূল উৎস হচ্ছে মানুষের প্রতি শরীয়ত প্রনেতা (অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা)’র আদেশ নিষেধ সম্বলিত বাণী, অতএব তাত্ত্বিকভাবে বলা যায় যে, নবুয়্যত প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (সা) এর মক্কী জীবন থেকেই ফিকহ এর যাত্রা শুরু। কিন্তু বস্তুতঃ, মক্কী জীবনে পবিত্র কুরআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নাযিল হলেও তার খুব সামান্য অংশই ছিল বিধি বিধান সম্বলিত এবং প্রায় সবটুকুই ছিলো দ্বীনের মৌলিক বিষয় বা আকীদা অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, পরকাল, জান্নান, জাহান্নাম এবং দ্বীনের প্রচার সৎগুনাবলীর বিকাশ, সামাজিক কু-প্রথাগুলোর নিন্দা ইত্যাদি বিষয়ে। আহকাম সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত আয়াতই তাঁর(সা) মদীনায় হিজরত করার পর থেকে নাযিল হতে থাকে এবং মাদানী জীবনের দশ বছরব্যাপী তা চলতে থাকে। অতএব, আমাদের জন্য এটা বলাই অধিকতর যথার্থ হবে যে, ফিকহের শুরু বা উৎপত্তি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মাদানী জীবনের শুরু থেকে অর্থাৎ প্রথম হিজরী সন হতে। [আস-শাকসিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ]
‘ফিকহ’ এর বিকাশ:
এটি একটি বিস্তৃত বিষয় এবং এই নিবন্ধে আমরা কেবল এর সংক্ষিপ্ত কিছু ধারণা-ই দিতে পারবো। উৎপত্তিকাল থেকে শুরু করে ‘ফিকহ’ এর ক্রমবিকাশকে প্রধান তিনটি পর্যায় বা যুগে ভাগ করা যায়।
১. রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগ:
এ যুগের সময়কাল হচ্ছে রাসূলূল্লাহ (সা) এর মদীনায় হিজরত তথা ১ম হিজরী সাল হতে তাঁর ওফাতের সময় অর্থাৎ ১০ম হিজরী সাল পর্যন্ত। এ যুগে ফিকহের যাবতীয় বিষয়ই সরাসরি তাঁর (সা) এর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর (সা) কাছে ছিল নাযিলকৃত প্রত্যক্ষ্য ওহী আল-কুরআন আর পরোক্ষ ওহী যা হাদীস রূপে আমাদের কাছে এসেছে। যেকোন বিষয়ে আইন প্রনয়ণ, উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফতওয়া, ফারাইয, দ্বীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, কুরআনের হুকুম আহকামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই ওহীর মাধ্যমে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন, সাহাবা (রা) দের তা শিক্ষা দিতেন এবং বাস্তবে সমাজে প্রয়োগ করে দেখাতেন। সে সময় স্বতন্ত্র ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। তথাপি, পরবর্তী যুগের ফিকহ শাস্ত্রের সব মৌলিক বিষয়ের গোড়াপত্তন এ যুগেই হয়েছিল। এমনকি, ফিকহের গতিশীলতার প্রধান উপকরণ যে ‘ইজতিহাদ’ ও ‘কিয়াস’ তার শিক্ষাও এ যুগেই। এ বিষয়ে অনেক সহিহ হাদীস বিদ্যমান।
রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুআয ইবনে জাবাল (রা) কে ইয়েমেনের গভর্ণর করে পাঠানোর সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুআয! তুমি কীসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? (كَيْفَ تَقْضِي) তিনি বললেন, “আল্লাহ’র কিতাব দিয়ে (أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ), তিনি (সা) বললেন, “যদি আল্লাহ’র কিতাবে তা না থাকে?” (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ) তিনি বললেন, “তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত দিয়ে” (فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ), তিনি (সা) বললেন, “যদি রাসূলের সুন্নতে তা না থাকে?” (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ) তিনি বললেন, “তখন আমি ইজতিহাদ করে ‘রায়’ দিবো।” (أَجْتَهِدُ رَأْيِي) তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যাতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ‘সন্তুষ্ট’ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ) [আহমদ] – এটি ইজতিহাদের বৈধতা প্রমাণে ব্যাপক ব্যবহৃত একটি হাদীস। অন্য রেওওয়াতে রয়েছে যে, “হযরত মুআয (রা) ও আবু মূসা আশ’যারী (রা) কে ইয়ামেনে কাযী হিসেবে প্রেরণ করার সময় অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেছিলেন, “সুন্নতে কোন নির্দেশ না পেলে আমরা (উদ্ভুত বিষয়টি) একটি বিদ্যমান সাদৃশ্য বিষয়ের উপর কিয়াস করবো এবং যা সত্যের নিকটবর্তী তার উপর আমল করবো”। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “তোমাদের উত্তর সঠিক হয়েছে”।
সাহাবা (রা) কে তিনি (সা) কিয়াসের মাধ্যমে ইজতিহাদের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। যেমন: উমর (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কে স্ত্রীকে চুম্বনের কারনে রোজা ভঙ্গ হবে কিনা তা জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি (সা) বললেন, “তুমি যদি কুলি কর তাতে কি রোজা ভঙ্গ হবে?” [ইবনে হাযম, ইহকাম] এখানে রাসূলুল্লাহ (সা) উমর (রা)-কে কিয়াস বা সাদৃশ্যমূলক তুলনার মাধ্যমে রোজাদারের চুম্বন ও কুলি করার মিল বোঝালেন এবং দেখালেন যে ওটার মতো এটাও রোজা ভঙ্গ করবে না।
এর পাশাপাশি তিনি সাহাবা (রা) গণকেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং ইজতিহাদের জ্ঞান প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এটা কখনো ঘটেছে তাঁর (সা) এর প্রত্যক্ষ্য শিক্ষার মাধ্যমে আবার কখনো ঘটেছে সাহাবীদের অনুরূপ কোন কাজ শোনার পর তা অনুমোদন ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে। সাহাবা (রা) গণ কখনও এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন যে বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর হুকুম তাদের জানা নেই তাহলে তা রাসূলুল্লাহ (সা) এর আমলে সমাধানের জন্য পেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবদ্দশায় তাঁর (সা) এর কাছ থেকে জেনে নেয়ার সুযোগ আছে এমন কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা কখনোই ইজতিহাদের দ্বারস্থ হননি বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-ই ছিলেন সমাধান। সাহাবা (রা) গণ তাঁর (সা)-এর জীবদ্দশায় এমন কোনো পরিস্থিতিতেই কেবল ইজতিহাদ করেছেন যখন বিধান জানার প্রয়োজন তাৎক্ষনিক ছিলো এবং দূরত্ব বা অন্য কোনো কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে তা উপস্থাপন করার কোন সুযোগ ছিলনা। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁরা পরবর্তীতে রাসূল্লাহ (সা) এর সামনে তা পেশ করতেন এর সঠিক জ্ঞানের জন্য। এ বিষয়ে অনেক প্রসিদ্ধ ও সহীহ হাদীস বিদ্যমান। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সা) খন্দকের যুদ্ধের দিন সাহাবীদের একটি দলকে বলেছিলেন, “বনি কুরায়জা’র মহল্লায় না পৌছেঁ কেউ আসর পড়বেনা”। পথে আসরের ওয়াক্ত হলে একদল (হাদীসের শাব্দিক নির্দেশ অনুযায়ী) বললো, আমরা সেখানে পৌছার পূর্বে সালাত আদায় করবো না। অন্যদল বললো, তাঁর (সা) ইচ্ছা এটা নয় (অর্থাৎ উক্ত আদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাড়াতাড়ি ঐ গোত্রে পৌছা, নামাজ না পড়া নয়), অতএব পথে সালাত পড়ে নাও। রাসূলুল্লাহ (সা) কাছে উভয় দলের ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি দুটোকেই অনুমোদন করেন। [বুখারী, মুসলিম]
অনুরূপে, আবু দাউদ বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, দুজন সাহাবী সফররত অবস্থায় সালাতের সময় হলে তারা পানির অভাবে তায়াম্মুম করে তা আদায় করেন। অতঃপর সালাতের ওয়াক্ত থাকতেই পানির সন্ধান পাওয়ার পর একজন অযু করে পুনরায় সালাত পড়েন আর দ্বিতীয়জন পুনরায় অযু, সালাত কোনোটাই করেননি। সফর শেষে তাঁর রাসূল (সা) এর কাছে এ ঘটনা জানালে, তিনি যিনি ওযু-সালাত দ্বিতীয়বার করেননি তাকে বললেন, “তুমি সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করেছো, আর তোমার আদায়কৃত সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট”, আর দ্বিতীয়জনকে বললেন, “তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।” আর এ মর্মেই বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “যখন হাকিম ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তখন সে দুটি সওয়াব পায়, (আর) তার সিদ্ধান্ত ভুল হলে সে অন্তঃত একটি সওয়াব পায়”।
এ সমস্ত হাদীস ও ঘটনার বিবরণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে উদ্ভুত ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানে কুরআন, সুন্নাহ ও এর ভিত্তিতে ইজতিহাদের প্রয়োগের ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মপন্থার সুস্পষ্ট দলীল।
রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে যেসব সাহাবী (রা) গণ ফতোয়া প্রদানে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত যায়িদ বিন ছাবিত (রা) অন্যতম।
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ তথা ‘ফিকহ’ এর উৎপত্তি যুগের কর্মপন্থার উপর ভিত্তি করেই শুরু হয় ফিকহের দ্বিতীয় যুগ।
২. সাহাবা (রা) গণের যুগে ফিকহ:
রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওফাত পরবর্তী সময় অর্থাৎ দশম হিজরী থেকে ফিকহে’র সাহাবা যুগের শুরু। এর ব্যপ্তি ৯০ বা ১০০ হিজরী পর্যন্ত ধরা যায় কারণ এ সময়ের পর কোন অঞ্চলে আর কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। কুফায় সর্বশেষ সাহাবী মারা যান ৮৬/৮৭ হিজরীতে, মদীনার সর্বশেষ সাহাবী সাহল ইবনে সাদ (রা) ৯১ হিজরীতে, বসরার শেষ সাহাবী আনাস ইবনে মালিক (রা) ৯১ বা ৯৩ হিজরীতে ও দামেস্কের শেষ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ৮৮ হিজরীতে মারা যান। ১০০ হিজরীতে সর্বশেষ সাহাবী আমির ইবনে ওয়াসিলাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বিদায় নেয়ার মধ্য দিয়ে সাহাবা যুগের সমাপ্তি ঘটে।
সাধারণভাবে এই সুদীর্ঘ সময়ে পুরোটাকে সাহাবা যুগ নাম দিলেও এর মধ্যে প্রধান দুটো ভাগ আছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে পরস্পর থেকে পৃথক। এই যুগ বিভাগ দুটি হচ্ছে:
ক) খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ (চল্লিশ হিজরী পর্যন্ত)
খ) খুলাফায়ে রাশেদীন পরবর্তী সাহাবাদের (রা) যুগ ও এর সমান্তরালে তাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত তাবঈদের যুগ (চল্লিশ হিজরী হতে একশ হিজরী)
ক) খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ: (চল্লিশ হিজরী পর্যন্ত)
রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগে বিভিন্ন জয়ের মাধ্যমে ইসলাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লে নতুন নতুন বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সামনে চলে আসে। ক্রম প্রসারমান সেই সভ্যতার চাহিদা পূরণে এবং বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নবাগত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর উপর গভীর গবেষনা করার প্রয়োজন তীব্রতর হয় সে প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতেই ‘ফিকহ’ আরো বিকশিত হতে থাকে।
এ যুগেই ফিকহ এর তৃতীয় উৎস তথা ইজমা আস সাহাবা অস্তিত্ব লাভ করে। ইজমাকে এ যুগে সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। এজন্য যোগ্যতা সম্পন্ন ও নেতৃস্থানীয় সাহাবা (রা) গণের একটি কমিটি গঠিত হয় আর তাদেরকে যথাসম্ভব খিলাফতের কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করা হয় যাতে করে উদ্ভুত কোন নতুন বিষয়ের ফায়সালা সরাসরি কুরআন – সুন্নাহতে না পাওয়া গেলে তাদের পারস্পরিক পরামর্শ ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে এর ফয়সালা বের করা যায়। উল্লেখ্য যে, সাহাবা (রা) গণ নিজ থেকে কোন ধারণা বা পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে এসব মত দিতেন না বরং কিতাব ও সুন্নাহ’র উপর তাদের সুগভীর জ্ঞান ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাহার্যের ফলে কুরআন-সুন্নাহ থেকে যেকোন বিষয়ে হুকুম আহরণে তাদের যে দক্ষতা তার ব্যবহারেই তাঁরা সম্মিলিত চিন্তা-গবেষণার মাধ্যেমে এরূপ কোন ঐক্যমতে বা ইজমা’য় পৌছাতেন।
‘ইজমা আস সাহাবা’ নামক শরীয়াহ’র তৃতীয় মূল উৎস রূপলাভ করা ছাড়াও এ যুগে বিশাল খিলাফতের নানা সমস্যা সমাধানে কুরআন-সুন্নাহ হতে ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর বিধান আহরণের ফলে প্রথম দুটি উৎস (কুরআন ও সুন্নাহ) হতে বিধান আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান আরো বিকশিত হয় এবং পরবর্তী যুগের ফিকহের জন্য এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা তৈরী হয়। পাশাপাশি যেসব বিষয়ের সমাধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ’তে পাওয়া যেতনা এবং যার সমাধানে সাহাবাদের সম্মিলিত কোন সিদ্ধান্ত ও ছিলনা, এরূপ অনেক ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবা (রা) গণ কিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। এভাবে এ যুগে কিয়াসের ব্যবহার আরো ব্যপকতা লাভ করে।
হযরত আবু বকর (রা) এর যুগ:
কোন বিষয়ে ফিকহ-এর বিধান আহরণে হযরত আবু বকর যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, মায়মুন ইবনে মাহরান তা এ ভাবে বর্ণনা করেছেন,
“আবু বকর (রা)-এর শাসনকালে কোন সমস্যা উপস্থিত হতে তিনি কুরআন খুলে দেখতেন। যদি তাতে সংশ্লিষ্ট বিবাদ মীমাংসার জন্য কিছু পেতেন তবে তার ভিত্তিতে উদ্ভুত বিবাদ মীমাংসা করতেন। যদি কুরআনে এ ব্যাপারে কোন সমাধান না পেতেন তবে তিনি রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মীমাংসা করতেন। যদি সুন্নাহতেও উল্লেখিত বিষয়ে কিছু না পেতেন তাহলে তিনি মুসলিমদের নিকট গিয়ে বলতেন, অমুক অমুক বিষয় আমার নিকট পেশ করা হয়েছে। তোমাদের কারো এ বিষয়ে রাসূল (সা)-এর কোন ফয়সালার কথা জানা আছে কি? ঐ বিষয়ে যদি কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিত এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহে সক্ষম হত তখন হযরত আবু বকর (রা) বলতেন: “আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাদের মধ্যকার কোন কোন ব্যক্তিকে রাসূলের (সা) নিকট থেকে তাঁর শ্রুত বিষয় স্মরণ রাখার সামর্থ্য দিয়েছেন।”
যদি তিনি রাসূল (সা)-এর এরূপ কোন সুন্নাহও না পেতেন তাহলে নেতৃস্থানীয় ও উত্তম লোকদের সাথে পরামর্শ করতেন। তারা ঐকমত্যে পৌছালে তার ভিত্তিতে তিনি রায় দিতেন। [ইলমূল মুওয়াকিঈন; সংগ্রহ, ইসলামী উসূলে ফিকহ]
“ঐভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে সমাধান না পেলে তাঁর ব্যক্তিগত বিচক্ষনতার সাহায্যে ‘নস’ ব্যাখ্যা করে অথবা তার মর্মার্থ থেকে অথবা কেবল ইজতিহাদের ভিত্তিতে তার নিজস্ব মত গঠন করতেন” [হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ]
যেমন: হযরত আবুবকরের সামনে যখন দাদীর মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলো তখন তিনি বললেন যে, এ বিষয়ে কুরআনে কোন নির্দেশ নেই এবং এ বিষয়ে কোন হাদীসও তাঁর জানা নেই, তাই এ বিষয়ে অন্যদের জিজ্ঞাস করতে হবে। অতঃপর যোহরের নামাজের পর তিনি সমবেত লোকদের এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে মুগীরা বিন শোবা (রা) ও মুহম্মদ বিন সালামা (রা) দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে এ বিষয়ে তাদের হাদীস জানা আছে এবং তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা) দাদীকে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। অতঃপর আবু বকর (রা) এ অনুযায়ীই ফায়সালা দিলেন।
এ বর্ণনা হতে ফিকহ এর ব্যাপারে আবু বকর (রা) এর কর্মপন্থা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ যেকোন সমস্যা সমাধান তিনি প্রথমে, কুরআন, তারপর সুন্নাহ, অতঃপর ইজমা-আস-সাহাবা এবং পরিশেষে কিয়াস এর সাহায্য নিতেন। এই কর্মপন্থাই পরবর্তী যুগের জন্য দলীল হয়ে যায়।
আবু বকর (রা) কৃত ইজতিহাদ:
যেমন ‘কালালাহ’ শব্দের অর্থ সম্পর্ক তিনি বলেন, “কালালাহ সম্পর্ক আমি যা বললাম তা আমার নিজের রায় এর ভিত্তিতে। আমার মতামত যদি সঠিক হয় তবে তা আল্লাহর কাছ থেকে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার নিজের ও শয়তানের কাছ থেকে। সেই ব্যক্তিই ‘কালালাহ’ যার পিতা-মাতাও নেই, সন্তানও নেই। তাঁর আরো ইজতিহাদের উদাহরণ হচ্ছে, যাকাত অস্বীকারকারী গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য বায়তুল মাল থেকে সমান বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি।
হযরত উমর (রা) এর যুগ:
হযরত উমর (রা) এর যুগে ফিকহ’ এর অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। তিনি নিজে ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ফকীহ। তিনি খুব দ্রুত কোন সম্পূরক বিষয়কে মূল বিষয়ের সাথে তুলনা করতে পারতেন। ফলে তিন তাঁর শাসনকালে ইসলামী আইনের এক বিশাল ভান্ডার রেখে যান। বিখ্যাত তাবেঈ ইবরাহীম নখঈ যথার্থই বলেছেন যে, “উমর (রা) শহীদ হওয়ার সথে সাথে ইলমের দশ ভাগের নয় ভাগ দুনিয়া থেকে তিরোহিত হয়ে গেছে” [১১. পূর্বোক্ত]
‘ফিকহ’ এর বিষয়ে হযরত উমর (রা) কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে লক্ষনীয় বিষয় ছেল যে, ফায়সালা গ্রহণের জন্য তিনি সর্বোৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে সাহাবীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ করতেন, বিতর্ক সভা করতেন। যখন তাঁর সামনে কোন ফিকহী সমস্যা উপস্থাপন করা হতো তিনি বলতেন, “ডাকো আলীকে ডাকো যায়েদকে” অর্থাৎ অন্যান্য সাহাবা (রা)-দের ডাকতেন, তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং এভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতেন।
মৌলিকভাবে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি হযরত আবু বকর (রা) এ প্রায় অনুরূপ ছিল। আগত সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান তিনি প্রথমে কুরআন, অতঃপর তাঁর সুন্নাহ’র জ্ঞান ভান্ডারে খুজতেন, যদি সেসব থেকে সরাসরি কিছু না পেতেন এবং বাকী সাহাবীদের কাছ থেকেও তার অজানা কোন হাদীসের সন্ধান না পেতেন তখন সবার সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন অথবা ইজতিহাদ করে রায় দিতেন।
যেমন : হযরত উমর (রা) নিকট গর্ভস্থ সন্তানের দিয়তের বিষয় উত্থাপিত। তখন মুগীরা ইবনে শোবা (রা) এ বিষয়ক একটি হাদীস জানালে উমর (রা) সে অনুযায়ী ফায়সালা করেন। অনুরূপে অগ্নি পূজকদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা সম্পর্কে তিনি আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে অবগত হন এবং অতঃপর এর ভিত্তিতে আইন করেন। অনুরূপে স্ত্রী স্বামীর দিয়তের রক্তপন অংশীদারী হবে কিনা এ সম্পর্কে তিনি দাহহাক বিন সুফিয়ান আল-কালাবি (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে অবগত হন এবং বলেন, “যদি আমরা এ হাদীস না শুনতাম, তবে ভিন্ন হুকুম দিতাম।” [১২, রাফউল মালাম, ইবনে তাইমিয়্যাহ]
অনেক সময় তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীস না পেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে রায় দিতেন; কিন্তু পরে এ সম্পর্কে কোন হাদীস জানতে পারলে পূর্ব রায় ত্যাগ করে হাদীস অনুসরে রায় দিতেন। যেমন : হাতের আঙ্গুলের দিয়তের ব্যাপারে তাঁর মত ছিলো, উপকারীতার পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন আঙ্গুলে দিয়ত ও কমবেশী হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আবু মুসা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে সব আঙ্গুলের দিয়ত সমান হওয়া সম্পর্কিত হাদীস শুনে সে অনুযায়ী রায় দেন।
‘ফিকহ’ এর ব্যাপারে তাঁর অনুসৃত আরেকটি নীতি হচ্ছ, তাঁর কাছে যদি হাদীসটি বিশুদ্ধ পন্থায় না পৌছাতো তবে তিনি তা গ্রহণ না করে বরং সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে রায় দিতেন। এই নীতি পরবর্তীতে ফিকহের অনেক ইমাম আরো সুসংবদ্ধ করেছেন। উদাহরণ: তালাকের পর ইদ্দত কালীন ভরনপোষণ বিষয়ে হযরত উমর (রা) ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) এর হাদীস বর্জন করেন এবং কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করেন।
এভবেই উমর (রা) ‘ফিকহ’ এর ব্যাপারে বিভিন্ন নীতিমালার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিভিন্ন কাজী ও গভর্ণরদের কাছে চিঠি লিখতেন এবং তারাও তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বিধান জানতে চেয়ে চিঠি লিখতেন। ঐসব গভর্ণররা নিজেরাই ছিলেন মর্যাদাবান সাহাবী ও শীর্ষস্থানীয় ফকীহ। তাই তারা নিজেরাও প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদ করে আইন দিতেন। এভাবেই উমর (রা) এর পুরো খিলাফত জুড়েই ফিকহের ব্যাপক উন্নতি ঘটে।
হযরত উসমান (রা) এর যুগ:
হযরত উসমান (রা) কে এই শর্তে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছিল যে, তিনি কুরআন, সুন্নাহ, ও পূর্ববর্তী দু’ইজন খলীফার অনুসৃত নীতি অনুসরণ করবেন। তাই তার খিলাফত কালে তিনি নিজে কদাচিৎ ইজতিহাদ করতেন বরং অধিকাংশ বিষয়ে পূর্ববর্তী দুই খলীফার সময় নেয়া সিদ্ধান্ত গুলোর বাস্তবায়নকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের উদাহরণ হচ্ছে মিনায় সালাত সংক্ষিপ্ত না করা বিষয়ে তার আমল। তবে তিনি নিজে স্বাধীন ইজতিহাদ কম করলেও পূর্ববর্তী দুই যুগের ন্যায় এ যুগেও সাহাবা (রা) ও বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ালী ও কাজীরা আগত নতুন নতুন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে সাহাবার ভিত্তিতে সমাধান করে ‘ফিকহ’ এর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখেন।
হযরত আলী (রা) এর সময়কাল:
হযরত আলী (রা) নিজেই ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ। তিনি উমর (রা) এর মতোই কুরআন সুন্নাহর গভীর গবেষণার মাধ্যমে সাধারণ নীতিমালার আলোকে কোন বিশেষ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতেন এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পৌছাতেন। খলীফার দায়িত্ব নেয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন মদীনার শ্রেষ্ঠতম বিচারক। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, “রাসূলূল্লাহ (সা) এর সুন্নত সম্পর্কে আলী (রা) অন্য সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন।”
তাঁর ইজতিহাদ সমূহে তিনি গভীর ও সূক্ষ্ম কিয়াস প্রয়োগ করতে পারতেন যা পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে মূলনীতি রচনায় দিক-নির্দশনা দেয়। যেমন: তিনি মদ্যপানকারীর ব্যাপারে হদ্দে কায্ফ অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি প্রদানের রায় দেন এ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যে, যে মাতাল সে যা ইচ্ছা তা ই বলে যা মিথ্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক অতএব তার শাস্তি মিথ্যা অপবাদের শাস্তির অনুরূপ। এই রায়ের ভিত্তি হচ্ছে ফিকহের এই মূলনীতি যে, যা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল তার হুকুম ঘটে যাওয়া বিষয়ের অনুরূপ যেমন এক্ষেত্রে মাতালের মিথ্যা বলার সম্ভাবনা প্রবল এবং সে অনুযায়ী তার শাস্তি।
অনুরূপে যৌথভাবে হত্যা পরিকল্পনার সাথে জাড়িত একদল লোককে কীভাবে শাস্তি দেয়া হবে এ বিষয়ে তার রায়ে ছিলো তদের সবাইকে হত্যা করা আর এটাকে তিনি চুরির ক্ষেত্রে একদল চোরের প্রত্যেকের হাত কেটে দেয়ার স্বীকৃত সিদ্ধান্ত থেকে কিয়াস করে বের করেছেন।
এভাবে আলী (রা) তাঁর যুগে বিভিন্ন সামজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ‘ফিকহ’ এর বিধান আহরণে ব্যাপক গবেষণা ও সাদৃশ্যমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা পরবর্তী যুগে ফিকহের মূলনীতি প্রণয়ণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ফিকহের বিকাশের মূলদিকগুলো হচ্ছে খলীফা ও সাহাবা (রা) গণ কুরআন-সুন্নাহ’তে বর্ণিত শরীয়াহ’র বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতেন এবং পরস্পররের জানা বিষয় দ্বারা উপকৃত হতেন। তারা যখনি একত্রিত হতেন তখন কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে গবেষণা করতেন এবং কোন একটি বিষয়ের হুকুম অনুসন্ধানের সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারো কোন হাদীস শুনেছেন কিনা তার অনুসন্ধান করতেন। এ নীতির ফলে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্নজনের জানা প্রায় সব হাদীসই জনসমক্ষে চলে এলো এবং অন্যরাও সেটা দ্বারা উপকৃত হবার এবং এর ভিত্তিতে ‘ফিকহ’ আহরণের সুযোগ পেলো সাহাবা (রা) গণের এই অনুসন্ধানী নীতির ফলে ফিকহ-এর অন্যতম উৎস হাদীসের ভান্ডার সমৃদ্ধ হলো এবং সেগুলো পরবর্তী যুগের ফকীহদের কাছেও পৌঁছে গেলো। অনুরূপভাবে তাদের জ্ঞান ও গবেষনার কারণে কুরআনের আহকাম সম্পর্কিত আয়াতগুলো থেকে আহরিত হুকুম এবং আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা ব্যাপকতর হলো। উপরন্তু, ফিকহ-এর তৃতীয় উৎস হিসেবে ‘ইজমা আস সাহাবা’ অস্তিত্ব লাভ করলো। ফলে, ‘ইলমুল ফিকহ’ তার মূল উৎসগুলোর যথাযথ বিকশিত রূপ সহ এক বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে পরবর্তী যুগের দিকে এগিয়ে গেল।
খ) খুলাফায়ে রাশেদীন পরবর্তী সাহাবা (রা) যুগ এবং এর সমান্তরালে তাবেঈ যুগ: (৪০ হিজরী-১০০ হিজরী)
এ যুগটি হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর শাসনকাল তথা ৪১ হিজরী এমন হতে প্রথম হিজরী ও শতকের শেষ পর্যন্ত ব্যপ্ত। এ যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সমূহ হচ্ছে:
১) জীবিত সাহাবী (রা) গণ আরব ও আরবের বাইরে বিশাল খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েন।
২) প্রতিটি অঞ্চলে তাদের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাবঈদের মধ্যে থেকে একদল ফকীহ তৈরী হয়ে যায় নিজ নিজ অঞ্চলে ফিকহ এর জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।
৩) প্রতিটি অঞ্চলে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে নতুন নতুন যেসব সমস্যা আমলে আসতো উক্ত অঞ্চলের সাহাবী তাঁর নিকট রক্ষিত প্রমাণাদি জ্ঞান (কুরআন-সুন্নাহ) দ্বারা বা প্রমাণিত জ্ঞানের আলোকে এসবের জবাব দিতেন এভাবে কোন বিষয়ে সমাধান পাওয়া না গেলে সে বিষয়ে ইজতিহাদ করে ফায়সালা দিতেন। যেহেতু একজন বা কয়েকজন সাহাবীর পক্ষে সমস্ত হাদীস এবং এর জ্ঞানে পূর্ণাঙ্গ হওয়া সম্ভব ছিলনা আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে অনেক দূরে অবস্থান করায় পূর্বের ন্যায় পারস্পরিক জিজ্ঞাসাও পরামর্শের মাধ্যমে একে অন্যের নিকট রক্ষিত জ্ঞান বা জ্ঞানের বিশ্লেষণ দ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ ছিলনা, ফলে এ যুগে বিভিন্ন অঞ্চলের সাহাবীদের রায়ে উল্লেখযোগ্য মত পার্থক্যের সূচনা হয়। তাদের ছাত্র তাবঈ ফকীহবৃন্দের মাঝে গিয়ে ‘ফিকহ’ এর বিভিন্ন বিষয়ে এই মতপার্থক্য ব্যাপকতর হয়। মতপার্থক্যের আবির্ভাব এ যুগের ফিকহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।
৪) এ যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতভেদ ও ধর্মীয় ফেরকা জন্মলাভ করে। এর ফলশ্র“তিতে বিভিন্ন ফেরকা কর্তৃক নিজ নিজ মতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এবং আরো নানাবিধ কারণে জাল হাদীসের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। ফলে “ফিকহ’ জানার জন্য হাদীস আহরণের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ ও বিভিন্ন মূলনীতি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়।
এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এ যুগেই সংগঠিতভাবে প্রথম দুই যুগের ফিকহের সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়। এজন্য একে ফিকহ সংকলনের ভিত্তিযুগও বলা যেতে পারে। এ যুগে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফাতওয়া সংকলনের জন্য কতিপয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে ঐ শহরের শীার্ষস্থানীয় তাবেঈ ফকীহগণ তাদের শিক্ষক সাহাবীগণ বর্ণিত হাদীস ও ‘ফিকহী’ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রন্থনার কাজ শুরু করেন। এসব কেন্দ্রের মধ্যে মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর ও ইয়েমেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় তাবেঈদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহ), আতা ইবনে আবু রাবাহ (রহ), হযরত ইবরাহীম নখঈ (রহ), হযরত শাবী (রহ), হযরত হাসান বসরী (রহ), হযরত মাকহুল (রহ) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয়।
এদের মধ্যে মদীনার সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও কুফার ইবরাঈম নখঈ ছিলেন বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাদেরকে কেন্দ্র করে মদীনা ও কূফা উভয় শহরে বিরাট ফকীহ গোষ্ঠী গড়ে উঠে। অসংখ্য লোক তাদের কাছ থেকে ফিকহে’র ইলম লাভ করে। হাফিয ইবনে কায়্যিম এর মতে সাহাবীদের মধ্যে ফতোয়া প্রদানকারী সাহাবারে কিরামের সংখ্যা একশত ত্রিশ এর কিছু বেশী ছিল। [আসারুল ফিকহীল ইসলামী]। তাবেঈ ফকীহগণের উপরোক্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে এই ত্রিশ জন সাহাবীর (রা) ফতোয়া বা ফিকহী’ মত সংরক্ষণ এবং যেসব মূলনীতির মাধ্যমে তারা এসব সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন তার অনুধাবন সম্ভব হয়।
এভাবেই, খুলাফায়ে রাশেদীন পরবর্তী তাবেঈ যুগে শীর্ষস্থানীয় ফকীহদের মাধ্যমে রাসূল (সা) এর যুগ ও সাহাবা (রা) যুগের ‘ফিকহ’ সম্পর্কিত জ্ঞান যথাযোগ্যভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়ে পরবর্তী যুগের নিকট পৌছে এবং ফিকহের পরবর্তী যুগ তথা চূড়ান্ত বিকাশপর্বের সূচনা হয়।
৩. তাবঈ-তাবঈন যুগ: ফিকহের চতুর্থ ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের যুগ:
ফিকহের ইতিহাসে এই যুগ সর্বাধিক গৌরবজ্জ্বল যুগ। এ যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে ফিকহের আকাশে এমন কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে যারা পূর্ববর্তী তিন যুগের জ্ঞানভান্ডারকে ব্যবহার করে নিজেদের সুউচ্চ প্রতিভা ও মৌলিক চিন্তার মাধ্যমে ‘ইলমুল ফিকহ’ কে ইসলামী জ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখায় রূপদান করেন এবং এ শাস্ত্রের মূলনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রায় সকল নীতিমালা প্রনয়ণ করেন। ফলতঃ ‘ফিকহ’ একটি স্বতন্ত্র, সুশৃংখল ও স্বয়সম্পূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ জ্ঞানের মূলসূত্র যদিও তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন কিন্তু তাদের পূর্ববর্তীদের কেউই এটাকে তাদের মতো বিস্তারিত আলোচনা করে যাননি এবং একে পৃথক একটি বিজ্ঞানের রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল নীতিমালার একত্রিত কোনো রূপ দেননি যদিও তারা নিজেরা এগুলো চর্চা করতেন।
এযুগের ব্যপ্তি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগের প্রথমার্ধে আবির্ভাব ঘটে আবু হানীফা (রহ), ইমাম মালিক (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ) এর মত ফিকহের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণের। তদুপরি, এ যুগের দ্বিতীয়র্ধে আরো একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের আর্বিভাবে হয় আর তা হলো হাদীস-বিজ্ঞান। এ সময় ইমাম বুখারী (রহ), ইমাম মুসলিম (রহ) এর মতো শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণের আবির্ভাব হয়, হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় নীতি তথা উসূলুল হাদীস প্রণীত হয় এবং এসবের ভিত্তিতে সিহাহ সিত্তাহ তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের সংকলন কাজ সম্পন্ন হয। এভাবেই ইসলামী জ্ঞানের দু’দুটো শীর্ষশাখার চরম বিকাশের মাধ্যমে এ যুগ এ অনন্য যুগে পরিণত হয়।
আমরা এ যুগে ফিকহের বিকাশকে এ যুগের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব তথা প্রসিদ্ধ ইমামদের আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করবো, কেননা এযুগের ফিকহের সামগ্রিক অগ্রগতি তাদেরকে কেন্দ্র করেই হয়েছিলো। সময়ানুক্রমিকভাবে আগত ইমাম গণের ফিকহী চিন্তাধারা ও অবদানের বিশ্লেষণ করলেই এ যুগে ফিকহের বিকাশ স্পষ্ট হয়ে যাবে।
ইমাম আবু হানিফা (রহ) ও ফিকহে তাঁর অবদান:
‘ইমামে আযম’ নামে খ্যাত নুমান ইবনে সাবিত ওরফে আবু হানীফা (রহ) প্রখ্যাত মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে সবার আগে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তাঁর জন্ম ৮০ হিজরীতের কুফা নগরীতে।
ইসলামী জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে কুফার খ্যাতি আগেই বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা কুফার শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ ও তাবে-তাবেঈ গণের কাছে থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে মক্কা মদীনা ও বসরা সফর করেন এবং সেখানকার শীর্ষস্থানীয় তাবঈ মুহাদ্দিস ও ফহীহদের কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা নেন। ইমাম যাহাবীর মতে কেবল কূফাতেই ইমাম আবু হানীফা ২৯ জন ওস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেন যাদের অধিকাংশই ছিলেন বড় বড় তাবেঈ। এদের মধ্যে ইমাম শাবী (রহ), ইমাম হাম্মাদ (রহ) অন্যতম। অন্য আরেক বর্ণনা মতে তিনি কূফায় তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈনসহ ৯৩ জন ওস্তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অজর্ন করেন। আর এভাবে তাদের কাছে সংরক্ষিত পূববর্তী তিন যুগের হাদীস ও ফিকহের বিশাল ভান্ডার তিনি সংগ্রহ করেন এবং তাঁর অসাধারণ মৌলিক প্রতিভা ও যোগ্যতার মাধ্যমে এসব থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা নিয়ে বিভিন্ন নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে ফিকহের এক বিশাল ভান্ডার তৈরী করেন এবং একে সুনির্দিষ্ট পন্থায় সংকলিত ও বিন্যস্ত করে ‘ফিকহ’ কে একটি স্বতন্ত্র ও সুবিন্যস্ত শাস্ত্রের রূপ দেন। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই সর্বপ্রথম ‘ফিকহ’ একটি পৃথক ও বিস্তৃত শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে। তাই ইমাম শাফেঈ (রহ) যথার্থই বলেন,
“মুসলিম জাতি ফিকহে আবু হানীফার সন্তানতুল্য” [আসারুল ফিকহীল ইসলামী]
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ) বলেন, “ইমাম আবু হানীফা (রহ) ই সর্বপ্রথম এই ইলমে ফিকহ সংকলন করেন এবং তা অধ্যায় হিসেবে বিন্যস্ত করেন। পূর্ববর্তী ফকীহদের কেউই তাকে এ বিষয়ে পিছনে ফেলতে সক্ষম হয়নি।” [মানাকিবে মুওয়াফফিক]
আবু হানীফা ফিকহ আহরনে তাঁর অনুসৃত নীতি সম্পর্কে নিজে বলেন, “আমরা প্রথমত কিতাবুল্লাহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ হাদীস দ্বারা। তারপর সাহাবায়ে কিরামের ফয়সালা দ্বারা। সাহাবায়ে কিরাম যে বিষয়ে সর্বসম্মত আমরা এর উপরে আমল করি। যদি তাঁদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হয়ে যায় তখন আমরা সামগ্রিক ইল্লাতের ভিত্তিতে এক হুকুমকে অন্য হুকুমের উপর কিয়াস করি যতক্ষণ না নসের (কুরআন-সুন্নাহ) অর্থ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।” [আল-মীযান: ইমাম শারানী]
তিনি নিজে সুউচ্চ পর্যায়ের মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও কোন বিষয়ে সর্বাধিক সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য এবং একইসাথে ফিকহ চর্চাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য তাঁর সুযোগ্য ও বিশিষ্ট সহচরদের মধ্য থেকে প্রধান চল্লিশজনকে নিয়ে ‘মাজমাউল ফিকহী’ বা ফিকহ পরিষদ’ গঠন করেন। এই চল্লিশজন তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও মুজতাহিদ ছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লামা মুওয়াফফিক মক্কী (রহ) বলেন, “আবু হানীফা (রহ) তাঁর ফিকহী চিন্তাধারা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। মজলিশে শূরার সাথে আলোচনা ব্যতীত তিনি নিজের একার মতে কিছু করতেন না। ফিকহী বোর্ডের সামনে তিনি এক একটি করে মাসআলা পেশ করতেন, সদস্যদের মতামত ও প্রমানাদি শুনতেন ও সবশেষে নিজের দলীল ও যুক্তিসমূহ পেশ করতেন। এভাবে এক এক মাসআলার উপর (প্রয়োজনে) মাসব্যাপী বা এর চেয়েও বেশী সময় পর্যন্ত তিনি বোর্ড সদস্যদের সাথে বিতর্ক চালিয়ে যেতেন। পরিশেষে কোন একটি অভিমতের উপর বোর্ড সদস্যগণ একমত হলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন। এভাবে ফিকহে হানাফী লিপিবদ্ধ হয়” [মানাকিব]
সবার ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি চলতে থাকতো। এক বর্ণনায় আছে, “তাঁদের মধ্য থেকে একজনও যদি ভিন্নমত পোষণ করতেন তাহলে তিনদিন পর্যন্ত সে বিষয়ের উপর আলোচনা হত”। ইবন আবুল আওয়াম, ইমাম আবু হানীফার অন্যতম প্রধান ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের (রহ) সূত্রে বর্ণনা করেন,
“যখন ইমাম আবু হানীফার নিকট কোন মাসআলা উপস্থিত হতো, তখন তিনি তাঁর ছাত্রগণকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কী হাদীস ও আসার আছে তা বর্ণনা কর। তারপর যখন আমরা হাদীস ও আসার পেশ করতাম এবং সে ভিত্তিতে নিজেদের রায় দিতাম, তখন তিনি তাঁর মতামত ও ব্যক্ত করতেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষে হাদীস ও আসার অধিক (শক্তিশালী) হতো, সেইসব হাদীস ও আসারই তিনি গ্রহণ করতেন। আর যদি উভয় পক্ষের হাদীস ও আসার সমান সমান হতো, তখন তিনি চিন্তা-গবেষণা করে একটি মতকে গ্রহণ করতেন।”
এই ‘ফিকহ পরিষদ’ এর তত্ত্বাবধানে বাইশ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার ফলে ৮৩ হাজার মাসআলা সংকলিত ও সন্নিবেশিত হয়। এরপরও মাসআলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং এভবে ৫ লাখে গিয়ে পৌছায়। আল্লামা খাওয়ারেযমী (রা) স্বাীয় ‘জামেউল মাসাইল’ গ্রন্থে বলেন,
“বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর (লিপিবদ্ধকৃত) মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছে ছিল। তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের গ্রন্থরাজি এর প্রমাণ বহন করে”।
এভাবে আবু হানীফা (রহ) প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা ও কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয় ভিত্তিকভাবে ফিকহের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে তোলেন এবং ‘ফিকহ’ কে আলাদা এক শাস্ত্রের রূপ দেন।
ইমাম আবু হানীফা বিপুল সংখ্যক মুজতাহিদ ছাত্র রেখে যান। প্রধান ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী ও ইমাম যুফার অন্যতম। এই তিনজন নিজেরাই মুজতাহিদ মুতলাক ছিলেন এবং স্বতন্ত্র মাযহাব প্রবর্তনের যোগ্যতা রাখতেন কিন্তু তারা নিজেদেরকে তাদের শিক্ষকের মাযহাবের সাথেই সম্পৃক্ত রাখেন। আবু হানীফার পর তাঁর ছাত্ররা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁর বিখ্যাত ছাত্র বৃন্দের মাধ্যমে তাঁর ফিকহী পদ্ধতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন খলীফা, শাসক এর কাযীগণ এই মাযহাবকে তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে হিসেবে গ্রহণ করলে এটা মুসলিম জগতের সর্বত্র বিস্তৃত হয়। ইবনে হাযম (রহ) বলেন,
“ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দুটি মাযহাব গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য অঞ্চলে হানাফী মাযহাব আর আন্দালুসে-স্পেনে মালিকী মাযহাব।”
এভাবে মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক লোক এই মাযহাবের অনুসারী হয়ে যায়।
ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ):
আবু আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস (রহ) ৯৩ হিজরীতে মদীনা তাইয়্যেবায় জন্মগ্রহন করেন।
মদীনার প্রখ্যাত তাবিঈ মুজতাহিদ রবীয়াতুর রায়, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম যুহরী নাফে (রহ) এবং এরূপ আরো অনেক শ্রেষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস তাবেঈন থেকে তিনি হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করে এক সময় ‘ইমাম দারুল হিজরত’ ও ‘মদীনার ইমাম’ নামে চতুর্দিকে খ্যাতি অর্জন করেন।
তাঁর সর্বশ্রেষ্ট কীর্তি তাঁর ‘মুওয়াত্তা’ নামক হাদীস সংকলন যেটা অনেকের মতে বুখারী, মুসলিমের সমপর্যায়ের বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন। একই সাথে ‘মুওয়াত্তা’ মালিকী ফিকহের ভিত্তিও বটে। তাই মালিকী ফিকহের আলোচনা ‘মুওয়াত্তা’-কে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।
ইমাম আওযাঈ (রহ) বলেন যে ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন “এই গ্রন্থখানি আমি চল্লিশ বছরে সংকলন করেছি।” তিনি আরো বলেন, “এই গ্রন্থটি সংকলনের পর আমি মদীনার সত্তর জন ফকীহ’র সম্মুখে তা উপস্থাপন করলাম। তাঁরা সবাই আমার সাথে (এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে) ঐক্যমত পোষন করলেন। এ কারনেই আমি গ্রন্থটির নাম রাখলাম “মুওয়াত্তা’।”
এ সংকলনে তিনি অনেক মুরসাল হাদীসকে স্থান দিয়েছেন। বস্তুতঃ ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মত তিনিও মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করতেন। ‘মুওয়াত্তা’য় সংকলিত হাদীস ও আমাদের ভিত্তিতেই মালিকী ফিকহ প্রসারিত হয়।
প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আব্বাসীয় খলীফা মনসুরের অনুরোধক্রমেই ইমাম মালিক (রহ) ‘মুওয়াত্তা’ সংকলনে হাত দেন। বর্ণিত আছে যে, আব্বাসীয় খলীফা আল মনসুর যখন বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিমগণ কর্তৃক ফিকহী বিষয়ে বিভিন্ন সব পার্থক্য লক্ষ্য করলেন তখন তিনি চাইলেন একক কোন হাদীস ও ফিকহ গ্রন্থের ভিত্তিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে। তাই হজ্জ্ব উপলক্ষ্যে মদীনায় এসে খলীফা মনসুর ইমাম মালিককে বললেন, “আমি আপনার ‘আল মুওয়াত্তা’র অনুলিপি প্রস্তুত করিয়ে এবং সেগুলো মুসলিমদের সকল শহরে পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে এ নির্দেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এখন থেকে এটারই অনুসরণ করতে হবে এবং একে ত্যাগ করে অন্য কোন মতের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম সুয়ুতীর বর্ণনায় অনুরূপ ঘটনা খলীফা হারুনুর রশিদের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে খলীফা তাঁকে বলেন, “আপনার ‘মুওয়াত্তা’ কাবার গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে লোকদেরকে সকল মতপার্থক্য ত্যাগ করে এর অনুসরন করতে বাধ্য করলে কেমন হয়? জবাবে ইমাম মালিক বলেন, “হে আমীরুল মু’মিনীন! এমনটি করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যেই খুঁটিনাটি বিষয়ে মতপার্থক্য ছিলো। অতঃপর তাঁরা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বিভিন্ন শহরে তাঁদের নিজ নিজ মতের অনুসারী লোক সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে লোকদের মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখা যাচ্ছে তা সাহাবা (রহ) গণের থেকেই চলে আসছে।” তার এই উত্তর শুনে খলীফা তাঁর ইচ্ছা দমন করলেন।
ইমাম মালিক তাঁর ফিকহ এর উৎস হিসেবে কুরআন, সুন্নাহ, মদীনার আলেমদের আমল, কিয়াস ও ইসতিসলাহ কে গ্রহণ করেন, [তারীখে ফিকহে ইসলামী]। মদীনাবাসীদের সম্মিলিত আমলকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং এর বিপরীত খবরে ওয়াহিদ হাদীস বর্জন করতেন। তাঁর নিজের সময়কালেই তাঁর মাযহাব মদীনার প্রধানতম মাযহাবে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে সমগ্র হিজাজেও তা বিস্তার লাভ করে। তাঁর মদীনার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক (রহ)। অন্যান্য অঞ্চল বিশেষত মিসর ও আফ্রিকা থেকে অনেকে তাঁর নিকট ‘ফিকহ’ শিখতে আসতেন। যাদের মাধ্যমে তার মাযহব অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষত আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে। তাঁর অনুসারী ছাত্ররা ছাড়াও তাঁর যুগের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও তাঁর নিকট হাদীস শিখতে আসতেন যাদের মধ্যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম শাফিঈ (রহ) অন্যতম।
ইমাম শাফিঈ (রহ) ও ফিকহে তাঁর অবদান:
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস ওরফে ইমাম শাফিঈ (রহ) ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার গাযা প্রদেশে জন্মগ্রহন করেন। একই বছর ইমাম আবু হানীফা (রহ) বিদায় নেন।
ইমাম শাফেঈ প্রথমে মক্কায় বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রহ) ও মুসলিম ইবনে খালিদ আল যিনজী (রহ) এর নিকট থেকে হাদীস ও ফিকহ এর জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর মদীনায় ইমাম মালিক (রহ) এর কাছ থেকে ‘মুওয়াত্তা’ শিক্ষা নেন। এছাড়াও আরো ৮০ জন ফকীহ ও মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস ও ফিকহ শিখেন। অতঃপর ইরাকে গিয়ে আবু হানীফার বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহ) এর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ১৯৫ হিজরীতে তিনি পুনরায় ইরাক যান এং তাঁর ফিকহী চিন্তাধারা পেশ করেন। তাঁর এ সময়ের ফতওয়াগুলো তাঁর ‘কওলে কাদিম’ বা পুরাতন অভিমত নামে পরিচিত। ১৯৮ হিজরীতে তিনি মিসরে চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই কাটান। মিসর গমনের পর মক্কা, মদীনা, ইরাক ও মিসরের ঐ সময়ের ফিকহী চিন্তাধারা গভীর ভাবে বিশ্লেষন করে তাঁর নিজস্ব ফিকহী চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং চিন্তাধারার এই পরিবর্তন তাঁকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ট কীর্তি ‘উসূলুল ফিকহ’ তথা ফিকহের মূলনীতি প্রনয়নের দিকে চালিত করে।
এ বিষয়ে জ্ঞানীদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, ‘উসূল আল ফিকহ’ এর সর্বপ্রথম প্রণেতা হচ্ছেন ইমাম শাফিঈ এবং এ বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রণীত গ্রন্থ তাঁর ‘আর-রিসালাহ’। দূর্বল একটি সূত্রে আবু হানীফার ছাত্র আবু ইউসুফ কর্তৃক সর্বপ্রথম উসূল আল ফিকহ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনার বর্ণনা থাকলেও এর স্বপক্ষে শক্তিশালী কোন প্রমাণ নেই আর গ্রন্থটি পরবর্তীকালে পাওয়াও যায়নি। আয যারকাশী তার আল-বাহরুল মুহীত গ্রন্থে লিখেছেন, “ইমাম শাফিঈ (রহ) প্রথম ব্যক্তি যিনি উসূল আল ফিকহ সম্পর্কে লিখেছেন। ইমাম জুয়াইনী বলেন, “ইমাম শাফিঈ (রহ) এর পূর্বে আর কেউ উসূল সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেননি কিংবা এ বিষয়ে তাঁর মতো এতো বেশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না।”
বস্তুতঃ প্রাথমিক যুগের ফকীহদের বিভিন্ন ফতোয়া থেকে ধারনা করা যায় যে, এ বিষয়ে বিভিন্ন নীতিমালার জ্ঞান তাদের ছিল, তবে তারা কেউই এসব নীতিমালা সম্পর্কে পৃথকভাবে কোন আলোচনা করেননি বা এ বিষয়ে কোন গ্রন্থনা করেননি। সর্বপ্রথম ইমাম শাফিঈ এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেন। তাঁর অন্য কোন অবদান যদি নাও থাকতো তাহলেও কেবল এই এক কারনেই তিনি ফিকহের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতেন।
যেসব বিষয়ে তাকে ‘উসূলে ফিকহ’ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হলো:
(১) তাঁর পূর্ববর্তী যুগের ইমাম ও ফকীহদের নিকট প্রধানত তাদের নিজ নিজ শহরের আলেমদের সূত্রে প্রাপ্ত হাদীস ও আসারই বর্তমান ছিলো, সকল শহরের বর্ণনা সমূহের কোন একক সংকলন ছিলনা, ফলে বিভিন্ন শহরের ফকীহদের রায়ে ব্যাপক মতপার্থক্য এতো বেশী নজরে আসেনি। শাফিঈর যুগে তিনি তা সংকলিত অবস্থা পান এবং এসবের মাঝে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখেন। তাছাড়া পূর্ববর্তী অন্যান্য ইমামরা প্রধানত নিজ শহরেই বাস করতেন কিন্তু ইমাম শাফিঈ এ সময়ে ফিকহের প্রধানতম চারটি কেন্দ্র মক্কা, মদীনা, কুফা ও মিসরে অবস্থান করে জ্ঞানার্জন করায় বিভিন্ন অঞ্চলে ফিকহী চিন্তাধারার পার্থক্য তাঁর নজরে আসে। তাই তিনি এমন কিছু মূলনীতি উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন যার ভিত্তিতে সকলেই একই ছক অনুসরণ করে মূল উৎস হতে ফিকহ আহরন করতে পারে যাতে মতভেদ যথাসম্ভব হ্রাস পায়।
(২) তিনি দেখলেন মদীনা ও কুফার ফকীহরা‘ মুরসাল ও মুনকাতি’ হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করছে, ফলে তাদের অনেক বক্তব্যে ত্র“টি প্রবেশ করছে। কেননা বহু মুরসাল হাদীস মুসনাদ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে, ফলে তিনি মুরসাল হাদীস গ্রহণে শর্ত নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করেন।
(৩) তিনি দেখলেন, ফকীহরা দুটি ইখতিলাফপূর্ণ প্রমাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে কোনো নির্দিষ্ট বিধি অনুসরন করেননি, যাতে তাদের ইজতিহাদ সমূহ ভ্রান্তি থেকে আরো সুরক্ষিত হতো। কাজেই তিনি এ বিষয়ে মূলনীতি দাঁড় করালেন।
(৪) তিনি দেখলেন, কোন ইমামের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট হাদীস না থাকায় তিনি হয়তো ঐ বিষয়ে ইজতেহাদ করে রায় দিয়েছেন, কিন্তু পরবর্তী যুগে তাঁর অনুসারী ফকীহদের এ বিষয়ে হাদীস নজরে এলেও যথাযথ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তা গ্রহণে মনোনিবেশ না করে, পূর্ববর্তী ইজতিহাদকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, ফলে তিনি এ বিষয়েও মূলনীতি প্রণয়ন করলেন।
(৫) তাঁর সময়ে সাহাবা (রহ) এর ‘কওল’ বা বানী সর্বাধিক পরিমানে সংগৃহীত ছিলো। তিনি এসব বিশ্লেষণ করে এর বিরাট অংশ সহীহ হাদীস এর বিপরীত পান। কারণ সব হাদীস এককভাবে সব সাহাবীর কাছে পৌছেনি। তাই তিনি এক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের বিপরীত সাহাবীদের যেসব বক্তব্য তা গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে নীতিমালা তৈরী করেন।
(৬) তিনি আরো দেখলেন, একদল ফকীহ ‘রায়’ ও ‘কিয়াস’ কে মিশিয়ে ফেলছে অথচ শরীয়ত ‘রায়’-কে নিষেধ করেছে ও ‘কিয়াস’-কে বৈধ ও উত্তম বলেছে। তিনি বলেন, “আমি রায় বলতে কোন যুক্তির ধারনা বা সম্ভাবনাকে কোনো বিধানের ভিত্তি বা কারণ ধরে নেয়া বুঝাচ্ছি। আর কিয়াস বলতে বুঝাচ্ছি কোনো সম্পূর্ণ বিধানের কারণ খুঁজে বের করা এবং সেই কারণের ভিত্তিতে অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে একই বিধান স্থির করা।” এভাবে তিনি ‘কিয়াস’ এর সঠিক পদ্ধতি বিষয়ে নীতিমালা তৈরী করেন।
(৭) তিনি দেখলেন, মিসরে লোকেরা কোন বাছবিচার ছাড়াই কঠোরভাবে ইমাম মালিক এর ফিকহ অনুসরন করছে। তিনি ইমাম মালিকের আইন বিষয়ক মতামত সমূহের সমালোচনা মূলক বিশ্লেষণ করে দেখলেন, “কখনো তিনি ঘটনাবিশেষকে গুরুত্ব না দিয়ে সাধারণ নীতিমালার আলোকে মত দিয়েছেন, আবার কখনো সাধারন নীতিমালার গুরুত্ব না দিয়ে ঘটনা বিশেষের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।” তিনি লক্ষ্য করেন, ইমাম মালিক (রহ) কোন সাহাবী বা তাবেঈ প্রদত্ত বক্তব্য বা মদীনাবাসীদের ঐক্যমতকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্য আরেকটি সহীহ হাদীসকে অগ্রাহ্য করছেন এবং যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ মজুত থাকা অবস্থায় অনেক সময় ‘মাসালিহ-মুরসালাহ’ প্রয়োগ করছেন। আবু হানীফা (রহ)-এর ব্যাপারে তাঁর মত ছিল, “অনেক ক্ষেত্রে তিনি ছোটখাট বিষয় ও বিশেষ কোন বিষয়ের ব্যাপারে তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু মূলনীতির প্রতি গুরুত্ব দেননি” ইত্যাদি। তাই ইমাম শাফিঈ উপরোক্ত বিষয় সমূহকে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।
উল্লেখিত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে ইমাম শাফেঈ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সবচেয়ে বেশী মনোযোগ দিতে হবে আইন প্রনয়নের নীতিমালার সুনির্দিষ্ট করন, সেগুলোর প্রয়োগের জন্য বুনিয়াদী নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও উসূল আল ফিকহের বিকাশ ঘটানোর প্রতি যাতে এসবের সাহায্যে যথার্থ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ফিকহ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। ‘ফিকহ’-কে হতে হবে উসূলুল ফিকহের বাস্তব প্রতিফলন। এ চিন্তাধারার ভিত্তিতেই তিনি তারা সুবিখ্যাত গ্রন্থ ‘আর রিসালাহ’ ও পরবর্তীতে ‘কিতাবুল উম্ম’ রচনা করেন যার মাধ্যমে তিনি ‘উসূল আল ফিকহ’ এর ভিত্তি স্থাপন করেন।
ইমাম শাফিঈর ‘আর রিসালাহ’তে উপস্থাপিত চিন্তাধারা সমসাময়িক ‘ফিকহী’ গবেষনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এরপর দীর্ঘ সময় উসূলুল ফিকহের উপর যা লিখা হয়েছে তা মূলত এই গ্রন্থের টিকা-টিপ্পনী বা এর পক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনা-সমালোচনা সম্বলিত। অর্থাৎ এটা ঐ যুগের ‘ফিকহী’ গবেষণার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।
তবে ইমাম শাফিঈ (রহ) তাঁর উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে উসূলুল ফিকহের ভিত্তি স্থাপন করলেও এ দুটো ‘উসূল আল ফিকহ’ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ নয়, বরং এ বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করে তাঁর পরবর্তীকালে প্রধানত তাঁর অনুসারী মুজতাহিদগণের মাধ্যমে। এ বিষয়ে প্রাচীনদের লেখা শ্রেষ্টতম তিনটি বই হচ্ছে- আবু আল হুসাইন মুহাম্মদ বিন আল বসরী’র ‘মু’তামাদ’, ইমামুল হারামাইন রচিত ‘আল বুরহান’, এবং ইমাম গাজ্জালী (রহ) রচিত ‘আল মুস্তাসফা মিন ইলমুল উসূল’। পরবর্তীতে আবুল আল হোসাইন আলী ওরফে ইমাম সাইফুদ্দিন আল আমিদি তাঁর ‘আল ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম’ নামক বিখ্যাত ও সুবৃহৎ গ্রন্থে উপরোক্ত গ্রন্থত্রয়ের সারবস্তুকে একত্রিত করেন।
আশ-শাফিঈর এই চিন্তাধারা সমকালীন অন্যান্য মাযহাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বাকীরাও তখন নিজ নিজ মাযহাবের উসূল প্রণয়নে মনোবিবেশ করে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ সমস্ত উসূলই ইমাম শাফিঈ প্রণীত ‘উসূল’ এরই কিছুটা বর্ধিত বা সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন- ইমাম শাফিঈর পরবর্তী হানাফী ফকীহগণ ‘উসূল আল ফিকহ’ রচনায় হাত দেন এবং শাফিঈ উসূলের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য খুব কম। পার্থক্য কেবলমাত্র শাখা-প্রশাখা পর্যায়ে বিধান আহরণের ক্ষেত্রে। হানাফীদের রচিত উসূলুল ফিকহের গ্রন্থের মধ্যে আলী বিন মুহাম্মদ আল বাযদাবী (রহ) রচিত ‘উসূল আল বাযদাবী’ অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মালিকীদের প্রণীত ‘উসূলুল ফিকহ’ও শাফিঈ’র প্রায় অনুরূপ এবং প্রধান পার্থক্যর মধ্যে ‘মদীনার আলেমদের ঐক্যমত’ শরীয়াহর দলীল না হওয়ার বিষয়ে শাফিঈর মতভেদ উল্লেখযোগ্য। হাম্বলীরাও এই উসূল গ্রহণ করে নিয়েছে, তবে তারা ইজমা’র অর্থ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ’র সাথে মতভেদ করেছে এই বলে যে, একমাত্র গ্রহণযোগ্য ইজমা হচ্ছে ‘ইজমা আস সাহাবা’। যারা তাঁর উসূলকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে সে ধারাটিই শাফিঈ মাযহাব নামে পরিচিত হয়।
এভাবেই ইমাম শাফিঈ ‘উসূলুল ফিকহ’ একদিকে যেমন তাঁর নিজস্ব মাযহাবের বুনিয়াদ স্থাপন করে, তেমনি অন্যদিকে আর সব মাযহাবের উসূল সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার উপরও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ‘উসূলুল ফিকহ’ এর আর্বিভাবের ফলে মূল উৎস হতে ‘ফিকহ’ আহরনের একটি ছক বা মানদন্ড তৈরী হয় এবং পরবর্তীকালের সকল ‘ফিকহ’ চর্চাকারীদের জন্য একটি সাধারণ পথ তৈরী হয়।
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ) এবং ফিকহে তাঁর অবদান:
আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে (রহ) ১৬৪ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের কাছে ফিকহ এর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দেস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ) ও শায়খ আব্দুর রাজ্জাক এর কাছ থেকে শিক্ষা নেন। পরবর্তীতে তিনি ইমাম শাফিঈ (রহ) এর কাছ থেকে ‘ফিকহ’ শিক্ষা করেন। এভাবে ফিকহ ও হাদীসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তিনি ‘ইমামুল হাদীস’ এর মর্যাদা লাভ করেন।
হাম্বলী ফিকহ মূলত শাফেঈ ফিকহের অনুগামী। তাদের উসূলও প্রায় শাফেঈ উসূলই বলা চলে। তবে ইমাম আহমদ হাদীসকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন, ইজমা বলতে ইজমা আস সাহাবাকে সুনির্দিষ্ট করতেন এবং ‘কিয়াস’ যথা সম্ভব পরিহার করতেন। তিনি বলেন, “কোন ব্যক্তি বিশেষের অভিমতের চেয়ে যঈফ-দূর্বল হাদীস আমার নিকট অধিকতর উত্তম”। এ মূলনীতির ফলে তিনি মারফূ অথাব মওকূফ উভয় অবস্থাতেই সহীহ হাদীসকে আমলযোগ্য মনে করতেন। ফলে তাঁর মাযহাবে একই মাসআলায় একাধিক হুকুম পাওয়া যায়। একান্ত বাধ্য হয়ে তিনি কিয়াস করতেন এবং কোন বিষয়ে কোন সাহাবীর রায় পেলে তাকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁর অনন্য কীর্তি হচ্ছে তাঁর সংকলিত মুসনাদে ইমাম আহমদ যাতে তিনি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে চল্লিশ হাজার হাদীস সংকলন করেন। ইমাম আহমদ, ‘ফকীহ’র চেয়ে মুহাদ্দিস হিসেবেই বেশী পরিচিত। তাঁর ছাত্রবৃন্দের মাধ্যমে তাঁর মাযহাব বাগদাদ, বসরা, প্রভৃতি জায়গায় বিস্তার লাভ করে।
উপরোক্ত এই চারজন ইমাম ‘ফিকহে’ তাদের গগনচুম্বী ব্যাক্তিগত অবদানের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক দক্ষ ছাত্র তৈরী করে যান যারা পরবর্তীতে তাদের ফিকহী চিন্তাধারায় সংরক্ষন করে এবং একে মাযহাবের রূপ দেয়। বস্তুত পরবর্তী যুগে এমনকি আজ পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী এই চার ইমামের মাযহাব টিকে থাকার প্রধান কৃতিত্ব তাঁদের ছাত্রদের যারা এটাকে একযুগ থেকে অন্যযুগে বহন করে নিয়ে গেছেন। এই চার জন ছাড়াও ঐ যুগে তাদের সমপর্যায়ের যোগ্যতা সম্পন্ন আরো কিছু মুজতাহিদ ছিলেন যাদের পৃথক মাযহাব ছিলো এবং তাদের বিপুল সংখ্যক অনুসারীও ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্র্ণধার কর্তৃক প্রচারিত না হওয়ায় এবং তাদের পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্র না থাকায় তাদের মৃত্যুর কিছুদিন পর ঐসব মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যারা তারা হলেন:
১) সিরিয়ার আবু আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল আওযাঈ ও তাঁর মাযহাব।
২) ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ও তাঁর মাযহাব।
৩) আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী ও তাঁর মাযহাব।
৪) ইমাম আবু সুলাইমান দাউদ যাহেরী ও তাঁর মাযহাব। (এই মাযহাবী চিন্তাধারার সাথে মূলধারার প্রধান পার্থক্য ছিলো যে এরা কিয়াসকে শরীয়াহকে উৎস হিসেবে অস্বীকার করতো যদিও তারা ‘কিয়াসে জলী’ বলতে যা বোঝায় ভিন্ন নামে তা অনুসরণ করতো)
এর মধ্যে প্রথম তিনটি হিজরী প্রায় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, অতঃপর বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর চতুর্থটি অর্থাৎ ইমাম দাউদ যাহেরী (রহ) এর মাযহাব ইবনে খালদূনের মতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো। এসব ছাড়াও আরো কিছু মাযহাব যেমন- ইমাম হাসান বসরী (রহ), ইমাম ইসহাক ইবনে রাওয়াহ (রহ), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ) ও নায়স ইবনে সাদ (রহ) এদের মাযহাবও কিছুকাল পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তীতে এগুলোর চর্চা ও অনুসরন বন্ধ হয়ে যায় এবং হানাফী. শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী এই চারটি ‘ফিকহী স্কুল’ অবশিষ্ট থেকে যায়।
এসবের বাইরে মূলধারা থেকে প্রায় পৃথক একটি ফিকহী চিন্তাধারা যা মাযহাবও সে যুগে গড়ে উঠেছিল যা এখনও বিদ্যমান আছে, আর তা হলো শিয়া মাযহাব। তাঁরা ইমাম জাফের সাদেকের মাযহাব গ্রহন করেছিলো যদিও বস্তুতঃ তাঁরা নিজেদের আকীদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তার মতের সাথে সত্য-মিথ্যা অনেক কিছু সংযোজন করে। তাদের ফিকহের উৎসের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ’র মত তাদের বারোজন ইমামের বক্তব্যও অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ তাদের বক্তব্যকে তারা কুরআন, সুন্নাহর সমপর্যায়ের আইনগত মর্যাদা দেয় এবং তাদের ইমামদের বর্ণিত হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস গ্রহণ করে না। এছাড়া তারা কিয়াসকে শরীয়াহর উৎস হিসেবে অস্বীকার করে, এভাবে তারা প্রধান সমস্ত মাযহাবের চিন্তা থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে ভিন্ন চিন্তা পোষণ করে।
উপরোক্ত প্রধান প্রধান ‘ফিকহী স্কুল’ ও তাঁদের প্রবক্তাদের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে ফিকহের বিন্যাস উসূলুল ফিকহ প্রণয়ন, হাদীস সংকলন ইত্যাদির মাধ্যমে এ যুগে ফিকহ তাঁর সর্বোচ্চ শিখরে পৌছায়। তাদের বিখ্যাত ছাত্রদের মাধ্যমে অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে যুগের শেষ পর্যায় তথা চতুর্থ হিজরীর মাঝামাঝি পর্যন্ত।
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ যুগে মুজতাহিদ সাহাবা ও ইমামগণের ফিকহী বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণ :
“যখন হাকিম ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তখন সে দুটি সওয়াব পায়, (আর) তার সিদ্ধান্ত ভুল হলে সে অন্তঃত একটি সওয়াব পায়” [বুখারী]
এটি একটি বিস্তৃত বিষয় এবং এ বিষয়ে পূর্ববর্তীরা পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমন কি এ বিষয়টি ‘ইলমুল খেলাফ’ বা মতভেদ সম্পর্কিত জ্ঞান নামে পৃথক একটি শাস্ত্রের রূপও গ্রহণ করে। তবে খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়ে আমরা কেবল সেই মৌলিক কারণগুলো উপস্থাপন করবে যেগুলোর ভিত্তিতে সাহাবা (রা) যুগ, তাবেঈ যুগ ও তাবে-তাবেঈন যুগ তথা মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে ফিকহী বিষয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল যা এখনো বর্তমান। এগুলো হচ্ছে:
১) কোন একটি প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে হয়তো একজন সাহাবীর উক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কোনো বক্তব্য জানা ছিল পক্ষান্তরে অন্যজনের জানা ছিল না ফলে বাধ্য হয়ে তিনি সে বিষয়ে ইজতিহাদ করে রায় দিয়েছেন। যেমন: পূর্ব উমর (রা)-এর কিছু উদাহরণে এটা দেখা যায়। অনুরূপ ঘটনা মুজতাহিদ ইমামদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে কেননা তারা যাদের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন তাদের নিকট সকল সাহাবী বর্ণিত হাদীস ছিলনা যেহেতু হাদীস সংকলনের যুগ হচ্ছে এর পরবর্তী যুগ। কাজেই এটা স্বাভাবিক ছিলো যে কোন হাদীস হয়তো একজন মক্কাবাসী ইমামের জানা ছিলনা কিন্তু কুফাবাসী ইমামের তা জানা ছিল।
২) হয়তো হাদীসটি সাহাবা বা ইমামের নিকট পৌছেছে কিন্তু তা তাঁর কাছে বিভিন্ন করণে নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়নি। যেমন-হয়তো হাদীস বর্ননাকারী ইমামের নিকট অজ্ঞাত, বা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত বা স্মৃতি শক্তিতে দূর্বল বা হাদীসটি তার কাছে মারফু অবস্থায় পৌছেনি বরং মুনকাতি অবস্থায় পৌছেছে, কিংবা হাদীসের শব্দাবলী (মতন) দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত ছিলনা ইত্যদি। পক্ষান্তরে হয়তো একই হাদীস অন্য ইমামের নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী দ্বারা মুত্তাসিল সনদে পৌছেছে বা অন্য কোন সনদে পৌছেছে বা এর স্বপক্ষীয় আরো এমন কিছু হাদীস পৌছেছে যার দ্বারা উক্ত হাদীস শুদ্ধ প্রমাণিত হয়। তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের মাঝে এরূপ ঘটনার সংখ্যা অনেক। এরূপ ক্ষেত্রে, যার নিকট হাদীসটি সঠিক পন্থায় পৌছেছে তিনি তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন পক্ষান্তরে যার নিকট দূর্বল সূত্রে পৌছেছে তিনি তা থেকে দলীল গ্রহণ করেননা। যেমন: ফিতনা ছাড়িয়ে পড়ার হেজাজ, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ইমামরা নিজের অঞ্চলে বাইরে অন্য অঞ্চলের হাদীস গ্রহণ করতেন না যদি না তা তাদের নিজেদের অঞ্চলেও তা প্রচলিত না থাকতো কেননা এ বিষয়ে তাঁরা হাদীস জাল হবার আশংকা করতেন।
৩) কোন ইমাম খবরে ওয়াহিদের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে এমন কিছু শর্তারোপ করেন যা অন্যরা করেন না ফলে উভয়ের মধ্যে উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে দলীল গ্রহণ করা বিষয়ে মতভেদ হয়। যেমন: কেউ বলেন খবরে ওয়াহিদ কুরআন হাদীস ভিত্তিক হতে হবে, বর্ণনাকারী ফকীহ হতে হবে ইত্যাদি।
৪) কিছু বিশেষ ধরণের হাদীস ব্যবহারে দলীল দেয়া কোন কোন ইমামের জন্য দোষণীয় নয় পক্ষান্তরে অন্যদের নিকট তা দোষণীয় ফলে তারা তা বর্জন করেন। যেমন: ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক মুরসাল হাদীস থেকে দলীল নিতেন কিন্তু ইমাম শাফেঈ তা নিতেন না, পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ যঈফ হাদীস থেকেও দলীল নিতেন যা অধিকাংশ ইমাম নিতেন না।
৫) মতভেদের এটাও কারণ যে, হয়তো ঐ বিষয়ে কোন হাদীস ইমামের জানা ছিল কিন্তু তিনি তা ভুলে গেছেন। ফলে তিনি তা থেকে দলীল গ্রহণ করেননি। যেমন: সফরে কোন ব্যক্তি নাপাক হলে এবং পানি না পাওয়া গেলে কীভাবে নিজেকে পবিত্র করবেন তা উমর (রা) এর জানা ছিল কিন্তু তিনি তা ভুলে যান। পরে আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা) তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন। অনুরূপে, তিনি মোহরের পরিমান ধার্য করে দিতে চাইলে এক মহিলা তাঁর সামনে কুরআনের আয়াত পেশ করেন যা তাঁর নিজেরও জানা ছিল ফলে তিনি ঐ অনুযায়ী রায় দিলেন। অনুরূপে সাহাবী ইবনে উমর যখন বললেন, “রাসূল (সা) একটি উমরা করেছেন রজব মাসে তখন আয়েশা (রা) বললেন, ইবনে উমর ব্যাপারটা ভুলে গেছেন। [জামউল ফাওয়ায়িদ]
৬) রাসূলুল্লাহ (সা) এর কোনো কাজের ধরণ নির্ণয়ে পার্থক্যের দরুণও মতপার্থক্য হতে পারে যদ্বরুন একই কাজকে কেউ মুবাহ আর কেউ সুন্নাহ মনে করতে পারে। যেমন : হজ্জের সফরে রাসুলুল্লাহ (সা) এর আবতাহ উপত্যকায় অবতরণ। একদল সাহাবী এটাকে ইবাদতের অংশ হিসেবে দেখেন আর অন্য দল বলেন যে তিনি ঘটনাক্রমে সেখানে অবতরণ করেছেন।
৭) মতপার্থক্যর আরেকটি কারণ হলো: সংশ্লিষ্ট ইমাম হয়তো হাদীসটি জানেন কিন্তু হাদীসের বক্তব্যের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেন। যেমন: “মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেযা হয়”-ইবনে উমর বর্ণিত ও হাদীস শুনে আয়েশা (রা) এ হাদীসের প্রকৃত ব্যাপার তুলে ধরেন যা থেকে বুঝা যায় ইবনে উমর হাদীসটির বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি।
৮) মতভেদের এটাও একটা কারণ যে, কোন হাদীস থেকে বিধান স্থির করার পিছনে ইল্লত বা কারণ কি ছিল তা নির্ধারণে কখনো কখনো মতানৈক্য হতো। যেমন: কফিন অতিক্রমকালে দাঁড়ানো সম্পর্কিত হাদীসে দাঁড়ানোর কারণ বর্ণনার সাহাবীদের একাধিক ব্যাখ্যা ছিল।
৯) কোন ইমাম কতৃক কোন কোন হাদীসে আমল না করার এটাও একটা প্রসিদ্ধ কারণ যে, তার দৃষ্টিতে উক্ত হাদীস আলোচ্য সমস্যার সমাধানে কোন ইঙ্গিত বহন করেনা বা এ আয়াত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে এ বিধান আসেনা। এই কারণের অধীনে আরো অনোকগুলো কারণ আছে যার সাথে আরবী ব্যাকরণের অনেক নিয়ম-কানুন ও সংযুক্ত। আম ও খাস নির্ধারণ, কোন বস্তু থেকে বিপরীত বোধগম্য বিষয়কে দলীলরূপে গ্রহণ করা, কোনো কারণ ভিত্তিক আম ঐ কারণের উপর সীমিত থাকা, কেবল আমর বা আদেশবাচক হলেই তা দ্বারা ওয়াজিব প্রতিষ্ঠা হওয়া না হওয়া ইত্যাদি আরো অনেক বিষয় এর অন্তর্ভূক্ত যা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। উসূল আল ফিকহ-এর বিরোধপূর্ণ মাসআলা গুলোর প্রায় অর্ধেক এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।
১০) এটাও মতপার্থক্যের অন্যতম কারণ যে, হয়তো কোন ইমাম কোন হাদীসের উপর আমল বর্জন করেন যেহেতু ঐ মাসআলায় তার কাছে এর বিপক্ষে অন্য দলীল আছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিরোধপূর্ণ হাদীস দ্বয়ের ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধানগত মতপার্থক্য তৈরী হয়। কেউ হয়তো একটিকে মূল ধরে আরেকটিকে তা’ওয়ীল করেন, আবার কেউ হয়তো একটিকে মনসুখ আর অন্যটিকে নাসেখ হিসেবে দেখেন ইত্যাদি। ফলে মতপার্থক্য অনিবার্য হয়। মুতআ বিবাহ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) এর মত বাকীদের বিপরীত হবার কারণ এ শ্রেণীতে পড়ে। অনুরূপে, সালাতে রফউল ইয়াদাইন বিষয়ে হানাফী ও শাফেঈদের মতপার্থক্যও এ বিষয়ের অধীন।
১১) মুজতাহিদ ইমামগণের মতপার্থক্যের এটাও একটা অন্যতম কারণ যে, ইমাম তাঁর প্রণীত উসুলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌছান। এমতবাস্থায় উসূলের যৎসামান্য ভিন্নতায় বিধান আহরণের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা তৈরী হয। যেমন: ইমাম মালিক “মদীনাবাসীদের সম্মিলিতি আমল’ কে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করায় এর বিপরীত অনেক সহীহ হাদীস তিনি বর্জন করেন কিন্তু অন্যান্য ইমামরা ঐ বিষয়কে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ না করায় তারা এ সমস্ত হাদীসের ভিত্তিতে দলীল গ্রহণ করেন।
এভাবে বিভিন্ন করণে মুজতাহিদ ইমামদের ফিকহী সিদ্ধান্তে মতপার্থক্য সূচিত হয় যদিও এর প্রায় সবই হচেছ শরীয়াহ’র শাখা-প্রশাখায়, মূল বিষয়গুলিতে নয়। এখানে যেটা সবচেয়ে উলে¬খযোগ্য তা হলো, এসব মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের ইজতিহাদকৃত বিষয়ই ‘ইসলামী মত’ কেননা তারা প্রমাণিত ইসলামী পদ্ধতি ব্যবহার করেই এসব সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। এ বিষয়ে তাদের সঠিক হওয়া বা ভূল হওয়া নিম্নের হাদীসের অধীন:
“যখন হাকিম ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তখন সে দুটি সওয়াব পায়, (আর) তার সিদ্ধান্ত ভুল হলে সে অন্তঃত একটি সওয়াব পায়”।
ফিকহের স্থবির যুগ:
হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ফিকহ চর্চায় এক ধরনের স্থবিরতার জন্ম নেয়। এ যুগে ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং উলামা ও সাধারণ মানুষ সবাই বিশিষ্ট ইমামদের ফিকহী চিন্তার অনুসরণ করার মাঝে নিজেদের প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। এ সময়ের ফিকহী আলোচনা নতুন কোন দিক নির্দেশনা মূলক না হয়ে বরং পূর্ববর্তীদের রচিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও তাতে টিকা-টিপ্পনী সংযোজন এবং পূর্ববর্তী ইমামগণ কর্তৃক মাসয়ালা-মাসায়েলের বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও নিজ নিজ মাযহাবের ইমামদের সমর্থনে ও পক্ষে বিপক্ষে মুনাযারা ও বাহাস বিতর্কের মাঝেই আবর্তিত হতে থাকে। এযুগে ফকীহগণ কদাচিৎ কোন সমস্যায় সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর দ্বারস্থ হতেন বরং স্বীয় মাযহাবের মধ্যেই ঐ সমস্যার সমাধান খুঁজতেন। এ সময় তারা কুরআন-সুন্নাহ’র অধ্যয়নকে স্বীয় মাযহাবের পক্ষ সমর্থনকারী আয়াত-হাদীস অনুসন্ধানের মাঝে সীমিত করেন, ফলে আগত নতুন সমস্যার সমাধান মূল দুটি উৎস থেকে খোঁজার ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের যে শিক্ষা তা চাপা পড়ে। এভাবে এ যুগে ফিকহ এর মূল প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কেবল অনুসরণ ও অনুসৃত বিষয়ের ব্যাখা-বিশ্লেষণে পর্যবসিত হয়। তাই এ যুগে ফিকহের স্থবিরতার যুগ। বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তিত্ব ও তাদের কিছু অবদান ছাড়া এযুগে ফিকহের বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হয়ে হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত চলে এ যুগ।
ফিকহের পতন যুগ:
স্থবিরতার স্বাভাবিক পরিনতি হিসেবেই ফিকহ তার পতন যুগের দিকে এগিয়ে যায়। হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এই যুগের সূচনা হয়। স্থবির যুগের প্রভাবে এ যুগে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা সম্পন্ন প্রজন্মই গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে এযুগে এসে ইজতিহাদ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি মাসআলার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যে অনুশীলন তাও হারিয়ে যায়। শুরু হয় পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া জিনিসের খালেস তাকলীদের যুগ। এ যুগে বিভিন্ন মাসআলায় পূর্ববর্তীদের ব্যবহৃত দলীল প্রমাণ উল্লেখ না করেই সরাসরি সেসব মাসআলা লিপিবন্ধ করার প্রচলন হয় এবং জনসাধারণের মাঝে তা প্রচারিত হয়। ফলে, মূল উৎস হতে ফিকহ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ফিকহ পরিণত হয় শুষ্ক আইনগ্রন্থে এবং এসবের শিক্ষার মাধ্যমে এমন এক পঙ্গু প্রজন্ম তৈরী হয় যারা ফিকহের বিকাশে ছিল সম্পূর্ণ অক্ষম।
এ যুগের একদম প্রথমদিকে যদিও বিভিন্ন মাযহাবে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যাদের অনেকেই ছিলেন স্বাধীন ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন কিন্তু স্থবিরতা এমন পর্যায়ে পৌছে ছিল যে তা ভাঙ্গার জন্য এই গুটিকয়েক ব্যক্তিত্বের সাময়িক আবির্ভাব যথেষ্ট ছিলনা। এদের মধ্যে হানাফী মাযহাবের কামাল ইবনে হুমাম (রহ), জামালুদ্দীন যায়লাঈ (রহ), শাফিঈ মাযহাবের ইযযুদ্দীন আবদুস সালাম (রহ), তাকীউদ্দিন সুযুকী (রহ), জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ), মালেকী মাযহাবের আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহ) ও হাম্বলী মাযহাবের আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ) ও হাফিয ইবনে কায়্যিম (রহ) উল্লেখযোগ্য। এদের প্রচেষ্টার কিছুকালের জন্য ‘ফিকহ’ এর প্রানবন্ত চর্চা চলে।
কিন্তু এর পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ফিকহের পতন চলতেই থাকে। তথাপি এ পতন ইসলামের সীমারেখার মধ্যেই ছিল অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত ফিকহের অনুশীলনে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটেনি।
কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ থেকে পতন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, শরীয়াহ’র আইনকে অনৈসলামী আইনের সাথে মিশিয়ে ফেলা শুরু হয় এবং এর যৌথ অনুসরণ চলতে থাকে। এর যাত্রা শুরু হয় ১২৭৪ হিজরীতে যখন উসমানী খিলাফতের অধীনে হুদুদ আইনগুলো পরিবর্তন করে তৎপরিবর্তে উসমানী পেনাল কোর্ড ইস্যু করা হয়। অতঃপর ১২৭৬ হিজরীতে অধিকার ও বাণিজ্য সম্পর্কিত আইন পাশ করা হয়। এভাবে ইসলামী উৎস ছাড়া অন্যান্য উৎস হতে আইন গ্রহণ করা চলতে থাকে যার মধ্যে দিয়ে ফিকহের তথা ইসলামী আইনশাস্ত্রের চরম অধঃপতন সূচিত হয়।
ইসলামী আইনের সাথে অনৈসলামী উৎস হতে আগত এসব আইনের মিশ্রণ চলতে থাকে উসমানী খিলাফতের শেষ তথা ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। অবশেষে, ১৯২৪ সালে খিলাফত ব্যবস্থার পতনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অবির্ভাবের ফলে ইসলামী ফিকহ পুরো পুরি রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং মুসলিম ভূমি গুলো অনৈসলামী আইনের ভিত্তিতে শাসিত হতে শুরু করে- যার মাধ্যমে ফিকহ এর চূড়ান্ত অধঃপতন সম্পূর্ণ হয়। সেই অধঃপতনের ধারাবাহিকতা পরবর্তী সময়ে আরো প্রকট রূপ ধারণ করে চলছে আজ পর্যন্ত।
‘ইলমুল ফিকহ’ পুনরুজ্জীবিত করার উপায়:
যেহেতু ফিকহ হচ্ছে বাস্তব জীবন পরিচালনার আইন কানুন সম্পর্কিত জ্ঞান অতএব জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে কখনোই এর পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়, বরং এই বিচ্ছিন্নতাই ফিকহ এর বর্তমান দুরবস্থার কারণ। বাস্তব জীবন পরিচালনায় যতবেশী ফিকহ ব্যবহৃত হবে ততই প্রয়োজনের তাগিদে এর বিকাশ ঘটতে থাকবে। তাই জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রে ফিকহ তথা ইসলামী আইনের প্রয়োগই ফিকহকে পুনরুজ্জীবিত করার একমাত্র পথ। বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলাম দিয়ে পরিচালিত না হওয়ায় উম্মাহর মাঝে ফিকহ জানার কোন চাহিদা নেই, কেননা এই সম্পর্কিত কোন জ্ঞান ছাড়াই বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রে সে তার সফল প্রয়োজন মেটাতে পারে। কিন্তু ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত একটি সমাজে জনগন স্বভাবিক প্রয়োজনের তাগিদেই ফিকহক চর্চায় বাধ্য হবে, যুগের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে মূল উৎসগুলোর দ্বারস্থ হবে, ইজতিহাদের চাকাকে সচল করবে আর এভাবেই ফিকহ আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে।
এজন্য প্রথমে প্রয়োজন এমন একটি দল যারা বিশুদ্ধ চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতি ফিকহ এর সঠিক চর্চার মাধ্যমে গৃহীত, যারা নিজ দলের অভ্যন্তরে এই সম্পর্কে সঠিক চিন্তার শিক্ষা দেয় এবং উম্মাহর মাঝেও এই চিন্তাকে ছড়িয়ে দেয়। একই সাথে এ দলটি উম্মাহকে এমনটি একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে আহবান জানায় যেখানে সব কিছু পরিচালিত হবে ইসলামী আইন তথা ফিকহ চর্চার মাধ্যমে- যাতে করে উম্মাহ ফিকহ এর বাস্তব উপযোগীতা বুঝতে পারে। এ আহ্বান এবং এর ভিত্তিতে নির্ধারিত তরীকা অনুসরন করে যখন সে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন নতুন যুগে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী চাহিদা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করার প্রয়োজনে ফিকহ চর্চায় আবারও গৌরবজ্জ্বল যুগের সূচনা হবে।
আহমেদ জামাল