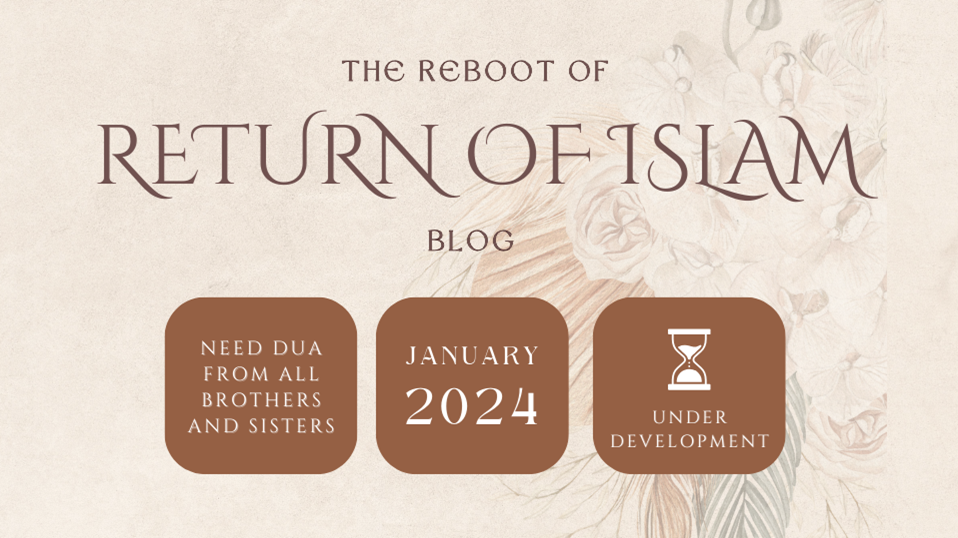আদালতের রায় কার্যকর করার লক্ষ্যে রায় প্রদান করা বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব। এ বিভাগ জনগণের মধ্যকার বিবাদের মীমাংসা করে, জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে বা জনস্বার্থের জন্য হুমকীস্বরূপ বিষয়সমূহ প্রতিহত করে এবং জনগণ ও শাসনব্যবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করে, এসব ব্যক্তিবর্গ হতে পারেন শাসক, সরকারী কর্মকর্তা, খলীফা বা অন্য কোন ব্যক্তি।
ইসলামী বিচারব্যবস্থার উৎস ও এর বৈধতার দলিল হল আল্লাহ্’র কিতাব ও রাসূল (সা) এর সুন্নাহ্।
আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,
‘আর আপনি তাদের পারষ্পরিক বিষয়সমূহে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন।’
[সূরা মায়েদা: ৪৯]
তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা’আলা) আরও বলেন,
‘তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের মধ্য হতে কোন কোন দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।’
[সূরা নূর: ৪৮]
সুন্নাহ্’র ক্ষেত্রে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে বিচারব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি (সা) স্বয়ং লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতেন।
রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে বিচারকদের নিয়োগ দিতেন। তিনি (সা) আলীকে ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং বিচারকার্য পরিচালনার জন্য এভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে,
‘যদি দুইজন ব্যক্তি তোমার কাছে বিচারের জন্য আসে তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত একজনের পক্ষে রায় দিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি অপরজনের কথা শুনো; আর, এভাবেই তুমি লোকদের মধ্যে ফায়সালা করতে পারবে।’
(সূনানে তিরমিযী, হাদীস নং-১৩৩১ এবং মুসনাদে আহমাদ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৫)
আহমেদ এর অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে:
‘যদি দু’জন বিবাদমান ব্যক্তি তোমার সামনে বসে তবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি অন্যজনের কথা শোন, যেভাবে তুমি প্রথমজনের কথা শুনেছো।’
(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৫)
এছাড়া, তিনি (সা) মুয়াজকে আল-জানাদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। উল্লেখিত এ প্রতিটি ঘটনা বিচারব্যবস্থার বৈধতাকে প্রমাণ করে।
বিচারব্যবস্থার সংজ্ঞার মধ্যে জনগণের মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তি করা অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া, এর মধ্যে হিসবাহ্ (জনগণের অধিকার) ও অন্তর্ভূক্ত, যার অর্থ হল: “বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনগণকে শারী’আহ্ বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করা, যে বিধিবিধান লঙ্ঘনের ফলে জনস্বার্থ ক্ষুন্ন বা জনগণের অধিকার বিনষ্ট হয়।” এই বিষয়টি খাদ্যের স্তুপ সম্পর্কিত হাদীসে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত আছে। আবু হুরাইরার বরাত দিয়ে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে,
‘রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার খাবারের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তুপের ভেতর তার আঙ্গুল প্রবেশ করানোর পর আর্দ্রতা অনুভব করলেন এবং তখন বিক্রেতাকে বললেন, ’এটা কি?’ তখন উক্ত বিক্রেতা তাকে বললেন, ‘হে ‘রাসূলুল্লাহ্ (সা), এগুলো বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।’ তখন তিনি (সা) বললেন, ‘তুমি এগুলোকে উপরে রাখছ না কেন যাতে লোকেরা দেখতে পায়? যে প্রতারণা করে সে আমাদের কেউ নয়।’
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১০২)
এছাড়া, বিভাগের মধ্যে মাযালিম (অন্যায় আচরণ) ও অন্তর্ভূক্ত। কারণ, মাযালিম বিচারকার্যের অংশ, শাসনকার্যের নয়। প্রকৃত অর্থে, মাযালিম বলতে শাসকের বিরুদ্ধে কৃত অভিযোগকে বোঝায়। মাযালিমকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে: “সাধারণ জনগণ এবং খলীফা কিংবা, তার কোন ওয়ালী বা কর্মকর্তার মধ্যকার বিবাদ নিরসনের জন্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে শারী’আহ্ রায় প্রদান করা; কিংবা, জনগণকে শাসন করার নিমিত্তে ব্যবহৃত কোন শারী’আহ্ দলিলের ব্যাখ্যার ব্যাপারে জনগণ ও শাসকের মধ্যে কোন প্রকার মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে সে বিষয়টি নিরসন করা।” রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত হাদীসে মাযালিম -এর ব্যাপারটি উল্লেখিত আছে, যেখানে তিনি (সা) বলেছেন:
‘এবং আমি অবশ্যই আশা করি যে, আমি আল্লাহ্ ওয়া জাল্লার সামনে এমনভাবে হাজির হব যাতে কেউ আমার বিরুদ্ধে মাযালিমা’র (অন্যায় আচরণের) অভিযোগ না করতে পারে, সেটা রক্ত সম্পর্কিত হোক বা অর্থ সম্পর্কিতই হোক।’
(আনাসের বরাত দিয়ে আহমাদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; দেখুন: আল হাইছামী, মাজমা’ আল-জাওয়ায়িদ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০২)
এ হাদীসটি আমাদের দিকনির্দেশনা দেয় যে, শাসক, ওয়ালী অথবা জনপ্রশাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে মাযালিমের বিচারকদের নিকট পেশ করতে হবে এবং তিনি প্রয়োগের নিমিত্তে এ ব্যাপারে শারী’আহ্ বিধিবিধান অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন।
সুতরাং, রাসূল (সা) এর হাদীস ও কর্মকান্ড থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বিচারব্যবস্থার সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত এবং এগুলো হল: জনগণের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করা, জনগণের অধিকার ক্ষুন্ন হতে পারে এমন কর্মকান্ড প্রতিরোধ করা এবং জনগণ ও শাসকের মধ্যকার বিরোধ অথবা জনপ্রশাসক ও জনগণের মধ্যকার বিরোধের মীমাংসা করা। বিচারকদের প্রকারভেদ
ইসলামী বিচারব্যবস্থায় তিন ধরনের বিচারক রয়েছে
১. কাজী আল-খুশুমাত: যিনি হুদুদ (শাস্তি সম্পর্কিত) এবং লেনদেন বিষয়ে জনগণের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করবেন।
২. কাজী আল-মুহতাসিব: যিনি কোন আইন লঙ্ঘনের কারণে যদি জনস্বার্থ ক্ষুন্ন বা জনসম্পদ বিনষ্ট হয় তাহলে সে বিষয়ে বিচার করবেন।
৩. কাজী আল- মাযালিম: যিনি রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যকার বিবাদের নিষ্পত্তি করবেন।
কাজী আল-খুশুমাত (যিনি জনগণের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করবেন) এর ব্যাপারে দলিল হল রাসূল (সা)এর কর্মকান্ড এবং রাসূল (সা) কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারক নিযুক্তকরণ। যেমন: তিনি মুয়াজ ইবন জাবালকে ইয়েমেনের একটি অঞ্চলের বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।
কাজী আল-মুহতাসিব (যিনি জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে বিচার করবেন) এর ব্যাপারে দলিল হল রাসূল (সা) এর কাজ এবং উক্তি যেখানে তিনি বলেছেন: “যে প্রতারণা করে সে আমাদের কেউ নয়।” [এটি আবু হুরাইরার বরাত দিয়ে আহমাদ বর্ণিত একটি হাদীসের অংশ]; এ হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা) প্রতারকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করতেন এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।
এছাড়া, তিনি (সা) ব্যবসায়ীদের ব্যবসাকালে সত্য কথা বলার এবং সাদাকা প্রদানের নির্দেশ দিতেন। কায়েস ইবনে আবি ঘারজা আল কিনানীর সূত্রে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, আবি ঘারজা বলেছেন: “আমরা মদিনাতে সাধারণত মালামাল ভর্তি কার্গো ক্রয় করতাম এবং নিজেদের ফরিয়া বলে পরিচয় দিতাম। রাসূল (সা) আমাদের কাছে এলেন এবং আমাদের উত্তম নামে অভিহিত করলেন এবং বললেন,
‘হে ব্যবসায়ীগণ, অবশ্যই ব্যবসার সাথে শপথ গ্রহণ ও কথাবলার বিষয়গুলো জড়িত। সুতরাং, তোমরা এর সাথে সাদাকাকে সম্পর্কিত করে নাও।’
এছাড়া, আবু আল মিনহাল থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে:
‘জায়েদ ইবনে আরকাম ও আল বারা ইবনু ’আযিব ব্যবসায়িক অংশীদার ছিল। তারা কিছু রৌপ্য নগদ অর্থে এবং কিছু বাকীতে খরিদ করল। এ খবর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট পৌঁছালো তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে, ‘যেখানে নগদ পরিশোধ করা হয়েছে সেখানে কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু, যা বাকীতে বিক্রয় করা হয়েছে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।’ এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ঋণের সাথে যুক্ত সুদ থেকে রক্ষা করলেন।
এ সবই কাজী হিসবাহ্’র বিচারকার্যের এখতিয়ারভূক্ত বিষয়। জনস্বার্থের জন্য হুমকীস্বরূপ বিষয়সমূহ মীমাংসা করার জন্য বিচারব্যবস্থার হিসবাহ্ নামক এ বিভাগটি আসলে একটি বিশেষ অর্থবোধক শব্দ যা দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পাদিত একটি বিশেষ কাজকে বোঝানো হয়ে থাকে; যেমন: ব্যবসায়ী ও দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করা যেন তারা তাদের ব্যবসা, তাদের শ্রম, উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে কিংবা পণ্যদ্রব্য ওজন ও পরিমাপের সময় কিংবা অন্যকোন পদ্ধতিতে জনগণকে প্রতারিত করতে না পারে, যা কিনা জনস্বার্থকে ক্ষুন্ন করতে পারে। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে সেই কাজ যা রাসূল (সা) নিজে করে দেখিয়েছেন, এ বিষয়ে তদারকি করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সরাসরি রায় প্রদান করেছেন; যা কিনা আল-বারা ইবনে আযিব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, যেখানে তিনি (সা) উভয়পক্ষকে সুদভিত্তিক ঋণে ক্রয়বিক্রয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।
এছাড়া, মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ্’র রাসূল (সা) সা’ইদ ইবনুল আসকে মক্কার বাজারের মুহতাসিব হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, যা ইবন সা’দ এর তাবাকাত ও ইবন ’আবদ আল-বার এর আল-ইসতিয়াব গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। সুতরাং, হিসবাহ্’র দলিল হল রাসূল (সা) এর সুন্নাহ্। এছাড়া, উমর (রা) তাঁর নিজ গোত্রের উম্ম সুলাইমান ইবন আবি হিশমা উরফে আশ-শিফা নামের এক মহিলাকে বাজার পর্যবেক্ষক (ইন্সপেক্টর) হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন; এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন উতবাহ’কে মদিনার বাজারের বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন, যা ইমাম মালিক তাঁর আল-মুয়াত্তা এবং ইমাম শাফী’ তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, তিনি নিজেও মুহাম্মদ (সা) এর মতো বাজারে টহল দিতেন এবং হিসবাহ সম্পর্কিত বিষয়াদি তদারকি করতেন। খলীফাগণ এভাবেই নিজেরা হিসবাহ্ সম্পর্কিত বিষয়াদি তদারকী করতে থাকেন যে পর্যন্ত না আল-মাহদী তার শাসনামলে হিসবাহ্’কে বিচারব্যবস্থার একটি বিশেষ বিভাগে পরিণত করেন। খলীফা হারুনুর রশীদের সময় মুহতাসিবগণ (হিসবাহ’র বিচারক) বাজারে ঘুরে ঘুরে টহল দিতেন, ওজন ও পরিমাপের বিষয়সমূহ তদারকি করতেন এবং সকল প্রকার লেনদেন পর্যবেক্ষণ করতেন।
আর, কাজী আল-মাযালিমের দলিল পাওয়া যায় পবিত্র কুর’আন থেকে যেখানে আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,
‘যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পর, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।’
[সূরা নিসা : ৫৯]
এর ঠিক আগে আল্লাহ্ বলেন,
‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্’র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের।’
[সূরা নিসা: ৫৯]
সুতরাং, সাধারণ জনগণ ও কর্তৃত্বশীলদের মধ্যকার যে কোন বিরোধ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) এর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ, আল্লাহ্’র হুকুমের নিকট পেশ করতে হবে। মূলতঃ এ ব্যাপারটিই একজন বিচারকের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে যিনি এ ধরনের বিবাদের ব্যাপারে আল্লাহ্’র হুকুম অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন; আর এ বিচারকই হচ্ছেন মাযালিমের বিচারক। এছাড়া, আল্লাহ্’র রাসূল (সা) এর কাজ ও উক্তি থেকেও এ বিষয়ে দলিল পাওয়া যায়। তবে, রাসূল (সা) সমগ্র রাষ্ট্রের উপর বিশেষ কাউকে মাযালিমের বিচারক হিসাবে নিয়োগ করেননি; কিংবা তাঁর পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদীনগণও তা করেননি। বরং, তাঁরা নিজেরাই এ দায়িত্ব পালন করেছেন; যেমনটি হয়েছিল ’আলী ইবন আবি তালেবের (রা) সময়। কিন্তু, তিনি মাযালিমের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় বা বিশেষ কোন পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি; তিনি এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই সেটি ফয়সালা করতেন। সুতরাং, এটা আসলে তিনি তার সাধারণ দায়িত্বকর্তব্যের অংশ হিসাবেই করতেন। খলীফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপারটি এভাবেই চলতে থাকে। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন প্রথম খলীফা যিনি মাযালিমের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেন। যখনই মাযালিম সম্পর্কিত কোন বিষয় তার কাছে অস্পষ্ট মনে হত তিনি তখন তার বিচারককে এ বিষয়টি ফয়সালার দায়িত্ব দিতেন। এর পরবর্তী সময় থেকে খলীফাগণ জনগণের অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয় দেখাশুনার জন্য সহকারী নিয়োগ করতেন। তখন থেকেই মাযালিমের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থার জন্ম হয়, যা কিনা ‘সুবিচারের গৃহ’ বা দার-উল-আদল নামে পরিচিতি লাভ করে। মাযালিমের বিচারক নিয়োগ করা এজন্য অনুমোদিত যে, খলীফা তার নির্বাহী ক্ষমতা বলে তার পক্ষ থেকে যে কাউকে তার সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন। সুতরাং, এ কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি একজন বিচারকও নিয়োগ করতে পারেন। এছাড়া, মাযালিমের জন্য কোন বিশেষ সময় বা পদ্ধতি নির্ধারণ করাও অনুমোদিত, কারণ এসবই মুবাহ্ (অনুমোদিত) কাজের অন্তর্ভূক্ত।
বিচারকের যোগ্যতার শর্তাবলী
যিনি বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তাকে অবশ্যই মুসলিম, স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, ন্যায় বিচারক, ফকীহ্ (বিজ্ঞ আলেম) এবং বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে শারী’আহ্ আইন প্রয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। এছাড়া, যিনি মাযালিমের বিচারকের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তাকে উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ করা ছাড়াও অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে পুরুষ ও মুজতাহিদ হতে হবে, যা কিনা প্রধান বিচারপতির (কাজী আল কুদাহ্) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, মাযালিমের বিচারকের কাজে বিচার ও শাসন এদু’টি বিষয়ই জড়িত ও এক্ষেত্রে শাসকের উপর শারী’আহ্ আইন বাস্তবায়ন করা হয়। সুতরাং, বিচারকের অন্যান্য পদের ব্যতিক্রম হিসেবে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে মাযালিমের বিচারককে পুরুষ হতে হবে। এছাড়া, শাসকগণ আল্লাহ্’র আইন ছাড়া অন্যকোন কিছু দিয়ে শাসন করছেন কিনা, অর্থাৎ, তারা এমন কোন আইন প্রয়োগ করছেন কিনা যার কোন শারী’আহ্ দলিল নেই, সে বিষয়গুলোকে প্রতিহত করতে, কিংবা, তারা এমন কোন দলিল ব্যবহার করছেন কিনা যা ঘটনার সাথে সম্পর্কিত নয় তা বোঝার জন্য তাকে মুজতাহিদও হতে হবে। কারণ, একমাত্র একজন মুজতাহিদই মাযালিমা সম্পর্কিত এ জটিল বিষয়সমূহ বুঝতে পারেন। আর, তিনি যদি মুজতাহিদ না হন তবে এমন হতে পারে যে, তিনি এমন সব বিষয়ে বিচার করতে পারেন যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই, যা কিনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। একারণে, শাসক বা অন্যান্য বিচারক পদের যোগ্যতার শর্তের ব্যতিক্রম হিসাবে মাযালিমের বিচারককে মুজতাহিদ হতে হবে।
বিচারক নিয়োগ
কাজী-উল খুশুমাত, মুহতাসিব এবং মাযালিমের বিচারকগণকে সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী সব বিষয়ে সাধারণ ক্ষমতা দিয়ে নিয়োগ করা অনুমোদিত। আবার, তাদের ভৌগলিক অঞ্চল ভেদে কোন বিশেষ এলাকায় কিংবা, কোন বিশেষ বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ দেয়াও অনুমোদিত। রাসূল (সা) এর সুন্নাহ্’তে এ ব্যাপারে দলিল রয়েছে; যেমন: তিনি (সা) আলী ইবনে আবি তালিবকে সমগ্র ইয়েমেনের উপর, মু’য়াজ ইবনে জাবালকে ইয়েমেনের কিছু অঞ্চলের উপর এবং আমর ইবনে আল আসকে একটি বিশেষ বিষয়ে বিচারক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।
বিচারকদের সম্মানী বা বেতন ভাতা
আল হাফিয তার আল-ফাতেহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে: সম্মানী বা বেতন ভাতা হচ্ছে সেটাই যা মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার কাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে ইমাম বাইতুল মাল থেকে প্রদান করেন। বিচারকার্য সম্পাদন করা রাষ্ট্রের এমন একটি কাজ যার জন্য অবশ্যই বাইতুল মাল থেকে সম্মানী গ্রহণ করা বৈধ। কারণ, এটি জনস্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কাজ। বস্তুতঃ কাউকে যদি মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার্থে শারী’আহ্ আইন অনুযায়ী কোন কাজ সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়, তা ইবাদত সংক্রান্ত হোক বা অন্য কোন বিষয় হোক, তাহলেই সে সম্মানী পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। এর পক্ষে দলিল হল আল্লাহ্’র আয়াত; কারণ, আল্লাহ্ তা’আলা সাদাকাহ্ সংগ্রহকারীদের জন্য সাদাকার (যাকাতের) একটি অংশ নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:
‘এবং যারা তা সংগ্রহ করে।’
[সূরা তাওবা: ৬০]
আবু দাউদের শুনান গ্রন্থে এবং ইবনে খুজায়মা’র সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে বুরাইদা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে – যাকে আল বায়হাকী ও আল হাকীম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ্ হাদীসের শর্ত পূরণ করেছে বলে মতামত দিয়েছেন এবং আল জাহাবীও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন যে:
‘আমরা যদি কোন কর্মচারীকে নিয়োগ দেই ও তার জন্য সম্মানী ভাতা নির্ধারণ করে দেই, তারপরও যদি কেউ এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তবে তা অবশ্যই প্রতারণা (ঘূলুল)।’
(সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২৯৪৩)
আল মাওয়ারদী তার আল-হাওয়ী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ‘বিচারকগণ বাইতুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন। কেননা আল্লাহ্ সাদাকার মধ্যে সাদাকা সংগ্রহকারীদের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছেন। এছাড়া, উমর (রা) সুরাই’কে নিয়োগ করেছিলেন এবং তার জন্য মাসিক একশত দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। আলীর (রা) খিলাফতের সময় তিনি সুরাই এর জন্য মাসিক পাঁচশত দিরহাম নির্ধারণ করেন; এছাড়া জায়েদ ইবনে সাবিতও (রা) বিচারকার্যের জন্য অর্থ গ্রহণ করতেন।’ আল বুখারী এ বক্তব্যের ব্যাপারে বলেছেন যে, ‘সুরাই বিচারকার্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন।’
এছাড়া, আল-হাফিয এ মন্তব্যের ব্যাপারে বলেন যে, ‘সা’ইদ ইবন মানসুর সুরাই এর অর্থ গ্রহণের বিষয়ে সুফিয়ান হতে, সুফিয়ান মুজাহিদ হতে, আবার মুজাহিদ আশ-শা’বী থেকে আমাদের জানান যে: ‘মাশরুক বিচারকার্যের জন্য অর্থ গ্রহণ করতেন না; আর, সুরাই সম্মানী গ্রহণ করতেন।’ আল-হাফিয তার আল-ফাতিহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে: ‘ইবন আল মুনদির বলেছেন যে, জায়িদ ইবন ছাবিত বিচারকার্যের জন্য সম্মানী গ্রহণ করতেন।’ নাফি’ থেকে ইবন সাদ বর্ণনা করেছেন যে: ‘উমর ইবনুল খাত্তাব যায়িদ ইবন ছাবিতকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ দেন এবং তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন।’ বিচারকার্যের জন্য সম্মানী গ্রহণ করা যে শারী’আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত এ ব্যাপারে সাহাবীদের (রা) ঐক্যমত এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের (তাবেঈনদের) ঐক্যমত ছিল। আল-হাফিয তার আল-ফাতিহ্ গ্রন্থে বলেছেন যে: “আবু আলী আলকারাবিজি বলেছেন: বিচারকদের বিচারকার্যের জন্য সম্মানী গ্রহণ করার মধ্যে কোন দোষ নেই; এ বিষয়টিকে সাহাবী (রা) ও তাবেঈনগণ সহ ইসলামের সকল পন্ডিত একইভাবে দেখেছেন এবং বুঝেছেন। সেইসাথে, সকল প্রদেশের আইনবিদদের এ বিষয়ে একই মতামত এবং জানামতে তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈততা নেই। মাশরুক এটিকে অপছন্দ করেছেন; কিন্তু, কেউই এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি।” ইবন কুদামাহ্ তার আল-মুগনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, “মুয়াজ ইবন জাবাল ও আবু উবাইদাহ’কে আল-শাম অঞ্চলে প্রেরণকালে উমর (রা) তাঁদের পত্র মারফত কিছু ভাল লোক খুঁজে বের করার এবং তাদেরকে বিচারকার্যে নিয়োগ করার নির্দেশ দেন। তিনি তাঁদের বলেন যে, “তাদের জন্য যথাসাধ্য কর, তাদের জন্য সম্পদ বরাদ্দ কর এবং আল্লাহ্’র সম্পদ দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট কর।”
ট্রাইবুনাল গঠন
ইসলামী বিচারব্যবস্থায় একের বেশী বিচারকের সমন্বয়ে ট্রাইবুনাল (Bench) গঠন করা, যাদের বিচারের রায় প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে, তা অনুমোদিত নয়। তবে, শুধুমাত্র পরামর্শ করার খাতিরে কিংবা, মতামত ব্যক্ত করার জন্য একের অধিক বিচারকের উপস্থিতি অনুমোদিত; তবে, এক্ষেত্রে একজন বিচারক ছাড়া অন্য কারো রায় প্রদানের কোন ক্ষমতা থাকবে না বা উক্ত বিচারকের জন্য অন্যান্যদের মতামত বা পরামর্শ গ্রহণে কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।
কারণ, রাসূল (সা) কখনও একটি বিষয়ের জন্য দু’জন বিচারক নিযুক্ত করেননি; বরং, তিনি (সা) একটি বিষয়ের জন্য শুধুমাত্র একজন বিচারক নিয়োগ করেছেন। এছাড়া, বিচারব্যবস্থা হল প্রয়োগের নিমিত্তে কোন বিষয়ে শারী’আহ্ রায় প্রদান করা। আর, একজন মুসলিমের জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে শারী’আহ্ বিধান একের অধিক হতে পারে না; কারণ, প্রদত্ত রায়টি তার জন্য আল্লাহ্’র বিধান এবং একটি বিষয়ে আল্লাহ্’র বিধান একটিই হবে। তবে এটা ঠিক যে, একটি শারী’আহ্ হুকুমের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু, মুসলিমদের জন্য বাস্তবিকভাবে হুকুমটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটা একটি মাত্র বিধান হতে হবে এবং তা কখনও বিভিন্ন রকম হতে পারবে না। সুতরাং, বিচারক যখন কোন বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগের নিমিত্তে কোন রায় প্রদান করবেন, তখন এই রায় অবশ্যই একটি হতে হবে। কারণ, প্রয়োগের বাধ্যবাধকতার শর্তে রায়টি প্রদান করা হয়েছে এবং এই রায় কার্যকর করার অর্থ হল উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্’র বিধান কার্যকর করা। আর, বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহ্’র বিধান কখনও বিভিন্ন রকম হবে না, যদিও এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। এজন্য, একই বিষয়ের জন্য একই আদালতে একের অধিক বিচারক নিয়োগ করা বৈধ নয়। তবে কোন দেশের ক্ষেত্রে, দুটি পৃথক আদালতে একটি অঞ্চলের সব ধরনের বিষয়সমূহ ফয়সালা করা অনুমোদিত। কারণ, বিচারব্যবস্থার কার্যাবলী খলীফার দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং, বিচারকার্য পরিচালনার জন্য কাউকে নিয়োগ করা আসলে খলীফার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ করার সাথে তুলনীয়, অর্থাৎ, একের অধিক প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ; আর তাই, একই অঞ্চলে একের অধিক বিচারক থাকা বৈধ। যদি বিবাদমান দু’পক্ষ কোন ট্রাইবুনাল বা আদালতে তাদের বিবাদ মীমাংসা করবে বা কোন বিচারকের দারস্থ হবে এ বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তবে বিবাদীর পছন্দের উপর বাদীর পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া হবে এবং তার পছন্দের বিচারকের হাতেই মামলা ন্যস্ত করা হবে। যেহেতু মামলা করার মাধ্যমে সে তার অধিকার দাবি করছে, তাই এক্ষেত্রে বিবাদীর চাইতে বাদীর পছন্দকে বেশী গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।
বিচারকগণ একমাত্র আদালতেই বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন; এবং শুধুমাত্র আদালতেই দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন, সাক্ষ্য প্রদান এবং শপথগ্রহণ করতে হবে। কারণ, আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের (রা) এর বরাত দিয়ে আবু দাউদের সূনানে বর্ণিত আছে যে:
‘রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিবাদমান দু’পক্ষকে অবশ্যই বিচারকের সামনে বসতে হবে।’
(সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৫৮৮)
এ হাদীসটি বিচারকার্য কিভাবে পরিচালনা করতে হবে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছে এবং এটাই বিচারকার্য পরিচালনার আইনসঙ্গত পদ্ধতি। অর্থাৎ, এ হাদীস নির্দেশ দিচ্ছে যে, বিচারকার্য পরিচালনার জন্য অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কাঠামো থাকতে হবে। আর, তা হল, বিবাদমান দু’পক্ষকে অবশ্যই বিচারকের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে এবং এটাই হবে আদালত। সুতরাং, বিচারকার্যক্রমের বৈধতার ক্ষেত্রে এটা শর্ত যে, প্রথমত: এ কাজের জন্য অবশ্যই একটি নির্ধারিত স্থান থাকতে হবে যেখানে মামলা সংক্রান্ত রায় প্রদান করা হবে এবং শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই এই রায়কে আইনসঙ্গত রায় বলে বিবেচনা করা হবে। আর, দ্বিতীয়ত: বিবাদমান দু’পক্ষকে অবশ্যই বিচারকের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে। এ বিষয়টি আলী (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাও সমর্থিত, যেখানে রাসূল (সা) বলেছেন:
‘হে ’আলী, যদি তোমার সামনে বিচারের জন্য বিবাদমান দু’পক্ষ বসে; তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত একজনের পক্ষে রায় দিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি প্রথম পক্ষের মত অন্য পক্ষের কথাও শুনে থাক।’
এ হাদীসটিও বিচারের জন্য একটি বিশেষ কাঠামোর প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে; কারণ, এ হাদীসে বলা হয়েছে: ‘যদি তোমার সামনে বিচারের জন্য বিবাদমান দু’পক্ষ বসে…’।
সুতরাং, বিচারের রায় বৈধ হিসাবে বিবেচিত হবার শর্ত হিসাবে আদালতের উপস্থিতি আবশ্যক; এবং একইসাথে এটা শপথগ্রহণের জন্যও আবশ্যকীয়। কারণ, রাসূল (সা) বলেছেন:
‘বিবাদীকে অবশ্যই শপথ নিতে হবে।’
এই হাদীসটি ইবনে আব্বাসের সূত্রে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন। (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-২৬৬৮)
বস্তুতঃ আদালত ব্যতীত বিবাদীকে বিবাদী হিসাবে বিবেচনা করা হবে না; এবং একই কথা সাক্ষ্যপ্রমাণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা ব্যতীত তা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। কারণ, রাসূল (সা) বলেছেন:
‘ফরিয়াদীকে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে হবে এবং শপথগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হবে তার প্রতিপক্ষের উপর (অর্থাৎ, আসামীর উপর)।’
(বায়হাকী)
উপরন্তু, আদালত ব্যতীত কোন ফরিয়াদীকে বাদী হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।
মামলার প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের আদালত থাকা অনুমোদিত। সুতরাং, এটা অনুমোদিত যে, কিছু সংখ্যক বিচারক একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কিছু বিশেষ ধরনের মামলার দায়িত্বে থাকবেন; এবং অন্য মামলাসমূহকে তারা অন্য আদালতে পাঠাবেন।
এর কারণ হল, বিচারকার্যের জন্য বিচারক নিয়োগ করা খলীফার পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি নিয়োগের অনুরূপ; এবং এদুটো বিষয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত অর্থে, বিচারব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বের (deputyship) আরেকটি রূপ, যা কিনা সাধারণভাবে খলীফার প্রতিনিধিত্ব করা হতে পারে, আবার কোন বিশেষ বিষয়ে তার প্রতিনিধিত্ব করার অনুরূপও হতে পারে। সুতরাং, একজন বিচারককে শুধু কিছু বিশেষ ধরনের মামলা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ করা যেমন অনুমোদিত, যেখানে উক্ত বিচারক নির্ধারিত ঐ ধরনের মামলা ছাড়া অন্য কোন মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না; আবার, অন্য কোন বিচারককে একই স্থানে নির্ধারিত ঐ ধরনের মামলাসমূহ সহ সকল প্রকার মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ করাও অনুমোদিত। সুতরাং, বিভিন্ন স্তরের ট্রাইবুনাল গঠন করা অনুমোদিত এবং অতীতে মুসলিমদের এই ধরনের ট্রাইবুনাল ছিল।
আল মাওয়ারদী তাঁর আল আহ্কাম আল সুলতানিয়্যাহ্ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে: ‘আবু আবদুল্লাহ আল যুবায়ের বলেছেন, “কিছুকাল যাবত এখানে বসরার আমীরগণ কেন্দ্রীয় মসজিদে (আল মাসজিদ আল-জামী’) একজন বিচারক নিয়োগ করতেন, তারা তাকে মসজিদের বিচারক বলে অভিহিত করতেন। তিনি (উক্ত বিচারক) সাধারণতঃ বিশ দিনার বা দুই’শ দিরহামের অনুর্ধ্ব পরিমাণ অর্থ সম্পর্কিত বিবাদগুলো মীমাংসা করতেন; এবং ভরণপোষণ আরোপ করতেন (অর্থাৎ, ভরণপোষণ সম্পর্কিত মামলাগুলো পরিচালনা করতেন)। তিনি তার জন্য নির্ধারিত ঐ স্থানের বাইরে যেতেন না কিংবা, তার জন্য বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করতেন না।”
আল্লাহ্’র রাসূল (সা) তাঁর পক্ষ থেকে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ করতেন। যেমন: তিনি (সা) আমর ইবনুল আস’কে (রা) একটি এলাকার মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেন; এবং তিনি (সা) ’আলী ইবন আবি তালিব’কে যে কোন ধরনের মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ইয়েমেনের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করেন। এ সমস্ত ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, সাধারণ কিংবা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত, এদু’টোই শারী’আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত।
ইসলামী বিচারব্যবস্থায় আপীল বা খারিজের জন্য কোন আদালত নেই। সুতরাং, একটি মামলার ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া অভিন্ন হবে এবং একই হবে। যদি কোন বিচারক কোন রায় প্রদান করেন, তবে তা কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হবে; এবং কোন অবস্থাতেই অন্য কোন বিচারকের এ রায় পরিবর্তন করার কোন এখতিয়ার থাকবে না। কারণ, শারী’আহ্ মূলনীতি অনুযায়ী: “একই বিষয়ের উপর কৃত একটি ইজতিহাদ আরেকটি ইজতিহাদ’কে বাতিল করে না।” সুতরাং, একজন মুজতাহিদের বিপক্ষে আরেকজন মুজতাহিদ প্রামাণ্য দলিল নন। সুতরাং, একটি আদালতের রায়কে খারিজ করে দিতে পারে এইরকম একটি আদালতের অস্তিত্ব অবৈধ।
তবে, যদি কোন বিচারক বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শারী’আহ্ পরিত্যাগ করেন এবং কুফর আইন দিয়ে বিচার করেন; কিংবা, তার অনুসৃত আইন যদি আল্লাহ্’র কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ্ এবং সাহাবীদের ইজমা’র সাথে সাংঘর্ষিক হয় কিংবা, যদি তিনি এমন কোন রায় দেন যা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়, যেমন: তিনি কাউকে খুনী সাব্যস্ত করার পর যদি প্রকৃত খুনী উপস্থিত হয় – তবে, এ সকল ক্ষেত্রে বিচারের রায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,
‘যদি কেউ আমাদের দ্বীনের (ইসলামের) ভেতর এমন কোন কিছু উদ্ভাবন করে যা আসলে ইসলাম থেকে নয়, তবে তা প্রত্যাখাত।’
এ হাদীসটি আয়শা (রা) এর সূত্রে সহীহ্ আল বুখারী [হাদীস নং-২৬৯৭] ও সহীহ্ মুসলিমে [হাদীস নং১৭৯৮] বর্ণিত আছে।
জাবির বিন আবদুল্লাহ’র সূত্রে বর্ণিত আছে যে: “এক ব্যক্তি এক মহিলার সাথে যিনাহ্ করলে রাসূল (সা) তাকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে যখন তিনি জানলেন যে, লোকটি বিবাহিত, তখন তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন।” এছাড়া, মালিক বিন আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: “আমি উসমান (রা) সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, তাঁর কাছে একজন (যিনাহকারী) মহিলাকে আনা হল যে ছয়মাস পরে একটি সন্তান প্রসব করেছে। উসমান মহিলাটিকে পাথর মারার নির্দেশ দিলেন। আলী (রা) তাঁকে বললেন, ‘মহিলাটিকে পাথর মারা বৈধ হবে না, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,
‘তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও দুগ্ধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।’
[সূরা আল আহকাফ: ১৫]
এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আরও বলেন,
‘আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।’
[সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩৩]
সুতরাং, তাকে (এখন) পাথর মারা বৈধ হবে না। একথা শুনে উসমান (রা) উক্ত মহিলাটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু, দেখা গেল যে, ততক্ষণে পাথর নিক্ষেপ হয়ে গেছে।” আব্দুর রাজ্জাক, ইমাম ছাওরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে: “যদি কোন বিচারক আল্লাহ্’র কিতাব কিংবা, রাসূল (সা) এর সুন্নাহ্ অথবা, সাহাবীদের ঐক্যমত আছে এমন কোন বিষয়ের বিপরীত কোন রায় প্রদান করে, তবে অন্য বিচারক চাইলে সে রায় পরিবর্তন করতে পারবেন।”
তবে, বিচারের রায় পরিবর্তনের দায়িত্ব আসলে মাযালিমের বিচারকের।
মুহ্তাসিব
মুহ্তাসিব হচ্ছেন সেই বিচারক, যিনি সেই সমস্ত মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করেন যেগুলো জনসাধারণের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত এবং যে সকল মামলার কোন বাদী বা ফরিয়াদী নেই, যদি না এ মামলাগুলো পেনাল কোড (হুদুদ) এবং ফৌজদারী আইন (Criminal Law) এর অন্তর্ভূক্ত হয়।
এটাই হচ্ছে হিসবাহ্’র বিচারকের সংজ্ঞা, যা কিনা রাসূল (সা) এর খাবারের স্তুপ সম্পর্কিত হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। রাসূল (সা) খাবারের স্তুপের ভেতর হাত দিয়ে স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা দেখতে পেলেন। তখন, তিনি (সা) ভেজা খাবারগুলোকে উপরে রাখার নির্দেশ দিলেন যেন লোকেরা তা দেখতে পায়। সুতরাং, এটা ছিল জনস্বার্থ সম্পর্কিত একটি বিষয়, যে ব্যাপারে রাসূল (সা) তদারকী করেছিলেন; এবং ঠকবাজি বা প্রতারণামূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধ করার জন্য তিনি (সা) ভেজা খাবারগুলোকে উপরে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ বিষয়টি জনগণের অধিকার বা স্বার্থসম্পর্কিত একই প্রকৃতির সকল বিষয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আর, পেনাল কোড (হুদুদ) এবং ফৌজদারী আইন (Criminal Law) এর অন্তর্ভূক্ত নয়, এগুলো এই প্রকৃতির (জনগণের অধিকার বা স্বার্থসম্পর্কিত) নয়, এগুলো জনগণের মধ্যকার বিবাদ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
মুহ্তাসিবের আবশ্যিক ক্ষমতা
কোন অপরাধ সংঘটিত হলে, সে বিষয়ে অবহিত হবার সাথে সাথে ঘটনাস্থলেই মুহ্তাসিব সে ব্যাপারে রায় প্রদান করতে পারেন; এবং এ রায় প্রদান অপরাধ সংঘটিত হবার স্থানে কিংবা, যে কোন স্থানে হতে পারে; এজন্য তার কোন আদালতের প্রয়োজন নেই। মুহ্তাসিবের নির্দেশ এবং (যে কোন স্থানে) রায় কার্যকর করার লক্ষ্যে তার অধীনে কিছু পুলিশ নিযুক্ত থাকবে।
তার অধীনস্থ মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য মুহ্তাসিবের কোন আদালতের প্রয়োজন নেই। যখনই তিনি নিশ্চিত হবেন যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তখনই তিনি এ ব্যাপারে রায় প্রদান করবেন; এবং তার যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে রায় প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে; সেটা হাট-বাজারে হোক, কিংবা, কোন গৃহে হোক, কিংবা, ভ্রমনরত অবস্থায় বা যানবাহনে থাকা অবস্থায় দিনে কিংবা রাতে যে অবস্থাতেই হোক না কেন। কারণ, যে সমস্ত দলিল-প্রমাণ আদালতের প্রয়োজনীয়তার অপরিহার্যতাকে প্রমাণ করে, তা মুহ্তাসিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যে হাদীসটি আদালতের অপরিহার্যতাকে প্রমাণ করে সেখানে বলা হয়েছে:
‘বিবাদমান দু’পক্ষকে বিচারকের সামনে বসতে হবে।’
এবং রাসূল (সা) আরও বলেছেন, ‘যদি বিবাদমান দু’পক্ষ তোমার সামনে বসে…।’ এ শর্তটি হিসবাহ’র বিচারকের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, তার এখতিয়ারভূক্ত মামলাসমূহে কোন বাদী বা বিবাদী নেই; বরং, এটা জনগণের অধিকার যা ক্ষুন্ন করা হয়েছে, অথবা, এ বিষয়ে শারী’আহ্ আইন লঙ্ঘিত হয়েছে।
এছাড়া, রাসূল (সা) যখন খাবারের স্তুপের বিষয়টি তদারকী করছিলেন, সে সময় তিনি (সা) বাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলেন এবং খাবারগুলো বিক্রির জন্য সাজানো ছিল। রাসূল (সা) উক্ত বিক্রেতাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হবার নির্দেশ দেননি; বরং, তিনি (সা) অপরাধটি শনাক্ত করার সাথে সাথে ঐ স্থানেই এ বিষয়ে রায় দিয়েছেন। এটিই প্রমাণ করে যে, রায় প্রদানের জন্য হিসবাহ্’র বিচারকের আদালতের প্রয়োজন নেই।
এছাড়া, মুহ্তাসিবের তার নিজের জন্য ডেপুটি নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। তবে, তাদেরকে অবশ্যই মুহ্তাসিব পদের সকল শর্ত পূরণ করতে হবে। এছাড়া, তিনি তার ডেপুটিদের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করতে পারেন। এসব ডেপুটি বা সহকারীগণ তাদের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলে এবং তাদেরকে যে সমস্ত বিষয় তদারকী করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে মুহ্তাসিবের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
অবশ্য এটা নির্ভর করবে, মুহ্তাসিবের নিয়োগপত্রে তাকে ডেপুটি নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা বা না করার উপর। যদি, এ বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করে তার নিয়োগপত্রে কোন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত থাকে, শুধুমাত্র তখনই তিনি তার নিজের জন্য সহকারী নিয়োগ করতে পারবেন। আর, যদি তাকে এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতা দেয়া না হয়, তবে নিজের জন্য কোন সহকারী নিয়োগ করার অধিকার তার থাকবে না।
মাযালিমের বিচারক
মাযালিমের বিচারক হলেন এমন একজন বিচারক যাকে রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কৃত সকল প্রকার মাযলিমা’র (অন্যায় আচরণ) মীমাংসা করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়; সে ব্যক্তি হতে পারে রাষ্ট্রের কোন সাধারণ নাগরিক কিংবা, হতে পারে রাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃত্বের নীচে বসবাসরত কেউ; এবং এ অন্যায় আচরণ (মাযলিমা) খলীফা কিংবা, তার অধীনে কর্মরত কেউ কিংবা, কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত হতে পারে।
এটাই হল মাযালিমের বিচারকের সংজ্ঞা। মাযালিমের বিচারকের উৎস হিসাবে রাসূল (সা) এর হাদীসকে উল্লেখ করা হয়, যেখানে তিনি (সা) জনগণের উপর শাসন পরিচালনা কালে শাসক কর্তৃক নাগরিকদের উপর কৃত অন্যায় আচরণকে মাযলিমা বলে অভিহিত করেছেন। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে:
‘রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সময়ে একবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। তখন তা তাঁরা (সাহাবীরা) তাঁকে বললেন, ‘হে আল্লাহ্’র রাসূল, আপনি কেন দাম নির্ধারণ করে দিচ্ছেন না?’ তখন তিনি (সা) বললেন, ‘অবশ্যই আল্লাহ্ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, সব বিষয়ের অধিকর্তা, সম্পদ বৃদ্ধিকারী, রিযিকদাতা এবং মূল্য নির্ধারণকারী, এবং আমি আশা করি যে, আমি এ অবস্থায় আল্লাহ্’র সাথে সাক্ষাৎ করবো যাতে কেউ আমার বিরুদ্ধে মাযালিমা’র অভিযোগ না আনতে পারে, হোক সেটা রক্ত সম্পর্কিতই হোক বা অর্থ সম্পর্কিত হোক।’
এ হাদীসটি ইমাম আহমদ তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন (মুসনাদে আহমদ খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৬)।
রাসূল (সা) এক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়ার বিষয়টিকে মাযালিমা বা অন্যায় আচরণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ, তিনি যদি মূল্য নির্ধারণ করে দিতেন, তাহলে এক্ষেত্রে তিনি তাঁর এখতিয়ার বর্হিভূত কাজ করতেন।
এছাড়া, তিনি (সা) রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কোন বিষয়, যা জনস্বার্থ ক্ষুন্ন করে তাকেও মাযলিমা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোন বিষয় পরিচালনার জন্য যদি কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠিত হয় এবং কোন ব্যক্তি যদি সে ব্যবস্থাকে তার স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করে, তবে তার বিষয়টি মাযালিমের বিচারক খতিয়ে দেখবেন। কারণ, এটি জনগণের স্বার্থরক্ষার নিমিত্তে রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। যেমন এটা হতে পারে, গণমালিকানাধীন কোন জলাধারের বিষয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বসাধারণের কৃষিজমিতে সেচকার্য করা।
এ ব্যাপারে দলিল হল, রাসূল (সা) এর সময় রাষ্ট্র কর্তৃক সেচকার্যের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মদিনার একজন আনসারীর অভিযোগ। রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাটি ছিল এরকম যে: যার জমির উপর দিয়ে জলধারা প্রথমে বয়ে যাবে সে প্রথমে সেচকাজ করবে, তারপর তার পরবর্তী জন করবে। আনসারী ঐ ব্যক্তিটি চাচ্ছিলেন যে, আল-যুবায়ের (রা) (যার জমির উপর দিয়ে প্রথমে জলধারা বয়ে গিয়েছিল) নিজের জমিতে সেচকার্য করার পূর্বেই তার (উক্ত আনসারীর) জমিতে পানি প্রবাহিত হতে দেবেন। কিন্তু, আল-যুবায়ের তা প্রত্যাখান করেন এবং শেষপর্যন্ত বিষয়টি রাসূল (সা) এর নিকট উত্থাপিত হয়। তিনি (সা) বিষয়টি ফয়সালা করে দেন এবং যুবায়েরকে তার জমিতে হালকা ভাবে সেচকার্য করার পর তার প্রতিবেশী আনসারীকে পানি ছেড়ে দিতে বলেন (অর্থাৎ, প্রতিবেশীকে সাহায্যের নিদর্শন হিসাবে তিনি (সা) আল-যুবায়েরকে তার প্রাপ্য পানি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করার পূর্বেই তা ছেড়ে দিতে বলেন)। কিন্তু, উক্ত আনসারী এ রায় প্রত্যাখান করে এবং আল-যুবায়েরের পূর্বে সে নিজ জমিতে সেচকার্য করার দাবি জানায়। তারপর সে রাসূল (সা) বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, আল-যুবায়ের সম্পর্কে তার চাচাতো ভাই হবার কারণে তিনি (সা) এ রায় দিয়েছেন (যা ছিল আল্লাহ্’র রাসূলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ; আল-বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে উক্ত আনসারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়)।
ঘটনার এ পর্যায়ে, রাসূল (সা) রায় দেন যে, যুবায়ের তার সেচকার্যের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে; অর্থাৎ, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার জমিতে সেচকার্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পানি তার দেয়ালের মূলে কিংবা গাছের মূল পর্যন্ত না পৌঁছায়। যাকে আলেমগণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানির উচ্চতা বাড়তে দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা মানুষের পা ডুবিয়ে দেয়। এই সম্পূর্ণ হাদীসটি ’উরওয়া ইবন আল-যুবায়েরের বরাত দিয়ে সহীহ্ মুসলিমে [হাদীস নং-২৩৫৭] এভাবে বর্ণিত আছে যে:
“আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়ের তাকে বলেছেন যে, আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর সামনেই সিরাজ আলহাররাহ্ নিয়ে আল-যুবায়েরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়, যার দ্বারা তারা তাদের খেজুর বাগানে পানি দিত। উক্ত আনসারী (আল-যুবায়েরকে) পানি ছেড়ে দিতে বলে; কিন্তু, আল-যুবায়ের তা প্রত্যাখান করেন। তারা রাসূল (সা) এর সামনেই বিবাদে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্’র রাসূল যুবায়েরকে বলেন: “হে যুবায়ের, তুমি প্রথমে সেচকাজ কর, তারপর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও।” এতে উক্ত আনসারী খুব রাগান্বিত হয়ে যায় এবং বলে: “হে আল্লাহ্’র রাসূল, এরকম রায়ের কারণ হল সে আপনার চাচাতো ভাই।” তার একথা শুনে রাসূল (সা) এর মুখের রঙ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তারপর তিনি (সা) বলেন: “হে যুবায়ের! তুমি সেচকাজ কর এবং ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ধরে রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত না তা দেয়ালের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছায়।” আল-যুবায়ের বলেন: “আল্লাহ্’র কসম, আমার মনে হয় এ বিষয়েই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে: “তোমার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনরকম সংকীর্ণতা না পায় এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেয়।” [সিরাজ আল-হাররাহ্ হল মদিনার আল-হাররাহ্ অঞ্চলের একটি নদী। আবু উবাইদ বলেছেন যে, মদিনাতে দু’টি নদী ছিল, যাতে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হত এবং মদিনার লোকেরা এ নদীগুলোর ব্যাপারে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতো। এজন্য রাসূল (সা) সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রথম ব্যক্তি প্রথমে সেচকাজ করবে; যার অর্থ হল, নদীর শুরুর দিকে যার জমি রয়েছে সে প্রথমে সেচকাজ করবে এবং তারপর সে পানিকে পরবর্তী জমিতে প্রবাহিত হতে দেবে এবং ব্যাপারটি এভাবে চলতে থাকবে]।
সুতরাং, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাসক বা রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠান বা নির্দেশের কারণে যদি কোন অন্যায় আচরণ ঘটে থাকে, তবে এ বিষয়টিকে মাযলিমা হিসাবে বিবেচনা করা হবে, যা কিনা উপরোল্লিখিত দু’টি হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে এ বিষয়সমূহ ফয়সালার জন্য খলীফার কাছে ন্যস্ত করা হবে কিংবা, তিনি মাযালিমের বিচারক হিসাবে তার পক্ষ থেকে যাকে নিয়োগ করবেন তার নিকট উপস্থাপন করা হবে। মাযালিমের
মাযালিমের বিচারক নিয়োগ ও অপসারণ
মাযালিমের বিচারক খলীফা বা প্রধান বিচারপতি (কাজী আল কুদাহ্) কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। এর কারণ হল, মাযালিম বিচারব্যবস্থার একটি অংশ, যার মাধ্যমে শারী’আহ্ আইন কার্যকর করার নিমিত্তে রায় প্রদান করা হয় এবং সকল ধরনের বিচারককে অবশ্যই খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হতে হয়। এছাড়া, রাসূল (সা) এর সীরাত থেকেও এটি প্রমাণিত যে, আল্লাহ্’র রাসূল (সা) নিজেই বিচারকদের নিয়োগ দিতেন। এ সবকিছুই প্রমাণ করে যে, খলীফাই মাযালিমের বিচারক নিয়োগ করবেন। তবে, প্রধান বিচারপতিও মাযালিমের বিচারক নিয়োগ করতে পারেন, যদি খলীফা তার নিয়োগপত্রে তাকে এ বিষয়ে ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি অনুচ্ছেদ আকারে যুক্ত করেন। এটি অনুমোদিত যে, রাষ্ট্রের কেন্দ্রে থাকা মাযালিমের প্রধান আদালত (মাহকামাতুল মাযালিম) শুধুমাত্র খলীফা, তার সহকারীবৃন্দ এবং প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে সংঘটিত অন্যায় আচরণের বিষয়ে তদন্ত করবে; অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রদেশে (উলাই’য়াহ্) অবস্থিত মাযালিম আদালতের শাখাসমূহ ওয়ালী বা রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত মাযলিমা তদন্ত করবে। খলীফা ইচ্ছা করলে মাযালিমের প্রধান আদালতকে বিভিন্ন উলাই’য়াহ্তে অবস্থিত মাযালিমের শাখা আদালত সমূহের বিচারক নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।
তবে, খলীফাই হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রের কেন্দ্রে অবস্থিত মাহকামাতুল মাযালিমের সদস্যদের নিয়োগ ও অপসারণ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তবে, মাহকামাতুল মাযালিমের প্রধান বিচারককে অপসারণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, যদিও তিনিই খলীফার অপসারণ সম্পর্কিত বিষয়ে তদন্ত করবেন, তারপরেও নীতিগতভাবে খলীফারই রয়েছে তাকে অপসারণের ক্ষমতা। এর কারণ হল, খলীফাই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার তাকে নিযুক্ত করার ক্ষমতা রয়েছে, ঠিক যেভাবে তিনি অন্যান্য বিচারকদের নিযুক্ত করে থাকেন। তবে, খলীফার বিরুদ্ধে কোন তদন্ত চলাকালে যদি তাকে মাযালিমের প্রধান বিচারককে অপসারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তবে প্রদত্ত এ ক্ষমতা তাকে হারামের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এজন্য, এ ধরনের পরিস্থিতিতে শারী’আহ্ মূলনীতি: “যা কিছু হারামের দিকে ধাবিত করে, তা নিজেই হারাম” এটি প্রযোজ্য হবে। যেহেতু এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু এক্ষেত্রে শারী’আহ্ এ মূলনীতিটি প্রযোজ্য হবে।
এই ধরনের পরিস্থিতি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, যখন খলীফা কিংবা, তার সহকারীবৃন্দ অথবা, তার প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে কোন তদন্ত বা মামলা চলতে থাকবে। এর কারণ হল, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি খলীফাকে মাযালিমের প্রধান বিচারককে অপসারণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তবে তা বিচারের রায়কে প্রভাবিত করতে পারে; এবং স্বাভাবিকভাবেই এ পরিস্থিতি, প্রয়োজনের খাতিরে উক্ত বিচারকের খলীফা বা, তার সহকারীবৃন্দ কিংবা, প্রধান বিচারককে অপসারণ করার ক্ষমতাকে সংকুচিত করবে। এক্ষেত্রে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে খলীফার হাতে উক্ত বিচারককে অপসারণ করার প্রদত্ত ক্ষমতা হারাম কার্য সম্পাদনের একটি উপায় বা পন্থা; অর্থাৎ, এ পরিস্থিতিতে খলীফার হাতে এ ক্ষমতা প্রদান করা শারী’আহ্ দৃষ্টিকোন থেকে হারাম বা নিষিদ্ধ।
এছাড়া অন্য সবক্ষেত্রে, বিধানটি একই রকম থাকবে। অর্থাৎ, মাযালিমের বিচারককে অপসারণ করার ক্ষমতা খলীফার হাতেই ন্যস্ত থাকবে, যেভাবে তার উক্ত বিচারককে নিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে।
মাযালিমের বিচারকের আবশ্যিক ক্ষমতা
মাযালিম আদালতের অন্যায় আচরণ (মাযলিমা) সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তদন্ত করার আবশ্যিক ক্ষমতা রয়েছে; সে অন্যায় আচরণ সরকারী কোন কর্মচারীর দ্বারা সংঘটিত হোক; কিংবা, খলীফার কাজের সাথে শারী’আহ্’র দ্বন্দ বিষয়ক হোক; কিংবা, সংবিধানের আইনী ব্যাখ্যা বিষয়ক হোক; কিংবা, খলীফা কর্তৃক গৃহীত আইনকানুন বা বিভিন্ন প্রকারের শারী’আহ্ বিধিবিধান যেমন: জনগণের উপর করধার্য করা বা অন্যকোন বিষয় সম্পর্কিত হোক।
মাযালিম আদালত যে কোন ধরনের অন্যায় আচরণ, তা কোন সরকারী কর্মচারীর সাথে সম্পর্কিত হোক, খলীফার দ্বারা শারী’আহ্ আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে হোক, সংবিধান, আইনী দলিল বা খলীফা কর্তৃক জারিকৃত কোন আইনকানুনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত হোক, জনগণের উপর করধার্যের বিষয়ে হোক; কিংবা, রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক জনগণের উপর কৃত জুলুম-নির্যাতন বিষয়ক হোক, যেমন: রাষ্ট্র কর্তৃক জোরপূর্বক জনগণের সম্পদ দখল করা বা, তাদের নিকট হতে সম্পদ সংগ্রহ কালে শারী’আহ্ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা; কিংবা, সরকারী কর্মচারী বা সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেতনভাতা কমিয়ে দেয়া বা বেতন প্রদানে বিলম্বিত করা ইত্যাদি বিষয়ক হোক: এ সকল বিষয়ের তদন্ত করার জন্য কোন ব্যক্তির বিচারকের সম্মুখে উপস্থিতি, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমনজারী বা, কোন ফরিয়াদীর প্রয়োজন নেই। বরং, এটা হল এ সকল বিষয়ে মাযালিম আদালতের তদন্ত করার আবশ্যিক ক্ষমতা, এমনকি এ সব বিষয়ে যদি কেউ কোন অভিযোগ দায়ের না করে তবুও।
এর কারণ হল, যে সমস্ত শারী’আহ্ দলিল-প্রমাণ বিচারকার্য চলাকালে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিতিকে শর্ত হিসাবে আরোপ করে, সেগুলো মাযালিম আদালতের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, এ সকল মামলার কোন ফরিয়াদী নেই, তাই ফরিয়াদীর আদালতে উপস্থিতি শর্ত হিসাবে বিবেচ্য নয়। বস্তুতঃ কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অভিযোগ দায়ের না করলেও মাযালিম আদালতের কোন মাযলিমা (অন্যায় আচরণ) তদন্ত করার অধিকার রয়েছে; এ কারণে বাদীর আদালতে হাজির হবার কোন প্রয়োজন নেই। একইসাথে, বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি ব্যতীতই এ আদালত এ সকল মামলার তদন্ত করতে পারে। সুতরাং, আদালতের প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য প্রমাণিত করে এমন শারী’আহ্ দলিল এক্ষেত্রে বিবেচিত হবে না। আদালতের প্রয়োজনীতাকে অপরিহার্য করে এ রকম দলিলসমূহ হল: আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়েরের বরাত দিয়ে আবু দাউদ ও আহমাদ বর্ণিত হাদীসটি, যেখানে তিনি বলেছেন: “আল্লাহ্’র রাসূল (সা) নির্দেশ দিয়েছেন যে, “বিবাদমান দু’পক্ষ যেন বিচারকের সামনে বসে।” এবং আলী (রা) এর প্রতি রাসূল (সা) এর নির্দেশ: “যদি বিবাদমান দু’পক্ষ তোমার সামনে উপস্থিত হয়…।”
সুতরাং, মাযালিমের বিচারক এ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন যে, কোন মাযলিমা সংঘটিত হলে যে কোন স্থানে, যে কোন সময় কিংবা, কোন আদালত ব্যতীতই এ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারেন। বস্তুতঃ এ আদালতের আবশ্যিক ক্ষমতা এবং এর অবস্থানগত মর্যাদার ভিত্তিতে, অতীতে সবসময়ই এটি উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও আড়ম্বরপূর্ণতা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মিশর ও আল-শামে সুলতানদের শাসনামলে, সুলতানদের কাউন্সিল যা কিনা মাযলিমা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ দেখাশুনা করতো, তা ‘ন্যায়বিচারের গৃহ’ (House Of Justice) নামে পরিচিত ছিল; যেখানে সুলতান তার পক্ষ থেকে সহকারী নিয়োগ করতেন এবং সেইসাথে, বিচারক ও ফকীহ্গণও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। আল মাকরিজী তার “আল-সুলুক ইলা মা’রিফাত দুওয়াল আল-মুলক” (The way to know the states of the king) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান আল-মালিক আল-সালিহ্ আইয়ুব হাউস অব জাস্টিস-এ তার পক্ষ থেকে ডেপুটি নিয়োগ করতেন; যেখানে তারা সাক্ষী, বিচারক এবং ফকীহ্’দের উপস্থিতিতে সকল প্রকার অন্যায় আচরণ দূরীভূত করার লক্ষ্যে কাজ করতেন। সুতরাং, মাযালিমের আদালতের জন্য চমৎকার ও আকর্ষণীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ভবন নির্মাণে কোন ক্ষতি নেই; কারণ, এটি মুবাহ্ (অনুমোদিত) কাজের অন্তর্ভূক্ত; বিশেষ করে এ রকম একটি ভবনের মাধ্যমে যদি বিচারব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিফলিত হয়।
খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেকার চুক্তি, লেনদেন ও বিচারিক রায়
খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও লেনদেন, সেইসাথে এ সংক্রান্ত আদালতের রায় যা ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ও খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই কার্যকর হয়েছে, তা খিলাফতের অধীনে বৈধ বলে বিবেচিত হবে। খিলাফতের বিচার বিভাগ এ মামলাগুলো পূণরায় তদন্ত করবে না, বা এগুলোকে পূণরায় নিষ্পত্তি করবে না। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পর এগুলোর ব্যাপারে আর নতুন কোন মামলা গৃহীত হবে না। তবে, দু’টি বিষয় এর বাইরে থাকবে:
১) খিলাফতের পূর্বে যে মামলাটি নিষ্পন্ন হয়েছে এবং কার্যকরী হয়েছে যদি এর ধারাবাহিকতা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পরও রয়ে যায় এবং তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।
২) যদি মামলাটি এমন কারও সাথে সম্পর্কিত হয়, যার কারণে ইসলাম ও মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
উপরোক্ত দু’টি বিষয় ব্যতীত, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেকার নিষ্পত্তিকৃত চুক্তি, লেনদেন এবং মামলাসমূহ, যে সংক্রান্ত রায় খিলাফতের পূবেই কার্যকরী হয়েছে, তা পূণরায় নিষ্পত্তি না করা বা এ সংক্রান্ত মামলা নতুন করে গৃহীত না হবার দলিল হিসাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে গৃহ থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, মক্কাবিজয়ের পর তিনি আর সে গৃহে ফিরে যাননি। কুরাইশদের আইন অনুসারে, উকাইদ ইবন আবি তালিব তার সে সব আত্মীয়-স্বজনের গৃহসমূহ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং হিজরত করেছিল।
উত্তরাধিকার সূত্রে এ গৃহসমূহের মালিকানা লাভ করার পর উকাইদ এগুলো অধিগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে বিক্রি করে দেয়, যার মধ্যে রাসূল (সা) এর গৃহও অন্তর্ভূক্ত ছিল। মক্কাবিজয়ের পর রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হল: “আপনি কোন গৃহে অবস্থান করতে চাচ্ছেন?” তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “উকাইদ কি আমাদের কোন গৃহ ছেড়ে দিয়েছে?” (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩০৫৮) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বললেন: “উকাইদ কি আমাদের জন্য কোন গৃহ ছেড়ে দিয়েছে?” তখন তাঁকে বলা হল যে, উকাইদ রাসূল (সা) এর বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে, কিন্তু রাসূল (সা) তা বাতিল বলে ঘোষণা করলেন না। এই হাদীসটি উসামা বিন যায়িদের সূত্রে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (উসামা (রা)) বলেছেন: মক্কা বিজয়ের দিন তিনি বললেন, “হে আল্লাহ্’র রাসূল! আগামীকাল আপনি কোথায় থাকতে চান?” তখন রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, “উকাইল কি আমাদের কোন বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে?” (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৩০৫৮)
এছাড়া, আরও বর্ণিত আছে যে, আবু আল-’আস ইবন আল-রাবী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন। কিন্তু, এর পূর্বে তার স্ত্রী যয়নাব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বদরের যুদ্ধের পর মদিনায় হিজরত করেন, তখনও তিনি (ইবন আল-রাবী) মুশরিক অবস্থায় মক্কায় ছিলেন। (মুসলিম হবার পর) রাসূল (সা) বিবাহচুক্তি নবায়ন না করেই তার স্ত্রী’কে তার নিকট ফেরত দেন। এটা ছিল অন্ধকার যুগে সম্পাদিত বিবাহচুক্তির স্বীকৃতি প্রদান। এছাড়া, ইবন আব্বাসের সূত্রে ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন যে:
“রাসূল (সা) দুই বছর পর তাঁর কন্যাকে অর্থাৎ, যয়নাবকে প্রথম বিবাহের চুক্তির উপর ভিত্তি করেই আবু আল-’আস ইবন আল-রাবী কাছে ফেরত পাঠান।”
(সূনানে তিরমিযী, হাদীস নং-১১৪২)
এছাড়া, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বের যেসব লেনদেন ও মামলার ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ধারাবাহিক প্রভাব বিদ্যমান থাকে, সেসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন: ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আসার পর মক্কার লোকদের উপর ইবন আব্বাসের ঋণের যে সুদ ছিল, তিনি (সা) তা বাতিল বলে ঘোষণা করেন এবং লোকেরা শুধু প্রকৃত ঋণ ফেরত দেয়। এর অর্থ হচ্ছে, দার-উল-ইসলামে তাদের উপর আরোপিত সুদ বাতিল বলে গণ্য হয়েছিল। সূলাইমান ইবন আমরু তার পিতা হতে এবং আবু দাউদ সুলাইমান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সুলাইমানের পিতা) বলেছেন যে:
‘আমি বিদায়হজ্জ্বের দিন আল্লাহ্’র রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি যে:
“সাবধান! অন্ধকার যুগের (জাহিলিয়াতের) সমস্ত সুদ বাতিল করা হয়েছে। তোমরা কেবলমাত্র আসল অর্থের দাবি করতে পারবে। তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করো না এবং জুলুমের শিকার হয়ো না।”
এছাড়া, জাহিলিয়াতের সময় যাদের চারের অধিক স্ত্রী ছিল, দার-উল-ইসলামে তাদেরকে শুধুমাত্র চারজন স্ত্রী রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, ঘাইলান ইবনে সালামাহ্ ইবনে ছাকাফি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল যারা তার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। “রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে স্ত্রীদের মধ্য হতে চারজনকে পছন্দ করার নির্দেশ দেন।”
সুতরাং, সেইসব চুক্তি, যার ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ধারাবাহিক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে, এই ধরনের প্রভাব অবশ্যই দূরীভূত করতে হবে। এই প্রভাব দূর করা আবশ্যকীয় বলে বিবেচিত হবে।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোন মুসলিম নারী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোন খ্রিষ্টান পুরুষকে বিয়ে করে, তাহলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে শারী’আহ্ নিয়ম অনুযায়ী সে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
আর, যাদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করার ব্যাপারে বলা যায় যে, এটা অনুমোদিত এ কারণে যে, মক্কাবিজয়ের পর আল্লাহ্’র রাসূল (সা) ক্ষমা ঘোষণার সাথে সাথে কিছু কিছু কাফের ব্যক্তিদের রক্তপাতের ঘোষণা দেন; কারণ, তারা সবসময় ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতিসাধনে ব্যস্ত ছিল। এমনকি যদি তারা কাবার চাদর ধরে ঝুলে থাকে তবুও তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। যদিও এর পূর্বে তিনি (সা) এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, “ইসলাম তার পূর্বের সবকিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়”, যে হাদীসটি আমর ইবনুল ’আস (রা) এর সূত্রে আহমাদ ও তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ হল, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা এ হাদীসের বর্হিভূত বলে বিবেচিত হবে।
তবে, যেহেতু রাসূল (সা) পরবর্তীতে এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যেমন, তিনি (সা) ইকরামা ইবন আবু জাহলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এজন্য খলীফা চাইলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন; কিংবা, তাদেরকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।
উপরোল্লিখিত বিষয় দু’টি বাদে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে নিষ্পত্তিকৃত সকল চুক্তি ও লেনদেন এবং এ সংক্রান্ত মামলার রায় বাতিল বলে গণ্য করা হবে না; বা, পূণরায় নিষ্পত্তি করা হবে না, যদি সেগুলো খিলাফতের পূর্বেই নিষ্পত্তি ও কার্যকরী হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি স্কুলের দরজা ভাঙ্গার দায়ে দু’বছরের কারাদন্ড প্রাপ্ত হয় এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই সে তার সাজার মেয়াদ শেষ করে এবং জেল থেকে বেরিয়ে যায়; এরপর, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পর যদি সে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা শুরু করতে চায়, কারণ, তার দৃষ্টিতে তার উপর অন্যায় করা হয়েছে, তবে এ বিষয়ে কোন মামলা গৃহীত হবে না। কারণ, ঘটনাটি ঘটে গেছে এবং এ ব্যাপারে রায় প্রদান করা হয়েছে এবং সাজার মেয়াদ খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বেই শেষ হয়েছে। এ ধরনের বিষয়সমূহ পুরস্কারের আশায় আল্লাহ্’র তা’আলার কাছে পেশ করতে হবে।
কিন্তু, যদি এমন হয় যে, উক্ত ব্যক্তিকে এ অভিযোগে দশ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়েছে এবং দশ বছরের মধ্যে সে দু’বছর সাজা ভোগ করেছে এবং এর মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন এক্ষেত্রে খলীফার বিষয়টি পুনঃতদন্ত করার এখতিয়ার রয়েছে; হয় তিনি শাস্তির এ রায় বাতিল করে এবং তাকে অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দিয়ে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে পারেন; কিংবা, যে শাস্তি সে ইতিমধ্যে ভোগ করেছে তা যথেষ্ট মনে করে তাকে মুক্ত করতে পারেন। আবার এমনও হতে পারে যে, তিনি জনস্বার্থ ও এ সংশ্লিষ্ট শারী’আহ্ আইন বিবেচনায় রেখে, বিশেষ করে এ বিষয়টি যদি জনস্বার্থের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে তিনি শাস্তির বাকী সময়টুকু পূণর্বিবেচনা করতে পারেন।