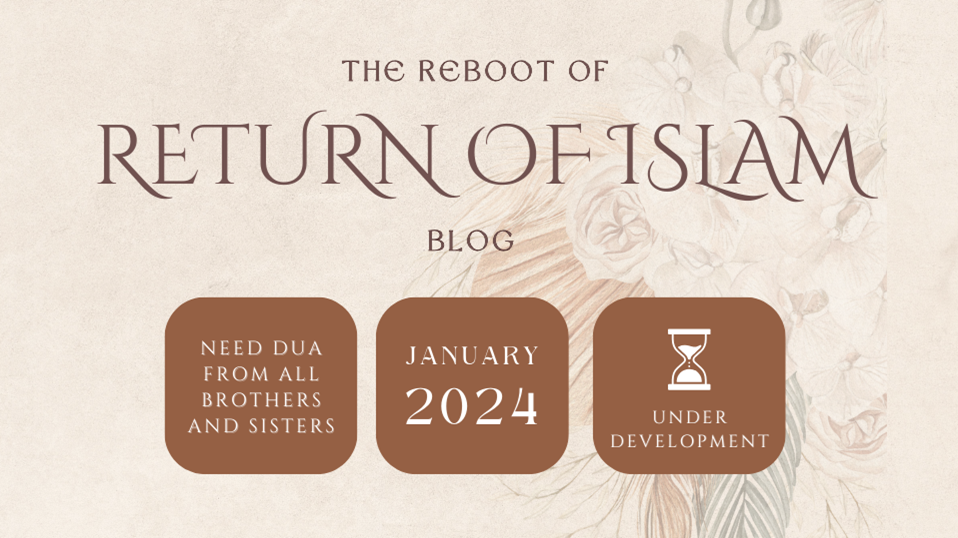একজন মতাদর্শিক মুসলিম হওয়ার অপরিহার্যতা

অক্সফোর্ড ডিকশনারি Ideology (আদর্শ) শব্দটির সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে:
“a system of ideas and ideals, especially one which forms the basis of economic or political theory and policy or a set of beliefs characteristic of a social group or individual.”
অর্থাৎ, একটি ধারণা ও বিশ্বাসের সমষ্টি, যা বিশেষভাবে কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও নীতির ভিত্তি গঠন করে, কিংবা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যমূলক বিশ্বাসব্যবস্থা।
“Ideology” শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি বিপ্লবের সময়। ১৭৮৯ সালে ফরাসি দার্শনিক Antoine Destutt de Tracy প্রথম এটি ব্যবহার করেন idéologie শব্দ থেকে, যার মূল অর্থ ছিল “science of ideas” বা ধারণার বিজ্ঞান। পরবর্তীতে এটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক চিন্তাধারার প্রসারে ব্যবহার হতে থাকে, যার উদ্দেশ্য ছিল মানবসমাজের ভাষা, বর্ণ, ভৌগোলিক পার্থক্য নির্বিশেষে এসব ধারণাকে বাস্তবে কার্যকর করা।
শেখ তাকিউদ্দিন আন-নাবাহানী রহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ نظام الإسلام (System of Islam)-এ Ideology (مبدأ) এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:
«المبدأ هو عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام»
অর্থাৎ, “আদর্শ (মাবদা’) হলো একটি বুদ্ধিভিত্তিক আক্বীদাহ, যার থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা উৎসারিত হয়। আক্বীদাহ হলো মানুষ, জীবন ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা—যা এই জীবনের পূর্ববর্তী বাস্তবতা, মৃত্যুর পরবর্তী বাস্তবতা এবং এ জীবনের সাথে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাস্তবতার সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে।”
কেউ যদি ইসলাম ও আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ এর জীবনকে বুঝতে চান, তবে সহজেই এই পরিভাষাটি ইসলাম ও নবীর সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, এ শব্দটি ইসলামের ক্ষেত্রে যথার্থভাবে প্রযোজ্য এবং স্পষ্টভাবে ব্যবহার করা যায় আমাদের নবী ﷺ -এর জীবন ও ইসলামের প্রকৃতি (The essence of Islam) বর্ণনা করতে। কেননা ইসলাম নিজেই একটি আদর্শ (Ideology)—যা পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ ব্যবস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা আল-কুরআনে সংজ্ঞায়িত এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর জীবনে বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবন ছিল এক আদর্শিক সংগ্রাম, যা পৃথিবীতে বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত হয়েছিল—মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে: ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে এবং নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের (public life) পর্যায়ে, যেখানে সমাজের কাঠামো, অর্থনৈতিক নীতি, এমনকি বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক সম্পর্ক পর্যন্ত ইসলামের নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত হতো।
ঐতিহাসিকভাবে ইসলামকে আদর্শ (Ideology) ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে বোঝার কোনো দ্ব্যর্থতা বা অস্পষ্টতা ছিল না। আমাদের পূর্বসূরিরা এর স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, তারা ইসলামকে শুধুমাত্র ইবাদত বা আধ্যাত্মিকতায় সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে বুঝেছিলেন। তাদের আদর্শিক উপলব্ধিই তাদেরকে দাওয়াহ ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলামকে বিশ্বব্যাপী বিস্তার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।যখন তারা ইসলামকে সর্বত্র প্রচার করেছেন এমন পর্যায়ে যে, খিলাফাহ রাষ্ট্র একটি ক্ষুদ্র চারাগাছের মতো মদিনা থেকে শুরু করে ৪৫০০ মাইল বিস্তৃত এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছিল পূর্ব দিকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত।
তাদের ইসলামের প্রতি এই আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিই এমন এক প্রজন্মের জন্ম দিয়েছিল, যারা আদর্শ দ্বারা চালিত মুসলিম ছিল। তাদের প্রতিটি কর্ম তাদের আক্বীদাহ’র (عقيدة) সঙ্গে যুক্ত ছিল। আর এই ইসলামী আক্বীদাহ-ই (عقيدة إسلامية) তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ইসলামকে পৃথিবীব্যাপী বাস্তবায়ন করতে।
অতএব, একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হলো ইসলামকে একই আদর্শিক কাঠামোর ভেতরে বুঝতে পারা। কারণ এই ধারণা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও একজন মুসলিমের কর্মকে প্রভাবিত করে এবং তা অবিশ্বাসী ঔপনিবেশিকদের সেই ষড়যন্ত্রকে সফল করতে পারে, যা ইসলামের প্রকৃত বার্তাকে (message) ক্ষীণ ও দুর্বল করে ফেলে। তারা ইসলামের সংগ্রামকে—যা বিশ্বের সব ভ্রান্ত মতবাদ ও আদর্শের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ—তা থেকে সরিয়ে এনে এক বহুত্ববাদী (pluralistic) ইসলাম উপস্থাপন করতে চায়। এমন এক ইসলাম, যেখানে রয়েছে পরস্পর বিরোধিতা, অসামঞ্জস্য, আপোস ও সংশয়বাদ—যা আজকাল আমরা সমাজে বহুলভাবে দেখতে পাই।
ইসলামের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি হারানোর বিপদ ও এর বাস্তব পরিণতি এবং তা আজ উম্মাহ হিসেবে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আমরা এমন মুসলিমদের দেখতে পাচ্ছি যারা ইসলামের বার্তায় (narration) ঈমান রাখে, কিন্তু নিজেদের উপর শাসন করার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। আমরা এমন মুসলিমদেরও দেখি যারা কিছু হারাম থেকে দূরে থাকে—যেমন মদ্যপান থেকে বিরত থাকে, বিবাহ-পূর্ব যৌন সম্পর্ক এড়িয়ে চলে এবং শূকরের মাংস খায় না—কিন্তু ব্যবসায় সুদের সঙ্গে খেলা করে কিংবা সুদভিত্তিক ছাত্রঋণ গ্রহণ করে। আমরা এমন মুসলিমদেরও দেখি যারা নিয়মিত মসজিদে যায় এবং এমনকি ইসলামের দাওয়াত কার্যক্রমেও যুক্ত থাকে; কিন্তু ইসলামের প্রতি আদর্শিক (Ideological) উপলব্ধি অনুপস্থিত থাকার কারণে তারা পশ্চিমা নৈতিকতা ও নীতিশাস্ত্রের ধারণার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত সংস্কার (individual reform) ও দানশীলতার (philanthropy) আহ্বান জানায়। আবার কেউ কেউ জাগতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহ্বান জানায়—ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালন করে কিন্তু জনসমক্ষে ইসলামের বাস্তবায়নের ব্যাপারে অবহেলা করে।
আরেকটি বিষয় যা একজন মুসলিমের জানা ও বোঝা জরুরি, তা হলো—ইসলামের আদর্শ (Ideology of Islam) ইতিহাসে, বর্তমানে এবং সর্বদা অন্যান্য সকল আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী থাকবে; তা সে আধুনিক ও প্রভাবশালী যেমন পুঁজিবাদ (Capitalism) হোক বা বিলুপ্তপ্রায় যেমন উপজাতীয়তাবাদ (Tribalism), সমাজতন্ত্র (Socialism), বিশৃঙ্খলাবাদ (Anarchism) কিংবা অন্য যে কোনো –বাদ যা বিশ্বে প্রবেশের চেষ্টা করে। এই আদর্শিক লড়াইয়ের মধ্যে একজন মুসলিম কোনোভাবেই ভীত, উৎকণ্ঠিত, লজ্জিত, ভেঙে পড়া বা কাপুরুষ হতে পারবে না—ইসলামের আদর্শ প্রচার ও বাস্তবায়নের কাজে—মিডিয়া, জনমত বা রাজনীতিবিদদের কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট চাপ যাই থাকুক না কেন।
গত দুই দশকে আমরা ইসলামী শরিয়াহর বিরুদ্ধে অসংখ্য আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছি, বিশেষত ৯/১১ ঘটনার পর এবং মার্কিন নেতৃত্বাধীন তথাকথিত “সন্ত্রাসবিরোধী বৈশ্বিক যুদ্ধ”-এর পর থেকে। এর পর লন্ডন বোমা হামলা, ভারতীয় বোমা হামলা, আত্মঘাতী বোমা হামলা, বোস্টন বোমা হামলা এবং লন্ডনে এক ব্রিটিশ সেনাকে ছুরিকাঘাত করার মতো ঘটনাগুলো ঘটেছে। এমনকি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, ইসলামের প্রেক্ষাপটে বলা যেকোনো রাজনৈতিক শব্দ, পদ বা অভিব্যক্তি জুড়ে দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত রাজনৈতিকভাবে কলুষিত পরিভাষার সঙ্গে—যেমন “সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ, র্যাডিকালিজম” ইত্যাদি। এ সকল আদর্শিক আক্রমণ আসলে ইসলামের জন্য নতুন কিছু নয় কিংবা কেলেঙ্কারির বিষয় নয়; কেননা ইসলামি উম্মাহ এ ধরনের বিরোধিতা বহু শতাব্দী ধরে প্রত্যক্ষ করেছে—আদম (আঃ) সৃষ্টির পর থেকেই এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে থাকবে।
নিশ্চয়ই ইসলামের আদর্শ হুমকি—আজকের বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য নয়, অমুসলিমদের জন্যও নয়, যারা ইসলামী রাষ্ট্রে ধিম্মি (ذِمِّي) হিসেবে বৈধ নাগরিকত্বের মর্যাদা পাবে; নয় বিশ্বের নিরীহ নারী বা শিশুদের জন্য, ধর্ম-বিশ্বাস বা মূল্যবোধ যাই হোক না কেন। বরং এ আদর্শ হুমকি তাদের জন্য—যারা অক্লান্তভাবে ও নিরন্তর চেষ্টা করছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা খিলাফাহ’র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঠেকাতে, ইসলামী আদর্শের পুনর্জাগরণকে বাধাগ্রস্ত করতে—নিজেদের কামনা-বাসনা পূরণ করার জন্য অথবা ইসলামের প্রতি তাদের ঘৃণাকে লালন করার জন্য।
ইসলাম এক চিরন্তন/ কালজয়ী আদর্শ হিসেবে আগমন করেছে, যা সমগ্র বিশ্বে বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য। ইসলামের একটি অনন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে শাসকদের জবাবদিহিতা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। ইসলামের একটি অনন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও রয়েছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্যতা দূর করা এবং সম্পদ বণ্টনে যে কোনো প্রতিবন্ধকতা দূর করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কিভাবে ইসলামকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। এটাই সেই আদর্শ, যা তাদের জন্য হুমকি যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রদত্ত স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করে উল্টো পথে চলে, অহংকারভরে পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং মানুষকে নিপীড়ন করে। এটাই সেই আদর্শ যা পুঁজিবাদের জন্যও হুমকি, কেননা এটি সেই অস্বাভাবিক ও অবিচারমূলক ফলাফলগুলোকে উল্টে দেবে, যেখানে আজকের দিনে বিশ্বের ৮০% সম্পদ পৃথিবীর মাত্র ৫% জনগণের হাতে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এটাই সেই আদর্শ, যা আজকে প্রবলভাবে আক্রমণ ও ধর্মনিরপেক্ষীকরণের (secularized) মাধ্যমে সংকুচিত করা হচ্ছে—যাতে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ থেকে শুধুমাত্র এক অন্ধ বিশ্বাসে (blind faith) পরিণত করা যায়।
একজন মুসলিম যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন সে মূলত আদর্শিক (ideological) হয়ে যায়। কারণ তার প্রত্যেকটি কর্মের বিধান তাকে ইসলামি ‘আক্বীদাহ’ থেকে গ্রহণ করতে হয়। আর এই আক্বীদাহই নির্ধারণ করে দেয় সে কিভাবে জীবন যাপন করবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে তার ধারণা কিরূপ হবে। ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা নির্ধারিত, যা সংবিধান ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সব সমস্যার সমাধান দেয়। ইসলামে বিশ্বাস করা মানেই এই বিশ্বাস করা যে ইসলামকে বিশ্ব শাসন করতে হবে, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন।
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
“তোমরা মানবজাতির জন্য উদ্ভূত সর্বোত্তম উম্মাহ। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজ থেকে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ।” (সূরা আলে ইমরান, ৩:১১০)
একজন আদর্শিক মুসলিম তার সকল কর্মকাণ্ডে সতর্ক থাকবেন যেন তা ইসলামের শরীয়াহ’র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং তিনি সর্বশক্তি ব্যয় করবেন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের জন্য। আদর্শিক মুসলিম বিশ্বে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করবেন, কেননা তিনি বুঝতে পারবেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর দাওয়াহ মিশন ও লক্ষ্য কী ছিল। আদর্শিক মুসলিম বিনয়ী হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন এবং সব কাজ করবেন একমাত্র তাঁর সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য, অন্য কোনো কামনা বা লালসার জন্য নয়। কেননা তিনি ভালো করেই জানেন তার কর্মকাণ্ডের পরিণতি কী এবং কিয়ামতের দিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কীভাবে হিসাব দিতে হবে।
যে মুসলিম নবী মুহাম্মদ ﷺ এর জীবনকে অনুকরণ করতে চায় এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সন্তুষ্ট করতে চায়, তার উচিত নিজের ইসলামের বোধ (understanding) সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। আপনার ইসলামের ধারণা কি সত্যিকার অর্থে ইসলামকে একটি আদর্শবাদী মতাদর্শ হিসেবে প্রতিফলিত করে? যদি না করে, তবে আপনি কোন ইসলামকে বিশ্বাস করছেন? একজন মুসলিম কখনো কুরআনের সেই আয়াতগুলোকে উপেক্ষা বা অবহেলা করতে পারে না, যেখানে স্পষ্টভাবে শরিয়াহর বিধান, জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু এ কারণে যে এগুলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে বা চরমপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত হয়, একজন আদর্শবাদী মুসলিমের উচিত নয় এগুলো থেকে দূরে সরে থাকা। বরং তার উচিত এসব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা, অধ্যয়ন করা এবং সঠিকভাবে বুঝে দাওয়াহ প্রদান করা, যাতে শরিয়াহ ও ইসলামের পররাষ্ট্রনীতিকে যথাযথভাবে রক্ষা করা যায়, যা আজ কঠোর সমালোচনার শিকার।
রাসূল ﷺ বলেছেন:
«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَى أَمْرِي فَهُوَ رَدٌّ»
“যে কোনো কাজ আমার প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী করা হয়নি, তা প্রত্যাখ্যাত।” (সহীহ বুখারি ৩৪২৫)
একজন আদর্শিক মুসলিম প্রতিটি সমস্যাকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবে। এটি সত্যিই একটি জীবনব্যাপী যাত্রা—একজন মুসলিমকে তার পূর্ববর্তী মনোভাব, পছন্দ-অপছন্দ, এবং ইসলামের বাইরে থাকা অন্যান্য আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে মুক্ত হতে হবে এবং তার কর্মকাণ্ডকে ইসলামের বিশুদ্ধ রূপের (pure form) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। বাস্তবতা হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের অভাবে, যা উম্মাহকে ইসলামিক সংস্কৃতির মাধ্যমে গড়ে তোলে, প্রত্যেক মুসলিম ভুল ধারণার শিকার হতে পারে, যা ইসলামের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। এই ভুল ধারণা যে কোনো রূপে হতে পারে—সেক্যুলার, আধুনিকতাবাদী, সংস্কারবাদী, সাংস্কৃতিক বা বিদেশী (Secular, Modernist, Reformist, Cultural বা Foreign) ইত্যাদি। এই কারণেই একজন মুসলিমের জন্য ইসলামকে একটি আদর্শ (Ideology) হিসেবে বোঝা দ্বিগুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, যাতে সে তার ইসলামী ব্যক্তিত্ব (Islamic Personality) সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে এবং জীবনযাপন করতে পারে ইসলামের নির্দেশিত পথ অনুযায়ী।
ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য যত্নসহকারে ও নিরলসভাবে কাজ করার প্রেরণা মূলত ইসলামের আদর্শগত উপলব্ধি (ideological understanding) থেকে উদ্ভূত। একজন মুসলিম যখন কোনো সমস্যার অনুভব করে—তা সে পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগত সমস্যা হোক, কিংবা বাইরের জগতে দৈনন্দিন লেনদেনের সময় (যেমন বাজার করা, কাজ করা, ভ্রমণ ইত্যাদি) উপলব্ধি করা সমস্যা হোক, অথবা রাজনৈতিক আলোচনা সম্পর্কিত সমস্যা হোক—যেমন মুসলিম বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি, স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কিংবা আমাদের ভূমিতে পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপ—তখন সে সমস্যার প্রকৃতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে এবং উপলব্ধি করে যে, এই সমস্যাগুলির মূল কারণ হলো দুনিয়ায় ইসলামী বিধানসমূহের অনুপস্থিতি। কারণ মুসলমানদের মাঝে ইসলামের আদর্শগত উপলব্ধির ঘাটতির কারণে তারা তাদের কর্মে ইসলামকে অবহেলা করছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ড হিসেবে ইসলামের পরিবর্তে পশ্চিমা ধারণাকে (Western ideas) ব্যবহার করছে। যেমন— মতপ্রকাশের স্বাধীনতা “freedom of speech” বা মালিকানার স্বাধীনতা “freedom of ownership” এর মানদণ্ড দিয়ে নির্ধারণ করছে কোনো কাজ করা যাবে কিনা, অথচ ইসলামের দিকে ফিরে যাচ্ছেনা। আমরা এর উদাহরণ দেখি, যখন কোনো মুসলিম কিশোর বলে বসে: “I can do what I want, it is my choice” (আমি যা খুশি তাই করতে পারি, এটা আমার পছন্দ)। অথবা যখন কোনো মুসলিম দম্পতি সুদভিত্তিক মর্টগেজে তাদের প্রথম বাড়ি কেনার সময় দাবি করে, “এটি আমাদের জন্য বৈধ।” কিংবা কোনো মুসলিম মনে করে যে, মুসলিমদের একটি নির্দিষ্ট এমপি (member of parliament) -কে ভোট দেওয়ার জন্য সংগঠিত করে সে ইসলামকে সাহায্য করছে। কিন্তু যে মুসলিম ইসলামকে তার সঠিক আদর্শিক রূপে (correct ideological narrative) বোঝে, সে এসব সমস্যার উৎসকে ইসলামের অনুপস্থিতি এবং জনজীবন (public life) থেকে ইসলামের বিচ্ছিন্নতার সাথে সম্পর্কিত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন:
«مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا»
অর্থাৎ: “আল্লাহর সীমারেখা (হুদূদ) রক্ষা করার চেষ্টা করা লোকদের দৃষ্টান্ত এবং যারা তা ভঙ্গ করে তাদের দৃষ্টান্ত একটি নৌকায় একসাথে বসবাসকারী লোকদের মতো। তাদের কেউ উপরের তলায় এবং কেউ নিচের তলায় বাস করে। নিচের তলার লোকেরা যখন পানি নিতে চায় তখন তাদের উপরের তলায় যেতে হয়। তখন তারা বলে, ‘যদি আমরা আমাদের অংশে নিচে একটি ছিদ্র করি (যাতে সরাসরি পানি নিতে পারি) এবং উপরতলার লোকদের কষ্ট না দিই, তাহলে কেমন হয়?’ যদি উপরতলার লোকেরা তাদের (নিচের তলার লোকদের) ইচ্ছামতো কাজ করতে দেয় তবে সবাই ধ্বংস হবে। আর যদি তারা তা থেকে বাধা দেয় তবে সবাই রক্ষা পাবে।”(সহীহ বুখারী)
তিনি (আদর্শিক মুসলিম) উপলব্ধি করবেন যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যেখানে একজন মানুষের পক্ষে বাড়ি কেনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং তাকে বাধ্য হয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয়। অথচ ইসলাম সুদকে (রিবা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং ঋণ-ভিত্তিক অর্থনীতির ধারণার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। তিনি বুঝবেন যে, যৌন স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত না থাকা এবং শরীয়াহ্ দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রণ না করাই হচ্ছে সে কারণ, যার ফলে একজন মুসলিম তার প্রবৃত্তি হারাম উপায়ে পূরণ করছে। কিংবা একজন মুসলিম নারী ইসলামী পোশাক বিধান পরিত্যাগ করছে, কারণ পশ্চিমা সামাজিক ব্যবস্থা তাকে উন্মুক্তভাবে ও আকর্ষণীয়ভাবে পোশাক পরার স্বাধীনতা দিচ্ছে; অথচ ইসলাম একজন মুসলিম নারীর জন্য নির্দিষ্ট পোশাকের বিধান সংজ্ঞায়িত করে দিয়েছে। আদর্শিক (Ideological) মুসলিম উপলব্ধি করেন যে, আজকের তরুণ মুসলিমরা ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত একটি পরিবেশে বেড়ে উঠছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির অনুপস্থিতিই হলো সেই কারণ, যার জন্য আজকের মুসলিম কিশোর তার খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করছে, ইসলামের মানদণ্ড অনুসারে নয়। তিনি উপলব্ধি করবেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি মুসলিমদের জন্য তাদের দ্বীন পালন করার প্রাকৃতিক পরিবেশ কেড়ে নিয়েছে এবং এর পরিবর্তে এমন এক আদর্শ চাপিয়ে দিয়েছে যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক—যেমন দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ধারণা অথবা গোত্রবাদ (tribalism)-প্রসূত সাংস্কৃতিক ভ্রান্ত চিন্তাধারা।
অনেক আন্তরিক মুসলিম (sincere Muslims) ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করার জন্য নানা কাজ সম্পাদন করেন। কিন্তু অত্যন্ত জরুরি হলো—এই কাজগুলো যেন ইসলামের সংজ্ঞায়িত আদর্শিক লক্ষ্য (Ideological objectives)-এর সাথে সম্পর্কিত হয়। এ বিষয়ে একজনকে শুধু মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মক্কী জীবনের দিকে মনোযোগ দিলেই যথেষ্ট। এমনকি একজন অমুসলিমও উপলব্ধি করবে যে, রাসূল ﷺ-এর মিশন ছিল আজকের ভাষায় যাকে বলা হয় একটি বিপ্লব। তিনি ﷺ আরব সমাজকে গোত্রীয় ও প্রথাগত সামাজিক রীতি থেকে ইসলামি বিধি-বিধানের দিকে রূপান্তরিত করেছিলেন। এ পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছিল এবং চলতে থাকে ১৯২৪ সালে ইসলামী খিলাফতের ধ্বংস পর্যন্ত। সুতরাং যে মুসলিম ইসলামের দাওয়াহ বহন করতে চায়, তার উদ্দেশ্যও একই হতে হবে—অর্থাৎ পুরো পৃথিবীতে ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো। আজ একশ বছরেরো অধিক সময় ধরে রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলামী বিধান ছাড়া জীবনযাপনের পর মুসলিম উম্মাহ আজ আবার শারিয়াহ্র বাস্তবায়নের জন্য তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষিত। অসংখ্য জরিপে দেখা গেছে—মুসলিম বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শারিয়াহ্র অধীনে জীবনযাপন করতে চায়। যদিও এ সত্য প্রমাণে জরিপের প্রয়োজন নেই। শুধু গত দুই দশক ধরে দেখা গেছে মুসলিম বিশ্ব ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে জীবন দিতেও প্রস্তুত, যেমন আমরা সিরিয়ার উম্মাহর দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষ করেছি। অতএব যে মুসলিম ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝেছে, সে উপলব্ধি করবে যে ইসলামী রাষ্ট্রই মুসলিমদের পুনর্জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাই সে ইসলামের দাওয়াহ ও রাসূল ﷺ-এর মিশন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাবে।
আদর্শিক মুসলিম, যে ইসলামী পুনর্জাগরণের চেষ্টা করে, তার জীবন হবে না একঘেয়ে—যেখানে কেবল অফিসে যাওয়া, ঘরে ফেরা, ঘুমানো ও ছুটির দিনে আরাম করা। বরং সে প্রতিদিন হাজারো সমস্যা অনুভব করে এবং উপলব্ধি করে যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কতটা জরুরি। সে জানে তার হাতে কী বিশাল দায়িত্ব রয়েছে এবং সর্বশক্তি দিয়ে সে এই চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী। তার মন মেনে নিতে পারে না যে মানবজাতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলাকে অবহেলা করে কুফরের অতল গহ্বরে পতিত হয়েছে, আর এর ফলেই মানবজাতির উপর নির্যাতন নেমে এসেছে—অথচ মুসলিমরা ব্যাপকভাবে এ সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আল্লাহ تعالى বলেন:
هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ
“তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এটিকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।”
(সূরা আত-তাওবাহ: ৩৩)তার সংবাদ অনুসরণ (following the news) করার অভ্যাস তাকে সপ্তাহান্তে আরামে থাকতে দেয় না। কারণ সে অনুভব করে, ইসলামকে ঘিরে প্রচারণা এবং আক্রমণের নতুন নতুন কৌশল চলছে। সে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা বোঝে এবং উপলব্ধি করে কীভাবে রাষ্ট্রগুলো চতুরভাবে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিম ভূমিগুলোর উপর তাদের সাম্রাজ্যবাদ কায়েম রাখছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের উত্থানকে রোধ করছে। ফলে সে অনুভব করে—এটার মোকাবিলা করতে হবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে তার সমাজের মধ্যে। সে চায় মানবজাতি শান্তিতে থাকুক এবং সে বোঝে যে, এটি কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন মানবজাতিকে ইসলাম দ্বারা পুনর্জীবিত (revived) করা হবে। অতএব অবসর সময়ে কোনো নির্দিষ্ট আলোচনার বিষয়ে তার বোধ (understanding) বৃদ্ধি করার জন্য তার হাত বই ছাড়া পিছিয়ে থাকে না। জনজীবনে (in public life) তার অংশগ্রহণও এমন আলোচনাহীন হয় না, যেখানে সে নিজের আদর্শ শেয়ার করতে পারে। স্ত্রী, পরিবার বা বন্ধুদের সাথে তার সময় শুধু বিনোদন বা অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সেই সময়কে সে একটি সুবর্ণ সুযোগে পরিণত করে—যাতে আরো মানুষকে ইসলামের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট ও আহ্বান জানাতে পারে। সে একটি পরিকল্পনার সাথে কাজ করে, যেখানে তার সপ্তাহগুলো যতটা সম্ভব ফলপ্রসূ হয় এবং অগ্রাধিকার থাকে ইসলামের পুনর্জাগরণের আহ্বান। এজন্য সে নিজের নফসী আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে—যেমন সিনেমায় নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র দেখতে যাওয়া, স্ত্রীকে নিয়ে নতুন রেস্টুরেন্টে ঘন ঘন ভ্রমণ করা, খেলাধুলায় অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা, কিংবা ঘর, গাড়ি বা ব্যক্তিগত যন্ত্রপাতি নিয়ে নিখুঁত সাজসজ্জায় অতিরিক্ত সময় নষ্ট করা। সে সর্বদা নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীসকে মনে রাখে-
আল্লাহ تعالى বলেন:
قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
“বলুন: নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু—সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক।” (সূরা আল-আন‘আম: ১৬২)
আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»
“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা নীরব থাকে।”
(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)“একজন মতাদর্শপ্রাণ মুসলিম বা আদর্শিকভাবে চালিত মুসলিম (ideologically driven Muslim) হওয়ার অর্থ হলো—এই আদর্শের দাওয়াহ’ই তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, যার চারপাশে তার সমগ্র জীবন আবর্তিত হয়। যদি এমন না হয়, তবে বুঝতে হবে সে মুসলিম ইসলামকে আদর্শ (Ideology) হিসেবে অনুধাবন করতে পারেনি। অর্থাৎ, ইসলাম এমন একটি চিন্তা-ধারা যা বর্ণ বা ভৌগোলিক সীমানাকে অতিক্রম করে এবং এমন বিধান ধারণ করে যা সকল মানুষের জন্য, সকল সময়ে, সকল পরিস্থিতিতে সমভাবে প্রযোজ্য—ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, তেমনি সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আমাদের ইসলামের নেয়ামত দান করেছেন, যাতে আমরা নির্বাচিত উম্মাহ হিসেবে ইসলামের আদর্শকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিই। আজ আমরা সারা বিশ্বে বিস্তৃত—এটি আমাদের পূর্বসূরিদের কর্মফল, যারা ইসলামের পতাকা (راية الإسلام) উঁচিয়ে ধরেছিলেন এবং তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করেছিলেন ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য, ইসলামের সঠিক আদর্শিক বোঝাপড়া (understanding) নিয়ে।
যদি আমরা ইসলামকে একইভাবে না বুঝি, তবে মুসলিমরা কুফরের ছায়ায় থেকেই যাবে এবং আমাদের প্রজন্ম ইসলামের বাস্তব রূপকে (practical manifestation of Islam) খিলাফাহর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। ইসলামী খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ কেবলমাত্র আদর্শিক মুসলিমদের দ্বারাই সম্পন্ন হবে, এবং ইসলামের পুনর্জাগরণ (revival) ঘটবে তখনই—যখন উম্মাহ স্পষ্টভাবে ইসলামকে একটি আদর্শ (ideology) হিসেবে বুঝবে।
আল্লাহ تعالى বলেন:
ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।”
(সূরা আল-মায়েদাহ: ৩)দু’আ:
“হে আল্লাহ, আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে ইসলামের আদর্শিক বোঝাপড়া দান করুন, যেভাবে আপনি আপনার প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে এবং তাঁর সাহাবীগণকে দান করেছিলেন। আমাদের চিন্তা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, পছন্দ-অপছন্দ ও কর্মসমূহ যেন কেবল আপনার দ্বীন ইসলাম অনুযায়ী হয়।” …আমীন।
আল্লাহর ইচ্ছায় সমাপ্ত
– কায়েস আবু মুহাম্মদ কর্তৃক অনুবাদকৃত ও পরিমার্জিত।
প্রশ্ন-উত্তর: যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর সাথে লেনদেন

প্রশ্ন-উত্তর
প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর সাথে লেনদেন
প্রাপক: আবু মুহাম্মদ সালিম
(অনুবাদিত)প্রশ্ন:
আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
আবু মুহাম্মদ সালিম
আমি মহান আল্লাহর কাছে দুআ করছি যে আপনি সুস্থ থাকুন, এবং আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিজয় দান করুন। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করছি যে তিনি আপনার হাত দিয়ে কল্যাণের সকল দরজা খুলে দিন।
আমি এই প্রশ্নটি আমাদের শেখ এবং প্রিয়, হিযবুত তাহরীরের আমির, আতা বিন খলিল আবু আল-রাশতাহকে উদ্দেশ্য করে করছি:
এক ভাই আমাকে বারকান বসতিতে কন্টেইনার তৈরির একটি কারখানায় কাজ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সম্প্রতি, এই কারখানার একটি অংশ ‘ইসরায়েলি’ সেনাবাহিনীর সুবিধার জন্য রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর এবং অন্যান্য সামরিক-সম্পর্কিত জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য ট্রেলার তৈরি করে। সেনাবাহিনীর জন্য ট্রেলার তৈরি করে এমন এই বিভাগে কাজ করা কি জায়েজ?
আল্লাহ আপনাকে বরকতময় করুন এবং আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।
আল্লাহ আপনাকে আশ্রয় দিন, আপনাকে বিজয় দান করুন, আপনাকে রক্ষা করুন, আপনাকে ক্ষমতায়িত করুন এবং আপনার হাতে বিজয় এবং ক্ষমতায়ন আনুন।
যদি সম্ভব হয়, তাহলে একটি দ্রুত উত্তর পেলে খুশি হবো – আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন।
উত্তর:
ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ,
উল্লেখিত কারখানার (যার একটি অংশ সম্প্রতি ‘ইসরায়েলি’ সেনাবাহিনীর সুবিধার জন্য রূপান্তরিত হয়েছে এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর এবং অন্যান্য সামরিক-সম্পর্কিত জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য ট্রেলার তৈরি করে) ক্ষেত্রে, এটি ইহুদি সত্তার অন্তর্গত, যা আসলে যুদ্ধরত একটি রাষ্ট্র। উত্তর দুটি ক্ষেত্রে নির্ভর করে:
১. দখলদারিত্বের অধীনে বসবাসকারী মুসলমানরা।
২. দখলদারিত্বের বাইরের মুসলমানরা।প্রথম ক্ষেত্রে:
ইহুদি দখলদারিত্বের অধীনে থাকা মুসলিমরা মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মক্কায় থাকা মুসলিমদের মতো। ইহুদি দখলদারিত্বের অধীনে থাকা ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদিতে জড়িত থাকা বৈধ, শত্রুকে শক্তিশালী করে এমন কাজ ছাড়া। একইভাবে, একজন মুসলিম, উদাহরণস্বরূপ, যার আমেরিকান নাগরিকত্ব রয়েছে, তার জন্য হুকম হচ্ছে মক্কার মুসলমানদের মতো যারা হিজরত করেনি, তাই তাদের জন্য দার আল-হারব (যুদ্ধরত দেশে) লেনদেন করা বৈধ, যেখানে তারা বাস করে। তবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের শক্তিশালী করে এমন বিষয় যার (তাহকিক আল-মানাত) করে আইনগত প্রয়োগ নিরূপন করা যায়, তা ছাড়া।
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে:
আমরা পূর্বে একাধিক জবাবে একই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, যার মধ্যে রয়েছে:
৩১/০৩/২০০৯ তারিখের একটি প্রশ্নের উত্তর:
১. যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর সাথে সরাসরি কাজ করা জায়েজ নয়, এবং সেই রাষ্ট্রগুলোর কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করাও জায়েজ নয়, কারণ প্রকৃত যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক একটি যুদ্ধ সম্পর্ক, শান্তিপূর্ণ ব্যবসায়িক সম্পর্ক নয়।
২. যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর সাথে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তবতা নিম্নরূপে নিরূপন করা হয়:
ক. যদি প্রতিষ্ঠানটি যে প্রকল্পে কাজ করছে তা আসলে যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির জন্য হয়, তাহলে সেই প্রকল্পে প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করা জায়েজ নয়।
খ. যদি প্রকল্পটি যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর জন্য না হয়, বরং স্থানীয় জনগণের জন্য হয়, যেমন স্কুল নির্মাণ বা রাস্তা নির্মাণ, তাহলে পাপ সেই প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে যারা যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির সাথে কাজ করে, তবে কাজটি জায়েজ যতক্ষণ না প্রকল্পটি যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির জন্য না হয়।
২৪/০৭/২০১১ তারিখের একটি প্রশ্নের উত্তর:
“… মুসলিম ভূখণ্ডের দখলদার রাষ্ট্রগুলোর (যারা আসলে যুদ্ধে লিপ্ত) কোম্পানি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরাসরি চুক্তি করা অনুমোদিত নয়, কারণ এটি আসলে যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রগুলির সাথে লেনদেনের একটি রূপ। স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় সংস্থার সাথে চুক্তি করার ক্ষেত্রে যা দখলদার রাষ্ট্রের সাথে (সরাসরি) সম্পর্কিত নয় কিন্তু এর সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:
১. যদি সম্পর্কটি দখলদার রাষ্ট্রের সাথে সামরিক প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকে, তবে এটি অনুমোদিত নয়।
২. যদি সম্পর্কের মধ্যে এমন বাণিজ্যিক প্রকল্প জড়িত থাকে যা দেশের ক্ষতি করে না, তবে এটি অনুমোদিত, তবে ক্ষতি করার সন্দেহের কারণে এটি এড়ানো ভাল।
৩. যদি কর্মী স্থানীয় রাষ্ট্র দ্বারা নিযুক্ত হন, তবে তার চুক্তি সরাসরি দখলদার রাষ্ট্রের সাথে হয়, তবে এটি অনুমোদিত নয়।
৪. যদি কর্মী স্থানীয় রাষ্ট্র দ্বারা নিযুক্ত হন এবং তার চুক্তি স্থানীয় রাষ্ট্রের সাথে হয়, তবে এটি অনুমোদিত, এমনকি যদি স্থানীয় রাষ্ট্র দখলদার রাষ্ট্র থেকে আর্থিক সহায়তা পায়।
৫. যদি কর্মী স্থানীয় রাষ্ট্র দ্বারা নিযুক্ত হন, তবে তার চুক্তিটি স্থানীয় রাষ্ট্রের সাথে , কিন্তু সে সরাসরি দখলদার রাষ্ট্র থেকে তার বেতন পায়, তাহলে তা জায়েজ নয়।
এর প্রমাণ হল যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর সাথে লেনদেনের বিধান।”
আমি আশা করি এটি যথেষ্ট, এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন এবং সর্বাধিক প্রজ্ঞাময়।
আপনার ভাই,
আতা বিন খলিল আবু আল-রাশতাহ১২ মহররম ১৪৪৭ হিজরি
০৭/০৭/২০২৫ ইংগণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার চিন্তা: হুকুম শরীয়াহ এবং ইতিহাসের আলোকে বাস্তবতা ও ভ্রান্তি

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد
আজকের মুসলিম সমাজে একটি প্রচলিত ধারণা হলো — “গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।” প্রথমে বিষয়টি শুনতে আকর্ষণীয় মনে হলেও, শরীয়াহর দৃষ্টিতে এবং বাস্তবতার আলোকে এটি একটি ভয়াবহ ভ্রান্তি। কেননা, এটি ইসলামের মৌলিক রাজনৈতিক চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক, এবং ইসলামী পদ্ধতির পরিবর্তে কাফিরদের পদ্ধতি গ্রহণের নামান্তর।
গণতন্ত্র কী এবং কেন এটি ইসলামের পরিপন্থী?
সংক্ষেপে, গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে। সংসদে বসে মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মত অনুযায়ী আইন তৈরি হয়। এক কথায়, মানুষ যা চাইবে, তাই হবে — এমনকি তা আল্লাহর বিধানের বিরোধী হলেও।
অন্যদিকে ইসলাম ঘোষণা করে:
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
“হুকুম তো কেবল আল্লাহরই।”
(সূরা ইউসুফ: ৪০)এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শাসন ও আইন প্রণয়নের পূর্ণ অধিকার একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং গণতন্ত্রের মূল দর্শন — মানবসৃষ্ট আইন — সরাসরি কুরআনের এই মৌলিক নীতির বিরোধিতা করে।
হারাম পথে হালাল প্রতিষ্ঠার চেষ্টার ভ্রান্তি
অনেকে যুক্তি দেন, “উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় — ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা — তাহলে গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করাতে দোষ কী?”
কিন্তু শরীয়াহর একটি মৌলিক নীতি হলো:
إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا
“নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি শুধুমাত্র পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০১৫)অতএব, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মতো পবিত্র কাজ হারাম পদ্ধতিতে করা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। উদ্দেশ্য পবিত্র হলেও যদি মাধ্যম হারাম হয়, তা ইসলামে বৈধ নয়।
কুরআনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা
১. যালিমদের সাথে আপস করার পরিণাম
আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
“আর তোমরা যালিমদের দিকে ঝুঁকো না, তা না হলে তোমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। তারপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।”
(সূরা হুদ: ১১:১১৩)গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করা মানে কুফরী আইনপ্রণেতাদের সাথে আপস করা, যা আল্লাহ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।
২. কুফরী ব্যবস্থার অংশীদার হওয়ার নিষেধাজ্ঞা
আল্লাহ বলেনঃ
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ
“তোমাদের প্রতি কিতাবে নাযিল করা হয়েছে যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং উপহাস করা হচ্ছে, তখন তাদের সাথে বসো না যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে প্রবেশ করে। নিশ্চয়ই তোমরা যদি (তাদের সাথে বসো) তবে তোমরা তাদের মতই হবে।” (সূরা আন-নিসা: ৪:১৪০)
অতএব, কুফরী ব্যবস্থার অংশীদার হওয়া মানে সেই অপরাধে শরিক হওয়া।
৩. আল্লাহর বিধানকে অগ্রাহ্য করা কুফরী
আল্লাহ বলেনঃ
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ
“আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা হুকুম করে না, তারাই কাফির।”
(সূরা আল-মায়িদাহ: ৫:৪৪)গণতন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের হাতে। এটি সরাসরি কুফরীর শামিল।
হাদীসের প্রমাণসমূহ
১. কাফিরদের পদ্ধতি অনুসরণের বিরুদ্ধে সতর্কতা
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
“যে কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।”
(সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৪০৩১)অতএব, গণতন্ত্রের মতো কাফিরদের জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা সরাসরি এই হাদীসের আওতায় পড়ে।
২. প্রতারণামূলক সময়ের সতর্কবার্তা
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ … وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ
“মানুষের উপর প্রতারণামূলক বছর আসবে … তখন তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট লোকেরা নেতৃত্বে কথা বলবে।”
(সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস: ৪০৩৬)গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকৃত নেতৃত্বের পরিবর্তে নিকৃষ্ট ও অযোগ্য লোকেরা নেতৃত্বের আসনে বসে — যা এই হাদীসের প্রতিফলন।
ইসলামী শূরা ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র:
অনেকেই গণতন্ত্র (ডেমোক্রেসি) ও শূরা (পরামর্শ) কে এক করে দেখে, অথচ বাস্তবে এ দু’টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। শূরা হলো— ইসলামী নেতৃত্বের পক্ষ থেকে যোগ্য আলেম ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করা। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র হলো— মানুষের খেয়াল-খুশি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা, যা আল্লাহর অবতীর্ণ শরীয়াহর বিপরীত।
কুরআনে আল্লাহ তাআলা শূরার কথা বলেছেন:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
“আর তাদের কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।”
(সূরা আশ-শূরা: ৩৮)এখানে স্পষ্টভাবে পরামর্শের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই পরামর্শ কেবল শরীয়াহর সীমার মধ্যে হবে।
অন্যদিকে গণতন্ত্রে সংসদে পরামর্শ হয় বটে, কিন্তু তা মানব-রচিত আইনের বলয়ের ভেতরে সীমাবদ্ধ। সেখানে কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রণয়নের কোনো কর্তৃত্ব নেই। বরং অধিকাংশ মানুষের মতামতকেই আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যা আল্লাহ তাআলার ঘোষণার স্পষ্ট বিরোধিতা:
অন্যদিকে গণতন্ত্রে সংসদে পরামর্শ হয় বটে, কিন্তু তা মানব-রচিত আইনের বলয়ের ভেতরে সীমাবদ্ধ। সেখানে কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রণয়নের কোনো কর্তৃত্ব নেই। বরং অধিকাংশ মানুষের মতামতকেই আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যা আল্লাহ তাআলার ঘোষণার স্পষ্ট বিরোধিতা:
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
“আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের নির্দেশ মানো, তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেবে। তারা শুধুমাত্র অনুমান অনুসরণ করে এবং শুধুমাত্র বাজে কথা বলে।” (সূরা আল‑আন‘আম : ১১৬)
আয়াতটি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্যের মানদণ্ড নয়, বরং অনেকেই শুধুমাত্র অনুমান (ظنّ) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয় ও সেই কারণেই তারা বিভ্রান্ত হয়।ইসলামিক চিন্তাভাবনায়, সত্য অনুসন্ধানে কুরআন- সুন্নাহ, বিচার-বিবেচনা ও জ্ঞানের গুরুত্ব অগ্রাধিকার পায়, শুধুমাত্র সংখাধিক্যের ভিত্তিতে নয়।
ইসলামে শূরার পদ্ধতি:
খিলাফাহ শাসনব্যবস্থায় খলিফা “আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ”-এর সঙ্গে পরামর্শ করবেন। এরা হবেন এমন যোগ্য আলেম ও বিশেষজ্ঞ, যারা উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য। হাদীসে এসেছে:مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ
“যে ইস্তিখারা করেছে সে ব্যর্থ হয়নি, আর যে পরামর্শ নিয়েছে সে অনুতপ্ত হয়নি।”
(মুসনাদ আহমাদ: ২৮৬)তবে খলিফা শূরা কমিটির সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নন; তিনি চাইলে নিজের সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে পারেন। শূরা ইসলামে বাধ্যতামূলক নয় বরং পরামর্শ গ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
সুতরাং, গণতন্ত্র ও শূরা এক নয়।
- গণতন্ত্রে: মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতই আইন।
- শূরায়: আল্লাহর শরীয়াহর সীমার মধ্যে যোগ্য আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ।
এ কারণে ইসলামী শূরা ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে এক করা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।
উপরের কুরআন ও হাদীসের দলীল থেকে স্পষ্ট যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার চিন্তা একটি আত্মপ্রতারণা। হারাম পদ্ধতিতে হালাল প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইসলামের পথ হলো — রাসূল ﷺ এর দেখানো পদ্ধতিতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা: দাওয়াহ, জনমত সৃষ্টি এবং আহলে কুওয়া ও নুসরাহর সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে।
গণতন্ত্রের পথে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা: ইতিহাস থেকে শিক্ষণীয় বাস্তবতা
দীর্ঘদিনের উপনিবেশিক শাসন ও পশ্চিমা আধিপত্য মুসলিম উম্মাহকে তাদের প্রকৃত শাসনব্যবস্থা খিলাফাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমন এক অচলাবস্থায় দাঁড় করিয়েছে যেখানে বহু ইসলামী দল ভেবেছে, “গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।” বাস্তবে দেখা গেছে, এই চিন্তা ইসলামী পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং ব্যর্থতাই এর পরিণতি।
নিচে ইতিহাস থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ বিশ্লেষণ করা হলো—
১. মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন (Muslim Brotherhood)
মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড (ইখওয়ানুল মুসলিমীন) দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। ২০১২ সালে মুহাম্মদ মুরসি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
কি হয়েছিল?
- মুরসি ক্ষমতায় এসেও পূর্ণ ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।
- মিশরের বিদ্যমান সংবিধানের কাঠামো ও আন্তর্জাতিক চাপের কারণে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
- তিনি পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য বহু আপস করেন।
ফলাফল
এক বছরের মধ্যেই সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। ইখওয়ান নেতাদের অনেকে গ্রেফতার ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।
শিক্ষণীয় দিক
গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও বাহ্যিক চাপ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
২. তুরস্কের রেফাহ পার্টি এবং এ.কে. পার্টি
১৯৯৬ সালে নাজমুদ্দিন এরবাকানের নেতৃত্বে রেফাহ পার্টি ক্ষমতায় আসে। পরে রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান নেতৃত্বে এ.কে. পার্টি (AKP) রাজনীতিতে আসে।
কি হয়েছিল?
- রেফাহ পার্টি ইসলাম প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করলেও সামরিক বাহিনী ও পশ্চিমা চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।
- এ.কে. পার্টি ক্ষমতায় এসে স্পষ্ট ঘোষণা দেয় যে তারা ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখবে।
- ইসলামী ফৌজদারি আইন, হুদুদ, শরীয়াহ আদালত কোনো কিছুই প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।
ফলাফল: তুরস্ক ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামো অটুট রাখে, বরং ইসলামী শাসনের দাবিগুলোকে পাশ কাটিয়ে গণতান্ত্রিক আধুনিকতাকে শক্তিশালী করে।
৩. তিউনিসিয়ার আন-নাহদাহ (Ennahda)
আরব বসন্তের পর ২০১১ সালে আন-নাহদাহ পার্টি তিউনিসিয়ায় গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসে।
কি হয়েছিল?
- শুরুতে ইসলামী শাসনের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে তারা ঘোষণা করে যে তারা “মডারেট ইসলাম” ও “গণতান্ত্রিক ইসলাম” প্রতিষ্ঠা করবে।
- শরীয়াহভিত্তিক আইন প্রণয়ন এজেন্ডা থেকে বাদ দেয়।
ফলাফল
আন-নাহদাহ এক প্রকার সেক্যুলার ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে পরিণত হয় এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ত্যাগ করে।
৪. পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলামী
পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলামী প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।
কি হয়েছিল?
- নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও তারা আজও ক্ষমতায় যেতে পারেনি তার মানেইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ।
- সংবিধানের ভেতরে থেকে কাজ করতে গিয়ে বহু ইসলামী এজেন্ডা ত্যাগ করে সমঝোতার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।
ফলাফল
পাকিস্তান আজও পশ্চিমা ধাঁচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে শরীয়াহ কেবল আংশিকভাবে আছে।
৫. ফিলিস্তিনের হামাস (Hamas)
২০০৬ সালে হামাস গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়লাভ করে গাজায় ক্ষমতায় আসে।
কি হয়েছিল?
- আন্তর্জাতিক চাপ, অর্থনৈতিক অবরোধ এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে পূর্ণ ইসলামী শাসন কায়েম সম্ভব হয়নি।
- হামাসও ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সমঝোতার পথে যায় এবং ফাতাহ’র সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল
ফলাফল
গাজায় ইসলামী শাসনের পরিবর্তে রাজনৈতিক বেঁচে থাকার কৌশলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
৬. আলজেরিয়ার ইসলামী সালভেশন ফ্রন্ট (FIS)
১৯৯১ সালে আলজেরিয়ার FIS (Islamic Salvation Front) নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে।
কি হয়েছিল?
- তারা পূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছিল।
- কিন্তু সেনাবাহিনী ও পশ্চিমা শক্তির চাপে নির্বাচন বাতিল করে দেওয়া হয়।
- FIS এর নেতারা গ্রেফতার হন এবং দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।
ফলাফল
গণতান্ত্রিক পথ চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং আলজেরিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংঘাত শুরু হয়।
বাস্তবতার সারসংক্ষেপ
১. কোনো ইসলামী দলই গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ইসলামী শাসন (খিলাফাহ) প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।
২. ক্ষমতায় গেলে তারা গণতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে এবং ইসলামী শরীয়াহর পূর্ণ বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকে।
৩. আন্তর্জাতিক চাপ, সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ, এবং পশ্চিমা শক্তির প্রভাব ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার যেকোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।কেন এমন হয়?
- গণতন্ত্র ইসলামী শাসনব্যবস্থার বিপরীত দর্শনে দাঁড়ানো। এখানে সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে, ইসলামে তা আল্লাহর হাতে।
- পশ্চিমা শক্তির হস্তক্ষেপ — কোনো ইসলামী দল গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে চাইলে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো কঠোর ব্যবস্থা নেয়।
- সমঝোতার রাজনীতি — ইসলামী দলগুলো গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে থাকতে গিয়ে ইসলামের মূলনীতি ত্যাগ করে কুফরের সাথে সমঝোতার রাজনীতি করতে বাধ্য হয়।
ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ:
ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ আসলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ আমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটি হলো রাসূল ﷺ যে পদ্ধতিতে মক্কা থেকে মদিনায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই নববী পদ্ধতি।
এটি সংক্ষেপে তিনটি ধাপে বোঝা যায়ঃ
১. দাওয়াহ ও চিন্তাগত সংগ্রাম
রাসূল ﷺ প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাস পরিবর্তনের দাওয়াহ দেন। মক্কায় তিনি আকীদাহ ভিত্তিক দাওয়াহ চালিয়ে মানুষের মনে ইসলামের চিন্তাধারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।
এর মূল কাজ হলো মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের সঠিক ধারণা দেওয়া, বিদ্যমান ভুল বিশ্বাস ও মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করা।
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
“তুমি যা আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর।”
(সূরা আল-হিজর: ১৫:৯৪)২. জনমত সৃষ্টি ও উম্মাহকে প্রস্তুত করা
রাসূল ﷺ মক্কায় সমাজের প্রভাবশালী ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটি জনমত তৈরি করেন যে, কেবল ইসলামই ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা।
এর মূল কাজ হলো মিথ্যা শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক প্রথার অন্যায়গুলো প্রকাশ্যে তুলে ধরা, সমাজে বিকল্প হিসেবে ইসলামের নিজস্ব মডেল তুলে ধরা।
৩. আহলে কুওয়া (ক্ষমতাধরদের) নুসরাহ গ্রহণ
রাসূল ﷺ মক্কায় বহু গোত্রের নেতাদের কাছে গিয়েছিলেন শক্তিশালী সমর্থন (নুসরাহ) চাওয়ার জন্য। অবশেষে আনসার সাহাবারা (আওস ও খাজরাজ) তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেন।
এক্ষেত্রে মূল কাজ হলো সমাজের ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালীদের কাছ থেকে শক্তির সহায়তা (নুসরাহ) গ্রহণ, যাতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।(সীরাতে ইবনে হিশাম দ্রষ্টব্যঃ)
وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ
“আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তবে তোমাদের কর্তব্য তাদের সাহায্য করা।”
(সূরা আনফাল: ৮:৭২)কী ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ নয়?
- গণতন্ত্রের ভেতরে প্রবেশ করা: কারণ এটি কুফরী ব্যবস্থা।
- সশস্ত্র বিদ্রোহ (অব্যবস্থিত জিহাদ): রাসূল ﷺ কখনো মক্কায় জোর করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেননি।
- সংস্কারবাদী আপস: বিদ্যমান শিরকী ও কুফরী ব্যবস্থাকে মানিয়ে নেওয়া ইসলামের পদ্ধতি নয়।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ
وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ
“তোমরা আমার সুন্নাহ এবং সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধর।”
(সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৪৬০৭)রাসূল ﷺ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন কুফরী কাঠামোর ভেতরে প্রবেশ করে নয়, বরং দাওয়াহ, জনমত সৃষ্টি এবং আহলে কুওয়া (ক্ষমতাশালী জনগোষ্ঠীর) নুসরাহ গ্রহণের মাধ্যমে।
তিনি কখনো মক্কার দারুন নাদওয়া (কুফরী রাজনৈতিক পরিষদ) তে অংশ নেননি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।
পরিশেষে আমরা বলতে পারি
- গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আশা ইতিহাসে ব্যর্থ হয়েছে এবং যা শরীয়াহ অনুমোদিত ও নয়।
- ইসলামী আন্দোলনের মূল এজেন্ডা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে গিয়েই দুর্বল ও লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে।
- রাসূল ﷺ এর পদ্ধতিই একমাত্র পথ: দাওয়াহ, জনমত সৃষ্টি এবং নুসরাহর মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা।
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক দীর্ঘ হাদীসের শেষে বলেনঃ
“ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ”
“…তারপর আবার আসবে খিলাফত, যা হবে নবুয়্যতের আদলে।”দোয়া
اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.
“হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্যকে সত্যরূপে দেখাও এবং তা অনুসরণ করার তাওফীক দাও; আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপে দেখাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও।”
আল্লাহর ইচ্ছায় সমাপ্ত।
একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা: গণতন্ত্র না খিলাফাহ — প্রেক্ষাপট ও বিশ্লেষণ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, ও কুরআন ও রাসূলের (সা.) মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে মানবজাতি এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম পেয়েছে।
বর্তমান দুনিয়ায় মুসলিম উম্মাহর একটি বড় অংশ ইসলামি শাসনব্যবস্থা তথা খিলাফাহ এবং পশ্চিমা শাসনব্যবস্থা, বিশেষ করে গণতন্ত্রের পার্থক্য বোঝে না। অনেকে এই দুটি ব্যবস্থাকে মিলিয়ে দেখে, কেউ আবার খিলাফাহকে মধ্যযুগীয় বা অগণতান্ত্রিক ভাবে অপপ্রচার করে। অথচ খিলাফাহ একটি স্বতন্ত্র এবং আল্লাহ-নির্ধারিত শাসনব্যবস্থা, যেখানে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। বিপরীতে, গণতন্ত্র মানুষের তৈরি একটি পদ্ধতি—যেখানে আইন প্রণয়ন ও শাসনের অধিকার জনগণের হাতে।
এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব—খিলাফাহ শাসনব্যবস্থা কী, এর মূল বৈশিষ্ট্য কীভাবে এটি গণতন্ত্রসহ অন্যান্য শাসনব্যবস্থা থেকে পৃথক, এবং কেন ইসলাম অনুযায়ী গণতন্ত্র একটি কুফরী শাসনব্যবস্থা।
গণতন্ত্র কেন একটি কুফরী শাসনব্যবস্থা
গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা (Democracy & Secularism): আধুনিক গণতন্ত্রের উৎস ইউরোপীয় রেনেসাঁ, তারপরে ১৭শ এবং ১৮শ শতকের আমেরিকান-ব্রিটিশ রাজনৈতিক আন্দোলনে নিহিত। এই কাঠামো ধর্ম ও রাজ্যের পৃথকীকরণ (secularism) থেকে উদ্ভূত, যেখানে শাসন ও আইনের উৎস জনগণ ও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব ধর্ম পুরোটাই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, রাষ্ট্র ধর্মীয় সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আইন ও নীতি সম্পূর্ণভাবে মানব তৈরি নিয়মে গঠিত, যা ধর্মীয় বিধির নয় বরং মানব ইচ্ছায় নির্ধারিত।
কিন্তু ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্থান নেই, কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই জীবনের কোনো অংশকে ধর্ম থেকে আলাদা করার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন:
إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
“নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্ম হলো ইসলাম।”
(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯)গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ (Democracy & Nationalism): বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদ বজায় রাখা ও লালন করা হয়। জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিটি জাতি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে, যাকে সীমানা বলা হয়। প্রত্যেক জাতি নিজেদের অন্য জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং এই শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকে তারা অন্য জাতিকে দমন করার চেষ্টা করে। এর ফলস্বরূপ সংঘটিত হয় যুদ্ধ। ফলে গণতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলো পরোক্ষভাবে বিশ্বে ঘৃণা ছড়ায় এবং আধিপত্য বিস্তার করে বেড়ায়। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে।
অন্যদিকে, ইসলামি রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত, কারণ জাতীয়তাবাদ হারাম। রাসূল (সা.) জাতীয়তাবাদ অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং উম্মাহকে তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। জাতীয়তাবাদের বিষয়ে রাসূল (সা.) একটি হাদীসে বলেন:
‘যে ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের আহ্বান জানায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।‘
(- মুসনাদে আহমদ/আবু দাউদ থেকে বর্ণিত হাদীস)- আইন প্রণয়নের উৎস (Source of Law) এবং সার্বভৌমত্বের (sovereignty) ধারণা:
- গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো ‘জনগণের সার্বভৌমত্ব’, যেখানে জনগণই সকল ক্ষমতার আধার ও আইনের উৎস।আধুনিক গণতন্ত্রে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে, অর্থাৎ মানুষই আইন গঠন করে ।
এর বিপরীতে, ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন। তাঁর এ ক্ষমতায় কোনো অংশীদার বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে তিনিই হচ্ছেন মৌলিক আইনের উৎস এবং সকল ক্ষমতার আধার।আল্লাহ বলেন:
“أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ”
“إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ…”“তোমরা জেনে রাখবে, সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র (সেই) আল্লাহরই, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।” (সূরা আরাফ ৭:৫৪)”
গণতন্ত্রে জনগণই আইনি অধিকারে অংশ রাখে, যা ইসলামি দৃষ্টিতে “সুবৎ শরীক” ধরা হয়, কেননা শুধু আল্লাহরই আইন প্রণয়নের অধিকার আছে।
ইসলামে আইন প্রণয়নের অধিকার কেবল আল্লাহর। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন:
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ
“যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের আলোকে বিচার করে না, তারা কাফের।” (সূরা মায়েদা: ৪৪)إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
“নিশ্চয় আইন প্রণয়নের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ব্যতীত আর কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। [সূরা ইউসুফ: ৪০]
গণতন্ত্র এই মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে মানুষ নিজেই আইন তৈরি করে, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বানায়। এই স্বেচ্ছাচারিতা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।
- সেন্স অফ প্লুরালিজম (Pluralism):
এটি হলো এমন এক মানসিকতা যেখানে সমাজে বিভিন্ন মতাদর্শ, ধর্ম, রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এক সঙ্গে টিকে থাকতে পারে এবং আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে। এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্ব পূর্ণ উপাদান। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বহুত্ববাদের চেতনা (sense of pluralism) বজায় রাখা হচ্ছে না; বরং বিশ্ব গণতন্ত্রে ইসলাম, মুসলিম এবং তাদের আদর্শিক মানসিকতার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন দেশে হিজাব নিষিদ্ধ করা, মুসলিমদের ধর্মীয় কারণে নির্যাতন করা, রাসূল (সা.)-এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি।
এখন প্রশ্ন হল এটি (সেন্স অফ প্লুরালিজম) কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক?
এখানে দুই দিক থেকে দেখা যায়:
- ইসলামে ভিন্ন মতের অস্তিত্ব:
ইসলাম মুসলিম সমাজে আলাদা মত, মাজহাব এবং এমনকি অমুসলিমদের ও (যেমন আহলে কিতাব) নিরাপদে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে—
لَاإِكْرَاهَفِيالدِّينِ
“দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।” (সূরাবাকারা: ২৫৬)অতএব, মানুষের নিজস্ব ধর্ম ও মত অনুসরণ করার স্বাধীনতা ইসলামে স্বীকৃত।
- কিন্তু ইসলামে সীমারেখা আছে:
ইসলামী রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্ম বা মতের অস্তিত্ব সহ্য করা হয়, কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিধান অস্বীকার বা ইসলাম বিরোধী আইন চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়না। অর্থাৎ, ইসলামে অসীম স্বাধীনতা বা ধর্মনিরপেক্ষ প্লুরালিজম (Pluralism) নেই।
সুতরাং গণতান্ত্রিক প্লুরালিজম (সেটি এখন প্রশ্নবিদ্ধ ) যেখানে সব মতবাদকে সমানভাবে সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, সেটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু অমুসলিমদের নিরাপদে বসবাস, নিজ ধর্ম পালন ও ন্যায্য অধিকার দেওয়া—এ অংশ ইসলামে স্বীকৃত।
নিম্নে কিছু বাস্তব উদাহরনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও ইসলামের সংঘর্ষিকতাকে তুলে ধরা হলো:
১. সমকামীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার সংরক্ষণ
গণতন্ত্রে: LGBTQ+ সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা, তাদের বিয়ে, দত্তক নেওয়ার অধিকার এবং এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের কোটা বা প্রতীক স্থাপন এখন অনেক দেশে বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে।
ইসলামে: সমকামীতা (লাওতী আমল) স্পষ্টত হারাম এবং নূহ (আ.) এর জাতি এ কাজের কারণে ধ্বংস হয়েছিল।
আল্লাহ বলেন:
أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
“তোমরা কি পুরুষের কাছে কামনা পূরণ করো নারীদের ছেড়ে?“ (সূরা আশ-শু‘আরা: ১৬৫-১৬৬)২. সুদ (ব্যাংকিং ব্যবস্থা)
গণতন্ত্রে: আধুনিক রাষ্ট্রগুলোতে সুদ (interest) ভিত্তিক ব্যাংকিং বৈধ এবং এটি একটি রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতি। সুদের হার নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, এবং এর ভিত্তিতে ঋণ ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা চলে।
ইসলামে: সুদ (রিবা) কুরআন ও সুন্নাহতে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।
আল্লাহ বলেন:
يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
“আর আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং সদকাকে বৃদ্ধি দেন।“ [সূরা আল-বাকারা: ২৭৬]আল্লাহ বলেন:
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ
“যদি তোমরা তা (সুদ) না ছাড়ো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।” (সূরা আল-বাকারা: ২৭৯)৩. অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফি
গণতন্ত্রে: বাকস্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে পর্নোগ্রাফি, নগ্নতা ও অশ্লীলতা প্রকাশকে ‘মতপ্রকাশের অধিকার’ হিসেবে বিবেচনা করে বৈধতা দেওয়া হয়। অনেক দেশেই এগুলোর জন্য বৈধ ও নিয়ন্ত্রিত ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে।
ইসলামে: পর্দা লঙ্ঘন, অশ্লীলতা, ও জিনা সংক্রান্ত যেকোনো কিছু কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
আল্লাহ বলেন:
وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
“তোমরা নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন।“ [সূরা আল-আন’আম: ১৫১]৪. ধর্মত্যাগ বা ধর্ম পরিবর্তনের স্বাধীনতা
গণতন্ত্রে: অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্ম পরিবর্তন, এমনকি ইসলাম ত্যাগ করাকেও “ব্যক্তিগত অধিকার” বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কেউ ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে সেটি আইনত বৈধ এবং শাস্তিযোগ্য নয়।
ইসলামে: ইসলাম পরিত্যাগ (রিদ্দা) মারাত্মক অপরাধ। শরীয়াহ অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ত্যাগকারীকে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে (যদি সে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয় বা বিদ্রোহ করে)।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:
‘مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
“যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো।” (সহীহ বুখারী: ৩০১৭)৫. অশ্লীল নারীদের “মডেল” বা “বডি পারেড” আইনি স্বীকৃতি
গণতন্ত্রে: অনেক দেশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অর্ধনগ্ন ফ্যাশন শো, বিউটি কনটেস্ট, এবং খোলামেলা পোশাককে আইনি অধিকার ও শিল্পের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
ইসলামে: নারীদের খোলামেলা পোশাক, বেপর্দা চলাফেরা এবং তাদের দেহকে বাণিজ্যিকভাবে উপস্থাপন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:
صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: … نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ
“দুই ধরনের জাহান্নামী মানুষ আমি (আমার জীবনে)দেখিনি … এমন কিছু নারী থাকবে যারা পোশাক পরিধান করেও নগ্ন থাকবে…” (সহীহ মুসলিম: ২১২৮)৬. মাতৃগর্ভে শিশু হত্যা (Abortion)
গণতন্ত্রে: অনেক দেশে গর্ভপাতকে নারীর “স্বাস্থ্যগত অধিকার” হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক থেকে জন্ম নেওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানদেরও হত্যার অনুমতি দেওয়া হয়।
ইসলামে: গর্ভপাত (নিষেধ না থাকলে) শুধুমাত্র নির্দিষ্ট যৌক্তিক কারণে করা যায় এবং ৪ মাস পর এটা স্পষ্টতই হারাম।
আল্লাহ বলেন:
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
“তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না দারিদ্র্যের আশঙ্কায়…“ (সূরা আল-আন’আম: ১৫১)৭. যৌন স্বাধীনতা (Sexual Freedom)
গণতন্ত্রে: প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে যেকোনো ধরনের যৌন সম্পর্ক, এমনকি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কও আইনত বৈধ (যদি তা জোরপূর্বক না হয়)। “Live-in relationship”, casual dating ইত্যাদি সামাজিকভাবে স্বীকৃত।
ইসলামে: বিবাহ ছাড়া যেকোনো ধরনের যৌন সম্পর্ক জিনা হিসেবে পরিগণিত এবং শরীয়াহ অনুযায়ী তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত।
আল্লাহ বলেন:
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
“আর জিনার কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।” (সূরা আল-ইসরা: ৩২)৮. ইসলাম ও নবীকে অবমাননা “মতপ্রকাশের অধিকার” বলে মনে করা
গণতন্ত্রে: অনেক দেশে নবী মুহাম্মদ ﷺ, কুরআন ও ইসলামী চিহ্ন অবমাননা করাকেও মতপ্রকাশের অধিকার বলে মনে করা হয় এবং সেসব আইনত দণ্ডনীয় নয়।
ইসলামে: নবী অবমাননার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সাহাবাগণ এমন দৃষ্টান্ত রেখেছেন।
আল্লাহ বলেন:
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনা রয়েছে।“
(সূরা আহযাব: ৫৭)১০. শরীয়া আইনকে “Radical” বা “সন্ত্রাসী” ঘোষণা করা
গণতন্ত্রে: অনেক দেশে শরীয়া আইনের প্রচার, বিশেষ করে শরীয়াহ অনুযায়ী শাস্তির কথা বলা (যেমন: চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীর শাস্তি) সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থা (extremism) হিসেবে গণ্য করা হয়।
ইসলামে: এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত বিধান, যা মানবজাতির শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রণীত।
আল্লাহ বলেন:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
“চোর, পুরুষ ও চোর, নারী—তাদের হাত কেটে দাও; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি…“
(সূরা আল-মায়িদা: ৩৮)১১. নারীদের “পুরুষের সমতুল্য” ঘোষণা করে সমস্ত যৌন পার্থক্য বিলোপ
গণতন্ত্রে: “Gender equality” এর নামে অনেক দেশে নারীদেরকে জোরপূর্বক পুরুষের মতো সব কাজ করতে বাধ্য করা হয়, এমনকি পুরুষদের সেনাবাহিনীতে, খনি বা যুদ্ধক্ষেত্রেও পাঠানো হয়।
ইসলামে: নারী ও পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকাকে সম্মান করা হয়। ইসলাম নারীর মর্যাদা রক্ষা করে তার জন্য আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা বিধান দিয়েছে।
আল্লাহ বলেন:
ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ
“পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন…”
(সূরা আন-নিসা: ৩৪)১২. বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানের বৈধতা ও উত্তরাধিকার অধিকার
গণতন্ত্রে: “Illegitimate children” বা বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের আইনি বৈধতা ও উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে। সন্তান পিতা-মাতার বিবাহ ছাড়া জন্ম নিলেও তাকে সমান অধিকার দেওয়া হচ্ছে।
ইসলামে: এ ধরনের সন্তান শরীয়তের দৃষ্টিতে পিতার নাম বা সম্পত্তিতে অধিকার পায় না। সমাজে জিনার দৃষ্টান্ত বন্ধ করতে ইসলাম এ বিধান দিয়েছে।
রাসূল ﷺ বলেন:
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
“শয্যা (বিবাহিত সম্পর্ক) সন্তানের জন্য, আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর (শাস্তি)।” (সহীহ বুখারী: ৬৭৭২)১৩. ‘প্রাইড মান্থ‘ ও LGBTQ+ শিক্ষাকে স্কুলে বাধ্যতামূলক করা
গণতন্ত্রে: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপসহ বহু দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শিশুদের “gender identity”, “same-sex family” বা “drag queen story hour” ইত্যাদি শেখানো হয়। মুসলিম পরিবারের শিশুরাও এসব পাঠে বাধ্য।
ইসলামে: এ ধরনের শিক্ষা বেহায়াপনায় উৎসাহ দেয় এবং শিশুদের ফিতরাহ নষ্ট করে।
রাসূল ﷺ বলেন:
كُلُّ وَلَدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
“প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাহ (প্রাকৃতিক স্বভাব) অনুযায়ী জন্ম নেয়…” (সহীহ মুসলিম: ২৬৫৮)১৪. ধর্মীয় (Islamic) অনুভূতিকে আইনগতভাবে অপরাধ না ধরা
গণতন্ত্রে: যেকোনো ধর্মের উপাস্য, ধর্মীয় প্রতীক বা নবীকে ব্যঙ্গ করে কেউ “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা” দাবি করলে তা অনেক রাষ্ট্রে বৈধ। যেমন: ফ্রান্সে মুহাম্মদ ﷺ এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ।
ইসলামে: এটি স্পষ্ট কুফরি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
আল্লাহ বলেন:
وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَا أُنزِلَ ٱللَّهُ يَسْتَہْزِئُونَ بِہِۦ فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ إِنَّكَ إِذًا مِّثْلُهُمْ
“তারা যখন শুনে যে আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে বসো না…”
(সূরা আন-নিসা: ১৪০)১৫. পর্দাহীনতা ও পোশাকের স্বাধীনতা আইন
গণতন্ত্রে: অনেক দেশে “freedom of dress” বা “bodily autonomy” নামক ধারণার আওতায় নারীরা যেকোনো ধরনের পোশাক পরতে পারে—even নগ্ন হওয়ার স্বাধীনতা দাবি করে। অনেক দেশে হিজাব নিষিদ্ধও করা হয়েছে (যেমন: ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি)।
ইসলামে: নারীদের জন্য নির্ধারিত পোশাকের নিয়ম রয়েছে। পর্দা করা ফরজ এবং বেহায়াপনা হারাম।
আল্লাহ বলেন:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ…
“হে নবী! মুমিন নারীদের বলো যেন তারা তাদের জামার ওপর অতিরিক্ত চাদর (জিলবাব) পরিধান করে…” (সূরা আহযাব: ৫৯)১৬. পতিতাবৃত্তি (Prostitution) বৈধতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ
গণতন্ত্রে: নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, থাইল্যান্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশে যৌনকর্ম (sex work) আইনি ও করযোগ্য পেশা হিসেবে বিবেচিত।বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম দেশেও আইন দ্বারা যৌনকর্ম বৈধ করা হয়েছে এবং সম্প্রতি সরকার ঘোষণা করেছে যে যৌনকর্মীদের সাধারণ শ্রমিকের মতোই ‘শ্রমিক’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।
ইসলামে: এটি জঘন্য হারাম। পতিতাবৃত্তির ব্যবসা করা, পরিচালনা করা কিংবা অনুমোদন দেওয়া সবই কবিরা গুনাহ।
আল্লাহ বলেন:
وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَزْكِيَّهَاۥ وَٱلَّٰهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۭا
“আর তোমরা তোমাদের দাসীদের পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করো না, যদি তারা পবিত্র থাকতে চায়…”
(সূরা নূর: ৩৩)১৭. কুকুর ও শূকরের মাংস খাওয়ার আইনগত বৈধতা
গণতন্ত্রে: পশ্চিমা অনেক দেশে কুকুর, শূকর বা যেকোনো প্রাণীর মাংস খাওয়া বৈধ এবং তা বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় করা হয়।
ইসলামে: শূকর ও মৃত পশুর মাংস হারাম। কুকুর ও অপবিত্র বলে বিবেচিত।
আল্লাহ বলেন:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ …
“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস…” (সূরা আল-মায়িদা: ৩)১৮. পিতৃ-মাতৃ পরিচয় নির্ধারণে “মায়ের নাম” কিংবা “নিরপেক্ষ পরিচয়” ব্যবহারের প্রচলন
গণতন্ত্রে: কিছু রাষ্ট্রে (যেমন: সুইডেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া) শিশুদের শুধু “guardian” হিসেবে মা বা অন্য কেউ নির্বাচন করতে পারে, এবং সন্তানের “father” পরিচয় আইনি ভিত্তিতে প্রয়োজন হয় না।
ইসলামে: সন্তান পিতার নামেই পরিচিত হবে; মিথ্যা পরিচয় কিয়ামতের দিনে গোনাহর কারণ হবে।
রাসূল ﷺ বলেন:
عَرَّفُوا أَنفُسَكُمْ بِأَبَوَاتِكُمْ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِأَنْ يَعْرِفَكُمْ اللَّهُ
“তোমরা নিজেদেরকে নিজেদের পিতার নামে পরিচিত করো, কেননা এটি আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত।” (সহীহ বুখারী: ৩৫১০)১৯. সমকামিতাকে উৎসাহ দেওয়া ও ‘গর্ভধারণে সক্ষম পুরুষ’ তত্ত্ব
গণতন্ত্রে: পশ্চিমা অনেক দেশে এমন শিক্ষা চালু হয়েছে যে, পুরুষ ও সন্তান ধারণ করতে পারে (যদি সে নিজেকে নারী হিসেবে দাবি করে)। এছাড়া “pregnant man emoji” ও “trans men birthing” কে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।
ইসলামে: এগুলো ফিতরাহ বিরোধী এবং জাহিলিয়াত যুগের চেয়েও নিচু স্তরের কুফরি।
রাসূল ﷺ বলেন:
مَنْ جَامَعَ ذَكَرًا فِي نَفْسِ الذَّكَرِ نَزَلَ عَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ
“পুরুষরা যখন পুরুষের সঙ্গে এবং নারীরা নারীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম করে, তখন আল্লাহর গজব নেমে আসে।” — (মুসনাদে আহমদ)২০. ইসলাম বিদ্বেষমূলক কার্টুন বা চিত্র প্রদর্শনের স্বাধীনতা (Blasphemy Laws Exemption)
গণতন্ত্রে: ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফ্রান্স ও সুইডেনে ইসলামবিদ্বেষী ব্যঙ্গচিত্র আঁকা “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা” হিসেবে বৈধ। এমনকি এই কার্টুনগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।
ইসলামে: এটি মহানবী ﷺ এর অবমাননা এবং স্পষ্ট কুফরি। মুসলিমদের জন্য তা সহ্য করা বা এই ব্যাপারে উদাসীন থাকা হারাম।
আল্লাহ বলেন:
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর লা’নত আছে।” (সূরা আহযাব: ৫৭)নির্বাচন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র নামে মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত করা:
আজকের মুসলিম সমাজে গণতন্ত্রকে ইসলামের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। ভোট, নির্বাচন, গণমত—এইসব শব্দকে ইসলামী মূল্যবোধ বলে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। নির্বাচন ব্যবস্থা নিজে গণতন্ত্র নয়; বরং এটি গণতন্ত্রে পৌঁছানোর একটি মাধ্যম মাত্র। যে কোনো শাসন ব্যবস্থাই তাদের নেতা বা শাসক বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। গণতন্ত্র, সাম্যবাদ এমনকি ইসলামী শাসন ব্যবস্থাতে ও নির্বাচন একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই ‘নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র’—এমন বলা চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক। বাস্তবে, গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা মানুষকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরি আইনের অধীনে পরিচালিত করে। এটি কেবল অজ্ঞতা নয়, বরং এক বিপজ্জনক বিপথগামিতা।
পরিশেষে একথা বলা যায় যে, গণতন্ত্র একটি কুফরী শাসনব্যবস্থা। এটি এ কারণে নয় যে, এটি মানুষকে শাসক নির্বাচনের ক্ষমতা দেয়। কারণ এটি প্রকৃত অর্থে মূল আলোচ্য বিষয়ও নয়। বরং, এটি এ কারণে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হলো মানুষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, স্বাধীনতা (Freedom) এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব।
খিলাফাহ একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা
খিলাফাহ: সংজ্ঞা ও ভিত্তি
খিলাফাহ বলতে বোঝায় একটি ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যার নেতৃত্ব দেয় একজন খলীফা। এই খলীফা নিযুক্ত হন মুসলিম উম্মাহর বাই‘আত বা আনুগত্যের মাধ্যমে। খলীফা নিজে আইনপ্রণেতা নন; বরং তিনি আল্লাহর আইন—কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস—অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করেন।
আল্লাহ তা’আলা রাসূল (সা.)-কে মানুষের মাঝে তাঁর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন:
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ…
“অতএব, তাদের মধ্যে বিচার করো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না, যা তোমার কাছে সত্য এসেছে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে…” [সূরা মায়েদাহ: ৪৮]। “আর তাদের মধ্যে বিচার করো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না, আর তাদের থেকে সতর্ক থাকো যেন তারা তোমাকে আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো কিছু থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।” [সূরা মায়েদাহ: ৪৯]।
“যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের আলোকে বিচার করে না, তারা কাফের।” (সূরা মায়েদা: ৪৪)
এই নির্দেশগুলো উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য, যা শরিয়া বাস্তবায়নের জন্য খলিফার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে, কারণ শরিয়া বাস্তবায়ন একজন ক্ষমতাসীন শাসক ছাড়া সম্ভব নয়।
(من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)
“যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যায়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে”আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
“যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার জন্য কোনো যুক্তি থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যায়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে।” [সহীহ মুসলিম ১৮৫১, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৬৭৪, সহীহাহ ৯৮৪, সহীহ আল জামি’ ৬২২৯]।
এই হাদিসটি মুসলিম উম্মাহর জন্য একজন স্বীকৃত ইমাম বা খলিফার বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) এর আবশ্যকতা নির্দেশ করে। জাহিলিয়াতের মৃত্যু বলতে ইসলামী নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় মৃত্যুকে বোঝায়, যা অত্যন্ত গুরুতর। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, মুসলিমদের জন্য একটি সুসংগঠিত ও স্বীকৃত নেতৃত্বের অধীনে থাকা অপরিহার্য, যা তাদের বিশৃঙ্খলা ও অনৈসলামিক জীবনযাত্রা থেকে রক্ষা করে । বাইয়াত ছাড়া মৃত্যুবরণকে জাহিলিয়াতের মৃত্যুর সাথে তুলনা করা একটি গুরুতর সতর্কবাণী। জাহিলিয়াত হলো বিশৃঙ্খলা, আইনহীনতা এবং ঐশী নির্দেশনার অনুপস্থিতির একটি অবস্থা। যদি বাইয়াত ছাড়া মৃত্যুবরণ এই অবস্থার সমতুল্য হয়, তবে এর অর্থ হলো একজন মুসলিমের জন্য ইসলামী অবস্থায়, সঠিক নির্দেশনা ও শৃঙ্খলার অধীনে মৃত্যুবরণ করতে হলে বাইয়াত (এবং যার কাছে বাইয়াত করা হয়, সেই ইমাম/খলিফা) অপরিহার্য। এটি খিলাফতের আবশ্যকতাকে একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার স্তরে উন্নীত করে, যা প্রতিটি মুসলিমের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে।
“ইমাম ঢালস্বরূপ” (إنما الإمام جنة)
আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “ইমাম তো ঢালস্বরূপ, যার পিছনে যুদ্ধ করা হয় এবং যার দ্বারা আত্মরক্ষা করা হয়। যদি তিনি আল্লাহর তাকওয়া অনুযায়ী আদেশ করেন এবং ন্যায়বিচার করেন, তবে এর জন্য তিনি পুরস্কার পাবেন। আর যদি এর বিপরীত করেন, তবে তার উপর এর দায়ভার বর্তাবে।” [সহীহ মুসলিম ১৮৫৯, সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ৪৬৮৭ [১৮৫১], সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ]।
এই হাদিসটি ইমাম বা খলিফার অপরিহার্য ভূমিকা তুলে ধরে। তিনি মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা এবং শরিয়া বাস্তবায়নের জন্য ঢালস্বরূপ। ঢাল যুদ্ধের সময় সুরক্ষা এবং সংহতি বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। এর অনুপস্থিতি দুর্বলতা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, খিলাফত কেবল একটি কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা নয়, বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য একটি অত্যাবশ্যক, অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান, যা ছাড়া তারা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকার হুমকির মুখে পড়ে। এটি খিলাফতের বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে ধর্মীয় আবশ্যকতায় রূপান্তরিত করে ।
“আমার পরে বহু খলিফা হবে” (وسيكون خلفاء فيكثرون)
আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “বনী ইসরাঈলকে নবীরা শাসন করতেন। যখন একজন নবী মারা যেতেন, আরেকজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আমার পরে কোনো নবী নেই, তবে খলিফা হবে এবং তারা অনেক হবে।” সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দেন?” তিনি বললেন: “প্রথমজনের পর প্রথমজনের বাইয়াত পূর্ণ করবে, তাদের অধিকার দেবে। কেননা আল্লাহ তাদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।” [সহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, অধ্যায়: বনী ইসরাঈল, হাদিস ৩২৬৮]।
এই হাদিসটি রাসূল (সা.)-এর পরে খিলাফতের ধারাবাহিকতা এবং বহু খলিফার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে খিলাফত একটি চলমান প্রতিষ্ঠান যা খোলাফায়ে রাশেদীনের পরেও টিকে থাকবে। “বহু খলিফা হবে” এবং “প্রথমজনের পর প্রথমজনের বাইয়াত পূর্ণ করবে” এই নির্দেশনাবলী নেতৃত্বের একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলার ধারণাটিকে আরও শক্তিশালী করে। এটি এই ধারণাকে খণ্ডন করে যে খিলাফত একটি অস্থায়ী ঘটনা ছিল যা কেবল প্রাথমিক ইসলামী সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি উম্মাহর মধ্যে নেতৃত্বের একটি চিরন্তন প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে, এমনকি যদি সেই শাসনের প্রকৃতি নবুয়তি পদ্ধতির মতো আদর্শ নাও হয়।
কোনটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা?
উপরের দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, খিলাফাহ একটি শাসন ব্যবস্থা হিসেবে কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এটি কেবল আদর্শ শাসন ব্যবস্থাই নয়, বরং প্রতিটি মুসলিমের জন্য খিলাফাহর অধীনে জীবন যাপন করা ফরজ বা আবশ্যিক।
খিলাফাহ এমন একটি শাসনব্যবস্থা যা কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, অমুসলিমদের জন্যও ন্যায়, নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। অপরদিকে, গণতন্ত্র অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ করে। তদুপরি, এর ভিত্তিই মানুষের ইচ্ছা—যা পরিবর্তনশীল, সীমাহীন এবং কখনো কখনো চরম অবিচারপ্রবণ।
সিদ্ধান্ত:
গণতন্ত্র মানুষকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়, ফলে মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও খেয়াল-খুশির ভিত্তিতে বহু আইন শরীয়াহর বিরুদ্ধে গঠিত হয়।গণতন্ত্র একটি কুফরী ভিত্তিক, মানবসৃষ্ট ও পরিবর্তনশীল শাসনব্যবস্থা যা শরীয়াহর মৌলিক ধারণার বিপরীত।
বিপরীতে, খিলাফাহ শাসনব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর বিধানকে চূড়ান্ত আইন হিসেবে গ্রহণ করে, যা মানুষ ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করে।খিলাফাহ একটি স্বতন্ত্র, আল্লাহ-নির্ধারিত শাসনব্যবস্থা যা ন্যায়, হেদায়াত এবং মানবকল্যাণের প্রকৃত মানদণ্ড।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٰٔتِهِمْ وَأَجْرَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَكَانَ رَبُّهُمْ غَفُورًا رَّحِيمًا
“যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তাদের জন্য তার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রস্তুত আছে; কারণ তিনি দয়ালু ও করুণাময়।” (সূরা নূর: ৫৫)وَعْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْـًٔا
“আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তাদের প্রতি যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেমন তিনি পূর্ববর্তী জাতিগুলোকেও দান করেছিলেন। তিনি তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করবেন, যা তিনি মুমিনদের জন্য পছন্দ করেছেন, এবং তাদের ভয়কে পরিবর্তে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না।” (সূরা নূর: ৫৬)গণতন্ত্র ইসলামি শরিয়াহ আইনকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে এবং এর অবস্থান ইসলামের বিরুদ্ধে। সুতরাং একজন মুসলিম গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে পারে না; বরং তাদের উচিত শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা।
হে আল্লাহ, আমাদেরকে সত্য বুঝার তৌফিক দান করো এবং ইসলামকে পরিপূর্ন দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবার দৃঢ় ঈমান দান করো, আমীন।
আল্লাহ’র ইচ্ছায় সমাপ্ত
ইসলাম কি আসলেই একটি মৌলবাদ?

১৯ শতকের শেষের দিকে সর্বপ্রথম ইউরোপে “মৌলবাদ” শব্দটির আবির্ভাব ঘটে। এটি তখন সাধারণত নব বিজ্ঞান ও দর্শনের বিরুদ্ধে চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি এবং খৃষ্টান বিশ্বাসের প্রতি গোঁড়া আনুগত্যকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো।
প্রোটেস্টেন্ট আন্দোলনকে মৌলবাদের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই মতবাদের মৌলিক নীতিমালা ১৮৭৮ সালের নায়াগ্রা কনফারেন্স এবং ১৯১০ সালে অনুষ্ঠিত জেনারেল প্রিসবিটারিয়ান সম্মেলনে চূড়ান্ত করা হয়। তারা এমন কিছু খ্রিস্ট-মতাদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের নীতি নির্ধারণ করে, যেগুলো সুস্পষ্টত জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদীদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার পথে অন্তরায় ছিল।
যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মতবাদ বিলীন হয়ে যায়, তথাপি ইউরোপীয়দের বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে উন্নতি এবং অগ্রযাত্রার পথে মৌলবাদ অন্যতম বাধা। এটিকে বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপদতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা নবজাগরণের যুগে বেমানান। এবং তারা ব্রত করে নেয় যে, এর প্রভাব সমাজ ও ব্যক্তি জীবন থেকে দূর করতে শক্তভাবে লড়াই করতে হবে।
খ্রিস্ট ধর্মকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে বিজ্ঞান ও শৈল্পিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই মতবাদ আবির্ভূত হয়। পুঁজিবাদ এবং ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা করার এই নব জীবনধারার সাথে খ্রিস্ট ধর্মের সমন্বয়হীনতা দূর করতে এই মতবাদ সামনে আসে। এটি খ্রিস্ট ধর্ম অনুসারীদের বস্তুগত উন্নতি এবং পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই মৌলবাদ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধান দিতে না পারায় এটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো এবং খ্রিস্টানদের কাছে অগ্রহণযোগ্য কিছু নীতিমালা তৈরি করার কারণে এই আন্দোলন সফলতার মুখ দেখেনি।
ইয়াহুদি ও খৃষ্টানদের আন্দোলনকে মৌলবাদ বলার মূল ক্রীড়নক হচ্ছে পশ্চিমারা। পুঁজিবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে সাধিত প্রযুক্তিগত, শৈল্পিক এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন অগ্রগতিকে প্রশ্ন করলেই এটিকে ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
তাই তো দেখা যায়, বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলন এবং মুসলমানদের সংশ্লিষ্ট কোনো সংগঠনকে পশ্চিমা রাষ্ট্র-চিন্তক, রাজনীতিবিদ আর তাদের পদলেহনকারী কিছু নামধারী মুসলমানেরা মৌলবাদের ধোঁয়া তুলে তাদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জনমত গড়ে তোলে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে মৌলবাদ মানে পশ্চাৎপদতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ করা। আর এটি বিজ্ঞান ও শৈল্পিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়।
কোনো নির্দিষ্ট দল বা আন্দোলনকে সেরেফ মৌলবাদী আখ্যা দেওয়াই এটিকে আধুনিক বস্তুবাদী সমাজ আর মানুষের সামনে ভয়ংকরভাবে উপস্থাপন করার জন্য যথেষ্ট। মিসর কিংবা আলজেরিয়ার মতো রাষ্ট্র যদি কোনো মুসলমানকে মৌলবাদী আখ্যা দিয়ে হত্যা করে, তখন পশ্চিমা সুশীল সমাজ এটিকে স্বাগত জানায় এবং নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করে। তখন কোনো মানবাধিকার সংগঠন এই মৃত্যুদণ্ড নিয়ে কথা বলে না। কারণ নিহত ব্যক্তি তাদের ভাষায় মৌলবাদী। সবাই তাদেরকে মানবতার শত্রু হিসেবে ঘৃণার নজরে দেখে। বিশেষ করে যখন তাদের বিরুদ্ধে খুবই জঘন্য অভিযোগ আরোপ করা হয়। যেমন: আলজেরিয়ার নিরীহ মানুষ হত্যা এবং মিসরে পর্যটক হত্যার জন্য তারা দায়ী।
ইসলামের খিলাফত ও শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের বর্তমান দুর্বিষহ জীবনকে ইসলামী জীবনে পরিবর্তন করতে যারা কাজ করে, এমন প্রতিটি আন্দোলন ও দলকে মৌলবাদী আখ্যা দিয়ে মৌলবাদ শব্দটিকে বর্তমানে এর মূল টার্ম থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে।
ইয়াহুদি, সার্বিয়ান, আমেরিকা এবং অন্যান্য নিপীড়ক ও মুসলমানদের ভূমি অন্যায়ভাবে দখলকারীদের বিরুদ্ধে চলমান সকল আন্দোলনকেও এভাবে মৌলবাদী আখ্যা দিয়ে দমনের চেষ্টা করা হয়। তাদের ভাষায় মুসলিম যোদ্ধা, যারা নিজেদের ভূমি দখলকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তারা মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসী। বিদেশি দখলবাজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়ে যারা শাহাদাত বরণ করেছে, তাদের ভাষায় তারাও আত্মঘাতী ও সন্ত্রাসী। প্রত্যেক মুসলমান এবং অন্যায় ও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী প্রতিটি দলের জন্য এই ট্যাগ বিপজ্জনক।
ইসলামি জীবনবিধান পুনরুদ্ধারের জন্য শরিয়ার নিরিখে কাজ করে এমন প্রতিটি দলের জন্য বিষয়টি উদ্বেগজনক। এই বয়ান দাঁড় করিয়ে মৌলবাদী তকমা ব্যবহার করে তারা পুঁজিবাদী রেনেসাঁর যুগে শিল্প ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান মৌলবাদীদের মতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য বৈধ ন্যায্যতা তৈরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইসলামি বিভিন্ন আন্দোলনকে এই মৌলবাদ ট্যাগ দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, পশ্চিমা সমাজে এই টার্মটির ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। মৌলবাদ শব্দটির কারণে পশ্চিমা লোকেরা জীবনবিধান হিসেবে রাজনৈতিক ইসলামকে রুখে দিতে তাদের শাসকের পক্ষে এসে দাঁড়াবে।
কোনো মুসলমানের এমনটি ভাবা উচিত নয় যে, দ্বীনের মূল ভিত্তি অথবা ফিকহি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত থাকার কারণে ইসলামি আন্দোলনকে মৌলবাদ আখ্যা দেওয়া হয়। ইসলামি আকীদার মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তা’আলা, ফেরেশতা, ঐশী গ্রন্থসমূহ, নবী-রাসুলগণ, বিচার দিবস এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। বিভিন্ন ফিকহি নীতিমালার মৌলিক বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন দলিল ও প্রমাণ, যেগুলোর ওপর গবেষণা করে মুজতাহিদ (স্কলার) আলেমগণ ব্যবহারিক শর’ঈ আইন প্রণয়ন করেছেন।
পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে মৌলবাদ প্রোটেস্টেন্ট খৃষ্টান সমাজ কর্তৃক পরিচালিত একটি আন্দোলন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে ওঠেছে, ইসলামি মূল্যবোধ বা ইসলামি আন্দোলনের সাথে এর সমসাময়িক কিংবা ঐতিহাসিক কোনো সম্পৃক্ততা নেই।
ইসলামের ইতিহাসে রাজনৈতিক আন্দোলন, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আইনি বিভিন্ন স্কুল অব থট সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো কোনোভাবেই খৃষ্টানদের মৌলবাদ মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমনকি হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে ‘ইজতিহাদ’ (শর’ঈ কোনো মাসআলা নিয়ে গবেষণা করা) এর রাস্তা এই জন্য বন্ধ করা হয়নি যে, উলামায়ে কিরাম পুরোনো নীতিমালাকে আঁকড়ে ধরতে চায় আর নতুন নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করতে চায়। বরং তারা ধরে নিয়েছিলেন যে, ইসলামি ফিক্বহ নিয়ে যত সমস্যা আছে, সব সালাফদের মাধ্যমে সমাধা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এখানে নতুন কোনো গবেষণার আর প্রয়োজন নেই।
ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে এই ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম যে, এটিই চূড়ান্ত ধর্ম এবং এর পূর্বে আগত সকল ধর্মকে রহিতকারী। আল্লাহ তা’আলা এটিকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-
إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهَ لَحَفِظُوْنَ
নিশ্চয় আমি কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর হিফাজত করব। [সুরা হিজর, আয়াত ৯]
এটি মানুষের মনস্তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত মতবাদ। যেখান থেকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আগত মানুষের যাবতীয় বিষয়ের সমাধানে একটি বিস্তৃত ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এটি একটি অকল্পনীয় বিষয় যে, এই আদর্শ মানুষের কোনো সমস্যার সমাধান প্রদান করতে পারবে না। এটি বরং সকল সমস্যার সমাধান প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি, যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। [সুরা নাহল, আয়াত ৮৯]
অতীতে মুসলিম বিশ্ব যে বৈজ্ঞানিক এবং শৈল্পিক উন্নতির মধ্য দিয়ে গিয়েছে, এটি ছিল ইসলামের ব্যাপক ভূমিকার ফল। জীবন থেকে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করে এটি সম্ভব হতো না। আজকের যুগেও মানুষ বিজ্ঞান ও শিল্পের যে উৎকর্ষতা দেখতে পাচ্ছে, এর পেছনে পূর্বেকার সেসব মুসলিম বিজ্ঞানীদের থিওরি এবং নীতিশাস্ত্রের অনেক প্রভাব রয়েছে, যারা ইসলামি জীবনধারা এবং ইসলামি রাষ্ট্রের ছায়ায় বসবাস করে এসব কাজ করেছেন।
তাই খৃষ্টানদের আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্য টেনে বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনকে মৌলবাদ আখ্যা দেওয়া চরম ভুল এবং পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা। এটি ইসলাম কিংবা যারা ইসলামকে প্রাণবন্ত করে তুলতে কাজ করে, তাদের প্রকৃত বাস্তবতা নয়। কারণ তারা শুধু মানবসৃষ্ট সিস্টেমের দুঃশাসনের কারণে মুসলমানদের জীবনে আগত এই দুর্বিষহ অবস্থা দূর করতে চায়। যেটি সুস্পষ্টত খৃষ্টান মৌলবাদের বিপরীত। তারা মূলত পুঁজিবাদের উত্থানের পূর্বে যে ভোগবাদী জীবন নিয়ে মেতেছিল, সেটি আবার ফেরত পেতে চাচ্ছিল।
সুতরাং বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনকে পশ্চিমা সমাজ কর্তৃক মৌলবাদ আখ্যা দেওয়া স্পষ্টতই এই বিষয়টি নির্দেশ করে যে, তারা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের প্রত্যাবর্তনের বিপক্ষে পরোক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।
এটি পশ্চিমাদের জন্য একটি কৌশলগত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তারা তৃতীয় বিশ্ব-বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে যে কোনো ধরনের সত্যিকার রেনেসাঁ থেকে পেছনে এবং দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। এটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা রুখে দেওয়ার অপচেষ্টা। কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, খিলাফাহ তাদের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উপড়ে ফেলবে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর লোভের ইতি ঘটাবে।
তাদেরই একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য শুনুন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য স্টাডিজের ভিজিটিং স্কলার। তিনি মার্কিন কংগ্রেসে একটি রিপোর্ট জমা দেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, ‘মৌলবাদীরা মনে করে, শরীয়া আইন অবশ্যই পূর্ণাঙ্গভাবে প্রয়োগ করা উচিত এবং আল্লাহ তা’আলার আদেশ-নিষেধ অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে হবে। আর এই নীতিমালা সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইসলাম তাদের চালিকাশক্তির প্রাথমিক উৎস। আর শরিয়া আইন পূর্বেও যেভাবে প্রয়োগ উপযোগী ছিল, আজও এর উপযোগিতা রয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘মৌলবাদীরা পশ্চিমা সভ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণার নজরে দেখে। ইসলামি আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা পশ্চিমা সভ্যতাকে পথের কাটা মনে করে।’
আমেরিকান স্কলার জন এসপজিটো মার্কিন কংগ্রেসে জমা দেওয়া রিপোর্টে উল্লেখ করেন, ‘মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠী আমেরিকার স্বার্থের জন্য মারাত্মক হুমকি।’
সুতরাং কাফিররা মূলত মৌলবাদের নামে জীবনে ইসলামের আইন পুনঃপ্রয়োগের আন্দোলনকে আক্রমণ করছে। এটা যদি মৌলবাদ হয়, তাহলে তাদের দৃষ্টিতে সকল মুসলমান মৌলবাদী। কারণ সকল মুসলমান অধীর আগ্রহ ও উৎফুল্লতার সাথে খিলাফতের ছায়ায় ইসলামের সকল বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা, এই বিশ্বকে পুঁজিবাদের থাবা থেকে মুক্ত করা এবং সবাইকে ইসলামের গৌরবান্বিত সোনালি যুগে ফিরিয়ে নিতে অপেক্ষা করছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন-
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ * يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ
যে ইসলামের আহ্বান পেয়েছে, তারপরও সে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। তারা ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নুর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নুর পরিপূর্ণ উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। [সুরা সফ, আয়াত ৭-৮]
Taken from the book “Dangerous Concepts”
Translated by “Sabah Publication”অনুন্নত দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, মেধা পাচার ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা

খবর:
বিএসসি প্রকৌশলীদের প্রতি বৈষম্য নিরসনের তিন দফা দাবিতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন চুয়েট, চবি, আইআইইউসি সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শনিবার (৫ জুলাই) বিকাল ৪টায় নগরীর ২ নং গেইট এলাকায় তারা এই প্রতিবাদ সমাবেশ পালন করেন।
এ সময় বিক্ষোভ মিছিলে হাজারো শিক্ষার্থীদের ‘আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই’; ‘কোটা না মেধা, মেধা, মেধা’; ‘কোটার নামে বৈষম্য, চলবে না, চলবে না’; ‘এই মুহূর্তে দরকার, কোটাপ্রথার সংস্কার’ প্রভৃতি স্লোগান দিতে দেখা যায়।
২ নং গেইট থেকে শুরু হয়ে জিইসি মোড় ঘুরে আবার উৎপত্তিস্থলে ফেরত আসে মিছিলটি। এরপর অনুষ্ঠিত সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দাবিতে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। এ সময় তারা তাদের পূর্বে উত্থাপিত তিন দফা দাবি তুলে ধরেন— প্রকৌশল নবম গ্রেডে সহকারী প্রকৌশলী বা সমমান পদে প্রবেশের জন্য সবাইকে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া এবং বিএসসি ডিগ্রিধারী হওয়া, কারিগরি দশম গ্রেডে উপ-সহকারী প্রকৌশলী বা সমমান পদ সবার জন্য উন্মুক্ত করা এবং বিএসসি ডিগ্রীধারী ব্যতীত অন্য কেউ ‘প্রকৌশলী’ পদবি ব্যবহার করতে পারবে না মর্মে আইন পাশ করে গেজেট প্রকাশ করা। এই তিন দফা দাবি দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানান শিক্ষার্থীরা।
তাদের মতে, ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কারণে প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারীরা পদোন্নতি ও নিয়োগে ন্যায্যতা থেকে অনেকদিন ধরেই বঞ্চিত হয়ে আসছেন। দীর্ঘ ৪ বছর কঠিন পাঠ্যক্রম, ল্যাব, থিসিস ও প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে পাস করা বিএসসি ডিগ্রিধারী প্রকৌশলীরা চাকরির বাজারে চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। সরকারি চাকরির দশম গ্রেডে একচেটিয়া শতভাগ ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ এবং নবম গ্রেডে পদোন্নতিতে ৩৩.৩ শতাংশ কোটা বরাদ্দ করা আছে ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের জন্য। অধিকন্তু নবম গ্রেডে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোটার ব্যবস্থা ৫০ শতাংশ করার অন্যায্য দাবিও জানিয়ে আসছিলেন তারা।
এ সময় প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন এর যুগ্ম আহ্বায়ক শাকিল আহমাদ ইকবাল বলেন, ‘যেই কোটার জন্য আমাদের গত জুলাইয়ে আন্দোলন করতে হয়েছে, সেই কোটার জন্য এক বছর পর আবার আন্দোলনে নামতে হচ্ছে। ডিপ্লোমারা ১০ম গ্রেড সরাসরি নিজেদের করে নিয়েছে, এখন ৯ম গ্রেডে ৩৩% কোটার নামে অনেক জায়গায় ১০০% প্রমোশন নিয়ে নিচ্ছে। এভাবে কোটার মাধ্যমে কেউ বিশেষ সুবিধা পেতে পারে না।’
এই আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক শাকিবুল হক লিপু বলেন, ‘ডিপ্লোমাদের বিএসসি সার্টিফিকেট নেই। এভাবে প্রকৌশলী না হয়েও তারা প্রকৌশলীদের জন্য বরাদ্দকৃত চাকরির পোস্টসমূহ নিয়ে নিচ্ছে। চার বছর কষ্ট করে, পরিশ্রম করে বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করতে হয়। এরপর এমন বৈষম্য মেনে নেয়া যায় না। এভাবে চলতে পারে না। আমরা তাই আমাদের নিজেদের দাবি আদায়ে মাঠে নেমেছি।’
বিক্ষোভকারী চুয়েট শিক্ষার্থী আমিনুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, ‘সমবাহু ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় শিখে এসে ডিপ্লোমারা প্রকৌশলের জন্য বরাদ্দকৃত পদ নিচ্ছে। এদিকে চার বছরে কঠিন কঠিন কোর্স শেষ করে আমরা চাকরিই পাচ্ছি না। আমাদেরকে আবেদন করা থেকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে। বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে সমমর্যাদার পদ বাগিয়ে নিচ্ছে। স্বাধীন বাংলায় এমন বৈষম্য মেনে নেয়া যায় না।’
একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান মোহাব্বত বলেন, ‘পেশিশক্তি ও লবিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ পদোন্নতি পাচ্ছে ডিপ্লোমারা। নিয়ম ভেঙে পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। চরম মাত্রার অনিয়ম চলছে। এগুলোর প্রমাণও রয়েছে। এরকম করেও তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। এমনটা হতে পারে না। সরকারের উচিত দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া। বৈষম্য দূর করা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সমাবেশ হচ্ছে। সবাই প্রকৌশলীই এই দাবির পক্ষে সোচ্চার।’
মন্তব্য:
দেশে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি বৈষম্য যে হচ্ছে, সেটা অবশ্যই সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো,এই বৈষম্য দূর হলেই কি তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান ও মূল্য পাবে? এই রাষ্ট্র কি এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করেছে, যেখানে এই উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়াররা দেশের নিজস্ব ইন্ডাস্ট্রিতে দক্ষতা ও মেধা কাজে লাগাতে পারবে? আসলে, এই দেশে এমন কোনো শক্তিশালী শিল্পখাতই নেই, যেখানে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের নলেজ বা স্কিল প্রপারলি কাজে লাগবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই কাজ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার বা টেকনিশিয়ান দিয়েই চালানো সম্ভব।

বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বের নানা প্রান্তে গিয়েও বিশ্বমানের কাজ করছে গুগল, মাইক্রোসফট, আমাজন, স্পেসএক্স থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা, সফটওয়্যার ডেভেলপাররা, ডাক্তাররা বিশ্বের বাজারে highly valued।
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই সক্ষমতা আমরা নিজের দেশে ব্যবহার করতে পারছি না কেন? এই সক্ষমতাকে কাজে লাগানোর মতো কোনো ভিশন আমাদের রাষ্ট্র দেয় না।
এখানে আসল সমস্যা ডিপ্লোমা বনাম বিএসসি নয়, আসল সমস্যা হচ্ছে এই রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিজেই একটা ভাঙা কাঠামো, যা কোনো বাস্তব ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠেনি।
এই কাঠামোটি গড়ে তোলা হয়েছে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার (Capitalism) শর্ত ও নির্দেশনা অনুযায়ী। পুঁজিবাদ এর প্রধান ধারক-বাহক পশ্চিমা দেশগুলা আমাদের শিক্ষিত, মেধাবী জনগোষ্ঠীকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। তারা আমাদের জন্য উন্নয়নের আশ্বাস দেয়, কিন্তু আসলে এমন একটি কাঠামো তৈরি করে রেখেছে যেখানে আমরা চিরকাল পরনির্ভরশীলই থেকে যাই।
এই সমস্যাগুলোর গোড়ায় আছে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুসৃত দাসসুলভ পলিসি, যা আমাদের শিক্ষা, শিল্প, গবেষণা সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে পশ্চিমা কর্পোরেট ও সংস্থাগুলোর স্বার্থ অনুযায়ী। যেমন বিশ্বব্যাংক, IMF, WTO এরা আমাদের দেশের পলিসিতে এমন সব শর্ত দিয়ে থাকে, যাতে আমরা নিজস্ব শিল্প, প্রযুক্তি বা উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারি। স্থানীয় প্রোডাকশন ও রিসার্চ বন্ধ হয়ে যায়, আর আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা হয় কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের যোগানদাতা। এর ফলে আমাদের দেশ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী বিদেশে পাড়ি জমায় উচ্চশিক্ষা, ভালো চাকরি কিংবা স্থায়ীভাবে বসবাসের আশায়। পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা দেশের জনগনের ট্যাক্স এর টাকায় পড়ে ৭০-৮০% বিদেশি কোম্পানির শ্রমিকে পরিণত হয়।
আমরা যারা এই সিস্টেমের ভুক্তভোগী, তারা নিজেদের মধ্যেই একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে ফেলেছি, বিএসসি বনাম ডিপ্লোমা, পাবলিক বনাম প্রাইভেট, গ্রেড-ভিত্তিক দ্বন্দ্ব। অথচ, এই বিভক্তি তৈরি করেছে সেই সিস্টেম, যারা চায় আমরা বিভক্ত থাকি, যেন মূল শত্রুর দিকে কেউ আঙুল না তোলে।
এই কাঠামো আমাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করে না, বরং আমাদের দারিদ্র্যই টিকিয়ে রাখে, যাতে পশ্চিমা কোম্পানিগুলো সস্তায় পণ্য তৈরি ও মেধা ব্যবহার করতে পারে। এটা শুধু অর্থনৈতিক শোষণ নয়, এটা আদর্শিক, কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক দাসত্ব।
এই বাস্তবতা বদলাতে হলে প্রয়োজন এই পুজিবাদী সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করা। একটা দুইটা আইন পরিবর্তন করলেই হবে না। প্রয়োজন এমন একটি কাঠামো যা আমাদের স্বার্থ, আমাদের মেধা, আমাদের সম্পদকে দেশেই কাজে লাগাবে। প্রয়োজন এমন এক আদর্শিক ব্যবস্থা, যা ন্যায়ভিত্তিক হবে এবং ১৩০০ বছর এই ব্যবস্থা পুরো বিশ্বে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে গেছে। যেখানে ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, শ্রমিক – সবার কাজই ছিল সম্মানিত ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নিবেদিত।
ইসলামই একমাত্র আদর্শ যা প্রকৃত সমাধান দেয়
ইসলাম শুধু একটা ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার মধ্যে আছে রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও জ্ঞানচর্চার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। এই আদর্শব্যবস্থায় মেধা কখনোই অবহেলিত ছিল না। বরং ইসলামি রাষ্ট্র মেধাকে সম্মান দিয়ে কাজে লাগিয়েছে, এবং সেটি শুধু থিওরিতে নয়, বাস্তবে ১৩০০ বছর ধরে বাস্তবায়িত হয়েছে।
কুরআনের নির্দেশনাই ছিল জ্ঞান, গবেষণা ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রের ভিত্তি:
“আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা বহু গুণে উন্নীত করেন।” সূরা আল-মুজাদিলা (৫৮:১১)
“যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?” সূরা আয-যুমার (৩৯:৯)
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সরাসরি জ্ঞানীদের মর্যাদা তুলে ধরেছেন, যা ইসলামি সভ্যতায় গবেষণা, শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- “প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।” [সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪]
মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের ইসলামি রাষ্ট্রে অবদান:
ইবনে সিনা (Avicenna): মেডিক্যাল সায়েন্স ও দর্শনের পথিকৃৎ। খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণা, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রশাসনে যুক্ত ছিলেন।
আল-খোয়ারিজমি: অ্যালজেব্রা ও অ্যালগরিদমের জনক। তার কাজ Bayt al-Hikmah (জ্ঞানাগার)-এ রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছিল।
আল-জাজারি: মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও রোবোটিক্সের প্রবর্তক। পানির মেশিন, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বানিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজে লাগিয়েছেন।
আল-রাযী ও আল-জাবির ইবনে হাইয়ান: রসায়ন ও চিকিৎসায় বিপ্লব এনেছেন। তাদের গবেষণাগার পরিচালিত হতো সরকারি তত্ত্বাবধানে।
আল-বাতানি ও মারিয়া আল-আস্ট্রোলাবি: জ্যোতির্বিদ্যা ও নেভিগেশন টেকনোলজিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নারীদের জন্যও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল খিলাফতের অধীনে।
ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা মেধাকে সংরক্ষণ করত, বিকাশ ঘটাত এবং বাস্তবে কাজে লাগাত – একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের জন্য। আজ যেখানে মেধা পাচার হয়, সেখানে ইসলামি আদর্শ মেধাকে সম্মান দেয়, রক্ষা করে এবং সমাজ-রাষ্ট্রে বাস্তব ভূমিকা রাখতে দেয়।
ইরান সরকারটি কেমন?

ইরানের যেকোনো ইস্যু আসা মাত্রই এক শ্রেণির মানুষ ইরানিদের শিয়া মতবাদ নিয়ে এমনভাবে আলোচনা তোলেন যেন ইরানকে নিয়ে যাবতীয় সমস্যার কারণ তাদের শিয়া মতবাদ। কারো কারো আক্বীদাগত উত্তেজনা এই সময়গুলোতে এতই বৃদ্ধি পায় যে, মনে হয় ইস*রা*য়ে*লই হয়ত আহলে সুন্নাহ ও সুন্নি মাজহাবগুলোর ভ্যানগার্ড হিসেবে ইরানের কুফরী আক্বীদাগুলোকে গুড়িয়ে দিচ্ছে!

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির সকল হিসাব-নিকাশ ছাপিয়ে কেবল শিয়া মতবাদ নিয়ে তারা মেতে থাকে।
তাই ইরানি শাসকদেরকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের আগে এই আক্বীদাগত বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত কিছু সত্য তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি।
বাস্তবতা হলো, শিয়া মতবাদ শুরুতে রাজনৈতিক বিরোধই ছিল। এই রাজনৈতিক বিরোধ পরবর্তীতে বৃহত্তর ফিকহী বিরোধে রূপান্তরিত হয়। গত ১০০ বছরে এই বিরোধটিকে অনেকটা আলাদা সম্প্রদায়গত বিরোধ হিসেবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।
ঐতিহাসিকভাবে সুন্নি স্কলাররা কখনোই শিয়াদেরকে ঢালাওভাবে কাফের বা অমুসলিম বলেননি। বরং সুনির্দিষ্ট আক্বীদাগত ভ্রষ্টতার শিকার ব্যক্তিদের কুফরের ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন, ইমাম আল-গাজ্জালী (রহ.) তাঁর “ফাদায়িহ আল-বাতিনিয়্যাহ” বইতে বলেছেন:
“أما الإمامية الاثنا عشرية فليسوا كفارًا ولا مرتدين، وإنما هم فساق مبتدعون”
অর্থ: “ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া [বর্তমান ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া] কাফের বা মুরতাদ নয়; বরং তারা বিদআতী ফাসিক।”
অর্থাৎ গাজ্জালী (রহ.) ইসনা আশারিয়া [ইরানের এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ] শিয়া বিদআতী আখ্যা দিলেও কুফরির অভিযোগ করেননি, তাদেরকে বিদআতী ও পাপাচারী বলেছেন।
শিয়াদের বিষয়ে অন্যতম কঠোর ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) তাঁর “মাজমু’ আল-ফাতাওয়া”-তে বলেছেন:
“التشيع ليس كفرًا مطلقًا، بل فيه تفصيل: فمن غلا في الأئمة وجعلهم مثل الأنبياء أو فوقهم، أو كفر الصحابة، فهو كافر”
অর্থ: “শিয়াবাদ সর্বদা কুফর নয়; এতে পার্থক্য আছে: যে ইমামদের নবীদের সমকক্ষ বা ঊর্ধ্বে স্থান দেয় অথবা সাহাবাদের কাফের বলে, সেই কাফের।”
ইমাম ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহ.) তাঁর “আস-সাওয়াইক আল-মুহরিকা” তে বলেছেন:
“الرافضة إذا سبّوا الصحابة أو كفّروهم فهم كفار”
অর্থ: “রাফিজি (চরমপন্থী শিয়া) যদি সাহাবাদের গালি দেয় বা কাফের বলে, তাহলে তারা কাফের।”
বর্তমানকালের সুন্নি স্কলার বা প্রতিষ্ঠানগুলোর ফতোয়াও প্রায় একই ধরনের। যেমন, দারুল ইফতা আল-মিসরিয়্যাহ (আল-আজহার)-এর ফতোয়া: “আহলুস সুন্নাহ ওয়া আল-জামা’আহ ইসনা আশারিয়া শিয়াদেরকে ‘কাফের’ বলে না, যতক্ষণ তারা ইসলামের মূল স্তম্ভে বিশ্বাসী।” (ফতোয়া নং ২৩৪১, ২০১২)।
সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি শেখ আবদুল আজিজ বিন বাজ (রহ.) বলেছেন: “কোনো শিয়া যদি সাহাবীগণকে ভালোবাসে ও কুরআন অপরিবর্তিত বলে বিশ্বাস করে, তার সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা জায়েজ।” [মাজমু’ ফাতাওয়া, ২/৩০৪]
ক্লাসিকাল স্কলারগণের ও বর্তমান কালের এসব ফতোয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়:
#কখন_শিয়াকে_“কাফের”_বলা_হয়েছে?
১. কুরআন বিকৃতির বিশ্বাস:
– যে বলে কুরআন অসম্পূর্ণ বা বিকৃত হয়েছে [ইবনে তাইমিয়াহ, দার আল-তা’আরুদ, ১/৩৫৬।]
২. সাহাবিদের (রা.) প্রতি চরম শত্রুতা:
– আবু বকর, উমর (রা.)-কে কাফের বলা বা তাদের প্রতি অভিশাপ দেওয়া [ইবনে তাইমিয়াহ, মিনহাজ আল-সুন্নাহ, ৪/৫৯০]।
৩. ইমামদের অতি ভক্তিবাদ:
– ইমামদের নবুওয়ত বা ইলাহী গুণাবলি দেওয়া [আল-শাহরাস্তানি, আল-মিলাল ওয়া আল-নিহাল, ১/১৯৩]।
#যাদের_“কাফের”_বলা_হয়নি
– সাধারণ ইসনা আশারিয়া শিয়া: যারা সাহাবিদের সমালোচনা করে না বা কুরআন বিকৃতি বিশ্বাস করে না [ইবনে আবিদিন, রাদ্দ আল-মুহতার, ৪/২৬৩]
– জাফরি ফিকহ অনুসারী: যারা শুধু ফিকহি পার্থক্য রাখে [আল-আজহারের ফতোয়া, ১৯৫৯]।
অর্থাৎ বাংলাদেশের ফেসবুক স্কলারদের মতো করে কোনো কালেই সুন্নি স্কলারগণ শিয়াদেরকে ঢালাওভাবে কাফের বলেননি; বরং সুনির্দিষ্ট আক্বীদাগত ভ্রষ্টতা (কুরআন বিকৃতি, সাহাবিদের প্রতি শত্রুতা, ইমামদের অতিমানবীকরণ)-কে কুফরের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ন্যায়সঙ্গত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।
শিয়া আসলে কারা?
ইতোমধ্যে ১ম পর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ক্ল্যাসিকাল সুন্নি স্কলাররা কখনোই শিয়াদেরকে ঢালাওভাবে “কাফের” বলেননি।

শিয়া ও সুন্নি বিভেদের বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এই পোস্টের সীমিত পরিসরে নেই। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে অন্য কোথাও বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইলো ইন’শা’আল্লাহ।
তবে বর্তমান ইসরায়েল ও ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শিয়াদের সম্বন্ধে ন্যূনতম যেটুকু আলোচনা এখন করা খুবই প্রয়োজন, সেটুকুই শুধু এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি।
আরবিতে “শিয়া” শব্দের অর্থ অনুসারী, সমর্থক বা কোনো দলের সদস্য। “শিয়া” শব্দটি এ ধরনের অর্থেই পবিত্র কুরআনে মোট ১১ বার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেছেন:
{وَاِنَّ مِنۡ شِيۡعَتِهٖ لَاِبۡرٰهِيۡمَۘ}
এবং অবশ্যই ইবরাহীম ছিল তারই অন্যতম শিয়া (অনুসারী/দলের লোক)। [আল কুরআন ৩৭:৮৩]
একইভাবে, সূরা আনআম: ৬৫; সূরা সাফফাত : ৮৩; সূরা কাসাস : ১৫ ইত্যাদি আয়াতেও শিয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
তবে পারিভাষিক অর্থে শিয়া শব্দটি “শিয়াতু-আলী” (রা.) অর্থাৎ মহান সাহাবী আলী (রা.)-এর অনুসারী/সমর্থক হিসেবে পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.) বলেছেন,
{مَا جَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا جَاءَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ}
[সূত্র: “مَنَاقِبُ الإِمَام أَحْمَد بن حَنبَل” لابن الجوزي, ص ١٦٣]
অর্থ: “সাহাবীদের মধ্যে কারও সম্পর্কে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ন্যায় এত অধিক ফজিলত (মর্যাদা) বর্ণিত হয়নি।”
এমনকি, আলী (রা.)-এর সমর্থক বা তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের ফজিলতও বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। যেমন, আলী (রা.) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, মহানবী (সা.) আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মুমিন ব্যক্তিই আমাকে ভালোবাসবে, আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৭৮]
রাসূল (সা.) বলেছেন,
{من أحبّ عليّا فقدْ أحبّنِي ، ومن أحبّنِي فقد أحبّ اللهَ عز وجلَ ، ومن أبغضَ عليّا فقد أبغضَني ، ومن أبغضَني فقد أبغضَ اللهَ عز وجل}
যে ব্যক্তি আলীকে ভালোবাসে, সে আমাকেই ভালোবাসে; আর যে আমাকে ভালোবাসে, সে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি আলীকে ঘৃণা করলো, সে আমাকে ঘৃণা করে; আর যে আমাকে ঘৃণা করে, সে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ঘৃণা করে। [আলবানী, সিলসিলা সহীহাহ ১২৯৯]
রাসূল (সা.) বলেন,
{يا علي أبشر فإنك و أصحابك و شيعتك في الجنَّة}
অর্থ: “হে আলী, তোমার জন্য সুসংবাদ! নিশ্চয়ই তুমি, তোমার সঙ্গীরা এবং তোমার শিয়া (সমর্থক/অনুসারী)-রা জান্নাতে থাকবে।” [সূত্রসমূহ: আহমদ ইবন হাম্বল (فضائل الصحابة, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫৫); হিল্যাতুল আওলিয়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৩২৯; মু’জাম আল-আওসাত, তাবারানী; মাজমাউ’জ যাওয়ায়েদ, খণ্ড ১০, পৃ. ২১-২২; আল-দারকুতনি, বিভিন্ন সনদে; আল-সাওয়ায়িক আল-মুহরিকাহ, ইবনে হাজার আল হাইতামী, অধ্যায় ১১, পৃ. ২৪৭; হাদীসটি বিপুল সংখ্যক সনদে বর্ণিত হলেও প্রতিটি সনদেই দুর্বলতা আছে। তবে হাদীসটি ফজিলত সংক্রান্ত হওয়ায় এবং অন্যান্য সহীহ হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় বহু সংখ্যক ক্ল্যাসিকাল সুন্নি স্কলার এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। আহলে সুন্নাহর সর্বসম্মত মত হলো, ফজিলতের ক্ষেত্রে “দুর্বল” সনদে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য, যদি না সেই হাদীসটি অন্যান্য সহীহ হাদীসের বিপরীত হয়।]
রাসূল (সা.) বলেছেন,
{“شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة}
অর্থ: “আলীর শিয়ারাই কিয়ামতের দিন প্রকৃত সফলকাম।” [সূত্রসমূহ: আল-মানাকিব (المناقب), আহমদ ইবনে হাম্বল; তারিখ দিমাশক (تاريخ دمشق), ইবনে আসাকির, খণ্ড ৪২, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৩২; তাফসীরে তাবারী, সূরা আল-বাইয়িনাহ (৯৮:৭) এর তাফসীরে উল্লেখিত; তাফসীর আল-দুররুল মানসুর, জালালুদ্দিন আল-সুয়ূতী, সূরা আল-বাইয়িনাহ (৯৮:৭); এই হাদীসটির সনদেও দুর্বলতা আছে। তবে হাদীসটি ফজিলত সংক্রান্ত হওয়ায় ক্ল্যাসিকাল সুন্নি স্কলারগণ এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।]
দেখা যাচ্ছে, এই হাদীসটি সূরা আল-বাইয়িনা (৯৮:৭)-এর তাফসীরে সুন্নি মুফাসসীরগণ উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট সুন্নি স্কলার ইমাম ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহ.) বলেন,
رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} (البينة: ٧)، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: “هُم أَنْتَ وَشِيعَتُكَ”. وَقَالَ: “يَا عَلِيُّ، أَنْتَ وَشِيعَتُكَ تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ، وَيَأْتِي عَدُوُّكُمْ غِضَابًا مُقْمَحِينَ”. قَالَ عَلِيٌّ: “مَنْ عَدُوِّي؟” قَالَ: “مَنْ تَبَرَّأَ مِنْكَ وَلَعَنَكَ، وَبَشَّرَى لِلسَّابِقِينَ إِلَى ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”. قَالَ عَلِيٌّ: “مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟” قَالَ: “شِيعَتُكَ يَا عَلِيُّ، وَمُحِبُّوكَ”.
ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন: যখন আয়াত “নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা” (সূরা আল-বাইয়িনাহ ৯৮:৭) নাযিল হলো, রাসূল (সা.) তখন আলী (রা.)-কে বললেন: “তারা হলেন তুমি ও তোমার শিয়া”।
রাসূল (সা.) আরও বললেন: “হে আলী, কিয়ামতের দিন তুমি ও তোমার শিয়ারা সন্তুষ্ট ও আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে উপস্থিত হবে, আর তোমাদের শত্রুরা ক্রোধান্বিত অবস্থায় ঘাড় বাঁকা করে আসবে।”
আলী (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন: “আমার শত্রু কারা?”
রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন: “যারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তোমাকে অভিশাপ দেয়। আর কিয়ামতের দিন ‘আরশের ছায়ায় আগে পৌঁছানোদের জন্য সুসংবাদ!”
আলী (রা.) বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা?”
রাসূল (সা.) বললেন: “হে আলী! তোমার শিয়া ও তোমার ভালোবাসার লোকেরা।”
[আল-সাওয়ায়িক আল-মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ১, পৃ. ২৪৬-২৪৭]
এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহ.) বলেন, “আলী (রা.)-এর শিয়ারা হলেন আহলে সুন্নত (সুন্নি), কারণ তারা শরিয়তের নির্দেশিত সীমার মধ্যে আহলে বাইতকে ভালোবাসেন। অন্যরা (সুন্নি ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠী) প্রকৃতপক্ষে আহলে বাইতের শত্রু; কারণ শরিয়তের সীমা লঙ্ঘনকারী ভালোবাসাই মহাশত্রুতা… আর আহলে বাইতের শত্রু ছিলেন খাওয়ারিজ ও সিরিয়ার অনুরূপ গোষ্ঠীগুলো; মুয়াবিয়া (রা.) ও অন্যান্য সাহাবি নন; কেননা তারা (মুয়াবিয়া প্রমুখ) সদুদ্দেশ্যে ভুল ব্যাখ্যাকারী (مُتَأَوِّلُوْنَ) — তাদের জন্য সওয়াব রয়েছে, আর আলী (রা.) ও তাঁর শিয়াদের জন্যও সওয়াব রয়েছে।” [আল-সাওয়ায়িক আল-মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ১, পৃষ্ঠা ২৩৬]
মূলত “শিয়া” বলতে ক্ল্যাসিকাল সুন্নি স্কলারগণ এটাই বুঝিয়েছেন: “শিয়াতু-আলী” (রা.) বা আলী (রা.)-এর অনুসারী/সমর্থক হলো সুন্নিগণ। যেমন, ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন,
{“كَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ: شِيعَةُ عَلِيٍّ هُمُ السُّنِّيُّونَ لِأَنَّهُمْ عَلَى طَرِيقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”}
অর্থ: “সালাফগণ বলতেন: আলীর শিয়ারাই সুন্নি, কারণ তারা নবীজি (সা.)-এর ত্বরীক্বা/পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত।” [তারীখুল খুলাফা, পৃ. ১৬৮]
অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগে “শিয়া” শব্দটি সুন্নি আলেমদের জন্যই ব্যবহৃত হতো। একইভাবে, ইবনে আবিল ইয আল-হানাফি (রহ.) বলেছেন,
{“أَهْلُ السُّنَّةِ هُمْ شِيْعَةُ عَلِيٍّ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَهُ فِي الدِّينِ”}
অর্থ; “আহলে সুন্নতই প্রকৃতপক্ষে আলীর শিয়া, কারণ তারা দ্বীনে তাঁর অনুসরণ করে।” [শারহু আকীদাতিত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৪৮২]
বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়ার স্বঘোষিত “মহাজ্ঞানী” ইসলামী পণ্ডিতেরা যাঁকে তাদের শ্রদ্ধেয় ইমাম দাবি করে, সেই সম্মানিত সুন্নি স্কলার ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,
{“الشِّيعَةُ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ عَلِيًّا وَيُقَدِّمُونَهُ عَلَى عُثْمَانَ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ إِذَا لَمْ يَكْفُرُوا أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ”}
অর্থ: “যারা আলীকে ভালোবাসে ও উসমানের উপর তাঁকে প্রাধান্য দেয়, তারাই শিয়া। তারা আহলে সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত—যতক্ষণ না সাহাবাদের কাউকে কাফির বলে।” [মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/১৫৬]
অর্থাৎ, শিয়া পরিচয় সত্ত্বেও সাহাবিদের প্রতি সম্মান বজায় রাখলে তারা সুন্নি বলেই গণ্য—এটাই ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মত।
আসলে এটিই ছিল মুসলিম স্কলারদের সর্বসম্মত মত: শিয়া মানে আহলে সুন্নাহ (সুন্নি) এবং সুন্নিরাই আলী (রা.)-এর শিয়া/সমর্থক। প্রথম দুই শতাব্দীতে শিয়া ও সুন্নি স্কলারগণ কোনো পার্থক্যহীনভাবে একে অন্যের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতেন। ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে কাঠামোবদ্ধ ফিকহ ও মাজহাব গড়ে উঠতে থাকে।
হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর বিশিষ্ট স্কলার ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) [জন্ম: ৭০২ খ্রি. – মৃত্যু: ৭৬৫ খ্রি.] ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ষষ্ঠ বংশধর, যিনি ইমাম হাসান বিন আলী (রা.)-এর পুত্র জয়নুল আবেদিনের (রহ.) নাতি। তিনি ইলম, তাকওয়া ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এতই খ্যাতিমান ছিলেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.)-সহ অনেক স্কলার তাঁর নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর ফিকহী উসুল ও মতামতের ভিত্তিতে হানাফী মাজহাব ও মালিকী মাজহাবের মতো বৃহৎ দুইটি ফিকহী ধারা (School of Thought) গড়ে ওঠে।
ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর অনুসারীরা পরবর্তীতে “জাফরী মাজহাব” নামে আরেকটি স্বতন্ত্র ফিকহী ধারা গঠন করেন। এই “জাফরী মাজহাব”-ই বর্তমান শিয়া মতবাদের ভিত্তি। তবে ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) নিজে কোনো নতুন মাজহাব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেননি; পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাকে তার অনুসারীরা পৃথক মাজহাব (School of Thought)-এ রূপান্তরিত করে। সুন্নি ও শিয়া উভয় ফিকহী ধারাতেই ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর ইলম, মর্যাদা ও বংশগত সম্মান সর্বজনবিদিত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়।
“জাফরী মাজহাব”-টি এখন “ইসনা আশারিয়া” বা বারো ইমাম-পন্থী শিয়া মতবাদ হিসেবে পরিচিত। ইরানের সরকার ও জনগণ মূলত এই “জাফরী মাজহাব” বা “ইসনা আশারিয়া” ফিকহী ধারা (School of Thought)-এর অনুসারী/শিয়া।
শিয়া–সুন্নি বিভক্তির কারণ
সাহাবী হিসাবে হযরত আলী (রা.)-এর উচ্চ মর্যাদার কারণে সাহাবীগণ তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন: “আল্লাহর কাছে আলীর চেয়ে প্রিয় কাউকে আমি দেখিনি।” [হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/৮৪]

আবু হুরায়রা (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ বলতেন, “আলীর দিকে তাকানো ইবাদত।” [মুস্তাদরাকে হাকিম; মুজামউল কবীর]
রাজনৈতিক উত্তরসূরিত্বের প্রশ্নেও একদল সাহাবী মনে করতেন খিলাফতের জন্য আলী (রা.)-ই সর্বাধিক হকদার। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) লিখেছেন:
“وَالْحَقُّ أَنَّ أَصْلَ الْخِلَافِ كَانَ فِي الْإِمَامَةِ”
অর্থ: “সত্য হলো, বিভেদের মূল ছিল ইমামতের (নেতৃত্বের) প্রশ্নে।” [ইযালাতুল খিফা, ১/৮৭]
এই রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ ধীরে ধীরে আকিদা ও ফিকহের স্তরে প্রবেশ করে।
হিজরি ৩৬ সালে (৬৫৬ খ্রি.) জামাল যুদ্ধ ও ৩৭ হিজরিতে (৬৫৭ খ্রি.) সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জামাল যুদ্ধের মূল ইস্যু ছিল উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার, আর সিফফিনে আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে খিলাফতের আনুগত্য নিয়ে সংঘাত। এ সময় আলী (রা.)-এর সমর্থকগণ “শিয়াতু আলী” (شيعة علي) নামে পরিচিত হন। ইমাম নববী (রহ.) এর ব্যাখ্যায়:
“أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا كَانَ مُصِيبًا فِي الْقِتَالِ”
অর্থ: “আহলে সুন্নত ঐকমত্য পোষণ করেন যে আলী (রা.) যুদ্ধে সঠিক ছিলেন।” [শারহু সাহিহ মুসলিম ১২/২২৯]
মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর পক্ষের সাহাবীরা ইজতিহাদি ভুল করলেও তারা “কাফির” বা “ফাসিক” ছিলেন না—এটি সুন্নি মাজহাবের ঐকমত্য। [ইবনে হাজার, ফাতহুল বারি, ১৩/৫৫; শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইযালাতুল খিফা, ১/৯০]
প্রথম শতাব্দীতে “শিয়াতু আলী” ছিল আলী (রা.)-এর রাজনৈতিক সমর্থকদের পরিচয়। হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষের সাহাবা ও তাবেয়ীগণ সাধারণভাবে এই পরিচয় বহন করতেন। তখন “সুন্নি” নামে পৃথক কোনো দল-মত ছিল না।
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) (মৃ. ২৪১ হি.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে “আহলে সুন্নত” / “সুন্নি জামাত” পরিভাষাটি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, যা দ্বারা তিনি রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহের অনুসারীদের নির্দেশ করেন। [তারীখ বাগদাদ, ৪/৪১২]
তবে তারও আগে হিজরি ১২২ সালে ইমাম হাসান (রা.)-এর নাতি, রাসূল (সা.)-এর পঞ্চম বংশধর হযরত যায়দ ইবনে আলী (রা.) উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে কুফার একদল উগ্রপন্থী তাকে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর নিন্দা করতে বলে। যায়দ (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করায় সেই উগ্রপন্থীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে। ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন:
“لَمَّا خَرَجَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ… قَالُوا: تَبَرَّأْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى نَنْصُرَكَ! فَقَالَ: بَلْ أَتَوَلَّاهُمَا. قَالُوا: إِذًا نَرْفُضُكَ! فَسُمُّوا: الرَّافِضَةَ”
অর্থ: “তারা বলল: আবু বকর-উমর থেকে বিমুখ হও, তবেই আমরা তোমাকে সমর্থন করব! তিনি বললেন: বরং আমি তাদের বন্ধু। তারা বলল: তাহলে আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করলাম! তাই তারা ‘রাফেজা’ নামে আখ্যায়িত হয়।” [মীযানুল ই‘তিদাল, ১/২৬]
এরপর “রাফেজী” শব্দটি উগ্রপন্থী শিয়াদের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে—যারা আবু বকর, উমর (রা.)-এর খিলাফতকে অস্বীকার করে, এমনকি সাহাবীদেরকে গালাগালিও করে। মূলধারার শিয়াগণ (ইমাম যায়দ বা জাফর সাদিকের অনুসারীগণ) এই উগ্র “রাফেজী”-দের থেকে আলাদা ছিলেন এবং তাদের প্রত্যাখ্যান করতেন। কিন্তু যায়দী শিয়া ও জাফরী শিয়াদের সাথে উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের রাজনৈতিক বিরোধের কারণে উমাইয়া ও আব্বাসীয়রা সকল শিয়াকেই “রাফিজী” ট্যাগিং করার চেষ্টা করতো।
একই সময়ে শিয়ারাও “নাসিবী” (ناصبي) শব্দের প্রচলন শুরু করে। “নাসিবী” শব্দটি এসেছে **”نَصَبَ الْعَدَاءَ”** (শত্রুতা স্থাপন করা) থেকে। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর সংজ্ঞা দেন:
“النَّوَاصِبُ هُمُ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ الْعَدَاءَ لِآلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”
অর্থ: “নাসিবী হল যারা নবী পরিবারের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করে।” [মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪/৫৩০]
খারেজি ও কিছু উমাইয়া সমর্থক গোষ্ঠীকে এই ট্যাগ দেওয়া হতো, কিন্তু সকল সুন্নি কোনো অবস্থাতেই “নাসিবী” নন।
খিলাফতের উত্তরাধিকার নিয়ে সূচিত বিভাজন উমাইয়া-আব্বাসীয় যুগে আকিদাগত রূপ নেয়। ইবনে খালদুন (রহ.) বলেছেন:
“تَعَمَّقَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الشِّيعَةِ وَالسُّنَّةِ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ حَتَّى صَارَتْ مَذَاهِبَ كَلامِيَّةً”
অর্থ: “আব্বাসীয় যুগে শিয়া-সুন্নি বিভক্তি এত গভীর হয় যে তা কালামী মতবাদে পরিণত হয়।” [মুকাদ্দিমাহ, ১/২৯৮]
আধুনিক যুগে সৌদি আরব ও ইরানের ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এই পুরনো বিভাজনকে পুনরায় রাজনীতি-কেন্দ্রিক করে তুলেছে। উভয় পক্ষের উগ্র সমর্থকেরা একে অপরকে “রাফেজী” ও “নাসিবী” আখ্যায়িত করে, যদিও শিয়াদের খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ এখনো “রাফিজী” এবং সুন্নীদেরও খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ এখনো “নাসিবী”।
লক্ষ করলেই দেখবেন, বাংলাদেশেও সৌদ-পরিবারের ভক্তরা ইরানি শিয়াদেরকে “রাফিজী” হিসেবে উল্লেখ করে, অথচ সকল শিয়াকে “রাফিজী” বলাটা বাংলাদেশের সকল সুন্নি মুসলিমকে “সুরেশ্বরী” বা “দেওয়ানবাগী” বলার মতো।
বিশেষত যখনই ইরানের সাথে মধ্যপ্রাচ্যে সৌদিদের বা সৌদের মনিব আমেরিকার কোনো দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তখনই বাংলাদেশে এক শ্রেণির শায়খরা মাথায় ঘোমটা দিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শিয়াদেরকে গণহারে “রাফিজী” বা “কাফের” ডাকা শুরু করে। সৌদি রাজপরিবারের হাজারো অপকর্মের বিরুদ্ধে তারা কখনো একটি শব্দও বলবে না। পারতপক্ষে তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধেও নিরব। কিন্তু ইরান প্রসঙ্গ আসলেই তাদের ছহিহ আক্বীদানুভূতি খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে!
শিয়াদের আক্বীদা কী?
“শিয়াদের আক্বীদা কী”—এই প্রশ্নটি কনসেপচুয়ালি সঠিক নয়। ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, শিয়া চিন্তাধারার সূচনা সাহাবায়ে কেরামের যুগে হযরত আলী (রা.)-কে অগ্রাধিকারমূলক ভালোবাসা ও খিলাফতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক পছন্দের বিষয়, তখন এটি ঈমান সংক্রান্ত কোনো আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়নি। উল্লেখ্য, “ঈমানের বিষয়বস্তু” বোঝানোর জন্য “আক্বীদা” শব্দটির ব্যবহারও সে যুগে ছিল না। পবিত্র কুরআন বা সহীহ হাদীসে “আক্বীদা” শব্দটি ঈমানের পরিভাষা হিসেবে অনুপস্থিত। বরং হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে (শিয়া চিন্তাধারা শুরু হওয়ার প্রায় ৪০০ বছর পর) ইসলামী পরিভাষায় “আক্বীদা” শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়।

ইসলামী পরিভাষায় “আক্বীদা” শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে “শিয়া” বলতে মূলত একটি রাজনৈতিক দল বা পক্ষকে বোঝানো হত। বিশেষ করে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের বিরোধিতা করা গোষ্ঠীগুলো এই পরিচয়ে পরিচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, উমাইয়া শাসকদের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কেও অনেক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক শিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সুন্নি মতবাদের বৃহত্তম ফিকহি মাযহাবের ইমাম হলেও, তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান তাকে “শিয়া” পরিচয় দিয়েছিল—এবং সেটি কোনো আক্বীদাগত বিভক্তি ছিল না।
#সাহাবা-তাবেঈন যুগে ঈমানের ভিত্তি:
সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে ঈমান বলতে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ছয়টি মৌলিক বিশ্বাসকেই বোঝানো হত:
১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
২. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস
৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস
৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস
৫. আখিরাতের (পরকাল) প্রতি বিশ্বাস
৬. তাকদীরের (ভাগ্যের) প্রতি বিশ্বাস
এই ছয়টি বিষয়ে বিশ্বাস করলেই কোনো ব্যক্তি “মুমিন” হিসেবে গণ্য হতেন। সে যুগে শিয়া ও সুন্নি—সকল মুসলিম এই মৌলিক বিশ্বাসে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন। অতএব, প্রাথমিক যুগে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে কোনো পৃথক ‘আক্বীদা’ বিদ্যমান ছিল না।
#তাত্ত্বিক_বিতর্কের_সূচনা ও আক্বীদা শাস্ত্রের উদ্ভব:
হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক তীব্র হতে থাকে। কাদরিয়া, মুতাজিলা, জাহমিয়া প্রভৃতি দার্শনিক গোষ্ঠীগুলো ঈমানের শাখাগত বিষয় নিয়ে জটিল বিতর্ক সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে ‘আক্বীদা’ নামে একটি স্বতন্ত্র ধর্মতাত্ত্বিক শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। এ সময়ই লেখ্যরূপে আক্বীদার চর্চা শুরু হয়, যেমন: আক্বীদা আত-তাহাবিয়্যা (রচনাকাল: হিজরী ৩য়/৯ম শতাব্দী, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী রহ.), আল-আক্বীদা আল-ওয়াসিতিয়্যাহ (রচনাকাল: ৭০৫ হি./১৩০৬ খ্রি., শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.) ইত্যাদি।
এভাবে ঈমানের সরল ছয়টি স্তম্ভের উপর শতাধিক শাখাগত প্রশ্নের উদ্ভব হয়। আক্বীদার চর্চা ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোকে এমন গভীরে নিয়ে যায় যেখানে মানবীয় ব্যাখ্যা ও দুর্বল সূত্রের হাদীসের ব্যবহার শুরু হয়। সাহাবী যুগের পর ইসলামের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের সাথে সাথে মুসলিম স্কলাররা বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মের সংস্পর্শে আসেন এবং ঈমানের জটিল দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বোঝার জন্য এই প্রচেষ্টা যুক্তিসঙ্গত ছিল, কিন্তু ক্রমে তা সীমা অতিক্রম করে। মানুষ নিজেদের সঠিকতা প্রমাণের পাশাপাশি অন্যদের ভুল প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আক্বীদা এতটাই বিস্তারিত ও জটিল হয়ে ওঠে যে ঈমানের মূলনীতিগুলো আর “আঙুলে গোনার” মতো সরল থাকল না—বরং ‘আক্বীদা আত-তাহাবিয়্যা’, ‘শারহুল আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ’ বা ‘কিতাবুত তাওহীদ’-এর মতো বিশাল গ্রন্থরাজিতে পরিণত হলো!
এই সকল গ্রন্থে আলোচিত কিছু জটিল বিতর্কের বিষয়:
– ওহী বনাম যুক্তি: ধর্মীয় জ্ঞানে ঐশী বাণী ও মানবীয় যুক্তির মধ্যে প্রাধান্য কাকে দেওয়া হবে?
– কুরআন সৃষ্ট নাকি অ-সৃষ্ট: কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, নাকি তাঁর অনন্ত জ্ঞানের প্রকাশ?
– আল্লাহর সর্বত্র উপস্থিতি: আল্লাহ কি সর্বত্র বিদ্যমান (সর্বব্যাপী), নাকি তিনি স্থান-কালের ঊর্ধ্বে?
– তাকদীর বনাম ইখতিয়ার: মানুষের কর্ম কি পূর্বনির্ধারিত, নাকি তার স্বাধীন ইচ্ছা আছে?
– ইবলিসের পরিচয়: শয়তান (ইবলিস) ফেরেশতা ছিল, নাকি জিন জাতির?
– রাসূলুল্লাহ (সা.) নূর (আলো) দিয়ে সৃষ্টি, নাকি অন্যান্য মানুষের মতো মাটি দিয়ে? রাসূলুল্লাহ (সা.) কি সবার আগে সৃষ্টি হয়েছিলেন?
এসব বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিরোধ কারও কারও কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা ধীরে ধীরে শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সকল ফিকহি মাযহাবের মধ্যে উপদলীয় বিভাজন তৈরি করে।
#শিয়া_মাযহাবসমূহ_ও_তাদের_আক্বীদাগত_পার্থক্য:
পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে শিয়াদের মধ্যে আক্বীদাগত যে ধারণা প্রবেশ করেছে তা নিচে মোটামুটি সামারি দেওয়া হলো। তবে মনে রাখা জরুরি: একই মাযহাবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে (যেমন, হানাফী সুন্নিদের মধ্যে দেওবন্দী-বেরেলভী)। শিয়া মাযহাবগুলোর সারাংশ:
১. ইসনা আশারিয়া (বারো ইমামী/জাফরী):
– ফাদলুল্লাহ ঘরানা (লেবানন, ইরাক; হি*জ*বুল্লা*হ গ্ৰুপের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা):
* ইমামত নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা, কুরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
* আলী (রা.)-এর নেতৃত্ব আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ধারিত ছিল বলে বিশ্বাস।
* তাকিয়া (প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মত গোপন) কৌশলগত বিষয়, ধর্মীয় ভিত্তি নয়।
* সুন্নিদের সাথে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস, সাহাবীদের প্রতি সম্মান।
* কারও প্রতি অভিশাপ বা গালিগালাজ হারাম।
[সূত্র: আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ হুসাইন ফাদলুল্লাহ রহ.-এর ফতওয়া ও বক্তব্য]
– আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি ঘরানা (ইরানের ক্ষমতাসীন সরকার ও অধিকাংশ শিয়া এই ঘরানার):
* ইমামত “ইলাহী নিয়োগ” (আল্লাহর ইশারায় নির্বাচন) এবং ইমামগণ মাসূম (নিষ্পাপ)।
* ইমামত ঈমানের অংশ।
* তাকিয়া ও ইমামদের অলৌকিক ক্ষমতা বিশ্বাস্য।
* ইমামদের প্রায়-নবীর মর্যাদা দেওয়া।
[সূত্র: ইমাম খোমেইনি রহ.-এর “কাশফুল আসরার”, “হুকুমাতে ইসলামী”]
২. যায়দিয়া (ইয়েমেনের সাধারণ শিয়া ও হু*তি বিদ্রোহীদের মাযহাব):
* ইমামতকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসেবে দেখা হয়, ধর্মীয় নেতৃত্ব নয়।
* ইমামগণ মাসূম (নিষ্পাপ) নন।
* সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।
* ফিকহে হানাফীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান।
* ইমাম যায়িদ বিন আলী (রহ.)-এর অনুসারী, যাঁকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করতেন।
[সূত্র: ইমাম যায়িদ রহ.-এর “মাজমুউল ফিকহ”, ঐতিহাসিক গ্রন্থ “তাবাকাতে ইবনে সাদ”]
৩. গুলাত (অতিরঞ্জনকারী) সম্প্রদায়:
“গুলাত” অর্থ অতিরঞ্জনকারী। এরা মূলধারার শিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার উদাহরণ:
* আলী (রা.)-কে “আল্লাহ” বা “আল্লাহর নূর” মনে করা।
* ইমামদের উপর খোদায়ী গুণ আরোপ করা (যেমন: অলৌকিক সৃষ্টি, গায়েব জানা)।
* গোপন ইমামত ও রূপক তাফসিরে বিশ্বাস।
* আলাউয়ী/নুসাইরী (সিরিয়া): আলী (রা.)-কে আল্লাহর সত্তার অংশ মনে করে।
* ইসমাইলিয়া: ইমামতকে গোপন জ্ঞানের ধারক বলে বিশ্বাস করে।
* আগাখানি: ইসমাইলিয়ার একটি শাখা, বর্তমান নেতা আগা খান।
* দাঊদী/সুলাইমানী বোহরা (ভারত-পাকিস্তান): ইসমাইলিয়ার উপশাখা।
#গুলাতদের_বিরুদ্ধে_মূলধারার_শিয়া আলেমদের কঠোর অবস্থান: শাইখ ইবনে বাবুয়াইহ আল-কুম্মী (আস-সাদূক) রহ. (মৃ. ৩৮১ হি.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আলী (আ.)-কে ‘ইলাহ’ (খোদা) বলে বিশ্বাস করে, সে কাফির। আমরা তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।” [আল-ই’তিকাদাত, পৃষ্ঠা ১০২]
আল্লামা আব্দুল্লাহ আল-মামাকানী রহ. (১৮৪৬–১৯৩২) বলেছেন, “গুলাতরা ইসলামের শত্রু। ইমামদেরকে খোদা বানানো বা দৈব গুণ দেয়া—এসব প্রকাশ্য কুফর।” [তানকীহুল মাকাল ফী ইলমির রিজাল, ২/১৮৫]
আয়াতুল্লাহ আগা বোজর্গ আত-তেহরানী রহ. (মৃ. ১৯৭০) বলেছেন, “যারা ইমামদের উপর আল্লাহর সিফাত আরোপ করে, তারা প্রকৃত শিয়া নয়।”
[আয-যারিয়াহ ইলা তাসানীফিশ শিয়া, ৪/২৮৩]
আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মাদ হুসাইন ফাদলুল্লাহ রহ. (লেবানন) বলেছেন, “আমরা এমন শিয়াবাদকে প্রত্যাখ্যান করি যাতে গালিগালাজ, অভিশাপ, ইমামদের দেবত্বকরণ বা অতিরঞ্জন থাকে। এটি আহলে বাইতের প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী।” [বিবৃতি: আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-মুয়াসিরাহ, ১/৩৪০]
আসলে “শিয়া আক্বীদা” বলতে একক, অভিন্ন কোনো মতাদর্শ নেই (জাফরী, যায়দিয়া, ইসমাইলিয়ার মধ্যে আক্বীদাগত পার্থক্য বিশাল), যেভাবে “সুন্নি আক্বীদা” বলতেও একক কিছু নেই (আশআরি, মাতুরিদি, সালাফি/আসারি ভিন্নতা বিদ্যমান)। মূলধারার জাফরী বা যায়দিয়া শিয়ারা ঈমানের ছয় মৌলিক স্তম্ভে সুন্নিদের সাথে সম্পূর্ণ একমত। তাদের মধ্যে ফিকহি মতপার্থক্য থাকলেও তা আক্বীদাগত বিভাজন নয়।
ইতঃপূর্বে রাফেজী ও নাসিবী নিয়েও আলোচনা করেছি। এখানে সেই আলোচনা আবার করা প্রাসঙ্গিক।
প্রাথমিক ইমামগণ (যেমন ইমাম যায়িদ রহ., ইমাম জাফর আস-সাদিক রহ.) সাহাবীদের গালি দেওয়া, আলী (আ.)-কে খোদা বানানো বা ইমামতকে নবুয়তের সমান দাবি করার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। প্রকৃত রাফেজী ছিল তারা যারা:
– হযরত আবু বকর, উমর, উসমান (রা.)-কে কাফের/মুনাফিক বলত।
– আলী (আ.)-কে প্রায় নবীর মর্যাদা দিত।
– কুরআন বিকৃত হয়েছে বলে বিশ্বাস করত।
– সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশকে গালি দিত।
(সূত্র: ইবনে তাইমিয়ার “মিনহাজুস সুন্নাহ”, ১/৩৫; শাহরাস্তানীর “আল-মিলাল ওয়ান নিহাল”)
বর্তমান ইসনা আশারিয়া/যায়দিয়ারা কি রাফেজী?
না। আধুনিক জাফরী আলেমগণ (যেমন আয়াতুল্লাহ ফাদলুল্লাহ, আয়াতুল্লাহ সিস্তানী, আয়াতুল্লাহ ফালাহাতপিশে) রাফেজী মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে সুন্নিদের সাথে সংলাপ ও সম্মানের আহ্বান জানিয়েছেন। যায়দিয়ারা তো সাহাবীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই পুরো শিয়া মতবাদকে “রাফেজী” আখ্যা দেওয়া অন্যায়।
#নাসিবী (ناصبي) কারা?
‘নাসিবী’ শব্দটি ‘নাসাবা’ (বিদ্বেষ পোষণ করা) ধাতু থেকে এসেছে। ইসলামী ইতিহাসে আহলে বাইত (বিশেষত আলী (রা.) ও তাঁর বংশধর)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, তাদের গালি দেওয়া বা মর্যাদা অস্বীকার করা ব্যক্তিকে নাসিবী বলা হতো।
বর্তমান সুন্নিরা কি নাসিবী?
মোটেও না। সুন্নি মাযহাবগুলো আহলে বাইতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করে। ইমাম বুখারী (সহীহ বুখারী, “ফাদাইলু আসহাবিন নবী” অধ্যায়), ইমাম আহমাদ (ফাদাইলুস সাহাবা), ইমাম নববী (শারহু মুসলিম), জালালউদ্দিন সুয়ুতি-সহ বহু সুন্নি মনীষী আহলে বাইতের মর্যাদা নিয়ে লেখালেখি করেছেন। যেমন, বুখারী শরীফে অন্যান্য সকল সাহাবীর নামের শেষে “রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু” লেখা হলেও আহলে বাইতগণের নামের শেষে, অর্থাৎ আলী (রা.), ফাতিমা (রা.), হাসান-হুসেন (রা.) প্রমুখের নামের শেষে প্রায় ২০ বার সম্মানসূচকভাবে “আলাইহিস সালাম” লেখা হয়েছে। কোনো সুন্নি মাযহাব “নাসিবী নীতি” সমর্থন করে না।
শিয়া-সুন্নি উভয় ঘরানার কিছু উগ্রপন্থী লোক অহেতুক একে অপরকে “রাফেজী” ও “নাসিবী” আখ্যা দিয়ে উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করে। ওয়েব সাইট, ব্লগ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব নোংরামি ও বিদ্বেষ খুবই পরিকল্পিতভাবে ছড়ানো হয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হলো—অন্য মুসলিমের ঈমান নিয়ে সন্দেহ না করা এবং দলিলভিত্তিক মতপার্থক্য থাকলেও সম্মান ও ন্যায়বিচার বজায় রাখা (কুরআন ৪৯:১২, সহীহ বুখারী ৬০৪৫)।
ঐতিহাসিকভাবে শিয়া-সুন্নি সম্পর্ক কেমন ছিল?
আগের পর্বগুলোতে আলোচনা হয়েছে যে, শিয়া ও সুন্নি বিভাজন মূলত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার রাজনৈতিক সংঘাত থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে, ঈমান-আক্বীদা বা ফিকহগত মতপার্থক্য থেকে নয়। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে আব্বাসীয়-ফাতেমী কিংবা উসমানীয়-সাফাভী দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রভাব বিস্তার ও আঞ্চলিক আধিপত্যের লড়াই। এসব লড়াই শিয়া-সুন্নি পরিচয়ের আড়ালে পরিচালিত হলেও এসবের মূলে ছিল ক্ষমতার রাজনীতি। তবে লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলয় থেকে মুক্ত আলেমগণ সাধারণত উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে এই ধরনের বিবাদে জড়াতেন না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উসমানীয় খিলাফতের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে শিয়া ও সুন্নি আলেমদের ঐতিহাসিক ঐক্য একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ১৯১৪ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ বাহিনী ইরাকের আল-ফাও উপকূলে অবতরণ করলে ইরাকের শিয়া নেতাগণ, যেমন গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ কাজিম আল-ইয়াযদি (রহ.) ও আয়াতুল্লাহ মির্জা মুহাম্মাদ তাকি শিরাজী (রহ.) তৎকালীন উসমানীয় খলিফার পক্ষে ফতোয়া জারি করেন। কারবালা ও নাজাফের শিয়া আলেমগণ স্থানীয় মুসলমানদেরকে উসমানীয়দের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। [ড. আলী আল-ওয়ার্দি ,”লামাহাত ইজতিমাইয়াহ মিন তারিখ আল-ইরাক আল-হাদিস”-এ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬]
অন্যদিকে, সহীহ আক্বীদার দাবিদার আহলে সৌদ (সৌদের বংশধর ও অনুসারীরা) সে সময় ব্রিটিশদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।
১৯১৯ সালে ইরাকের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে শিয়া-সুন্নি নেতারা “We, being of the Muslim Arab nation and representing the Shia and Sunni communities inhabiting Baghdad and its suburbs…” – এমন বিবৃতি দিয়ে জাতীয় ঐক্যের অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক দলিলটি ব্রিটিশ জাতীয় সংরক্ষণাগারে (UK National Archives, FO 371/4148) সংরক্ষিত আছে। ১৯২০ সালের ইরাকি বিপ্লবকালে মির্জা তাকি শিরাজীর নেতৃত্বে শিয়া-সুন্নি আলেমগণ ও সাধারণ মানুষ সংযুক্তভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। [ড. আব্দুল্লাহ আল-ফায়াদ, “The Iraqi Revolution of 1920”, পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯১]
তবে ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের পতনের মাধ্যমে শিয়া-সুন্নির ঐক্যের প্রতীকটি ধ্বংস হয় এবং গত ১০০ বছর ধরে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভাজনটি উস্কে দিতে সক্রিয় রয়েছে।
ভারতীয় উপমহাদেশে দিল্লি সালতানাত ও মুঘল আমলে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২) তার বিখ্যাত গ্রন্থ “ইজালাতুল খিফা আন খিলাফতুল খুলাফা”-তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন: “শিয়ারা ইসলামবিরোধী নয়”, “আলী (রা.)-এর মর্যাদা আমরা স্বীকার করি” এবং “বিভাজন মূলত রাজনৈতিক কারণে সৃষ্টি হয়েছে”। [গ্রন্থের ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৭]
বাংলা অঞ্চলে নবাব আলীবর্দী খান ও সিরাজউদ্দৌলার শিয়া পরিচয় সত্ত্বেও স্থানীয় সুন্নি আলেম ও সাধারণ মুসলিমগণ তাদেরকে সমর্থন করেছিলেন। [ড. মুহাম্মদ মোহর আলী, “History of the Muslims of Bengal”, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২]
ব্রিটিশ আমলেও এই সম্প্রীতি অব্যাহত ছিল। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের নেতাই ছিলেন – নবাব ওয়াকার-উল-মুলক মৌলভী (সুন্নি), স্যার আদমজী পিরভয় (শিয়া) সুলতান মুহাম্মদ শাহ আগা খান (শিয়া), ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ (সুন্নি) এবং স্যার সৈয়দ আমির আলী (শিয়া)। পাকিস্তান আন্দোলনের সর্বজনীন নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর শিয়া পরিচয় সত্ত্বেও ভারতের সকল প্রধান সুন্নি নেতারা তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন।
বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শিয়া প্রভাব অত্যন্ত গভীর। হাজী মুহাম্মদ মহসিনের মতো শিয়া সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে মহররম ও কারবালাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার এই সম্প্রীতিরই স্বাক্ষর বহন করে। এখনো বাঙালি মুসলিমের নামের মধ্যে আলী, হাসান, হুসেনের বিপুল প্রাধান্য দেখা যায়, যা মূলত শিয়া সংস্কৃতি। ১৯৮০ দশকে বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্মানিত আলেম মাহমুদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) ইরান সফর করেছিলেন এবং তিনি আয়াতুল্লাহ খোমেনির ইমামতিতে সালাত আদায় করেছিলেন এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনিও হাফেজ্জী হুজুরের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছিলেন।
১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের পর থেকে শিয়া-সুন্নি সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ইতিহাসবিদ ফাউজি আল-জিয়াদ তার “The Shia-Sunni Divide: Myths and Realities” (পৃষ্ঠা ৭৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইরানের শাহ পাহলভীর আমলে সৌদি আরবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় ছিল, যদিও ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তখনও শিয়া ছিল। পশ্চিমাপন্থী শাহের সাথে পশ্চিমাপন্থী সৌদি রাজতন্ত্রের যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল।
কিন্তু আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে পশ্চিমা দালাল শাহের উৎখাতের পর পশ্চিমা দালাল সৌদি সরকারের নীতি পরিবর্তন হয়। তারা শিয়াবিরোধী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে।
তবুও সৌদি আরব কখনোই সরকারিভাবে শিয়াদেরকে কাফের ঘোষণা করেনি এবং শিয়াদেরকে হজ্ব করতে অনুমতি দেয়। ২০১০ সালে লেবাননের শিয়া নেতা আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ হুসাইন ফাদলুল্লাহর মৃত্যুর পর সৌদি প্রতিনিধিদল তার জানাজায় অংশ নিয়েছিল (আল-জাজিরা রিপোর্ট, ৬ জুলাই ২০১০)।
বর্তমান সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের জটিল ভূরাজনীতিতে ইরান ও সৌদি আরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অনেকেই শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি আঞ্চলিক ক্ষমতার লড়াই। ড. ভ্যালি নাসর তার “The Shia Revival” (পৃষ্ঠা ১৫৬) গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইরাক যুদ্ধের পর থেকে এই বিভাজন কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হয়েছে।
ইসলামের ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়গুলো প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক প্রয়োজন ছাড়া শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায় সাধারণত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে এবং উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে একতাবদ্ধ থেকেছে। বর্তমানকালেও আসল সত্য হলো, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইরান ও সৌদি আরবের দ্বন্দ্বের কারণেই মূলত সৌদিপন্থী আলেমরা বিশ্বব্যাপী শিয়াবিদ্বেষ প্রচার করে। বিশেষত ইস*রা*য়েল বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের যে কোনো লড়াইয়ের সময় এই ধরনের অপপ্রচার বৃদ্ধি পায়।
“ইরানের সরকারটি কেমন”—এই আলোচনার আগে শিয়া-সুন্নি বিষয়ে এত আলোচনা করার কারণ হলো, ইরানসংক্রান্ত যে-কোনো আলোচনায় অনেকের একটা কমন টেনডেন্সি হলো বিষয়টাকে শুধুমাত্র শিয়া-সুন্নির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। সেই আলোচনায় ইরানের রাষ্ট্রীয় দর্শন, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, সামরিক নীতি, অর্থনীতি ও ভূ-রাজনীতি ইত্যাদির কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি লড়িবার শিয়া-সুন্নি!


বাস্তবতা হলো, ইরানের সরকারের কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই শিয়া মতবাদকে প্রতিনিধিত্ব করে না, যেমন সৌদি রাজপরিবারের কর্মকাণ্ডও কোনোভাবেই সুন্নি মতবাদ বা ওহাবী মাযহাবকে প্রতিনিধিত্ব করে না। ইরানি সরকার বা সৌদি রাজপরিবার উভয়ই এক একটি রাজনৈতিক শক্তি। তারা প্রত্যেকে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তা, বৈদেশিক শক্তির প্রভাব, রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা ও আঞ্চলিক উচ্চাভিলাস দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই শিয়া-সুন্নি, জাফরী-ওহাবী ইত্যাদি মতবাদ এড়িয়ে আসলে ফোকাস করা উচিত দেশগুলোর রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, সামরিক নীতি, অর্থনীতি ও ভূ-রাজনীতি ইত্যাদির হিসাব-নিকাশে। তবে ধর্মীয় আবেগ ও শিয়া-সুন্নি পরিচয়কে উভয় সরকারই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য ব্যবহার করে।
১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবকে অনেকেই মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রকৃত ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখেন। তবে বাস্তবতা হলো, এই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীগুলোর সবাই ইসলামপন্থী ছিল না; বরং এতে কমিউনিস্ট, বুদ্ধিজীবী, বামপন্থী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীসহ বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ অংশ নিয়েছিল, যাদের মূল লক্ষ্য ছিল মার্কিন-ব্রিটেনপন্থী বাদশাহ রেজা শাহের শাসনের অবসান ঘটানো। আয়াতুল্লাহ খোমেনি জনগণের কাছে “পরিবর্তন”-এর প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হন। তবে ক্ষমতায় আরোহণের পর ইসলামী নীতি বাস্তবায়নের চেয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রক্ষাই তাঁর প্রধান অগ্রাধিকারে পরিণত হয়। খোমেনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সমর্থকরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন; অন্যদিকে বিপ্লব সংঘটনে সহায়তা করা অনেককেই পরবর্তীতে নির্বাসিত বা কারাবন্দি করেন। বিপ্লবের পর ইরানে একটি নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় “সুপ্রিম লিডার”-এর হাতে। এই পদে এখন পর্যন্ত মাত্র দু’জন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হয়েছেন: প্রথমত আয়াতুল্লাহ খোমেনি (১৯৭৯-১৯৮৯) এবং পরবর্তীতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই (১৯৮৯-বর্তমান)।
ঐতিহাসিকভাবে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ছিল এবং বর্তমানেও এই নীতি অব্যাহত রেখেছে। ইরানের রাজনৈতিক নেতারা বারবার তাদের আঞ্চলিক পরাশক্তি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ একবার বলেছিলেন, “আমরা দ্রুত একটি পরাশক্তিতে পরিণত হচ্ছি। আমাদের শক্তি সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক সক্ষমতা থেকে আসে না, বরং মানুষের হৃদয় ও মননে প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য থেকে আসে – আর এটাই তাদের ভীত করে।” এই লক্ষ্য অর্জনে ইরান লেবাননের হিজবুল্লাহ, ফিলিস্তিনের হামাসের মতো সংগঠনগুলোকে সমর্থন দিয়েছে এবং সিরিয়ার জালিম বাশার আল-আসাদের আলাওয়ি শাসনকে সহায়তা করেছে।
ইরান তার আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী সৌদি আরবের মতোই প্রায়ই শিয়া-সুন্নি বিভেদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তারা নিজেদেরকে বৈশ্বিক শিয়া সম্প্রদায়ের রক্ষক হিসেবে দাবি করলেও বাস্তবে শুধুমাত্র সেই শিয়াদেরই সহায়তা করে যারা তাদের আঞ্চলিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল (যেখানে অধিকাংশ শিয়া বসবাস করে এবং দেশের প্রধান তেলক্ষেত্রগুলো অবস্থিত) ও বাহরাইনে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করে ইরান। অন্যদিকে আজারবাইজান বা তাজিকিস্তানের শিয়াদের প্রতি ইরান কোনো সমর্থন দেখায় না, কারণ এগুলো তাদের কৌশলগত স্বার্থের বাইরে পড়ে।
#মার্কিন_যুক্তরাষ্ট্রের_সাথে_ইরানের_সম্পর্ক
আমেরিকার সাথে ইরানের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের সূচনা ১৮৫৬ সালে। ইরানের [তখন “পারস্য” নামে পরিচিত] তৎকালীন কাজার বংশীয় রাজা নাসের উদ্দিন শাহ কাজার ১৮৫৬ সালে ওয়াশিংটনে প্রথবারের মতো পারস্যের রাষ্ট্রদূত পাঠান। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিকতার যুগে আফগানিস্তান ও ইরান অঞ্চলকে ঘিরে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের “গ্রেট গেইম” চলাকালে আমেরিকাকেই নিরাপদ মিত্র হিসেবে দেখেছিলেন ইরানের তৎকালীন রাজা নাসের উদ্দিন শাহ। কাজার বংশীয় শাহদের আমলে ইরানের সাথে আমেরিকার এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় যে, পরবর্তীতে ১৯১১ সালে আমেরিকান সরকারের পরামর্শে আমেরিকান কর্মকর্তা উইলিয়াম শাসটারকে ইরানের ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য ইরানের ট্রেজারার-জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। পরে আরেক আমেরিকান কর্মকর্তা আর্থার মিল্সপগকে ১৯২২-২৭ সালে ও ১৯৪২-৪৫ সালে দুই মেয়াদে একই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল!
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আমেরিকা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষনীতি (Isolationism) কিংবা অন্তত অন্য দেশে হস্তক্ষেপ না-করার (Non-interventionism) নীতি অনুসরণ করতো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঔপনিবেশিকতার পতনের পর আমেরিকা অন্য দেশে হস্তক্ষেপ না-করার (Non-interventionism) নীতি ত্যাগ করে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ (Neo-colonialism) নীতি গ্রহণ করে এবং দেশে দেশে হস্তক্ষেপ শুরু করে। আমেরিকার সেই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার প্রথম বলি হয় দীর্ঘদিনের মিত্র ইরান।
১৯৫৩ সালে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআইসিক্স মিলে এক অভ্যুত্থানে গণতান্ত্রিক ভোটে নির্বাচিত ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করে। প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের “অপরাধ” ছিল তিনি ইরানি তেলক্ষেত্রগুলোতে ব্রিটিশ লুণ্ঠন বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং ইরানি তেলক্ষেত্রগুলোকে জাতীয়করণ করেছিলেন।
মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের অদম্য প্রেমে আমেরিকা-ব্রিটেনের সেই যুগলবন্দীই পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে শুরু করে। আমেরিকা আর ইরানের সম্পর্কও আমেরিকার সেই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ও তেলপ্রেমের আঁচলে বাঁধা পড়ে।
ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ইরানের বাদশা রেজা শাহ পাহলভীর হাতে দেশের সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করে আমেরিকা-ব্রিটেন। স্বৈরশাসক রেজা শাহ পাহলভীকে ইরানের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে শত শত কোটি ডলারের সাহায্য পাঠায় আমেরিকা। সিআইএ-র কর্মকর্তারা ইরানে গিয়ে পাহলভীকে গড়ে দেয় ইরানের নিষ্ঠুর নিপীড়নকারী গুপ্ত পুলিশ সংস্থা “সাভাক”।
ইতিহাসের পরিহাস হলো, আজকের রিপাবলিকান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঙ্কার দিচ্ছে ইরানকে কিছুতেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দিবে না, অথচ ১৯৫০-এর দশকের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান আইজেনহাওয়ারই ১৯৫৭ সালে ইরানকে প্রথম পারমাণবিক চুল্লি তৈরিতে সহযোগিতা করে। আমেরিকাই ১৯৬৭ সালের পরে ইরানকে প্রথম অস্ত্র তৈরির উপযোগিতা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সরবরাহ করে। আমেরিকা-ব্রিটেনসহ পশ্চিমা শক্তির মিত্র পাহলভী যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন, আমেরিকা-ইউরোপের সরকারগুলো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে গেছে।
১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে মার্কিন-ব্রিটেনপন্থী রেজা শাহ পাহলভীর পতন হলে তিনি সপরিবারে আমেরিকা পালিয়ে যান। [প্যাটার্নটি কি খুব পরিচিত মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, রেজা শাহও পালিয়ে যাওয়ার আগে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করার টাইম পাননি এবং রেজা শাহের উজবুক পুত্রটিও আমেরিকাতেই বসবাস করে।
 ]
]ইরানে বিপ্লবের পর ইরাকের তৎকালীন মার্কিনপন্থী প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে দিয়ে ইরানের সাথে যুদ্ধ বাঁধায় আমেরিকা। ১৯৮০ থেকে শুরু হওয়া সেই যুদ্ধে ইরাককে সার্বিক সহযোগিতা করে আমেরিকা। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়। ১৯৯৫ সালে ক্লিনটন প্রশাসন ইরানের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেয়।
ইরানের বিপ্লবের পর থেকে এখন পর্যন্ত আমেরিকার সাথে ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। আমেরিকার সাথে ইরানের অফিসিয়াল যোগাযোগ হয় পাকিস্তানের মাধ্যমে। ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের “ইরানিয়ান ইন্টারেস্টস সেকশন” ইরানের পক্ষ থেকে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ করে। আমেরিকার পক্ষে দূতিয়ালি করে সুইজারল্যান্ড। তেহরানের সুইস দূতাবাসের “ইউএস ইন্টারেস্টস সেকশন” আমেরিকার পক্ষে ইরানের সাথে যোগাযোগ সারে।
তবে এটা মুদ্রার একপিঠের বয়ান। মুদ্রার অপর পিঠ হলো, ইরান যতই আমেরিকাকে “বড় শয়তান” আখ্যা দিয়ে তীব্র সমালোচনা করুক না কেন, বাস্তবে বেশ কিছু কৌশলগত ইস্যুতে দুটি দেশ একসাথে কাজ করে। ১৯৮৩ সালে ইরানের সরকারের বিভিন্ন স্তরে ইরানের সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট সংগঠন “তুদেহ পার্টি”-এর লোকজনের ব্যাপক অনুপ্রবেশের কথা আমেরিকাই জানিয়েছিল আয়াতুল্লাহ খোমেনির সরকারকে। আমেরিকার দেওয়া সেই তথ্য ব্যবহার করে খোমেনির সরকার তখন ইরানে কমিউনিস্ট প্রভাব নির্মূল করে।
১৯৮০-এর দশকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের প্রশাসন গোপনে ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি শুরু করে এবং নিকারাগুয়ার বামপন্থী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ইরানের মাধ্যমেই নিকারাগুয়ার ডানপন্থী কন্ট্রা বিদ্রোহীদের কাছে সাহায্য পাঠায়।
নাইন-ইলেভেনের পর আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে উৎখাতের ক্ষেত্রে আমেরিকাকে সহযোগিতা করে ইরান। অনুরূপভাবে, ইরাকের সাদ্দাম সরকারকে উৎখাতেও ইরান সহযোগিতা করে আমেরিকাকে, বিশেষত ইরাকের শিয়া বিদ্রোহী দলগুলোকে আমেরিকার প্রতি নমনীয় করে ইরান।
ইরানি সরকার গত ১৫ বছর ধরে তার সমস্ত সামর্থ্য – অর্থনীতি, সশস্ত্র বাহিনী, রেভোলিউশনারি গার্ড, কুদস ফোর্স এবং হি*জবু*ল্লাহ প্রোক্সি – কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা দালাল বাশার আল-আসাদ ও তার শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু ইস*রায়ে*লকে মোকাবেলা করার জন্য কখনোই নিজস্ব সামরিক ঘাঁটি স্থাপন বা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করেনি। ফিলিস্তিনের জনগণের উপর ইস*রায়ে*লি হামলার সময় ইরান নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় ছিল। হিজ*বুল্লা*হকে ইস*রায়ে*ল-বিরোধী কোনো পদক্ষেপ নিতে ইরান নির্দেশ দেয়নি। বরং সিরিয়ার মুসলিমদেরকে ইরান হ*ত্যা ও নির্যাতন করেছে শুধু পশ্চিমাপন্থী বাশারের শাসন টিকিয়ে রাখতে। আমেরিকা যখন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের মাধ্যমে সিরিয়ায় বাশারকে সরিয়ে নতুন “জি*হা*দি*স্ট” (
 ) দালাল ক্ষমতায় আনল, ইরান নিশ্চিন্তে তার সেনা ফিরিয়ে নিল।
) দালাল ক্ষমতায় আনল, ইরান নিশ্চিন্তে তার সেনা ফিরিয়ে নিল।ইস*রায়ে*ল বছরের পর বছর ইরানি নেতাদের হত্যা করেছে, কিন্তু ইরান কখনোই মর্যাদা রক্ষার মতো জবাব দিতে পারেনি। ইরাক যুদ্ধের সময় গড়ে তোলা সামরিক শক্তি এবং সিরিয়ায় অর্জিত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ইরানের প্রতিক্রিয়া খুবই সামান্য। সম্প্রতি ইস*রায়ে*লি হামলায় ৬১০ ইরানি নিহত ও ৪,৭৪৬ আহত হয়েছে। অন্যদিকে ইস*রায়ে*লি মরেছে খুবই কম সংখ্যক।
ট্রাম্প যেভাবে ইস*রায়ে*লকে দিয়ে এই যুদ্ধ শুরু করিয়েছিল, সেভাবেই যুদ্ধবিরতিও ঘোষণা করেছে। ইরান ও ইস*রায়ে*ল দু’পক্ষই এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। ট্রাম্প বলেছে, “ইরানের পরমাণু স্থাপনা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে” এবং “ইরান কখনোই তার পরমাণু কর্মসূচি পুনর্নির্মাণ করতে পারবে না”।
বাস্তবে ইরানি সরকারটিও আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট। আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, সিরিয়া সবখানে ইরানি সরকারের একই ভূমিকা। কিন্তু আমেরিকা যখন দেখেছে ইরান তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে, তখনই সামরিক চাপ প্রয়োগ করেছে।
এবারের যুদ্ধবিরতির পর আমেরিকা ইরানকে ৩০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রস্তাব করেছে শুধু শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচির জন্য। শর্ত একটাই—ইরানকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। অবশ্য আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা (IAEA) এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের তথ্য অনুযায়ী, ইরান ইতোমধ্যে ৪০০ কেজির বেশি ৬০% সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুদ করেছে। এই মাত্রার ইউরেনিয়াম সামরিক ব্যবহারের জন্য খুবই বিপজ্জনক। কারণ এখান থেকে ৯০% weapon-grade পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া প্রযুক্তিগতভাবে খুব বেশি সময়সাপেক্ষ নয়—কয়েক মাসের মধ্যেই সম্ভব।
তবে সাম্প্রতিক ইস*রায়ে*ল-ইরান সংঘর্ষ এবং সামরিক হামলার ফলে এই enrichment‑এর কাজ ১-২ বছরের মতো হয়ত বিলম্বিত হবে। কিন্তু এই বিলম্ব ইরানি পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থামিয়ে রাখতে পারবে না। কেননা ইরানের সরকারটি মধ্যপ্রাচ্যের রিজিওনাল পাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে উদ্গ্রীব। তাই ইরান নতুন করে enrichment কেন্দ্র চালু করছে এবং ৬০% পর্যায়ের ইউরেনিয়াম উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে।
বর্তমান ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা ইঙ্গিত দিচ্ছে, ২০২৬-২০২৭ সালের মধ্যে ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচিতে আরও বড় অগ্রগতি অর্জন করবে। বিশেষ করে, weapon-grade ইউরেনিয়াম মজুদে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসতে পারে। এছাড়া ২০২৭-২০২৯ সময়ের মধ্যে ইরান অন্তত ১-২টি কার্যকর পারমাণবিক ডিভাইস তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও তারা তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে না, তবে সামরিক ও কূটনৈতিক মহলে এই তথ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
অবশ্য অভ্যন্তরীণভাবে ইরানি সরকার নানাবিধ সংকটে জর্জরিত। দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ডস কর্পস (IRGC) এবং ধর্মীয় নেতাদের পরিবারবর্গ। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত অবনতির দিকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, মদ্যপানের হার বিবেচনায় ইরান বিশ্বে ১৯তম স্থানে রয়েছে, যেখানে রাশিয়া ৩০তম এবং সৌদি আরব ১৮৪তম অবস্থানে আছে। ইরানে মাদকাসক্তির হারও বিশ্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। দেশের তেল ও গ্যাস অবকাঠামোর বেশিরভাগই শত বছরের পুরনো এবং আধুনিকায়নের অভাবে জরাজীর্ণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ইরানের ৮০% এরও বেশি জনসংখ্যার বয়স ৩৫ বছরের নিচে, যারা ১৯৭৯ সালের বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু দেশ শাসন করছে ৬০/৭০ বছর ঊর্ধ্ব একদল ধর্মীয় নেতা। এই প্রজন্মগত বিভাজন আগামী ২/৩ বছরে ইরানে আরও ব্যাপক গণঅসন্তোষের জন্ম দিতে পারে। মদত দেওয়ার জন্য মার্কিন-ইস*রায়ে*ল তো থাকছেই!
~~~~~~~~~~~~
[আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যে সমাপ্ত, আলহামদুলিল্লাহ]
আকীদা, আয়াতুল্লাহ, ইরান, কেমন, নাসিবী, বিপ্লব, মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাফিজী, শিয়া, সম্পর্ক, সরকার, সুন্নী, হিজবুল্লাহআল্লাহ হচ্ছে সেই সত্য যার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা যায় এবং এটি মস্তিস্কপ্রসুত কোনো ধারণা না

অনেক মানুষই বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, কিন্তু তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ ভিত্তি থেকে যে আল্লাহ (শুধুমাত্র) একটি চিন্তা, (সর্বজনীন) সত্য না।
এধরনের ব্যক্তিগণ কোনো সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাসকে কোনো উপাস্যের উপর বিশ্বাসের মতোই মনে করে; তারা বলে, এটি একটি সুন্দর চিন্তা। এটি এ জন্য, যতক্ষন মানুষ এটি কল্পনা করবে, এতে বিশ্বাস করবে এবং এর শক্তির কাছে সমর্পণ করবে, ততক্ষন সে এ ধারণার উদ্দীপনায় মন্দ হতে নিজেকে দুরে রাখবে এবং কল্যাণে নিকটবর্তী হবে। তাই এটি একটি অন্তর্নিহিত নিরোধক যা বাহ্যিক নিরোধক হতে বেশি প্রভাব রাখে। তাই তারা সমর্থন করে যে মানুষের অবশ্যই আল্লাহতে বিশ্বাস করা উচিত এবং তারা এই বিশ্বাসে উৎসাহ প্রদান গুরুত্বপূর্ণ মনে করে যাতে মানুষ সৎকর্মপরায়ণ ও উদ্ধুদ্ধ থাকে, যাকে তারা ‘ধর্মীয় বাঁধা’ (الوازع الديني) বলে থাকে!!
এ ধরণের ব্যক্তিদের খুব সহজেই নাস্তিকতার দিকে টানা যায়, এবং ধর্মত্যাগের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায় যখন তাদের মানসিকতা এধরনের ধারণার অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় নিপতিত হয়। যদি মানুষ এই উপস্থিতিকে অনুভব না করে এবং এ উপস্থিতির প্রভাবকে উপলব্ধি না করে তাহলে সে একজন উপাস্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে এবং ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলাকে অবিশ্বাস করবে। উপরন্তু, আল্লাহ একটি চিন্তা মাত্র, কোনো সত্য নয়, এটি বিশ্বাস করার মাধ্যমে কল্যাণ (goodness)ও একটি সত্যহীন চিন্তায় পরিণত হয়, একইভাবে মন্দ (evil)ও একটি সত্যহীন চিন্তায় পরিণত হয়। এই ধরণের বিশ্বাস (ঈমান) এই লোকদের এই কারণেই তৈরি হয়েছিল যে তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) অর্জনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি (‘আকল) ব্যবহার করেনি, এবং, মানব, জীবন ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে সহজাত প্রশ্ন, (তথা) পার্থিব জীবনের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জীবন সম্পর্কে, এবং এর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জীবনের সাথে এর সম্পর্কের ব্যপারে সহজাত প্রশ্নগুলোর ফলে উদ্ভূত বড় সমস্যাটির বুদ্ধিবৃত্তিক সমাধানের জন্যও তাদের পরিচালিত করা হয়নি।
বরং তাদের শিক্ষকের ইচ্ছানুযায়ী সমাধানটি তাদের শেখানো হয়েছিল, তাই তারা এই সমাধানটি গ্রহণ করেছিল এবং তারা যা বিশ্বাস করত তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা না পেয়েই এতে বিশ্বাস করতে থাকে। তাদের অনেকেই তাদের মন ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের উত্তর দেওয়া হয়েছিল যে ধর্ম মনের বাইরে এবং (তাদের) নীরব থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল।
সঠিক কথা হলো, আল্লাহ তাআলা একটি সত্য, কোন ধারণা নয়; এবং তাঁর অস্তিত্ব (চিন্তা করে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে) স্পর্শ করা যায় এবং বোঝা যায়, যদিও তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা’আলার) স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব। তুমি কি দেখতে পাও না যে মানুষ তার ঘরের ভেতরে বসে আকাশে বিমানের শব্দ না দেখেও শুনতে পারে?
তবে, সে শব্দ শুনে এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, যদিও সে এটি দেখেনি এবং এর স্বরূপ অনুভব করেনি। তাই সে শব্দ শুনে আকাশে একটি বিমানের উপস্থিতিতে বিশ্বাস করে। অন্যকথায়, সে নিশ্চিতভাবে এবং সন্দেহাতীতভাবে, বিমানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সুতরাং, বিমানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা তার স্বরূপ বোঝার চেয়ে আলাদা বিষয়। এর স্বরূপ বোঝা যায়না কারণ স্বরূপ ইন্দ্রিয় কর্তৃক অনুভূত হয়নি; অন্যদিকে এর অস্তিত্বের উপলব্ধি তার শব্দের অনুভূতি থেকে নিশ্চিত। সুতরাং, বিমানের অস্তিত্ব একটি সত্য এবং (নিছক) কোনো ধারণা নয়।
বোধগম্য এবং অনুভূত জিনিসের ক্ষেত্রেও এটিই প্রযোজ্য। তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিত কারণ তাদের পর্যবেক্ষন করা যায় এবং তারা অনুভূত। তাদের ব্যতীত অন্য কিছুর উপর তাদের নির্ভরশীলতাও নিশ্চিত, কারণ এটি পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং অনুভূত। আকাশের নক্ষত্রগুলোর ব্যবস্থার প্রয়োজন; এবং যারা কোনো কিছু পোড়াতে চায় তার জন্য তাদের আগুনের প্রয়োজন। প্রতিটি বোধগম্য এবং অনুভূত জিনিসের ক্ষেত্রে এটিই হয় কারণ সে নিজের নয়, অন্যের প্রয়োজন। নির্ভরশীল জিনিস চিরন্তন হতে পারে না, কারণ যদি এটি চিরন্তন হত তবে এটি নিজের ছাড়া অন্যের প্রয়োজন হত না। এটি নির্ভরশীল হওয়ার অর্থ হল এটি চিরন্তন নয়।
অতএব, সমস্ত বোধগম্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত। কারণ যা চিরন্তন (আজালি) নয় তার অর্থ হল এটি একজন স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট। এই সৃষ্ট জিনিসগুলোর সংবেদন, সেইসাথে প্লেনের শব্দের সংবেদনও নিশ্চিত। একইভাবে, এই সৃষ্ট জিনিসগুলোর (বস্তুর) স্রষ্টার অস্তিত্ব, যেখান থেকে তারা আসে, সেই প্লেনের অস্তিত্বের মতোই যেখান থেকে শব্দ এসেছে; যা একটি সুনিশ্চিত বিষয়। সুতরাং, এই সৃষ্ট বস্তুগুলোর স্রষ্টার অস্তিত্ব একটি সুনিশ্চিত বিষয়। অতএব, মানুষ তার সংবেদন এবং চিন্তার মাধ্যমে সৃষ্ট জিনিসগুলো (বস্তুকে) উপলব্ধি করেছে; এবং সে তাদের অনুভূতি থেকে তাদের স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছে। সুতরাং, স্রষ্টার অস্তিত্ব এমন এক সত্য যা সংবেদনের মাধ্যমে মানুষ তার অস্তিত্বকে ধরতে পেরেছে; এবং এটি নিছক কোনো ধারণা নয় যা মানুষ তার মনে কল্পনা করেছে।
Taken from the Book “Islamic Thought”
পপুলিস্ট দাওয়াহ ইসলামী পুনর্জাগরণের পথকে বাধাগ্রস্থ করে তোলে

সোশ্যাল মিডিয়ার আজ সবার জন্য জনপ্রিয় হবার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আজকের যুগে যেন একটাই মন্ত্র: “জনপ্রিয়তা মানেই টাকা”। যত বেশি সাবস্ক্রাইবার বা ফলোয়ার তত বেশি সফলতা—এই ধারণা আজকের প্রজন্মের স্বপ্ন হয়ে উঠেছে। আজকের তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর যুগে, পপ কালচার দর্শনীয় ও মোহময় উদ্দীপনার মাধ্যমে চিত্রসংস্কৃতি ও রুচিসংস্কৃতি গঠনে বড় ভূমিকা রাখছে।
ধূসর শক্তি (Gray Power)
গত এক দশকে সোশ্যাল মিডিয়ার নতুন এক প্রভাবশালী শক্তি উঠে এসেছে— সেলেবগ্রাম বা ইউটিউবারদের মতো ইনফ্লুয়েন্সাররা, যারা ধূসর সম্প্রদায় ও তথাকথিত ‘সংবেদনশীলদের’ প্রতিনিধিত্ব করে, এবং মূলত পুঁজিবাদী শক্তির প্রতিনিধি হয়ে কাজ করে। যদিও এটা নতুন কিছু নয়, তথাপি ডিজিটালাইজেশনের যুগে এই ধূসর নৈতিক শক্তি (gray moral force) আরও পরিপক্ব হচ্ছে।
স্নায়ুযুদ্ধ (cold war) পরবর্তী যুগে, এই শক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের সাথে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে টার্গেট করা বাজারদেশগুলোতে পুরাতন নৈতিক মূল্যবোধকে প্রশমিত করা যায়। বিশেষ করে যখন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জগতে এগিয়ে চলেছে, তখন তাদের পশ্চিমা নৈতিক মূল্যবোধ বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য করে তোলা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন দার্শনিক আয়ন র্যান্ড বলেছেন:
“The cult of moral grayness is a revolt against moral values.” অর্থাৎ, ধূসর নৈতিকতা আসলে নৈতিকতার বিরুদ্ধেই এক বিদ্রোহ।
এর ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্যে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি ২০শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনপ্রিয় সংস্কৃতি তৈরি করতে সফল হয়েছে; যা এশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে এবং এখন কোরিয়া তার K-POP জোয়ারের মাধ্যমে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে। যেমনটি দেখা যাচ্ছে, চলচ্চিত্র ও শিল্প ধীরে ধীরে নৈতিকতার সাদা-কালো বিভাজন থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে সরে আসছে, তেমনি করে সেগুলো ক্রমশ আরও বেশি ধূসর ছায়ায় বা অস্পষ্টতায় পরিণত হচ্ছে। এই মূল্যবোধগুলিকে অস্পষ্ট করার লক্ষ্য হল এগুলিকে বিশ্ববাজারে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।
অবশেষে জনপ্রিয়তা হয়ে ওঠে নতুন এক নৈতিক মানদণ্ড, যা উদ্ভূত হয়েছে সেকুলার সাংস্কৃতিক শিল্পের হাত ধরে। পপ সংস্কৃতি যেকোনো বিষয়ের গুণগত মান ও নৈতিকতা উপেক্ষা করে শুধুমাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে ‘চিত্র’ ও ‘রুচি’র জনপ্রিয়তাকেই গুরুত্ব দেয়। বিজ্ঞাপনগুলো এই দর্শনীয় ভিজ্যুয়াল স্টাইলের মাধ্যমে বাজারকে প্রভাবিত করে এবং ধূসর শক্তিকে (Gray Power) লালন-পালন করে। সীমাহীন সৃজনশীলতা’ স্লোগানকে ভিত্তি করে আদর্শিক বিবেচনায় দুর্বল কিছু শিল্পী ও নির্মাতাদের মধ্যে শিল্প ও সৃজনশীলতার অপব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়।
জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে হিজরাহ কমিউনিটি:
সমস্যাটি হলো, এই জনপ্রিয় সংস্কৃতি শুধু সাধারণ মানুষকেই প্রভাবিত করে না, বরং তা মুসলিম সমাজের সেই অংশকেও প্রভাবিত করে যারা ইতোমধ্যে পরিবর্তনের প্রতি সচেতন – awareness to change (hijrah), যাদেরকে ইন্দোনেশিয়ায় ‘হিজরাহ কমিউনিটি’ বলা হয়ে থাকে। ইসলামী দাওয়াত ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির এই সম্মিলন মুসলিম তরুণদের মধ্যে একটি ইসলামী পপুলিজম (জনপ্রিয়তাবাদ) তৈরি করেছে।
এর ফলে হিজরাহ কর্মীরা জনপ্রিয়তার প্রভাব (popularity syndrome) থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না। এমনকি তারা ধূসর মনোভাব (graying attitudes) থেকেও নিরাপদ নয়। দাওয়াহ সফল কিনা—তা এখন পরিমাপ করা হয় ফলোয়ার সংখ্যা এবং কনটেন্ট ভাইরাল হওয়ার উপর, ইসলামী শিক্ষার গুণমান ও পদ্ধতির উপর নয়, যা নবী ﷺ এর উত্তরাধিকার অনুযায়ী হওয়া উচিত। এর ফলস্বরূপ, দাওয়াহ আজ জনপ্রিয়তার সংকট দ্বারা প্রভাবিত। অনেক আলেম, দাঈ, এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন। তারা দাওয়াহকে সৃজনশীল শিল্পে রূপ দিয়েছেন এবং নিজেরাই হারিয়ে যাচ্ছেন ধূসর সংস্কৃতির প্রবাহে আড়ালে (gray wave)।
আবু ইসহাক আশ-শাতিবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:
“الصالحين من قلوب الناس آخر ما يخرج: حب السلطة وحب الظهور”
“নেককারদের অন্তর থেকে নেতৃত্বপ্রেম ও পরিচিতির ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত যায় না, তা কেবল মৃত্যুর সময়ই দূর হয়।” যারা হিজরাহ করে (পরিবর্তনের প্রতি সচেতন হয়েছে) হঠাৎ করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তাদের ঘটনা আমাদের জন্য শিক্ষা। দাওয়াহর প্রভাব ছড়ানোর বদলে তারা ধূসর মনোভাবকে জোরদার করে তোলে, যা পশ্চিমা ধারণা ‘religious moderation’-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—এটি ইসলামী পরিচয়কে দুর্বল ও অস্পষ্ট করার একটি বৈশ্বিক পরিকল্পনা।
Wunderman Thompson Intelligence কর্তৃক মালয়েশিয়ার Muslim Intel Lab-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত “The New Muslim Consumer” শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ২৫ কোটি মুসলমানের মধ্যে আজকের প্রজন্ম তাদের পিতামাতার তুলনায় একেবারে ভিন্নধর্মী জীবন যাপন করছে। এই পরিবর্তনের পেছনে দুটি বিশাল প্রভাব কাজ করেছে: একটি হলো ধর্মীয় চেতনার পুনরুজ্জীবন (আস্তিকতা/ধর্মপরায়ণতা) এবং অপরটি হলো পশ্চিমা ধাঁচের ভোক্তাবাদ বা ভোগবাদের প্রসার।
এই প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম তরুণদের মধ্যে ইসলাম এখন একটি জনপ্রিয় জীবনধারা হয়ে উঠেছে, যদিও তা মূলত বাহ্যিক এবং ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদের ধর্মপরায়ণতা তাদেরকে পশ্চিমা বা কোরিয়ান বিনোদন সামগ্রী ভোগ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।
যেমন “হিজরাহ কে-পপার” নামক একটি প্রবণতা, যেখানে একদিকে তারা ধার্মিক মুসলিম হওয়ার দাবি রাখে, কিন্তু অন্যদিকে তারা কোরিয়ান বিনোদনের ভোক্তা হিসেবেও থাকতে চায়। এই দ্ব্যর্থতা (ambiguity) এক ধরনের ধূসর মনোভাবের (gray attitude) জন্ম দেয়, যা তাদের জন্য পুঁজিবাদীদের ‘বাজার হিসেবে উপনিবেশিত’ করা সহজ করে তোলে—যাতে তারা ধর্মনিরপেক্ষ জীবনধারার পণ্যের চিরন্তন ভোক্তায় পরিণত হয়।
অন্যদিকে, জনপ্রিয় সংস্কৃতির প্রবণতা হলো—ইসলামের বার্তাকে এমনভাবে হালকা করে উপস্থাপন করা, যাতে তা সাধারণ মানুষের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা কোনো বইয়ের দোকানে যাই, তাহলে দেখতে পাবো যে “হিজরাহ” শব্দটি লেখা এক সারি বই সহজেই বেস্টসেলার শেলফে প্রদর্শিত হচ্ছে। ধর্মীয় বইগুলো সাধারণত যেভাবে গম্ভীর ও আনুষ্ঠানিকভাবে লেখা হয়, তার বিপরীতে জনপ্রিয় হিজরাহ বইগুলোতে পপ-স্টাইলের প্রচ্ছদ থাকে, যেগুলো টিনএজ প্রেমের গল্প বা কমিক বইয়ের মতো চিত্রায়নে সাজানো হয় এবং ভাষাও হয় হালকা ও স্বচ্ছন্দ। একই রকম অবস্থা সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা ইনস্টাগ্রামে #hijrah হ্যাশট্যাগটি টাইপ করি, তখন প্রায় ৭ কোটি পোস্ট দেখা যায় যেগুলো হিজরাহ বিষয়ে আলোচনা করে এবং সেগুলোতে আকর্ষণীয় গ্রাফিক ডিজাইন ও হালকা ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও ইসলামী দাওয়াহ—এই দুটি ধারা যখন মুসলিম যুবসমাজের মধ্যে মিলিত হয়, তখন তা সবসময় নেতিবাচক হয় না। বরং এই ঘটনাটি আসলে দুটি সংস্কৃতির মধ্যকার মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব (সিরা‘উল ফিকর- صراع الفكر) বা চিন্তার সংঘর্ষকে প্রকাশ করে। তাই, এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রয়োজন এমন দাওয়াহকারীদের (প্রজ্ঞাবান দাঈদের), যারা আদর্শিকভাবে পরিপক্ব এবং মূল্যবোধ ও পরিচয়সংক্রান্ত এই ধরনের টানাপোড়েনে সচেতন। যাতে করে ইসলামই অন্য সংস্কৃতির রঙে রঞ্জিত হয়ে না যায়, বরং ইসলামী আদর্শই সমাজকে রঞ্জিত করে এবং তা সমাজে বৃহৎ পরিবর্তন আনতে পারে।
জনপ্রিয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী দাওয়াহ পরিচালনায় সক্ষম দাওয়াহ কর্মীদের যোগ্যতা হলো—তাদের মধ্যে একটি শক্তিশালী চিন্তাগত সংবেদনশীলতা থাকতে হবে, যেন তারা ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামী মূল্যবোধের পার্থক্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারেন; একইসাথে জনপ্রিয় শৈলী (popular styles) ব্যবহার করে সৃজনশীল পদ্ধতি ও উপকরণের ব্যবহারে যেন কোনো ঘাটতি না থাকে। তদুপরি, দাওয়াহ কর্মীদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, দাওয়াহর সফলতার মানদণ্ড কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব কিংবা দাওয়াহর গণগ্রহণযোগ্যতা বা মানুষের প্রশংসা নয়, বরং তা নির্ভর করে শরীয়াহর মানদণ্ড ও মূল উদ্দেশ্যের ওপর—যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করে। দাওয়াহ কর্মীদের উচিত ইসলাম নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকৃত পরিবর্তনের পথ অবলম্বন করা, অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থতা (ambiguity) পরিহার করা এবং দাওয়াহতে ধূসর মনোভাব (gray attitude) থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:
«إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام»
নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এদের মাঝে কিছু বিষয় আছে যা সন্দেহজনক, যা অধিকাংশ মানুষ জানে না। তাই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে রক্ষা করে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়, সে হারামের মধ্যেই পড়ে যায়।” (বুখারী ও মুসলিম)
কায়েস আবু মুহাম্মদ কর্তৃক অনুবাদকৃত
ইরানের উপর পরিকল্পিত হামলা – কারণ ও প্রেক্ষাপট

বিশ্বাসঘাতকতা, ভুল হিসাব, অথবা কৌশলগত কারণেই হোক না কেন, ফলাফল অনস্বীকার্য: ১৩ জুন ইরানের সামরিক ও পারমাণবিক অবকাঠামোর উপর ইসরায়েলের ভোরবেলা আক্রমণ তেহরানের জন্য কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তার উপর আঘাত। কয়েক ঘন্টা ধরে চালানো এই হামলায় ইরানের সামরিক উচ্চ কমান্ড এবং শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানীদের একাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
নিহতদের মধ্যে ছিলেন ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এর কমান্ডার-ইন-চিফ মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি; সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ বাঘেরি; ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন কৌশলের স্থপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির আলী হাজিজাদেহ; এবং কুদস বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল ইসমাইল কানি। এছাড়াও নিহত হয়েছেন সর্বোচ্চ নেতার একজন সিনিয়র উপদেষ্টা অ্যাডমিরাল আলী শামখানি এবং পারমাণবিক শক্তি সংস্থার প্রাক্তন প্রধান ফেরেয়দুন আব্বাসি দাভানি সহ পারমাণবিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল এবং ইরানের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট পারমাণবিক পদার্থবিদ।
ইসরায়েলি অভিযানের মাত্রা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত অর্থাৎ একাধিক সামরিক ও পারমাণবিক স্থাপনায় আঘাত হানা, ইরানসহ বিশ্বের অনেককেই দৃশ্যত অস্থির করে তুলেছে। তেহরান এবং ইসফাহান থেকে প্রচারিত ভিডিওগুলোতে বিমান প্রতিরক্ষা তৎপরতার স্পষ্ট অভাব দেখা যাচ্ছে – আক্রমণের তীব্রতা সত্ত্বেও ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র বা কামানের কোনও উৎক্ষেপণ হয়নি। ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষায় প্রচুর বিনিয়োগকারী একটি দেশের জন্য, আকাশ প্রতিরক্ষার এই দুর্বল রূপ ছিল দুঃর্ভাগ্যজনক।

এই হামলার তালিকাটি পরিস্কারভাবে ইরানের সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সের নীলনকশাকে সামনে রেখে আক্রমনের একটি প্রয়াস। লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল নাতানজে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ স্থাপনা, ইসফাহান ও খোন্দাবের পারমাণবিক স্থাপনা এবং আরাক, ফোরদো, শিরাজ এবং তাবরিজের অতিরিক্ত গবেষণা কেন্দ্র। যদিও নাতানজে দৃশ্যমান কাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে, তবুও তেজস্ক্রিয়তা নির্গমণের অনুপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে হয় সেন্ট্রিফিউজ হলগুলি অক্ষত ছিল অথবা আগেভাগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পাহাড়ের গভীরে থাকা ফোরদো সম্ভবত গুরুতর ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে – এর দুর্গটি প্রচলিত বাঙ্কার-বাস্টারদের নাগালের বাইরে অবস্থিত।
পারমাণবিক স্থাপনা ছাড়াও, ইসরায়েল ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র, রাডার স্থাপনা এবং বেশ কয়েকটি ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র (SAM) ব্যাটারিতে হামলা চালানো হয়েছে। তেহরানের জেনারেল স্টাফ সদর দপ্তর, হামাদানের নোজেহ বিমানঘাঁটি এবং রাজধানী জুড়ে আইআরজিসি স্থাপনা সহ সামরিক কমান্ড হাবগুলিতেও হামলা চালানো হয়। এমনকি আইআরজিসি কমান্ডারদের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত আবাসিক এলাকাগুলি – যেমন শাহরাক-ই মহল্লাতি, ঘেয়তারিয়েহ এবং নিয়াভারান -ও বাদ পড়েনি।

বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক প্রভাব সম্ভবত আরও তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষ্যবস্তুতে থাকা ব্যক্তিরা মূলত আইআরজিসির অভ্যন্তরে একটি কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, যারা প্রয়াত জেনারেল কাসেম সোলাইমানির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। প্রভাবশালী কিন্তু ধর্মযাজক নন এমন এই গোষ্ঠীটি দীর্ঘদিন ধরে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের বিষয়ে যেকোনো কূটনৈতিক আপসের বিরোধিতা করে আসছিল। তাদের অপসারণের ফলে শাসনব্যবস্থার মধ্যে একটি কট্টরপন্থী অংশ দুর্বল হয়ে পড়েছে – যা অজনপ্রিয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। জনসাধারণের শোক প্রচুর হবে, তবে বন্ধ দরজার পিছনে, ইরানের নেতৃত্বের কেউ কেউ তাদের বিদায়কে স্বাগতও জানাতে পারেন।
যুক্তরাষ্ট্র ইরান এবং ইসরাইলের সাম্প্রতিক যে অস্থিরতা তা বোঝার জন্য আমাদের গত এক দশক ধরে এ অঞ্চলে ইরানের ভূমিকা, যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে ইরানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে এবং ইসরাইল কিভাবে এখানে প্রেক্ষাপটে এল তা বোঝাটা জরুরি।
সর্বপ্রথম আমাদের ২০১৫ সালে ইরান ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত পারমাণবিক চুক্তি হওয়ার সময়টি পর্যালোচনা করতে হবে। এরপর আমাদের ২০১৮ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই চুক্তি থেকে বের হয়ে আসার উপর আলোকপাত করতে হবে। এরপর আমরা বর্তমান পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করতে পারবো।
এছাড়া আমরা এরও পূর্বে ইরাক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দেখতে পেয়েছিলাম কিভাবে ইরানের সরকার ইরাকে তাদের প্রভাব বলয় খাটিয়ে সেখানে আমেরিকার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছিল। সিরিয়া ও ইরাক সীমান্তে সুন্নি গোষ্ঠীর উত্থান এর পেছনে ইতিপূর্বে মার্কিন মদদে ইরান কর্তৃক ইরাকে শিয়া গোষ্ঠীর উত্থান যে সম্পর্কিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মার্কিনিরা একটি সমস্যা সমাধান করতে যেয়ে আরেকটি সমস্যার তৈরি করে অর্থাৎ বুশের আমলের সমস্যার ঘানি শেষ পর্যন্ত ওবামাকে টানতে হয়।
২০১৫ সাল। সিরিয়া ও ইরাক সীমান্তে ইতোমধ্যে সুন্নি গোষ্ঠীর উত্থান পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত এবং একটি তথাকথিত ইসলামিক খেলাফত রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রাষ্ট্রটির প্রভাব বলয় যাতে সত্যিকার অর্থে বৃদ্ধি না পায় সেজন্য পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উঠে পড়ে লাগে এই গণআকাঙ্খাকে দমন করবার জন্য।
২০১৫ সালের ১৪ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরানের সাথে একটি পারমাণবিক চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি সম্পাদনের আরো বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনের এ চুক্তির ব্যাপারে প্রচন্ড আগ্রহ ও উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ময়দানে ইরানের প্রভাবকে আরো উন্মুক্ত করবার জন্য যাতে ইরানের জন্য সেখানে কাজ করা আরও সহজতর হয়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিধি নিষেধ থেকে অনেকটা মুক্ত হয়ে তার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তবে এ চুক্তির একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল সিরিয়ার জনগণের ইসলাম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাকে ধুলিস্যাৎ করবার জন্য ইরানকে ব্যবহার করা।
যেসব কারণে ২০১৮ সালে ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের সাথে ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল:
ক. ওয়াশিংটন সৌদি আরব এবং তুরস্ককে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে নিয়ে আসে। তুরস্ক এই অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। ২০১৬ সালে, তুরস্ক “ইউফ্রেটিস শিল্ড” অপারেশন শুরু করে এবং ২০১৮ সালের মার্চ মাসে, তারা “অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চ” চালু করে। এটি সৌদি আরবের আঞ্চলিক ভূমিকার অতিরিক্ত ছিল। ফলস্বরূপ, সিরিয়ায় ইরানের আর কোনও প্রধান ভূমিকা পালনের প্রয়োজন ছিল না এবং এটি হ্রাস করতে হয়েছিল। ট্রাম্প ঠিক এটিই করেছিল; তিনি এই অঞ্চলে ইরানের ভূমিকা হ্রাস করেছিলেন, তাকে একটি প্রধান খেলোয়াড় থেকে একটি গৌণ বা পরিপূরক ভূমিকায় রূপান্তরিত করেছিল।
খ. ইউরোপীয় দেশগুলিও ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তির পক্ষ ছিল এবং এর প্রধান সুবিধাভোগী ছিল। তবে, ট্রাম্প চাননি যে ওবামা প্রশাসনের সময় স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে ইউরোপ উপকৃত হোক, তাই তিনি এটি বাতিল করে দেন।
এইভাবে, ট্রাম্প ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি থেকে তার প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন, কারণ এই অঞ্চলে ইরানের ভূমিকা হ্রাস করার জন্য নতুন শর্তের প্রস্তুতির জন্য চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করা আমেরিকার স্বার্থের পক্ষে ছিল।
সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখতে পেলাম ট্রাম্প প্রশাসন আবারও ইরানকে সমঝোতার টেবিলে ডাকছে এবং অনেকটা বলপ্রয়োগ করে তাদের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতায় পৌছতে চাচ্ছে এবং দ্রুত চাচ্ছে। এই সমীকরণে ইসরাঈল ঢুকে পড়ে কারণ নেতানিয়াহুর ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নিজস্ব কিছু অভিলাষ রয়েছে। ইসরাঈল ও ইরানের যুদ্ধ যাতে আরো ছড়িয়ে না পড়ে কিংবা দীর্ঘায়িত না হয় সেজন্য ট্রাম্প অনেক জোর করেই যুদ্ধে ঢুকে পড়ে এবং ইরানের নির্দিষ্ট কিছু টার্গেট ধ্বংস করার জন্য আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধবিমান বি২ বম্বার ব্যবহার করে। তবে এখানে ইরানকে আগেভাগেই জানিয়ে দেয়া হয় আমেরিকার উদ্দেশ্য কী। একইভাবে ইরানও কাতারে অবস্থিত মার্কিন ঘাটি আক্রমন করার বিষয়টি আগেভাগেই মার্কিনিদের জানিয়ে দেয়। সবশেষে ট্রাম্প অনেকটা জোর করেই যুদ্ধ সমাপ্তির ঘোষনা দেয় এবং ইরান ও ইসরাঈলের মধ্যে চিরতরে যুদ্ধবিরতিরও ঘোষণা দেয়। অপরদিকে ইরানও এই যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়, যদিও একই সময়ে গাজার নিরীহ মুসলিমরা প্রতিনিয়ত মারা পড়ছে।
এ সবকিছু দেখে খুব সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে আমেরকিা ও ইরান উভয়ের কেউই যুদ্ধে জড়াতে চায় না, বরং নিজেদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতার সম্পর্ক চায়। ট্রাম্প তার বর্তমান মেয়াদের মধ্যেই মধ্যপ্রাচের শান্তির দূত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তার ছলে বলে কৌশলে যেভাবে হোক না কেন। ইরান মুখে যদিও ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলে কিন্তু কাজে ঠিক তার উল্টোটিই করছে। এমনকি পারমানবিক শক্তি হবার ব্যপারেও ইরান পাবলিকলি কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করে না, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল উভয়ে তাদের পারমানবিক শক্তি টিকিয়ে রেখেছে এবং তা ধ্বংস করার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র NPT তে স্বাক্ষর করেছে, তারপরও তার পারমানবিক শক্তি ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহারের জন্য বহাল তবিয়তে রেখে দিয়েছে, আর ওদিকে অন্য কেউ সেই সক্ষমতা তৈরি করতে চাইলে তাদের লেকচার দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে বেড়াচ্ছে। এসকল ঘটনা আমাদের মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির গুরুত্বকেই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমনটি আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। [আনফাল: ৬০]