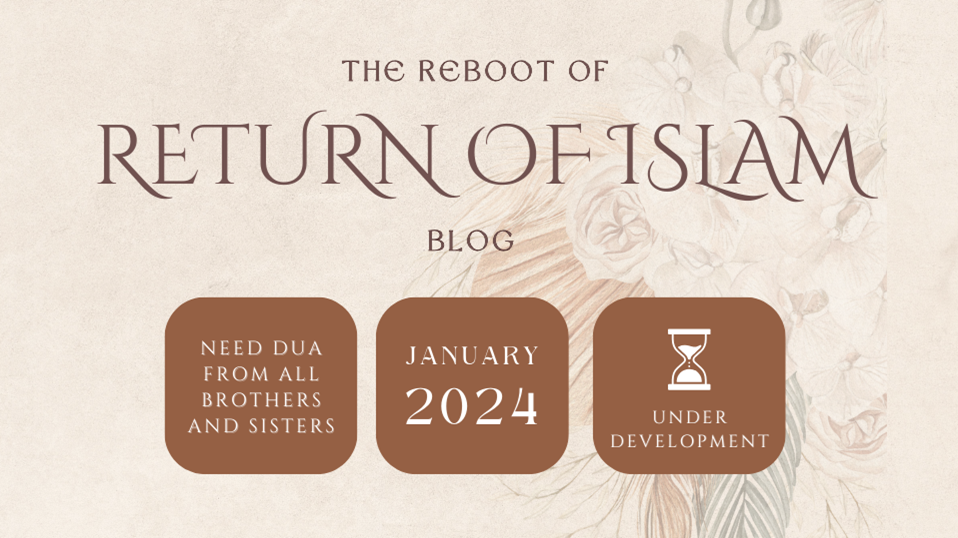ইরানের যেকোনো ইস্যু আসা মাত্রই এক শ্রেণির মানুষ ইরানিদের শিয়া মতবাদ নিয়ে এমনভাবে আলোচনা তোলেন যেন ইরানকে নিয়ে যাবতীয় সমস্যার কারণ তাদের শিয়া মতবাদ। কারো কারো আক্বীদাগত উত্তেজনা এই সময়গুলোতে এতই বৃদ্ধি পায় যে, মনে হয় ইস*রা*য়ে*লই হয়ত আহলে সুন্নাহ ও সুন্নি মাজহাবগুলোর ভ্যানগার্ড হিসেবে ইরানের কুফরী আক্বীদাগুলোকে গুড়িয়ে দিচ্ছে!

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির সকল হিসাব-নিকাশ ছাপিয়ে কেবল শিয়া মতবাদ নিয়ে তারা মেতে থাকে।
তাই ইরানি শাসকদেরকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের আগে এই আক্বীদাগত বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত কিছু সত্য তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি।
বাস্তবতা হলো, শিয়া মতবাদ শুরুতে রাজনৈতিক বিরোধই ছিল। এই রাজনৈতিক বিরোধ পরবর্তীতে বৃহত্তর ফিকহী বিরোধে রূপান্তরিত হয়। গত ১০০ বছরে এই বিরোধটিকে অনেকটা আলাদা সম্প্রদায়গত বিরোধ হিসেবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।
ঐতিহাসিকভাবে সুন্নি স্কলাররা কখনোই শিয়াদেরকে ঢালাওভাবে কাফের বা অমুসলিম বলেননি। বরং সুনির্দিষ্ট আক্বীদাগত ভ্রষ্টতার শিকার ব্যক্তিদের কুফরের ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন, ইমাম আল-গাজ্জালী (রহ.) তাঁর “ফাদায়িহ আল-বাতিনিয়্যাহ” বইতে বলেছেন:
“أما الإمامية الاثنا عشرية فليسوا كفارًا ولا مرتدين، وإنما هم فساق مبتدعون”
অর্থ: “ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া [বর্তমান ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া] কাফের বা মুরতাদ নয়; বরং তারা বিদআতী ফাসিক।”
অর্থাৎ গাজ্জালী (রহ.) ইসনা আশারিয়া [ইরানের এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ] শিয়া বিদআতী আখ্যা দিলেও কুফরির অভিযোগ করেননি, তাদেরকে বিদআতী ও পাপাচারী বলেছেন।
শিয়াদের বিষয়ে অন্যতম কঠোর ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) তাঁর “মাজমু’ আল-ফাতাওয়া”-তে বলেছেন:
“التشيع ليس كفرًا مطلقًا، بل فيه تفصيل: فمن غلا في الأئمة وجعلهم مثل الأنبياء أو فوقهم، أو كفر الصحابة، فهو كافر”
অর্থ: “শিয়াবাদ সর্বদা কুফর নয়; এতে পার্থক্য আছে: যে ইমামদের নবীদের সমকক্ষ বা ঊর্ধ্বে স্থান দেয় অথবা সাহাবাদের কাফের বলে, সেই কাফের।”
ইমাম ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহ.) তাঁর “আস-সাওয়াইক আল-মুহরিকা” তে বলেছেন:
“الرافضة إذا سبّوا الصحابة أو كفّروهم فهم كفار”
অর্থ: “রাফিজি (চরমপন্থী শিয়া) যদি সাহাবাদের গালি দেয় বা কাফের বলে, তাহলে তারা কাফের।”
বর্তমানকালের সুন্নি স্কলার বা প্রতিষ্ঠানগুলোর ফতোয়াও প্রায় একই ধরনের। যেমন, দারুল ইফতা আল-মিসরিয়্যাহ (আল-আজহার)-এর ফতোয়া: “আহলুস সুন্নাহ ওয়া আল-জামা’আহ ইসনা আশারিয়া শিয়াদেরকে ‘কাফের’ বলে না, যতক্ষণ তারা ইসলামের মূল স্তম্ভে বিশ্বাসী।” (ফতোয়া নং ২৩৪১, ২০১২)।
সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি শেখ আবদুল আজিজ বিন বাজ (রহ.) বলেছেন: “কোনো শিয়া যদি সাহাবীগণকে ভালোবাসে ও কুরআন অপরিবর্তিত বলে বিশ্বাস করে, তার সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা জায়েজ।” [মাজমু’ ফাতাওয়া, ২/৩০৪]
ক্লাসিকাল স্কলারগণের ও বর্তমান কালের এসব ফতোয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়:
#কখন_শিয়াকে_“কাফের”_বলা_হয়েছে?
১. কুরআন বিকৃতির বিশ্বাস:
– যে বলে কুরআন অসম্পূর্ণ বা বিকৃত হয়েছে [ইবনে তাইমিয়াহ, দার আল-তা’আরুদ, ১/৩৫৬।]
২. সাহাবিদের (রা.) প্রতি চরম শত্রুতা:
– আবু বকর, উমর (রা.)-কে কাফের বলা বা তাদের প্রতি অভিশাপ দেওয়া [ইবনে তাইমিয়াহ, মিনহাজ আল-সুন্নাহ, ৪/৫৯০]।
৩. ইমামদের অতি ভক্তিবাদ:
– ইমামদের নবুওয়ত বা ইলাহী গুণাবলি দেওয়া [আল-শাহরাস্তানি, আল-মিলাল ওয়া আল-নিহাল, ১/১৯৩]।
#যাদের_“কাফের”_বলা_হয়নি
– সাধারণ ইসনা আশারিয়া শিয়া: যারা সাহাবিদের সমালোচনা করে না বা কুরআন বিকৃতি বিশ্বাস করে না [ইবনে আবিদিন, রাদ্দ আল-মুহতার, ৪/২৬৩]
– জাফরি ফিকহ অনুসারী: যারা শুধু ফিকহি পার্থক্য রাখে [আল-আজহারের ফতোয়া, ১৯৫৯]।
অর্থাৎ বাংলাদেশের ফেসবুক স্কলারদের মতো করে কোনো কালেই সুন্নি স্কলারগণ শিয়াদেরকে ঢালাওভাবে কাফের বলেননি; বরং সুনির্দিষ্ট আক্বীদাগত ভ্রষ্টতা (কুরআন বিকৃতি, সাহাবিদের প্রতি শত্রুতা, ইমামদের অতিমানবীকরণ)-কে কুফরের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ন্যায়সঙ্গত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।
শিয়া আসলে কারা?
ইতোমধ্যে ১ম পর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ক্ল্যাসিকাল সুন্নি স্কলাররা কখনোই শিয়াদেরকে ঢালাওভাবে “কাফের” বলেননি।

শিয়া ও সুন্নি বিভেদের বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এই পোস্টের সীমিত পরিসরে নেই। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে অন্য কোথাও বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইলো ইন’শা’আল্লাহ।
তবে বর্তমান ইসরায়েল ও ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শিয়াদের সম্বন্ধে ন্যূনতম যেটুকু আলোচনা এখন করা খুবই প্রয়োজন, সেটুকুই শুধু এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি।
আরবিতে “শিয়া” শব্দের অর্থ অনুসারী, সমর্থক বা কোনো দলের সদস্য। “শিয়া” শব্দটি এ ধরনের অর্থেই পবিত্র কুরআনে মোট ১১ বার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেছেন:
{وَاِنَّ مِنۡ شِيۡعَتِهٖ لَاِبۡرٰهِيۡمَۘ}
এবং অবশ্যই ইবরাহীম ছিল তারই অন্যতম শিয়া (অনুসারী/দলের লোক)। [আল কুরআন ৩৭:৮৩]
একইভাবে, সূরা আনআম: ৬৫; সূরা সাফফাত : ৮৩; সূরা কাসাস : ১৫ ইত্যাদি আয়াতেও শিয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
তবে পারিভাষিক অর্থে শিয়া শব্দটি “শিয়াতু-আলী” (রা.) অর্থাৎ মহান সাহাবী আলী (রা.)-এর অনুসারী/সমর্থক হিসেবে পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.) বলেছেন,
{مَا جَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا جَاءَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ}
[সূত্র: “مَنَاقِبُ الإِمَام أَحْمَد بن حَنبَل” لابن الجوزي, ص ١٦٣]
অর্থ: “সাহাবীদের মধ্যে কারও সম্পর্কে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ন্যায় এত অধিক ফজিলত (মর্যাদা) বর্ণিত হয়নি।”
এমনকি, আলী (রা.)-এর সমর্থক বা তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের ফজিলতও বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। যেমন, আলী (রা.) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, মহানবী (সা.) আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মুমিন ব্যক্তিই আমাকে ভালোবাসবে, আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৭৮]
রাসূল (সা.) বলেছেন,
{من أحبّ عليّا فقدْ أحبّنِي ، ومن أحبّنِي فقد أحبّ اللهَ عز وجلَ ، ومن أبغضَ عليّا فقد أبغضَني ، ومن أبغضَني فقد أبغضَ اللهَ عز وجل}
যে ব্যক্তি আলীকে ভালোবাসে, সে আমাকেই ভালোবাসে; আর যে আমাকে ভালোবাসে, সে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি আলীকে ঘৃণা করলো, সে আমাকে ঘৃণা করে; আর যে আমাকে ঘৃণা করে, সে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ঘৃণা করে। [আলবানী, সিলসিলা সহীহাহ ১২৯৯]
রাসূল (সা.) বলেন,
{يا علي أبشر فإنك و أصحابك و شيعتك في الجنَّة}
অর্থ: “হে আলী, তোমার জন্য সুসংবাদ! নিশ্চয়ই তুমি, তোমার সঙ্গীরা এবং তোমার শিয়া (সমর্থক/অনুসারী)-রা জান্নাতে থাকবে।” [সূত্রসমূহ: আহমদ ইবন হাম্বল (فضائل الصحابة, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫৫); হিল্যাতুল আওলিয়া, খণ্ড ৪, পৃ. ৩২৯; মু’জাম আল-আওসাত, তাবারানী; মাজমাউ’জ যাওয়ায়েদ, খণ্ড ১০, পৃ. ২১-২২; আল-দারকুতনি, বিভিন্ন সনদে; আল-সাওয়ায়িক আল-মুহরিকাহ, ইবনে হাজার আল হাইতামী, অধ্যায় ১১, পৃ. ২৪৭; হাদীসটি বিপুল সংখ্যক সনদে বর্ণিত হলেও প্রতিটি সনদেই দুর্বলতা আছে। তবে হাদীসটি ফজিলত সংক্রান্ত হওয়ায় এবং অন্যান্য সহীহ হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় বহু সংখ্যক ক্ল্যাসিকাল সুন্নি স্কলার এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। আহলে সুন্নাহর সর্বসম্মত মত হলো, ফজিলতের ক্ষেত্রে “দুর্বল” সনদে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য, যদি না সেই হাদীসটি অন্যান্য সহীহ হাদীসের বিপরীত হয়।]
রাসূল (সা.) বলেছেন,
{“شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة}
অর্থ: “আলীর শিয়ারাই কিয়ামতের দিন প্রকৃত সফলকাম।” [সূত্রসমূহ: আল-মানাকিব (المناقب), আহমদ ইবনে হাম্বল; তারিখ দিমাশক (تاريخ دمشق), ইবনে আসাকির, খণ্ড ৪২, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৩২; তাফসীরে তাবারী, সূরা আল-বাইয়িনাহ (৯৮:৭) এর তাফসীরে উল্লেখিত; তাফসীর আল-দুররুল মানসুর, জালালুদ্দিন আল-সুয়ূতী, সূরা আল-বাইয়িনাহ (৯৮:৭); এই হাদীসটির সনদেও দুর্বলতা আছে। তবে হাদীসটি ফজিলত সংক্রান্ত হওয়ায় ক্ল্যাসিকাল সুন্নি স্কলারগণ এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।]
দেখা যাচ্ছে, এই হাদীসটি সূরা আল-বাইয়িনা (৯৮:৭)-এর তাফসীরে সুন্নি মুফাসসীরগণ উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট সুন্নি স্কলার ইমাম ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহ.) বলেন,
رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} (البينة: ٧)، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: “هُم أَنْتَ وَشِيعَتُكَ”. وَقَالَ: “يَا عَلِيُّ، أَنْتَ وَشِيعَتُكَ تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ، وَيَأْتِي عَدُوُّكُمْ غِضَابًا مُقْمَحِينَ”. قَالَ عَلِيٌّ: “مَنْ عَدُوِّي؟” قَالَ: “مَنْ تَبَرَّأَ مِنْكَ وَلَعَنَكَ، وَبَشَّرَى لِلسَّابِقِينَ إِلَى ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”. قَالَ عَلِيٌّ: “مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟” قَالَ: “شِيعَتُكَ يَا عَلِيُّ، وَمُحِبُّوكَ”.
ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন: যখন আয়াত “নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা” (সূরা আল-বাইয়িনাহ ৯৮:৭) নাযিল হলো, রাসূল (সা.) তখন আলী (রা.)-কে বললেন: “তারা হলেন তুমি ও তোমার শিয়া”।
রাসূল (সা.) আরও বললেন: “হে আলী, কিয়ামতের দিন তুমি ও তোমার শিয়ারা সন্তুষ্ট ও আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে উপস্থিত হবে, আর তোমাদের শত্রুরা ক্রোধান্বিত অবস্থায় ঘাড় বাঁকা করে আসবে।”
আলী (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন: “আমার শত্রু কারা?”
রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন: “যারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তোমাকে অভিশাপ দেয়। আর কিয়ামতের দিন ‘আরশের ছায়ায় আগে পৌঁছানোদের জন্য সুসংবাদ!”
আলী (রা.) বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা?”
রাসূল (সা.) বললেন: “হে আলী! তোমার শিয়া ও তোমার ভালোবাসার লোকেরা।”
[আল-সাওয়ায়িক আল-মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ১, পৃ. ২৪৬-২৪৭]
এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহ.) বলেন, “আলী (রা.)-এর শিয়ারা হলেন আহলে সুন্নত (সুন্নি), কারণ তারা শরিয়তের নির্দেশিত সীমার মধ্যে আহলে বাইতকে ভালোবাসেন। অন্যরা (সুন্নি ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠী) প্রকৃতপক্ষে আহলে বাইতের শত্রু; কারণ শরিয়তের সীমা লঙ্ঘনকারী ভালোবাসাই মহাশত্রুতা… আর আহলে বাইতের শত্রু ছিলেন খাওয়ারিজ ও সিরিয়ার অনুরূপ গোষ্ঠীগুলো; মুয়াবিয়া (রা.) ও অন্যান্য সাহাবি নন; কেননা তারা (মুয়াবিয়া প্রমুখ) সদুদ্দেশ্যে ভুল ব্যাখ্যাকারী (مُتَأَوِّلُوْنَ) — তাদের জন্য সওয়াব রয়েছে, আর আলী (রা.) ও তাঁর শিয়াদের জন্যও সওয়াব রয়েছে।” [আল-সাওয়ায়িক আল-মুহরিকাহ, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ১, পৃষ্ঠা ২৩৬]
মূলত “শিয়া” বলতে ক্ল্যাসিকাল সুন্নি স্কলারগণ এটাই বুঝিয়েছেন: “শিয়াতু-আলী” (রা.) বা আলী (রা.)-এর অনুসারী/সমর্থক হলো সুন্নিগণ। যেমন, ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন,
{“كَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ: شِيعَةُ عَلِيٍّ هُمُ السُّنِّيُّونَ لِأَنَّهُمْ عَلَى طَرِيقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”}
অর্থ: “সালাফগণ বলতেন: আলীর শিয়ারাই সুন্নি, কারণ তারা নবীজি (সা.)-এর ত্বরীক্বা/পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত।” [তারীখুল খুলাফা, পৃ. ১৬৮]
অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগে “শিয়া” শব্দটি সুন্নি আলেমদের জন্যই ব্যবহৃত হতো। একইভাবে, ইবনে আবিল ইয আল-হানাফি (রহ.) বলেছেন,
{“أَهْلُ السُّنَّةِ هُمْ شِيْعَةُ عَلِيٍّ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَهُ فِي الدِّينِ”}
অর্থ; “আহলে সুন্নতই প্রকৃতপক্ষে আলীর শিয়া, কারণ তারা দ্বীনে তাঁর অনুসরণ করে।” [শারহু আকীদাতিত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৪৮২]
বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়ার স্বঘোষিত “মহাজ্ঞানী” ইসলামী পণ্ডিতেরা যাঁকে তাদের শ্রদ্ধেয় ইমাম দাবি করে, সেই সম্মানিত সুন্নি স্কলার ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,
{“الشِّيعَةُ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ عَلِيًّا وَيُقَدِّمُونَهُ عَلَى عُثْمَانَ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ إِذَا لَمْ يَكْفُرُوا أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ”}
অর্থ: “যারা আলীকে ভালোবাসে ও উসমানের উপর তাঁকে প্রাধান্য দেয়, তারাই শিয়া। তারা আহলে সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত—যতক্ষণ না সাহাবাদের কাউকে কাফির বলে।” [মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/১৫৬]
অর্থাৎ, শিয়া পরিচয় সত্ত্বেও সাহাবিদের প্রতি সম্মান বজায় রাখলে তারা সুন্নি বলেই গণ্য—এটাই ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মত।
আসলে এটিই ছিল মুসলিম স্কলারদের সর্বসম্মত মত: শিয়া মানে আহলে সুন্নাহ (সুন্নি) এবং সুন্নিরাই আলী (রা.)-এর শিয়া/সমর্থক। প্রথম দুই শতাব্দীতে শিয়া ও সুন্নি স্কলারগণ কোনো পার্থক্যহীনভাবে একে অন্যের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতেন। ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে কাঠামোবদ্ধ ফিকহ ও মাজহাব গড়ে উঠতে থাকে।
হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর বিশিষ্ট স্কলার ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) [জন্ম: ৭০২ খ্রি. – মৃত্যু: ৭৬৫ খ্রি.] ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ষষ্ঠ বংশধর, যিনি ইমাম হাসান বিন আলী (রা.)-এর পুত্র জয়নুল আবেদিনের (রহ.) নাতি। তিনি ইলম, তাকওয়া ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এতই খ্যাতিমান ছিলেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.)-সহ অনেক স্কলার তাঁর নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর ফিকহী উসুল ও মতামতের ভিত্তিতে হানাফী মাজহাব ও মালিকী মাজহাবের মতো বৃহৎ দুইটি ফিকহী ধারা (School of Thought) গড়ে ওঠে।
ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর অনুসারীরা পরবর্তীতে “জাফরী মাজহাব” নামে আরেকটি স্বতন্ত্র ফিকহী ধারা গঠন করেন। এই “জাফরী মাজহাব”-ই বর্তমান শিয়া মতবাদের ভিত্তি। তবে ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) নিজে কোনো নতুন মাজহাব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেননি; পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাকে তার অনুসারীরা পৃথক মাজহাব (School of Thought)-এ রূপান্তরিত করে। সুন্নি ও শিয়া উভয় ফিকহী ধারাতেই ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)-এর ইলম, মর্যাদা ও বংশগত সম্মান সর্বজনবিদিত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়।
“জাফরী মাজহাব”-টি এখন “ইসনা আশারিয়া” বা বারো ইমাম-পন্থী শিয়া মতবাদ হিসেবে পরিচিত। ইরানের সরকার ও জনগণ মূলত এই “জাফরী মাজহাব” বা “ইসনা আশারিয়া” ফিকহী ধারা (School of Thought)-এর অনুসারী/শিয়া।
শিয়া–সুন্নি বিভক্তির কারণ
সাহাবী হিসাবে হযরত আলী (রা.)-এর উচ্চ মর্যাদার কারণে সাহাবীগণ তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন: “আল্লাহর কাছে আলীর চেয়ে প্রিয় কাউকে আমি দেখিনি।” [হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/৮৪]

আবু হুরায়রা (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ বলতেন, “আলীর দিকে তাকানো ইবাদত।” [মুস্তাদরাকে হাকিম; মুজামউল কবীর]
রাজনৈতিক উত্তরসূরিত্বের প্রশ্নেও একদল সাহাবী মনে করতেন খিলাফতের জন্য আলী (রা.)-ই সর্বাধিক হকদার। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) লিখেছেন:
“وَالْحَقُّ أَنَّ أَصْلَ الْخِلَافِ كَانَ فِي الْإِمَامَةِ”
অর্থ: “সত্য হলো, বিভেদের মূল ছিল ইমামতের (নেতৃত্বের) প্রশ্নে।” [ইযালাতুল খিফা, ১/৮৭]
এই রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ ধীরে ধীরে আকিদা ও ফিকহের স্তরে প্রবেশ করে।
হিজরি ৩৬ সালে (৬৫৬ খ্রি.) জামাল যুদ্ধ ও ৩৭ হিজরিতে (৬৫৭ খ্রি.) সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জামাল যুদ্ধের মূল ইস্যু ছিল উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার, আর সিফফিনে আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে খিলাফতের আনুগত্য নিয়ে সংঘাত। এ সময় আলী (রা.)-এর সমর্থকগণ “শিয়াতু আলী” (شيعة علي) নামে পরিচিত হন। ইমাম নববী (রহ.) এর ব্যাখ্যায়:
“أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا كَانَ مُصِيبًا فِي الْقِتَالِ”
অর্থ: “আহলে সুন্নত ঐকমত্য পোষণ করেন যে আলী (রা.) যুদ্ধে সঠিক ছিলেন।” [শারহু সাহিহ মুসলিম ১২/২২৯]
মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর পক্ষের সাহাবীরা ইজতিহাদি ভুল করলেও তারা “কাফির” বা “ফাসিক” ছিলেন না—এটি সুন্নি মাজহাবের ঐকমত্য। [ইবনে হাজার, ফাতহুল বারি, ১৩/৫৫; শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইযালাতুল খিফা, ১/৯০]
প্রথম শতাব্দীতে “শিয়াতু আলী” ছিল আলী (রা.)-এর রাজনৈতিক সমর্থকদের পরিচয়। হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষের সাহাবা ও তাবেয়ীগণ সাধারণভাবে এই পরিচয় বহন করতেন। তখন “সুন্নি” নামে পৃথক কোনো দল-মত ছিল না।
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) (মৃ. ২৪১ হি.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে “আহলে সুন্নত” / “সুন্নি জামাত” পরিভাষাটি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, যা দ্বারা তিনি রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহের অনুসারীদের নির্দেশ করেন। [তারীখ বাগদাদ, ৪/৪১২]
তবে তারও আগে হিজরি ১২২ সালে ইমাম হাসান (রা.)-এর নাতি, রাসূল (সা.)-এর পঞ্চম বংশধর হযরত যায়দ ইবনে আলী (রা.) উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে কুফার একদল উগ্রপন্থী তাকে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর নিন্দা করতে বলে। যায়দ (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করায় সেই উগ্রপন্থীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে। ইমাম যাহাবী (রহ.) লিখেন:
“لَمَّا خَرَجَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ… قَالُوا: تَبَرَّأْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى نَنْصُرَكَ! فَقَالَ: بَلْ أَتَوَلَّاهُمَا. قَالُوا: إِذًا نَرْفُضُكَ! فَسُمُّوا: الرَّافِضَةَ”
অর্থ: “তারা বলল: আবু বকর-উমর থেকে বিমুখ হও, তবেই আমরা তোমাকে সমর্থন করব! তিনি বললেন: বরং আমি তাদের বন্ধু। তারা বলল: তাহলে আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করলাম! তাই তারা ‘রাফেজা’ নামে আখ্যায়িত হয়।” [মীযানুল ই‘তিদাল, ১/২৬]
এরপর “রাফেজী” শব্দটি উগ্রপন্থী শিয়াদের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে—যারা আবু বকর, উমর (রা.)-এর খিলাফতকে অস্বীকার করে, এমনকি সাহাবীদেরকে গালাগালিও করে। মূলধারার শিয়াগণ (ইমাম যায়দ বা জাফর সাদিকের অনুসারীগণ) এই উগ্র “রাফেজী”-দের থেকে আলাদা ছিলেন এবং তাদের প্রত্যাখ্যান করতেন। কিন্তু যায়দী শিয়া ও জাফরী শিয়াদের সাথে উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের রাজনৈতিক বিরোধের কারণে উমাইয়া ও আব্বাসীয়রা সকল শিয়াকেই “রাফিজী” ট্যাগিং করার চেষ্টা করতো।
একই সময়ে শিয়ারাও “নাসিবী” (ناصبي) শব্দের প্রচলন শুরু করে। “নাসিবী” শব্দটি এসেছে **”نَصَبَ الْعَدَاءَ”** (শত্রুতা স্থাপন করা) থেকে। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর সংজ্ঞা দেন:
“النَّوَاصِبُ هُمُ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ الْعَدَاءَ لِآلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”
অর্থ: “নাসিবী হল যারা নবী পরিবারের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করে।” [মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪/৫৩০]
খারেজি ও কিছু উমাইয়া সমর্থক গোষ্ঠীকে এই ট্যাগ দেওয়া হতো, কিন্তু সকল সুন্নি কোনো অবস্থাতেই “নাসিবী” নন।
খিলাফতের উত্তরাধিকার নিয়ে সূচিত বিভাজন উমাইয়া-আব্বাসীয় যুগে আকিদাগত রূপ নেয়। ইবনে খালদুন (রহ.) বলেছেন:
“تَعَمَّقَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الشِّيعَةِ وَالسُّنَّةِ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ حَتَّى صَارَتْ مَذَاهِبَ كَلامِيَّةً”
অর্থ: “আব্বাসীয় যুগে শিয়া-সুন্নি বিভক্তি এত গভীর হয় যে তা কালামী মতবাদে পরিণত হয়।” [মুকাদ্দিমাহ, ১/২৯৮]
আধুনিক যুগে সৌদি আরব ও ইরানের ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এই পুরনো বিভাজনকে পুনরায় রাজনীতি-কেন্দ্রিক করে তুলেছে। উভয় পক্ষের উগ্র সমর্থকেরা একে অপরকে “রাফেজী” ও “নাসিবী” আখ্যায়িত করে, যদিও শিয়াদের খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ এখনো “রাফিজী” এবং সুন্নীদেরও খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ এখনো “নাসিবী”।
লক্ষ করলেই দেখবেন, বাংলাদেশেও সৌদ-পরিবারের ভক্তরা ইরানি শিয়াদেরকে “রাফিজী” হিসেবে উল্লেখ করে, অথচ সকল শিয়াকে “রাফিজী” বলাটা বাংলাদেশের সকল সুন্নি মুসলিমকে “সুরেশ্বরী” বা “দেওয়ানবাগী” বলার মতো।
বিশেষত যখনই ইরানের সাথে মধ্যপ্রাচ্যে সৌদিদের বা সৌদের মনিব আমেরিকার কোনো দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তখনই বাংলাদেশে এক শ্রেণির শায়খরা মাথায় ঘোমটা দিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শিয়াদেরকে গণহারে “রাফিজী” বা “কাফের” ডাকা শুরু করে। সৌদি রাজপরিবারের হাজারো অপকর্মের বিরুদ্ধে তারা কখনো একটি শব্দও বলবে না। পারতপক্ষে তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধেও নিরব। কিন্তু ইরান প্রসঙ্গ আসলেই তাদের ছহিহ আক্বীদানুভূতি খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে!
শিয়াদের আক্বীদা কী?
“শিয়াদের আক্বীদা কী”—এই প্রশ্নটি কনসেপচুয়ালি সঠিক নয়। ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, শিয়া চিন্তাধারার সূচনা সাহাবায়ে কেরামের যুগে হযরত আলী (রা.)-কে অগ্রাধিকারমূলক ভালোবাসা ও খিলাফতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক পছন্দের বিষয়, তখন এটি ঈমান সংক্রান্ত কোনো আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়নি। উল্লেখ্য, “ঈমানের বিষয়বস্তু” বোঝানোর জন্য “আক্বীদা” শব্দটির ব্যবহারও সে যুগে ছিল না। পবিত্র কুরআন বা সহীহ হাদীসে “আক্বীদা” শব্দটি ঈমানের পরিভাষা হিসেবে অনুপস্থিত। বরং হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে (শিয়া চিন্তাধারা শুরু হওয়ার প্রায় ৪০০ বছর পর) ইসলামী পরিভাষায় “আক্বীদা” শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়।

ইসলামী পরিভাষায় “আক্বীদা” শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে “শিয়া” বলতে মূলত একটি রাজনৈতিক দল বা পক্ষকে বোঝানো হত। বিশেষ করে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের বিরোধিতা করা গোষ্ঠীগুলো এই পরিচয়ে পরিচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, উমাইয়া শাসকদের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কেও অনেক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক শিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সুন্নি মতবাদের বৃহত্তম ফিকহি মাযহাবের ইমাম হলেও, তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান তাকে “শিয়া” পরিচয় দিয়েছিল—এবং সেটি কোনো আক্বীদাগত বিভক্তি ছিল না।
#সাহাবা-তাবেঈন যুগে ঈমানের ভিত্তি:
সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে ঈমান বলতে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ছয়টি মৌলিক বিশ্বাসকেই বোঝানো হত:
১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
২. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস
৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস
৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস
৫. আখিরাতের (পরকাল) প্রতি বিশ্বাস
৬. তাকদীরের (ভাগ্যের) প্রতি বিশ্বাস
এই ছয়টি বিষয়ে বিশ্বাস করলেই কোনো ব্যক্তি “মুমিন” হিসেবে গণ্য হতেন। সে যুগে শিয়া ও সুন্নি—সকল মুসলিম এই মৌলিক বিশ্বাসে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন। অতএব, প্রাথমিক যুগে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে কোনো পৃথক ‘আক্বীদা’ বিদ্যমান ছিল না।
#তাত্ত্বিক_বিতর্কের_সূচনা ও আক্বীদা শাস্ত্রের উদ্ভব:
হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক তীব্র হতে থাকে। কাদরিয়া, মুতাজিলা, জাহমিয়া প্রভৃতি দার্শনিক গোষ্ঠীগুলো ঈমানের শাখাগত বিষয় নিয়ে জটিল বিতর্ক সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে ‘আক্বীদা’ নামে একটি স্বতন্ত্র ধর্মতাত্ত্বিক শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। এ সময়ই লেখ্যরূপে আক্বীদার চর্চা শুরু হয়, যেমন: আক্বীদা আত-তাহাবিয়্যা (রচনাকাল: হিজরী ৩য়/৯ম শতাব্দী, ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী রহ.), আল-আক্বীদা আল-ওয়াসিতিয়্যাহ (রচনাকাল: ৭০৫ হি./১৩০৬ খ্রি., শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.) ইত্যাদি।
এভাবে ঈমানের সরল ছয়টি স্তম্ভের উপর শতাধিক শাখাগত প্রশ্নের উদ্ভব হয়। আক্বীদার চর্চা ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোকে এমন গভীরে নিয়ে যায় যেখানে মানবীয় ব্যাখ্যা ও দুর্বল সূত্রের হাদীসের ব্যবহার শুরু হয়। সাহাবী যুগের পর ইসলামের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের সাথে সাথে মুসলিম স্কলাররা বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মের সংস্পর্শে আসেন এবং ঈমানের জটিল দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বোঝার জন্য এই প্রচেষ্টা যুক্তিসঙ্গত ছিল, কিন্তু ক্রমে তা সীমা অতিক্রম করে। মানুষ নিজেদের সঠিকতা প্রমাণের পাশাপাশি অন্যদের ভুল প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আক্বীদা এতটাই বিস্তারিত ও জটিল হয়ে ওঠে যে ঈমানের মূলনীতিগুলো আর “আঙুলে গোনার” মতো সরল থাকল না—বরং ‘আক্বীদা আত-তাহাবিয়্যা’, ‘শারহুল আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ’ বা ‘কিতাবুত তাওহীদ’-এর মতো বিশাল গ্রন্থরাজিতে পরিণত হলো!
এই সকল গ্রন্থে আলোচিত কিছু জটিল বিতর্কের বিষয়:
– ওহী বনাম যুক্তি: ধর্মীয় জ্ঞানে ঐশী বাণী ও মানবীয় যুক্তির মধ্যে প্রাধান্য কাকে দেওয়া হবে?
– কুরআন সৃষ্ট নাকি অ-সৃষ্ট: কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, নাকি তাঁর অনন্ত জ্ঞানের প্রকাশ?
– আল্লাহর সর্বত্র উপস্থিতি: আল্লাহ কি সর্বত্র বিদ্যমান (সর্বব্যাপী), নাকি তিনি স্থান-কালের ঊর্ধ্বে?
– তাকদীর বনাম ইখতিয়ার: মানুষের কর্ম কি পূর্বনির্ধারিত, নাকি তার স্বাধীন ইচ্ছা আছে?
– ইবলিসের পরিচয়: শয়তান (ইবলিস) ফেরেশতা ছিল, নাকি জিন জাতির?
– রাসূলুল্লাহ (সা.) নূর (আলো) দিয়ে সৃষ্টি, নাকি অন্যান্য মানুষের মতো মাটি দিয়ে? রাসূলুল্লাহ (সা.) কি সবার আগে সৃষ্টি হয়েছিলেন?
এসব বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিরোধ কারও কারও কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা ধীরে ধীরে শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সকল ফিকহি মাযহাবের মধ্যে উপদলীয় বিভাজন তৈরি করে।
#শিয়া_মাযহাবসমূহ_ও_তাদের_আক্বীদাগত_পার্থক্য:
পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে শিয়াদের মধ্যে আক্বীদাগত যে ধারণা প্রবেশ করেছে তা নিচে মোটামুটি সামারি দেওয়া হলো। তবে মনে রাখা জরুরি: একই মাযহাবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে (যেমন, হানাফী সুন্নিদের মধ্যে দেওবন্দী-বেরেলভী)। শিয়া মাযহাবগুলোর সারাংশ:
১. ইসনা আশারিয়া (বারো ইমামী/জাফরী):
– ফাদলুল্লাহ ঘরানা (লেবানন, ইরাক; হি*জ*বুল্লা*হ গ্ৰুপের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা):
* ইমামত নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা, কুরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
* আলী (রা.)-এর নেতৃত্ব আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ধারিত ছিল বলে বিশ্বাস।
* তাকিয়া (প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মত গোপন) কৌশলগত বিষয়, ধর্মীয় ভিত্তি নয়।
* সুন্নিদের সাথে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস, সাহাবীদের প্রতি সম্মান।
* কারও প্রতি অভিশাপ বা গালিগালাজ হারাম।
[সূত্র: আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ হুসাইন ফাদলুল্লাহ রহ.-এর ফতওয়া ও বক্তব্য]
– আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি ঘরানা (ইরানের ক্ষমতাসীন সরকার ও অধিকাংশ শিয়া এই ঘরানার):
* ইমামত “ইলাহী নিয়োগ” (আল্লাহর ইশারায় নির্বাচন) এবং ইমামগণ মাসূম (নিষ্পাপ)।
* ইমামত ঈমানের অংশ।
* তাকিয়া ও ইমামদের অলৌকিক ক্ষমতা বিশ্বাস্য।
* ইমামদের প্রায়-নবীর মর্যাদা দেওয়া।
[সূত্র: ইমাম খোমেইনি রহ.-এর “কাশফুল আসরার”, “হুকুমাতে ইসলামী”]
২. যায়দিয়া (ইয়েমেনের সাধারণ শিয়া ও হু*তি বিদ্রোহীদের মাযহাব):
* ইমামতকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসেবে দেখা হয়, ধর্মীয় নেতৃত্ব নয়।
* ইমামগণ মাসূম (নিষ্পাপ) নন।
* সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।
* ফিকহে হানাফীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান।
* ইমাম যায়িদ বিন আলী (রহ.)-এর অনুসারী, যাঁকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করতেন।
[সূত্র: ইমাম যায়িদ রহ.-এর “মাজমুউল ফিকহ”, ঐতিহাসিক গ্রন্থ “তাবাকাতে ইবনে সাদ”]
৩. গুলাত (অতিরঞ্জনকারী) সম্প্রদায়:
“গুলাত” অর্থ অতিরঞ্জনকারী। এরা মূলধারার শিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার উদাহরণ:
* আলী (রা.)-কে “আল্লাহ” বা “আল্লাহর নূর” মনে করা।
* ইমামদের উপর খোদায়ী গুণ আরোপ করা (যেমন: অলৌকিক সৃষ্টি, গায়েব জানা)।
* গোপন ইমামত ও রূপক তাফসিরে বিশ্বাস।
* আলাউয়ী/নুসাইরী (সিরিয়া): আলী (রা.)-কে আল্লাহর সত্তার অংশ মনে করে।
* ইসমাইলিয়া: ইমামতকে গোপন জ্ঞানের ধারক বলে বিশ্বাস করে।
* আগাখানি: ইসমাইলিয়ার একটি শাখা, বর্তমান নেতা আগা খান।
* দাঊদী/সুলাইমানী বোহরা (ভারত-পাকিস্তান): ইসমাইলিয়ার উপশাখা।
#গুলাতদের_বিরুদ্ধে_মূলধারার_শিয়া আলেমদের কঠোর অবস্থান: শাইখ ইবনে বাবুয়াইহ আল-কুম্মী (আস-সাদূক) রহ. (মৃ. ৩৮১ হি.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আলী (আ.)-কে ‘ইলাহ’ (খোদা) বলে বিশ্বাস করে, সে কাফির। আমরা তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।” [আল-ই’তিকাদাত, পৃষ্ঠা ১০২]
আল্লামা আব্দুল্লাহ আল-মামাকানী রহ. (১৮৪৬–১৯৩২) বলেছেন, “গুলাতরা ইসলামের শত্রু। ইমামদেরকে খোদা বানানো বা দৈব গুণ দেয়া—এসব প্রকাশ্য কুফর।” [তানকীহুল মাকাল ফী ইলমির রিজাল, ২/১৮৫]
আয়াতুল্লাহ আগা বোজর্গ আত-তেহরানী রহ. (মৃ. ১৯৭০) বলেছেন, “যারা ইমামদের উপর আল্লাহর সিফাত আরোপ করে, তারা প্রকৃত শিয়া নয়।”
[আয-যারিয়াহ ইলা তাসানীফিশ শিয়া, ৪/২৮৩]
আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মাদ হুসাইন ফাদলুল্লাহ রহ. (লেবানন) বলেছেন, “আমরা এমন শিয়াবাদকে প্রত্যাখ্যান করি যাতে গালিগালাজ, অভিশাপ, ইমামদের দেবত্বকরণ বা অতিরঞ্জন থাকে। এটি আহলে বাইতের প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী।” [বিবৃতি: আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-মুয়াসিরাহ, ১/৩৪০]
আসলে “শিয়া আক্বীদা” বলতে একক, অভিন্ন কোনো মতাদর্শ নেই (জাফরী, যায়দিয়া, ইসমাইলিয়ার মধ্যে আক্বীদাগত পার্থক্য বিশাল), যেভাবে “সুন্নি আক্বীদা” বলতেও একক কিছু নেই (আশআরি, মাতুরিদি, সালাফি/আসারি ভিন্নতা বিদ্যমান)। মূলধারার জাফরী বা যায়দিয়া শিয়ারা ঈমানের ছয় মৌলিক স্তম্ভে সুন্নিদের সাথে সম্পূর্ণ একমত। তাদের মধ্যে ফিকহি মতপার্থক্য থাকলেও তা আক্বীদাগত বিভাজন নয়।
ইতঃপূর্বে রাফেজী ও নাসিবী নিয়েও আলোচনা করেছি। এখানে সেই আলোচনা আবার করা প্রাসঙ্গিক।
প্রাথমিক ইমামগণ (যেমন ইমাম যায়িদ রহ., ইমাম জাফর আস-সাদিক রহ.) সাহাবীদের গালি দেওয়া, আলী (আ.)-কে খোদা বানানো বা ইমামতকে নবুয়তের সমান দাবি করার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। প্রকৃত রাফেজী ছিল তারা যারা:
– হযরত আবু বকর, উমর, উসমান (রা.)-কে কাফের/মুনাফিক বলত।
– আলী (আ.)-কে প্রায় নবীর মর্যাদা দিত।
– কুরআন বিকৃত হয়েছে বলে বিশ্বাস করত।
– সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশকে গালি দিত।
(সূত্র: ইবনে তাইমিয়ার “মিনহাজুস সুন্নাহ”, ১/৩৫; শাহরাস্তানীর “আল-মিলাল ওয়ান নিহাল”)
বর্তমান ইসনা আশারিয়া/যায়দিয়ারা কি রাফেজী?
না। আধুনিক জাফরী আলেমগণ (যেমন আয়াতুল্লাহ ফাদলুল্লাহ, আয়াতুল্লাহ সিস্তানী, আয়াতুল্লাহ ফালাহাতপিশে) রাফেজী মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে সুন্নিদের সাথে সংলাপ ও সম্মানের আহ্বান জানিয়েছেন। যায়দিয়ারা তো সাহাবীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই পুরো শিয়া মতবাদকে “রাফেজী” আখ্যা দেওয়া অন্যায়।
#নাসিবী (ناصبي) কারা?
‘নাসিবী’ শব্দটি ‘নাসাবা’ (বিদ্বেষ পোষণ করা) ধাতু থেকে এসেছে। ইসলামী ইতিহাসে আহলে বাইত (বিশেষত আলী (রা.) ও তাঁর বংশধর)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, তাদের গালি দেওয়া বা মর্যাদা অস্বীকার করা ব্যক্তিকে নাসিবী বলা হতো।
বর্তমান সুন্নিরা কি নাসিবী?
মোটেও না। সুন্নি মাযহাবগুলো আহলে বাইতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করে। ইমাম বুখারী (সহীহ বুখারী, “ফাদাইলু আসহাবিন নবী” অধ্যায়), ইমাম আহমাদ (ফাদাইলুস সাহাবা), ইমাম নববী (শারহু মুসলিম), জালালউদ্দিন সুয়ুতি-সহ বহু সুন্নি মনীষী আহলে বাইতের মর্যাদা নিয়ে লেখালেখি করেছেন। যেমন, বুখারী শরীফে অন্যান্য সকল সাহাবীর নামের শেষে “রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু” লেখা হলেও আহলে বাইতগণের নামের শেষে, অর্থাৎ আলী (রা.), ফাতিমা (রা.), হাসান-হুসেন (রা.) প্রমুখের নামের শেষে প্রায় ২০ বার সম্মানসূচকভাবে “আলাইহিস সালাম” লেখা হয়েছে। কোনো সুন্নি মাযহাব “নাসিবী নীতি” সমর্থন করে না।
শিয়া-সুন্নি উভয় ঘরানার কিছু উগ্রপন্থী লোক অহেতুক একে অপরকে “রাফেজী” ও “নাসিবী” আখ্যা দিয়ে উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করে। ওয়েব সাইট, ব্লগ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব নোংরামি ও বিদ্বেষ খুবই পরিকল্পিতভাবে ছড়ানো হয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হলো—অন্য মুসলিমের ঈমান নিয়ে সন্দেহ না করা এবং দলিলভিত্তিক মতপার্থক্য থাকলেও সম্মান ও ন্যায়বিচার বজায় রাখা (কুরআন ৪৯:১২, সহীহ বুখারী ৬০৪৫)।
ঐতিহাসিকভাবে শিয়া-সুন্নি সম্পর্ক কেমন ছিল?
আগের পর্বগুলোতে আলোচনা হয়েছে যে, শিয়া ও সুন্নি বিভাজন মূলত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার রাজনৈতিক সংঘাত থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে, ঈমান-আক্বীদা বা ফিকহগত মতপার্থক্য থেকে নয়। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে আব্বাসীয়-ফাতেমী কিংবা উসমানীয়-সাফাভী দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রভাব বিস্তার ও আঞ্চলিক আধিপত্যের লড়াই। এসব লড়াই শিয়া-সুন্নি পরিচয়ের আড়ালে পরিচালিত হলেও এসবের মূলে ছিল ক্ষমতার রাজনীতি। তবে লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলয় থেকে মুক্ত আলেমগণ সাধারণত উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে এই ধরনের বিবাদে জড়াতেন না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উসমানীয় খিলাফতের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে শিয়া ও সুন্নি আলেমদের ঐতিহাসিক ঐক্য একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ১৯১৪ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ বাহিনী ইরাকের আল-ফাও উপকূলে অবতরণ করলে ইরাকের শিয়া নেতাগণ, যেমন গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ কাজিম আল-ইয়াযদি (রহ.) ও আয়াতুল্লাহ মির্জা মুহাম্মাদ তাকি শিরাজী (রহ.) তৎকালীন উসমানীয় খলিফার পক্ষে ফতোয়া জারি করেন। কারবালা ও নাজাফের শিয়া আলেমগণ স্থানীয় মুসলমানদেরকে উসমানীয়দের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। [ড. আলী আল-ওয়ার্দি ,”লামাহাত ইজতিমাইয়াহ মিন তারিখ আল-ইরাক আল-হাদিস”-এ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬]
অন্যদিকে, সহীহ আক্বীদার দাবিদার আহলে সৌদ (সৌদের বংশধর ও অনুসারীরা) সে সময় ব্রিটিশদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।
১৯১৯ সালে ইরাকের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে শিয়া-সুন্নি নেতারা “We, being of the Muslim Arab nation and representing the Shia and Sunni communities inhabiting Baghdad and its suburbs…” – এমন বিবৃতি দিয়ে জাতীয় ঐক্যের অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক দলিলটি ব্রিটিশ জাতীয় সংরক্ষণাগারে (UK National Archives, FO 371/4148) সংরক্ষিত আছে। ১৯২০ সালের ইরাকি বিপ্লবকালে মির্জা তাকি শিরাজীর নেতৃত্বে শিয়া-সুন্নি আলেমগণ ও সাধারণ মানুষ সংযুক্তভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। [ড. আব্দুল্লাহ আল-ফায়াদ, “The Iraqi Revolution of 1920”, পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯১]
তবে ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের পতনের মাধ্যমে শিয়া-সুন্নির ঐক্যের প্রতীকটি ধ্বংস হয় এবং গত ১০০ বছর ধরে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভাজনটি উস্কে দিতে সক্রিয় রয়েছে।
ভারতীয় উপমহাদেশে দিল্লি সালতানাত ও মুঘল আমলে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২) তার বিখ্যাত গ্রন্থ “ইজালাতুল খিফা আন খিলাফতুল খুলাফা”-তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন: “শিয়ারা ইসলামবিরোধী নয়”, “আলী (রা.)-এর মর্যাদা আমরা স্বীকার করি” এবং “বিভাজন মূলত রাজনৈতিক কারণে সৃষ্টি হয়েছে”। [গ্রন্থের ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৭]
বাংলা অঞ্চলে নবাব আলীবর্দী খান ও সিরাজউদ্দৌলার শিয়া পরিচয় সত্ত্বেও স্থানীয় সুন্নি আলেম ও সাধারণ মুসলিমগণ তাদেরকে সমর্থন করেছিলেন। [ড. মুহাম্মদ মোহর আলী, “History of the Muslims of Bengal”, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২]
ব্রিটিশ আমলেও এই সম্প্রীতি অব্যাহত ছিল। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের নেতাই ছিলেন – নবাব ওয়াকার-উল-মুলক মৌলভী (সুন্নি), স্যার আদমজী পিরভয় (শিয়া) সুলতান মুহাম্মদ শাহ আগা খান (শিয়া), ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ (সুন্নি) এবং স্যার সৈয়দ আমির আলী (শিয়া)। পাকিস্তান আন্দোলনের সর্বজনীন নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর শিয়া পরিচয় সত্ত্বেও ভারতের সকল প্রধান সুন্নি নেতারা তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন।
বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শিয়া প্রভাব অত্যন্ত গভীর। হাজী মুহাম্মদ মহসিনের মতো শিয়া সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে মহররম ও কারবালাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার এই সম্প্রীতিরই স্বাক্ষর বহন করে। এখনো বাঙালি মুসলিমের নামের মধ্যে আলী, হাসান, হুসেনের বিপুল প্রাধান্য দেখা যায়, যা মূলত শিয়া সংস্কৃতি। ১৯৮০ দশকে বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্মানিত আলেম মাহমুদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) ইরান সফর করেছিলেন এবং তিনি আয়াতুল্লাহ খোমেনির ইমামতিতে সালাত আদায় করেছিলেন এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনিও হাফেজ্জী হুজুরের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছিলেন।
১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের পর থেকে শিয়া-সুন্নি সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ইতিহাসবিদ ফাউজি আল-জিয়াদ তার “The Shia-Sunni Divide: Myths and Realities” (পৃষ্ঠা ৭৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইরানের শাহ পাহলভীর আমলে সৌদি আরবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় ছিল, যদিও ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তখনও শিয়া ছিল। পশ্চিমাপন্থী শাহের সাথে পশ্চিমাপন্থী সৌদি রাজতন্ত্রের যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল।
কিন্তু আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে পশ্চিমা দালাল শাহের উৎখাতের পর পশ্চিমা দালাল সৌদি সরকারের নীতি পরিবর্তন হয়। তারা শিয়াবিরোধী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে।
তবুও সৌদি আরব কখনোই সরকারিভাবে শিয়াদেরকে কাফের ঘোষণা করেনি এবং শিয়াদেরকে হজ্ব করতে অনুমতি দেয়। ২০১০ সালে লেবাননের শিয়া নেতা আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ হুসাইন ফাদলুল্লাহর মৃত্যুর পর সৌদি প্রতিনিধিদল তার জানাজায় অংশ নিয়েছিল (আল-জাজিরা রিপোর্ট, ৬ জুলাই ২০১০)।
বর্তমান সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের জটিল ভূরাজনীতিতে ইরান ও সৌদি আরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অনেকেই শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি আঞ্চলিক ক্ষমতার লড়াই। ড. ভ্যালি নাসর তার “The Shia Revival” (পৃষ্ঠা ১৫৬) গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইরাক যুদ্ধের পর থেকে এই বিভাজন কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হয়েছে।
ইসলামের ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়গুলো প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক প্রয়োজন ছাড়া শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায় সাধারণত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে এবং উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে একতাবদ্ধ থেকেছে। বর্তমানকালেও আসল সত্য হলো, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইরান ও সৌদি আরবের দ্বন্দ্বের কারণেই মূলত সৌদিপন্থী আলেমরা বিশ্বব্যাপী শিয়াবিদ্বেষ প্রচার করে। বিশেষত ইস*রা*য়েল বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের যে কোনো লড়াইয়ের সময় এই ধরনের অপপ্রচার বৃদ্ধি পায়।
“ইরানের সরকারটি কেমন”—এই আলোচনার আগে শিয়া-সুন্নি বিষয়ে এত আলোচনা করার কারণ হলো, ইরানসংক্রান্ত যে-কোনো আলোচনায় অনেকের একটা কমন টেনডেন্সি হলো বিষয়টাকে শুধুমাত্র শিয়া-সুন্নির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। সেই আলোচনায় ইরানের রাষ্ট্রীয় দর্শন, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, সামরিক নীতি, অর্থনীতি ও ভূ-রাজনীতি ইত্যাদির কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি লড়িবার শিয়া-সুন্নি! ![]()

বাস্তবতা হলো, ইরানের সরকারের কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই শিয়া মতবাদকে প্রতিনিধিত্ব করে না, যেমন সৌদি রাজপরিবারের কর্মকাণ্ডও কোনোভাবেই সুন্নি মতবাদ বা ওহাবী মাযহাবকে প্রতিনিধিত্ব করে না। ইরানি সরকার বা সৌদি রাজপরিবার উভয়ই এক একটি রাজনৈতিক শক্তি। তারা প্রত্যেকে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তা, বৈদেশিক শক্তির প্রভাব, রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা ও আঞ্চলিক উচ্চাভিলাস দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই শিয়া-সুন্নি, জাফরী-ওহাবী ইত্যাদি মতবাদ এড়িয়ে আসলে ফোকাস করা উচিত দেশগুলোর রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, সামরিক নীতি, অর্থনীতি ও ভূ-রাজনীতি ইত্যাদির হিসাব-নিকাশে। তবে ধর্মীয় আবেগ ও শিয়া-সুন্নি পরিচয়কে উভয় সরকারই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য ব্যবহার করে।
১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবকে অনেকেই মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রকৃত ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখেন। তবে বাস্তবতা হলো, এই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীগুলোর সবাই ইসলামপন্থী ছিল না; বরং এতে কমিউনিস্ট, বুদ্ধিজীবী, বামপন্থী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীসহ বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ অংশ নিয়েছিল, যাদের মূল লক্ষ্য ছিল মার্কিন-ব্রিটেনপন্থী বাদশাহ রেজা শাহের শাসনের অবসান ঘটানো। আয়াতুল্লাহ খোমেনি জনগণের কাছে “পরিবর্তন”-এর প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হন। তবে ক্ষমতায় আরোহণের পর ইসলামী নীতি বাস্তবায়নের চেয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রক্ষাই তাঁর প্রধান অগ্রাধিকারে পরিণত হয়। খোমেনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সমর্থকরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন; অন্যদিকে বিপ্লব সংঘটনে সহায়তা করা অনেককেই পরবর্তীতে নির্বাসিত বা কারাবন্দি করেন। বিপ্লবের পর ইরানে একটি নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় “সুপ্রিম লিডার”-এর হাতে। এই পদে এখন পর্যন্ত মাত্র দু’জন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হয়েছেন: প্রথমত আয়াতুল্লাহ খোমেনি (১৯৭৯-১৯৮৯) এবং পরবর্তীতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই (১৯৮৯-বর্তমান)।
ঐতিহাসিকভাবে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ছিল এবং বর্তমানেও এই নীতি অব্যাহত রেখেছে। ইরানের রাজনৈতিক নেতারা বারবার তাদের আঞ্চলিক পরাশক্তি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ একবার বলেছিলেন, “আমরা দ্রুত একটি পরাশক্তিতে পরিণত হচ্ছি। আমাদের শক্তি সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক সক্ষমতা থেকে আসে না, বরং মানুষের হৃদয় ও মননে প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য থেকে আসে – আর এটাই তাদের ভীত করে।” এই লক্ষ্য অর্জনে ইরান লেবাননের হিজবুল্লাহ, ফিলিস্তিনের হামাসের মতো সংগঠনগুলোকে সমর্থন দিয়েছে এবং সিরিয়ার জালিম বাশার আল-আসাদের আলাওয়ি শাসনকে সহায়তা করেছে।
ইরান তার আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী সৌদি আরবের মতোই প্রায়ই শিয়া-সুন্নি বিভেদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তারা নিজেদেরকে বৈশ্বিক শিয়া সম্প্রদায়ের রক্ষক হিসেবে দাবি করলেও বাস্তবে শুধুমাত্র সেই শিয়াদেরই সহায়তা করে যারা তাদের আঞ্চলিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল (যেখানে অধিকাংশ শিয়া বসবাস করে এবং দেশের প্রধান তেলক্ষেত্রগুলো অবস্থিত) ও বাহরাইনে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করে ইরান। অন্যদিকে আজারবাইজান বা তাজিকিস্তানের শিয়াদের প্রতি ইরান কোনো সমর্থন দেখায় না, কারণ এগুলো তাদের কৌশলগত স্বার্থের বাইরে পড়ে।
#মার্কিন_যুক্তরাষ্ট্রের_সাথে_ইরানের_সম্পর্ক
আমেরিকার সাথে ইরানের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের সূচনা ১৮৫৬ সালে। ইরানের [তখন “পারস্য” নামে পরিচিত] তৎকালীন কাজার বংশীয় রাজা নাসের উদ্দিন শাহ কাজার ১৮৫৬ সালে ওয়াশিংটনে প্রথবারের মতো পারস্যের রাষ্ট্রদূত পাঠান। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিকতার যুগে আফগানিস্তান ও ইরান অঞ্চলকে ঘিরে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের “গ্রেট গেইম” চলাকালে আমেরিকাকেই নিরাপদ মিত্র হিসেবে দেখেছিলেন ইরানের তৎকালীন রাজা নাসের উদ্দিন শাহ। কাজার বংশীয় শাহদের আমলে ইরানের সাথে আমেরিকার এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় যে, পরবর্তীতে ১৯১১ সালে আমেরিকান সরকারের পরামর্শে আমেরিকান কর্মকর্তা উইলিয়াম শাসটারকে ইরানের ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য ইরানের ট্রেজারার-জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। পরে আরেক আমেরিকান কর্মকর্তা আর্থার মিল্সপগকে ১৯২২-২৭ সালে ও ১৯৪২-৪৫ সালে দুই মেয়াদে একই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল!
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আমেরিকা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষনীতি (Isolationism) কিংবা অন্তত অন্য দেশে হস্তক্ষেপ না-করার (Non-interventionism) নীতি অনুসরণ করতো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঔপনিবেশিকতার পতনের পর আমেরিকা অন্য দেশে হস্তক্ষেপ না-করার (Non-interventionism) নীতি ত্যাগ করে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ (Neo-colonialism) নীতি গ্রহণ করে এবং দেশে দেশে হস্তক্ষেপ শুরু করে। আমেরিকার সেই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার প্রথম বলি হয় দীর্ঘদিনের মিত্র ইরান।
১৯৫৩ সালে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআইসিক্স মিলে এক অভ্যুত্থানে গণতান্ত্রিক ভোটে নির্বাচিত ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করে। প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের “অপরাধ” ছিল তিনি ইরানি তেলক্ষেত্রগুলোতে ব্রিটিশ লুণ্ঠন বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং ইরানি তেলক্ষেত্রগুলোকে জাতীয়করণ করেছিলেন।
মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের অদম্য প্রেমে আমেরিকা-ব্রিটেনের সেই যুগলবন্দীই পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে শুরু করে। আমেরিকা আর ইরানের সম্পর্কও আমেরিকার সেই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ও তেলপ্রেমের আঁচলে বাঁধা পড়ে।
ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ইরানের বাদশা রেজা শাহ পাহলভীর হাতে দেশের সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করে আমেরিকা-ব্রিটেন। স্বৈরশাসক রেজা শাহ পাহলভীকে ইরানের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে শত শত কোটি ডলারের সাহায্য পাঠায় আমেরিকা। সিআইএ-র কর্মকর্তারা ইরানে গিয়ে পাহলভীকে গড়ে দেয় ইরানের নিষ্ঠুর নিপীড়নকারী গুপ্ত পুলিশ সংস্থা “সাভাক”।
ইতিহাসের পরিহাস হলো, আজকের রিপাবলিকান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঙ্কার দিচ্ছে ইরানকে কিছুতেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দিবে না, অথচ ১৯৫০-এর দশকের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান আইজেনহাওয়ারই ১৯৫৭ সালে ইরানকে প্রথম পারমাণবিক চুল্লি তৈরিতে সহযোগিতা করে। আমেরিকাই ১৯৬৭ সালের পরে ইরানকে প্রথম অস্ত্র তৈরির উপযোগিতা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সরবরাহ করে। আমেরিকা-ব্রিটেনসহ পশ্চিমা শক্তির মিত্র পাহলভী যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন, আমেরিকা-ইউরোপের সরকারগুলো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে গেছে।
১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে মার্কিন-ব্রিটেনপন্থী রেজা শাহ পাহলভীর পতন হলে তিনি সপরিবারে আমেরিকা পালিয়ে যান। [প্যাটার্নটি কি খুব পরিচিত মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, রেজা শাহও পালিয়ে যাওয়ার আগে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করার টাইম পাননি এবং রেজা শাহের উজবুক পুত্রটিও আমেরিকাতেই বসবাস করে। ![]() ]
]
ইরানে বিপ্লবের পর ইরাকের তৎকালীন মার্কিনপন্থী প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে দিয়ে ইরানের সাথে যুদ্ধ বাঁধায় আমেরিকা। ১৯৮০ থেকে শুরু হওয়া সেই যুদ্ধে ইরাককে সার্বিক সহযোগিতা করে আমেরিকা। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়। ১৯৯৫ সালে ক্লিনটন প্রশাসন ইরানের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেয়।
ইরানের বিপ্লবের পর থেকে এখন পর্যন্ত আমেরিকার সাথে ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। আমেরিকার সাথে ইরানের অফিসিয়াল যোগাযোগ হয় পাকিস্তানের মাধ্যমে। ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসের “ইরানিয়ান ইন্টারেস্টস সেকশন” ইরানের পক্ষ থেকে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ করে। আমেরিকার পক্ষে দূতিয়ালি করে সুইজারল্যান্ড। তেহরানের সুইস দূতাবাসের “ইউএস ইন্টারেস্টস সেকশন” আমেরিকার পক্ষে ইরানের সাথে যোগাযোগ সারে।
তবে এটা মুদ্রার একপিঠের বয়ান। মুদ্রার অপর পিঠ হলো, ইরান যতই আমেরিকাকে “বড় শয়তান” আখ্যা দিয়ে তীব্র সমালোচনা করুক না কেন, বাস্তবে বেশ কিছু কৌশলগত ইস্যুতে দুটি দেশ একসাথে কাজ করে। ১৯৮৩ সালে ইরানের সরকারের বিভিন্ন স্তরে ইরানের সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট সংগঠন “তুদেহ পার্টি”-এর লোকজনের ব্যাপক অনুপ্রবেশের কথা আমেরিকাই জানিয়েছিল আয়াতুল্লাহ খোমেনির সরকারকে। আমেরিকার দেওয়া সেই তথ্য ব্যবহার করে খোমেনির সরকার তখন ইরানে কমিউনিস্ট প্রভাব নির্মূল করে।
১৯৮০-এর দশকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের প্রশাসন গোপনে ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি শুরু করে এবং নিকারাগুয়ার বামপন্থী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ইরানের মাধ্যমেই নিকারাগুয়ার ডানপন্থী কন্ট্রা বিদ্রোহীদের কাছে সাহায্য পাঠায়।
নাইন-ইলেভেনের পর আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে উৎখাতের ক্ষেত্রে আমেরিকাকে সহযোগিতা করে ইরান। অনুরূপভাবে, ইরাকের সাদ্দাম সরকারকে উৎখাতেও ইরান সহযোগিতা করে আমেরিকাকে, বিশেষত ইরাকের শিয়া বিদ্রোহী দলগুলোকে আমেরিকার প্রতি নমনীয় করে ইরান।
ইরানি সরকার গত ১৫ বছর ধরে তার সমস্ত সামর্থ্য – অর্থনীতি, সশস্ত্র বাহিনী, রেভোলিউশনারি গার্ড, কুদস ফোর্স এবং হি*জবু*ল্লাহ প্রোক্সি – কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা দালাল বাশার আল-আসাদ ও তার শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু ইস*রায়ে*লকে মোকাবেলা করার জন্য কখনোই নিজস্ব সামরিক ঘাঁটি স্থাপন বা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করেনি। ফিলিস্তিনের জনগণের উপর ইস*রায়ে*লি হামলার সময় ইরান নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় ছিল। হিজ*বুল্লা*হকে ইস*রায়ে*ল-বিরোধী কোনো পদক্ষেপ নিতে ইরান নির্দেশ দেয়নি। বরং সিরিয়ার মুসলিমদেরকে ইরান হ*ত্যা ও নির্যাতন করেছে শুধু পশ্চিমাপন্থী বাশারের শাসন টিকিয়ে রাখতে। আমেরিকা যখন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের মাধ্যমে সিরিয়ায় বাশারকে সরিয়ে নতুন “জি*হা*দি*স্ট” (![]() ) দালাল ক্ষমতায় আনল, ইরান নিশ্চিন্তে তার সেনা ফিরিয়ে নিল।
) দালাল ক্ষমতায় আনল, ইরান নিশ্চিন্তে তার সেনা ফিরিয়ে নিল।
ইস*রায়ে*ল বছরের পর বছর ইরানি নেতাদের হত্যা করেছে, কিন্তু ইরান কখনোই মর্যাদা রক্ষার মতো জবাব দিতে পারেনি। ইরাক যুদ্ধের সময় গড়ে তোলা সামরিক শক্তি এবং সিরিয়ায় অর্জিত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ইরানের প্রতিক্রিয়া খুবই সামান্য। সম্প্রতি ইস*রায়ে*লি হামলায় ৬১০ ইরানি নিহত ও ৪,৭৪৬ আহত হয়েছে। অন্যদিকে ইস*রায়ে*লি মরেছে খুবই কম সংখ্যক।
ট্রাম্প যেভাবে ইস*রায়ে*লকে দিয়ে এই যুদ্ধ শুরু করিয়েছিল, সেভাবেই যুদ্ধবিরতিও ঘোষণা করেছে। ইরান ও ইস*রায়ে*ল দু’পক্ষই এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। ট্রাম্প বলেছে, “ইরানের পরমাণু স্থাপনা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে” এবং “ইরান কখনোই তার পরমাণু কর্মসূচি পুনর্নির্মাণ করতে পারবে না”।
বাস্তবে ইরানি সরকারটিও আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট। আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, সিরিয়া সবখানে ইরানি সরকারের একই ভূমিকা। কিন্তু আমেরিকা যখন দেখেছে ইরান তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে, তখনই সামরিক চাপ প্রয়োগ করেছে।
এবারের যুদ্ধবিরতির পর আমেরিকা ইরানকে ৩০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রস্তাব করেছে শুধু শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচির জন্য। শর্ত একটাই—ইরানকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। অবশ্য আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা (IAEA) এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের তথ্য অনুযায়ী, ইরান ইতোমধ্যে ৪০০ কেজির বেশি ৬০% সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুদ করেছে। এই মাত্রার ইউরেনিয়াম সামরিক ব্যবহারের জন্য খুবই বিপজ্জনক। কারণ এখান থেকে ৯০% weapon-grade পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া প্রযুক্তিগতভাবে খুব বেশি সময়সাপেক্ষ নয়—কয়েক মাসের মধ্যেই সম্ভব।
তবে সাম্প্রতিক ইস*রায়ে*ল-ইরান সংঘর্ষ এবং সামরিক হামলার ফলে এই enrichment‑এর কাজ ১-২ বছরের মতো হয়ত বিলম্বিত হবে। কিন্তু এই বিলম্ব ইরানি পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থামিয়ে রাখতে পারবে না। কেননা ইরানের সরকারটি মধ্যপ্রাচ্যের রিজিওনাল পাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে উদ্গ্রীব। তাই ইরান নতুন করে enrichment কেন্দ্র চালু করছে এবং ৬০% পর্যায়ের ইউরেনিয়াম উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে।
বর্তমান ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা ইঙ্গিত দিচ্ছে, ২০২৬-২০২৭ সালের মধ্যে ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচিতে আরও বড় অগ্রগতি অর্জন করবে। বিশেষ করে, weapon-grade ইউরেনিয়াম মজুদে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসতে পারে। এছাড়া ২০২৭-২০২৯ সময়ের মধ্যে ইরান অন্তত ১-২টি কার্যকর পারমাণবিক ডিভাইস তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও তারা তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে না, তবে সামরিক ও কূটনৈতিক মহলে এই তথ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
অবশ্য অভ্যন্তরীণভাবে ইরানি সরকার নানাবিধ সংকটে জর্জরিত। দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ডস কর্পস (IRGC) এবং ধর্মীয় নেতাদের পরিবারবর্গ। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত অবনতির দিকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, মদ্যপানের হার বিবেচনায় ইরান বিশ্বে ১৯তম স্থানে রয়েছে, যেখানে রাশিয়া ৩০তম এবং সৌদি আরব ১৮৪তম অবস্থানে আছে। ইরানে মাদকাসক্তির হারও বিশ্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। দেশের তেল ও গ্যাস অবকাঠামোর বেশিরভাগই শত বছরের পুরনো এবং আধুনিকায়নের অভাবে জরাজীর্ণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ইরানের ৮০% এরও বেশি জনসংখ্যার বয়স ৩৫ বছরের নিচে, যারা ১৯৭৯ সালের বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু দেশ শাসন করছে ৬০/৭০ বছর ঊর্ধ্ব একদল ধর্মীয় নেতা। এই প্রজন্মগত বিভাজন আগামী ২/৩ বছরে ইরানে আরও ব্যাপক গণঅসন্তোষের জন্ম দিতে পারে। মদত দেওয়ার জন্য মার্কিন-ইস*রায়ে*ল তো থাকছেই!
~~~~~~~~~~~~
[আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যে সমাপ্ত, আলহামদুলিল্লাহ]