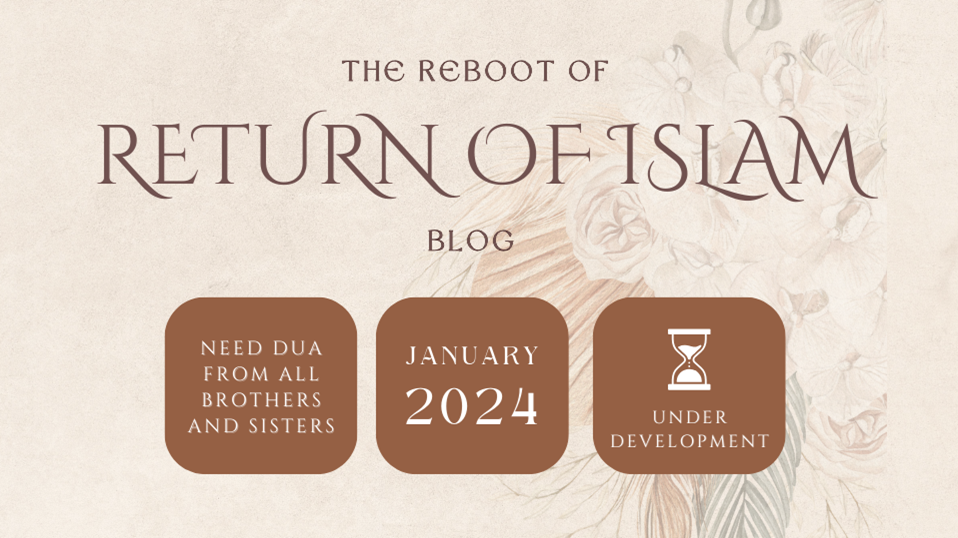ভূ-রাজনৈতিক কল্পকথা
আদনান খান
"আলিফ লাম মীম, রোমকরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্তর বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহ্র হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহ্র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" (সূরা রূম: ১-৫)
সূচীপত্র
- গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্বশর্ত
- পৃথিবী জনসংখ্যার আধিক্যে ভারাক্রান্ত
- চীন এবং ভারতের উন্নয়নই বৈশ্বিক উঞ্চায়নের জন্য দায়ী
- বিশ্বের তেলসম্পদ ফুরিয়ে যাচ্ছে
- ১৯৯০ সালে বলকান অঞ্চলে পশ্চিমাদের অনুপ্রবেশ মুসলমানদের সাহায্য করবার জন্য ছিল
- জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ততা প্রমাণ করে
- ঔপনিবেশিক শাসকরা আফ্রিকায় স্থিতিশীলতা নিয়ে এসেছিল এবং তাদের প্রস্থানই বর্তমান অস্থিতিশীলতার কারণ
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অজেয়
- ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করে
- চারটি যুদ্ধে ইতোমধ্যে ইসরাইল নিজেকে অপরাজেয় প্রমাণ করেছে; মুসলিম উম্মাহ্’র উচিত এর অস্তিত্বকে মেনে নেয়া
- খাদ্যের অপ্রতুলতাই তৃতীয় বিশ্ব দারিদ্রের কারণ
- তৃতীয় বিশ্বকে তাদের উন্নয়নের জন্যই অর্থনীতিকে আরও উদার করতে হবে
- বিশ্বায়ন হল মুক্তবাণিজ্যের শীর্ষ পর্যায় এবং একুশ শতকের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য
- পশ্চিমাদের বৈদেশিক সাহায্যই উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে ভুমিকা রাখছে
- বিগত দুই শতাব্দী ধরে বিশ্ব যে উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেখেছে তা ইতিহাসে বিরল এবং তা পুজিঁবাদের আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ
- মুসলিম বিশ্ব ইসলাম চায় না এবং তারা এর জন্য প্রস্তুতও নয়
- ইসলাম সেকেলে
- বিভিন্ন উপদল ও দেশে বিভক্ত হওয়ার কারণে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য নিতান্তই অসম্ভব
- ইসলামে কোনো শাসনব্যবস্থা নেই
- শিল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের কারণ মুক্তবাজার ও মুক্ত বাণিজ্য
- ঐতিহাসিকভাবে জাপানের উন্নয়ন এবং চীনের উন্নয়ন বিশ্বায়নের ফসল
- মুক্তবাজারের কারণে এশিয়ান টাইগারদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে
- মুসলিম বিশ্বের জন্য দুবাই এখন নতুন অর্থনৈতিক মডেল
- যুক্তরাষ্ট্র-ইরান দ্বন্দ্ব কি আসল?
গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্বশর্ত
প্রায় সব গবেষণায় ধরে নেয়া হয় যে, গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্বশর্ত – হোক সেটা অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত কিংবা বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন। মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির জগৎবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যানকার ওলসেন তার পুরষ্কারপ্রাপ্ত Power & Prosperity (2000)- গ্রন্থে উল্লেখ করেন, অন্যান্য যে কোন সরকার ব্যবস্থার চেয়ে গণতন্ত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতি বেশী হয়ে থাকে। ওলসেন যুক্তি প্রদান করেন যে, সাংঘর্ষিক পরিবেশ সবসময় ধ্বংসপ্রবণতা ও দুর্নীতিকে উষ্কে দেয়, অন্যদিকে একনায়কতন্ত্রে শাসককে বেশী সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে লুটপাটের প্রবনতা দেখা যায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তিনি পর্যবেক্ষণ করেন, ব্যক্তি এবং তার উন্নয়নকে এ ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়-কেননা শাসককে ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়। ওলসেন গণতন্ত্রের পথে অগ্রযাত্রার মধ্যে সভ্যতার উম্মেষ দেখতে পান যা অগ্রগতির পথকে সুগম করে। এর ফলে জনগণের ইচ্ছার সাথে আরও নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমে সুশাসন ফলপ্রসু হয়ে উঠতে পারে।
অন্যান্য গবেষণায়ও এটা বেরিয়ে এসেছে যে, গণতন্ত্র হল উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এমনকি ইলিয়নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইভান রডরিক যুক্তি প্রদান করেন যে, “‘বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান’ (মেটা ইনস্টিটিউশন) হিসেবে গণতন্ত্র অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং গণতন্ত্রই হল সাফল্যের একমাত্র পূর্বশর্ত”।
| গণতন্ত্রে প্রবেশ | |
| সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্জনের বছর | |
| নিউজিল্যান্ড | ১৯০৭ |
| ডেনমার্ক | ১৯১৫ |
| সুইডেন | ১৯১৮ |
| যুক্তরাজ্য | ১৯২৮ |
| ফ্রান্স | ১৯৪৬ |
| জার্মানী | ১৯৪৬ |
| ইতালী | ১৯৪৬ |
| বেলজিয়াম | ১৯৪৮ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৬৫ |
যদিও গণতন্ত্রের কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা নেই; তারপরও গণতন্ত্রের যে কোন সংজ্ঞায় দু’টি মৌলিক নীতি থাকতে হবে। প্রথম নীতিটি হল ক্ষমতায় সমাজের সকলের সমান অধিকার থাকতে হবে এবং সকলে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তি ভোগ করবে।
যেসব রাষ্ট্র গণতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের বিস্তার চায় তাদেরকে উপরের উপাত্তের সাথে মিলিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় যে, গণতন্ত্রের পক্ষে উপরে উল্লেখিত যুক্তিসমূহ মেলে না। অধিকাংশ উন্নত দেশসমূহে উন্নয়ন সুনিশ্চিত হয়েছে অগণতান্ত্রিক নীতিমালার কারণে এবং গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে। পশ্চিমে যখন সর্বপ্রথম ভোটকে কার্যকরী করা হয়-তখন এ সুযোগ কেবলমাত্র কিছু ধনী ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল এবং ভোটের গুরুত্বের দিক থেকে সম্পদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেয়া হত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের পর ভোটাধিকার আইন ১৯৬৫ এর মাধ্যমে শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ সালে মার্কিন সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের ভোটের অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা দক্ষিণের রাজ্যসমূহ ভোট কর প্রদানের মাধ্যমে বৈষম্যের স্বীকার হয়।
ফ্রান্স ১৮৩০ সালে ত্রিশোর্ধ ব্যক্তিদের ৩০০ ফ্রাঙ্ক প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করে – যারা ৩২ মিলিয়ন জনসংখ্যার মাত্র ০.০২% ছিল। ১৮৪৮ সালে পুরুষদের ভোট প্রদান সার্বজনীন হয় এবং শিল্পায়ন হওয়ার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নারীদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। জাপান ব্যাপক সামরিক শক্তি অর্জনের পর যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে চাপ দেয় তখনই ভোটদানকে সার্বজনীন করে। মার্কিনীরা জাপানকে ১৯৫২ সালে ভোট প্রদানের ক্ষমতা দিতে সম্মত হলেও তার নিজের দেশের জনগণকে পুরোপুরিভাবে তা দিতে আরও ১৩ বছর সময় নেয়।
১৮০০ সালে যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের স্বর্ণযুগ-তখন সেখানে মাত্র ৩ ভাগ জনগণ ভোটের অধিকার পায়। মধ্যযুগ থেকে প্রতি জেলায় বড় বড় ভূমিস্বামীরা কেবলমাত্র হাউস অব কমনসের সদস্য নির্বাচিত করতে পারত। এই ব্যবস্থা ভূমিহীন ব্যবসায়ী এবং দক্ষ শ্রমিকদের ভোটদানকে অস্বীকার করত। শত শত বছর ধরে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহকে সংসদে বারংবার গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হত। অথচ নতুন গড়ে উঠা শহরসমূহ সেভাবে উল্লেখ করা হত না। সংসদের কিছু কিছু আসন কিছু ব্যক্তির জন্য সবসময় সংরক্ষিত থাকত। ১৮৬৭ সালে জনসংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগ লোক ভোট দিতে পারত। ৬১বছর পর ১৯২৮ সালে পুরুষ মহিলা উভয়ের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্র এসেছে উন্নয়নের পর এবং বৃটেনের উন্নয়নে এর কোন ভূমিকা ছিল না।
উন্নত বিশ্বকে অনুসরণ করে বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলো অনেক বেশী পরিমাণে জনগণকে ভোটার অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ করে দিয়েছে। অথচ গণতন্ত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে-এ ধারণা গ্রহণ করার আগে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
চীন, রাশিয়া (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন) এবং জার্মানী কার্যতই প্রমাণ করেছে যে, গণতন্ত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত নয়। রাশিয়া এবং চীন পশ্চিমা উদারপন্থী গণতন্ত্রকে অনুসরণ না করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশ এগিয়ে গেছে। সেকারণে এখন প্রশ্ন করার সময় এসেছে, গণতন্ত্রের সাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতির আদৌ কি কোন সম্পর্ক আছে?
অর্থনৈতিক অগ্রগতি বলতে একটি দেশের নিজস্ব স্বার্থে জনগণকে সাথে নিয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে শিল্পোন্নত হওয়াকে বুঝায়। এর জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দরকার যা পুরো দেশকে একটি লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে। আর না হয় তা হবে দ্বান্দ্বিক। ব্রিটেনের মূল প্রণোদনা আসে গীর্জার আধিপত্য খর্ব করে উদার মূল্যবোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে। মূলত: এর ভিত্তিতে তারা একত্রিতও হয়েছিল। অভিজাত শ্রেনী কর্তৃক সম্পদ ও ভূমির মালিক হবার সুযোগ লাভ এবং এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিকতার গতিপথ নির্ধারনের ক্ষমতা তাদের উন্নতি সুনিশ্চিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জারদের ব্যর্থতা থেকে প্রণোদনা লাভ করে এবং পরবর্তীতে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে একত্রিত হয়। পরবর্তীতে তাদের অর্থনীতিবিদেরা সমাজতান্ত্রিক জীবনদর্শন থেকে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। মার্কিনীরা ব্রিটেনের কাছ থেকে মুক্ত হবার পর একত্রিত হয়ে কাজ শুরু করে। আর জাপানীরা যখন বুঝতে পারল তারা উন্নত বিশ্বব্যবস্থা থেকে কতটা পিছিয়ে আছে, তখনই অর্থনীতিকে উন্নত করার যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল। চীন একমাত্র দেশ-যার উন্নয়ন কেবলমাত্র আদর্শিক নয়। তবে সেদেশের নীতি নির্ধারকরা জনগণের ভেতর ‘চীনারা একটি মহান জাতি’ এ চেতনাবোধ জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছে। জার্মানীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এমনকি তারা বর্ণবাদকে উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করে।
প্রকৃত প্রস্তাবে গণতন্ত্র উন্নয়নের জন্য কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। সেকারণে উপরে উল্লেখিত দেশসমূহ কখনই জনগণের রায়ের জন্য অপেক্ষমান থাকেনি। উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক খুবই দুর্বল। বর্তমানে যারা গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলে তারা গণতান্ত্রিক হয়েছে উন্নত হবার পর। আর চীন প্রমাণ করে উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্র কোন বিষয়ই নয়।
পৃথিবী জনসংখ্যার আধিক্যে ভারাক্রান্ত
জিনের গঠন নিয়ে বর্তমান আধুনিক গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, ১৫০০০ বছর আগে পৃথিবীর জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ মিলিয়ন (বর্তমান ঢাকা ও দিল্লীর সমান)। যীশু খ্রীস্টের সময় অর্থাৎ আজ থেকে ২০০০ বছর আগে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫০ মিলিয়ন (বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার সমান)। শিল্প বিপ্লবের শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৮০০ শতকের দিকে জনসংখ্যা তিনগুন বেড়ে দাঁড়ায় ৭০০ মিলিয়ন (বর্তমান ইউরোপের সমান)। গত দুই শতাব্দীতে বার্ষিক ৬ ভাগ হারে বৃদ্ধিতে ১৯৫০ সালে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২.৫ বিলিয়ন। আর ২১ শতকের শুরুর দিকে বিগত ৫০ বছরে শতকরা ১৮ ভাগ হারে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ বিলিয়ন। যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গেছে এবং কিছু কিছু এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে, তারপরেও ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৯ বিলিয়ন। সেপ্টেম্বর ২০০৮ অনুসারে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬.৭২ বিলিয়ন।
বিগত শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এমন মাত্রায় এসে পৌঁছেছে যে, একেই দেখানো হয় পৃথিবী এখন বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনিত হবার মূল কারন হিসেবে। যু্ক্তি দেখানো হয় যে, আমরা এখন এই বিশাল জনসংখ্যাকে যোগান দেয়ার মত খাদ্যেও অপ্রতুলতার সম্মুখীন। এছাড়াও বলা হয় এ ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি দরিদ্রতা, পরিবেশ বিপর্যয়, সামাজিক অস্থিরতা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহের অনুন্নয়নের জন্য দায়ী। এ কারণে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং সরকারসমূহ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নানাবিধ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।
তথাকথিত এই অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে এমন কোন কিছুর সাথে তুলনা করতে হবে যা সীমিত। আর তা হল পৃথিবীর মোট সম্পদের পরিমাণ।
| বিশ্বের জনসংখ্যা ২০০৭ | |
| ১. সমগ্র বিশ্ব | ৬.৭ বিলিয়ন |
| ২. এশিয়া | ৩.৯ বিলিয়ন |
| ৩. চীন | ১.৩ বিলিয়ন |
| ৪. ভারত | ১.১ বিলিয়ন |
| ৫. আফ্রিকা | ৮৮৭ মিলিয়ন |
| ৬. ইউরোপ | ৭৭৪ মিলিয়ন |
| ৭. লাতিন আমেরিকা | ৫৫৮ মিলিয়ন |
| ৮. উত্তর আমেরিকা | ৩৩২ মিলিয়ন |
| ৯. যুক্তরাষ্ট্র | ৩০৪ মিলিয়ন |
| ১০. ইন্দোনেশিয়া | ২৩১ মিলিয়ন |
| ১১. ব্রাজিল | ১৮৭ মিলিয়ন |
| ১২. পাকিস্তান | ১৬৩ মিলিয়ন |
| ১৩. বাংলাদেশ | ১৫৮ মিলিয়ন |
| জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ জনসংখ্যা বিভাগ | |
কিন্তু খুব সূক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর অনেক বড় বড় সমস্যা – যেগুলোর দায়ভার জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর চাপানো হয়েছে-তা আদৌ সঠিক নয়। বরং এগুলোর পেছনে রয়েছে স্পষ্ট রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য। মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখবার জন্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে সামনে তুলে ধরা হয়েছে। মূল সমস্যা হল জীবনযাপন প্রণালী, ভোগবাদী মনোবৃত্তির স্ববিনাশী প্রবণতা, দরিদ্রতা এবং নিজেদের স্বাচ্ছন্দের স্বার্থে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শোষণ করবার হীন মানসিকতা।
উন্নত বিশ্ব বিশেষত: জাপান, রাশিয়া, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড এবং পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ আরেকটি বড় সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে-যা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের নিম্নগতি। পশ্চিমের অন্যান্য অংশেও এ নিম্ন হার অব্যাহত রয়েছে। তবে অভিবাসনের মাধ্যমে সেটা কিছুটা ঠেকানো হয়েছে। যদি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোসহ পুরো মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার অব্যাহত থাকে, তাহলে তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব আনুপাতিক হারে বেড়ে যাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঠেকানো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে শক্তিশালী হওয়া জাতিকে পদানত করবার এক হীন প্রক্রিয়া। এ ব্যাপারটি স্পষ্ট ফুটে উঠবে তুরষ্কের ইউরোপীয় ইউনিয়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। প্রায় ৭০ মিলিয়ন জনসংখ্যার অনুপাতে ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য রয়েছে তুরষ্কের। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এটা প্রমাণ করে ২০২০ সালের মধ্যে পার্লামেন্টে এ দেশটি জার্মানীকে ছাড়িয়ে যাবে। তুরষ্কের অন্তর্ভুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ফেলবে। সে কারণে ফ্রান্সের ভ্যালেরি গিসকার্ড ডি’এস্টাইং তুরষ্কের অন্তর্ভুক্তিতে আপত্তি তুলেন। ডি’এস্টাইং- এর মতে তুরষ্কের অন্তর্ভুক্তি মরক্কোর অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করবে।
যদিও এ ব্যাপারে কোন ঐকমত্য নেই যে, কেন ব্রিটেন পৃথিবীর প্রথম শিল্পোন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারপরেও যে আটটি পূর্বশর্তের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা হয়; তার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি। ১৭০৭ সালে স্কটল্যান্ডের সাথে সংযুক্তির পর ব্রিটেনের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৬.৫ মিলিয়ন। এক শতাব্দী পর সেটি প্রায় দ্বিগুন হয়ে দাঁড়ায় ১৬ মিলিয়ন। ১৭৫০ এর পরে এ বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ-যা ব্রিটেনের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি থেকে তৈরি হয় দক্ষ শ্রমিক এবং ভোক্তা।
চীন এবং ভারত ইতোমধ্যে প্রমাণ করতে সমর্থ্য হয়েছে যে, বিরাট জনসংখ্যা এক বড় আর্শীবাদ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে সংকুচিত করবার অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকলেও চীন ও ভারত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক থেকে অন্যতম বৃহৎ দু’টি দেশ। এই জনসংখ্যার উচ্চ বৃদ্ধি হারের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাদের অর্থনীতি। যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফলতার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক।
পৃথিবী কখনই জনসংখ্যা ভারক্রান্ত নয়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তুলনায় এখনও অতিরিক্ত সম্পদ রয়ে গেছে। যদিও তার সিংহভাগ পশ্চিমারা একা ভোগ করছে।
চীন ও ভারতে উন্নয়নই বৈশ্বিক উঞ্চায়নের জন্য দায়ী
জলবায়ু পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সব বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করলে এটা ঠিক বিজ্ঞান নয়। জলবায়ু বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। জলবায়ু পরিবর্তন নতুন কিছু নয়, সবসময় জলবায়ু পরিবর্তন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। যেমন-বরফ যুগ, যখন বিশ্বের তাপমাত্রা দীর্ঘ সময়ের জন অত্যন্ত কম ছিল।
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন বলতে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বুঝায়। প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট কারণ বিশ্বের গড় তাপমাত্রার এই বৃদ্ধির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয় – আর এটাই এখন বিতর্কের বিষয়। এই উষ্ণায়নের জন্য প্রধানত দায়ী গ্রীনহাউসের বৃদ্ধি অর্থাৎ বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এটা হল মুলত বায়ুমন্ডলের কিছু গ্যাস কর্তৃক কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মত তাপ নির্গমনকারী গ্যাসসমূহকে আটকে ফেলার প্রক্রিয়া। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এ সময়কাল শিল্প বিপ্লবের সমসাময়িক- যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। এর ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণের পরিমাণের সাথে উষ্ণায়নের আনুপাতিক সম্পর্কের দিকে নির্দেশ করে। আরও অনেকের মত আল গোরও বলেন, এই গ্যাসটিই বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রধানত দায়ী। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণকেই বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ হিসেবে গন্য করা হয়। যদিও এটিই শেষ কথা নয় এবং এ সিদ্ধান্তে পৌছানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নমুনাগুলোর বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে।
প্রতি কয়েক বছর পর পর, জাতিসংঘের জলবাযু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তসরকার প্যানেল (আই.পি.সি.সি) এর বিখ্যাত জলবায়ু বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গবেষণার অগ্রগতি সর্ম্পকিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। উষ্ণায়ন হ্রাসের জন্য নিঃসরণ কমানো উচিত বলে তারা শুরু থেকেই সুপারিশ করে আসছেন। সারা বিশ্বের শত শত বিজ্ঞানীদের নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত। আই.পি.সি.সি-এর চতুর্থ তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন জানুয়ারী ২০০৭ অনুসারে, “তৃতীয় মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে জলবায়ুর উষ্ণায়ন এবং শীতলীকরণের নৃতাত্বিক প্রভাবকগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। ফলাফল ̄স্বরূপ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ১৭৫০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী মানুষের কর্মকান্ডের গড় নীট পরিণতি হল উষ্ণায়ন- এই সম্ভাবনাই অতি প্রবল।’ তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী “অতি প্রবল সম্ভাবনা” এবং “খুব সম্ভব” এর ধারণা ৯০ ভাগ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাকে অন্তর্ভূক্ত করে (যদিও ২০০১ এর রিপোর্ট অনুসারে ৬৬ ভাগ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল)।
বিশ্বের দূষণকারী দেশসমূহ (২০০৪)
মানব কর্মকান্ডের মাধ ̈মে কার্বন -ডাই-অক্সাইড নিঃসরনকে
মোট নিঃসরেেনর শতকরা ভাগ হিসেবে গণনা করে
১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২২%
২. চীন ১৮%
৩. রাশিয়া ৫%
৪. ভারত ৪.৯%
৫. জাপান ৪.৬%
৬. জার্মানী ৩.১%
৭. কানাডা ২.৩%
৮.যুক্তরাজ্য ২.২%
৯. দক্ষিন কোরিয়া ১.৭%
১০. ইতালী ১.৬%
ইতিহাস বলে যে, আজ পর্যন্ত শতকরা ৮০ ভাগ নিঃসরণের জন শিল্পোন্নত বিশ্ব দায়ী। ১৯৫০ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বসাকুল্যে এ পর্যন্ত ৫০.৭ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করেছে। একই সময়ে চীন করেছে ১৫.৭ বিলিয়ন টন (যেখানে আমেরিকার তুলনায় চীনের জনসংখ্যা ৪.৬ গুন বেশী) এবং ভারত করেছে ৪.২ বিলিয়ন টন (যেখানে আমেরিকার তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা ৩.৫ গুন বেশী)। শিল্পোন্নত বিশ্বে যেখানে পৃথিবীর ২০ ভাগ লোক বসবাস করে সেখানে ৬০% ভাগ কার্বন নিঃসরণ হয়।
শিল্প বিপ্লবের শুরুর দিক থেকেই শিল্পোন্নত বিশ্ব ব্যপক পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ করে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ১৪ ট্রিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থনীতি নিয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দূষণকারী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে কোন ধরণের নিঃসরণ হ্রাসকারী চুক্তির ব্যাপারে বাধাদানকারী দেশ হিসেবেও এ দেশটির ভূমিকা রয়েছে। নিঃসরণ কমানোর অর্থ হচ্ছে পশ্চিমাদের উৎপাদন কমাতে হবে-যা তাদের অর্থনীতি-পুঁজিবাদকে সংকুচিত করবে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহার কার্বন নিঃসরণের আরও একটি প্রধান কারণ। মার্কিনীদের মাত্রাতিরিক্ত ভোগের কারণেই পরিবেশ দূষণ বেড়েই চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বৈশ্বিক গড় ব্যবহারের প্রায় পাঁচ গুন।
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন পশ্চিমাদের ব্যপক শিল্পায়নের মাধ্যমে অধিক মুনাফা করার হীন প্রবৃত্তি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। নিঃসরণ কমানোর উন্নত প্রযুক্তি থাকলেও এর সাথে প্রচুর ব্যয় যুক্ত থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে রাজী নয়। কেননা এতে করে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজারে মার্কিন পণ্য কম মূল্যে বিক্রি হবে না । মাত্র ২০ বছর আগে চীন এবং ভারত উন্নয়নের ব্য়পক ধারায় সংযুক্ত হয়। কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যাটি আরও পুরনো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি হিসেবে ভারত ও চীনের উন্নয়নের গতিতে পরশ্রীকাতর হয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন তাদেরকে দোষারোপ করে আসছে।
বিশ্বের তেল কি ফুরিয়ে যাচ্ছে?
বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটেন ও জার্মানীর বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বজায় রাখার দ্বন্দ্ব তাদেরকে তাদের কয়লাভিত্তিক বৃহদাকার যুদ্ধযানগুলোর জন্য বিকল্প জ্বালানী উৎসের অনুসন্ধানের দিকে ঠেলে দেয়। আর ঐ সমসাময়িক সময়েই মধ্যপ্রাচ্যে তেলক্ষেত্রগুলোর আবিষ্কার ও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন নতুন ধারার ভোগের সমাজব্যবস্থা ও বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করে।
স্বাভাবিকভাবেই জীবাশ্ম জ্বালানি অপ্রতুল এবং এটা একসময় শেষ হয়ে যাবে। বিংশ শতাব্দী জুড়ে অধিকাংশ তেলক্ষেত্রগুলোর অধিকাংশ অনাবিষ্কৃত থাকায় তেলের বিষয়টি খুব একটা আলোচনায় আসেনি। পরবর্তিতে জঙ্গি বিমান, ট্যাঙ্ক, অটোমোবাইল ইত্যাদির আবিষ্কার এ জ্বালানীর উপর সবার নির্ভরশীলতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদি একসময় তেল শেষ হয়ে যায় তাহলে এসব যন্ত্রপাতি ও প্রযু্ক্তি একেবারেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।
১৯৭০ সালে প্রথম ‘পিক অয়েল’ থিওরী আবির্ভূত হয়। এর মাধ্যমে দেখানো হয় তেলের সেই পরিমান যে পরিমান উত্তোলন হলে পৃথিবীর মোট তেলের অর্ধেক উত্তোলন করা হবে।
বিশ্বের তেল মজুদের পরিমান (২০০৬)
==============================
বিশ্ব ১.১৩ ট্রিলিয়ন
সৌদি আরব ২৬০ বিলিয়ন
কানাডা ১৭৯ বিলিয়ন
ইরান ১৩৬ বিলিয়ন
ইরাক ১১৫ বিলিয়ন
কুয়েত ৯৯ বিলিয়ন
সংযুক্ত আরব আমিরাত ৯৭ বিলিয়ন
ভেনিজুয়েলা ৮০ বিলিয়ন
রাশিয়া ৬০ বিলিয়ন
লিবিয়া ৪১ বিলিয়ন
নাইজেরিয়া ৩৬ বিলিয়ন
ইউ.এস.এ ২১ বিলিয়ন
বিপি বিশ্বের জ্বালানীর পরিসংখ্যাগত পর্যালোচনা ২০০৭
===============================
ভবিষ্যতে কতটুকু তেল উৎপাদন করা যাবে তা নিরূপনের জন্য তিনটি উপাত্ত খুব দরকার। প্রথমে দরকার হল, এ পর্যন্ত সর্বমোট কত ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হয়েছে- যাকে সর্বমোট উৎপাদন বলা হয়। দ্বিতীয়ত দরকার হল, বিভিন্ন কোম্পানীগুলো একটি তেলক্ষেত্রকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করবার আগে কতটুকু তেল উত্তোলন করতে সমর্থ্য হবে। সবশেষে দরকার হল, একটি বিশেষজ্ঞ দল অনাবিষ্কৃত ও উত্তোলনযোগ্য তেলের পরিমাণ সম্পর্কে গবেষণা ভিত্তিক তথ্য প্রদান করবে। এই তিনটি উপাত্ত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাবে কয়েক দশক পর থেকে এই খনিটি পরিত্যক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত ঠিক কতটুকু তেল উত্তোলন করা সম্ভবপর হবে- একে সর্বমোট উত্তোলন বলে।
সর্বোচ্চ কি পরিমাণ তেল উৎপাদিত হবে তা বুঝার জন্য এ পর্যন্ত উৎপাদিত তেল আবিষ্কৃত তেলের পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেল কিনা সেদিকে তাকাতে হবে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল প্রমাণ হল এ পর্যন্ত তেলক্ষেত্র আবিষ্কারের দিক থেকে ১৯৬০ এর দশক ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ের সর্ববৃহৎ তেলক্ষেত্রটি ১৯৮৫ সালে মেক্সিকোতে আবিষ্কৃত হয় আর ১৯৫০ এর দশকে আবিষ্কৃত তেলক্ষেত্রগুলোর উৎপাদন প্রায় শেষের দিকে। অথচ পৃথিবীতে এখন যে পরিমান তেল উৎপাদন হচ্ছে তার প্রায় চারগুন ব্যবহার হয়। ফলে তেল কোম্পানিগুলো নতুন তেলক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু যাই মিলছে তা আবার ছোট ছোট এবং উৎপাদনও খুবই যৎসামান্য। নতুন নতুন তেল ক্ষেত্রর আবিষ্কার নিম্নগামী হওয়ায় এবং তেলের উত্তোলন অব্যাহত থাকায় কালোসোনার বর্তমান মজুদও নিঃশেষ হবার দিকেই এগুচ্ছে।
কোন কোন অতি উৎসাহী ভবিষ্যতদ্রষ্টা বলেন যে, ২০৬০ সাল পর্যন্ত তেলের সর্বোচ্চ (পিক) উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা হল, বর্তমান সময় থেকে ২০১২ সালের মধ্যেই তেলের উৎপাদন সর্বোচ্চ (পিক) পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাবে।
আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকাতে পারি যারা ইতোমধ্যে তেল উৎপাদনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে অথবা অতি শীঘ্রই যাবে। তেল উৎপাদনের দিক থেকে প্রথম সাতটি দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে হয় তাদের উৎপাদন নিম্নমুখী অথবা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালে, নরওয়ে ২০০১ সালে এবং ব্রিটেন ১৯৯৮ সালে সর্বোচ্চ উৎপাদনে পৌঁছে গেছে। রাশিয়া, মেক্সিকো ও চায়না ২০০৮ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে। সৌদি আরব ২০০৫ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ইরানই কেবল এ উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে।
বৈশ্বিক তেল ব্যবহারের পরিমান (ব্যারেল প্রতিদিন ২০০৭)
========================================
বিশ্ব ৮৫ মিলিয়ন
ইউ.এস.এ ২০.৬ মিলিয়ন ২৪%
চীন ৭.৮ মিলিয়ন ৯.৩%
রাশিয়া ২.৬ মিলিয়ন ৩.২%
জার্মানী ২.৩ মিলিয়ন ২.৮%
ফ্রান্স ১.৯ মিলিয়ন ২.৩%
ইউকে ১.৬ মিলিয়ন ২%
স্পেন ১.৬ মিলিয়ন ২%
বিপি বিশ্বের জ্বালানীর পরিসংখ্যাগত পর্যালোচনা ২০০৭
=======================================
এছাড়াও আরও অনেক কারণ থাকতে পারে যেগুলো দ্রুত তেল উৎপাদনের শেষপ্রান্তে পৌঁছানোর জন্য দায়ী। সেকারণে বড় বড় তেল কোম্পানীগুলোর (যেমন: শেল) জন্য তেলের মজুদ সম্পর্কে করা অতিরঞ্জিত বক্তব্য মেলানো কঠিন হয়ে পড়েছে।
বর্তমান মজুদকে সামনে নিয়ে এসে তেল উৎপাদনকারী দেশের সংগঠনগুলো তেল ঘাটতিকে ঢাকবার চেষ্টা করছে। তেল উৎপাদনকারী কোম্পানী যেমন ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম নতুন তেলক্ষেত্র আবিষ্কার নয় বরং পুরনো ক্ষেত্রগুলো থেকে তেল উত্তোলন চুক্তির ভিত্তিতে মজুদ সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে। নতুন তেলক্ষেত্র আবিষ্কারের পেছনে বিনিয়োগ বরাবরই কমছে। সৌদি আরবের অধিকাংশ ক্ষেত্রসমূহে চালানো বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধানে তেল প্রাপ্তির নিম্নমুখী প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, ভারত, চীন ও অন্যান্য এশিয়ান দেশসমূহের প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে তেল ও গ্যাস ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।
এ কারণসমূহ ‘তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে’- এ ধরণের প্রচারণাকে মূল ধারায় নিয়ে এসেছে এবং এটি এখন বিশ্বশক্তিসমূহের ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এর আড়ালে আরও কিছু রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে।
পশ্চিমাদের অতিরিক্ত তেল খরচার উপযুক্ত অজুহাত হল তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। সীমিত মজুদের তেল সম্পদের প্রতি অন্যান্য জাতিরাষ্ট্রসমূহের চাহিদা তৈরি হোক এটা পশ্চিমারা চায় না। পশ্চিমারা মোট তেল উৎপাদনের চার ভাগের এক ভাগ করলেও প্রায় অর্ধেক তারা ভোগ করে। তাদের অতিরিক্ত ব্যয়ই তেল সম্পদ ফুরিয়ে যাওয়ার পেছনে মূল কারণ-তেলের প্রাকৃতিক মজুদ নয়।
যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ৮ ভাগ তেল উৎপাদন করলেও প্রায় ২৫ ভাগ তেল খরচ করে। তাদের এ বিশাল খরচ বহন করা অসম্ভব। কারণ মাত্র কয়েকটি বিশাল তেলক্ষেত্রের উপরই তাদের তেলের সিংহভাগ চাহিদা পূরণের দায়ভার বর্তায়। পুরো পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার তেলক্ষেত্র থাকলেও মাত্র ১১৬ টি ক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন ১০০০০০ ব্যারেল উৎপাদিত হয়-যা পুরো বিশ্বের উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ। এদের হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি ছাড়া বাকীগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে সিঁকি শতাব্দীরও আগে। যেগুলো এখন প্রায় ফুরিয়ে যাবার পথে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে সৌদি আরবের ঘাওয়ার, কুয়েতের বারগান, মেক্সিকোর কেণ্টারেল এবং রাশিয়ার সামোতলর-এখন উৎপাদনের দিক থেকে নিম্নমুখী। এসব বৃহৎক্ষেত্রসমূহের নিম্নমুখী উৎপাদন একটি বড় ঘটনা। এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ছোট ছোট ক্ষেত্রসমূহের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হবে। তবে এর মাধ্যমেও সমস্যার সমাধান সুদূর পরাহত। যেহেতু মার্কিন তেল খরচ বেড়েই চলেছে সেহেতু সীমিত মজুদের এ জ্বালানীশক্তিকে ঘিরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েই চলবে। একারণে ইরাকের মত মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অংশও এ কালো সোনার জন্য মার্কিনীদের রাহুগ্রাসের শিকার হতে পারে।
তেল সম্পদের স্বল্পতার জন্য নয় বরং পশ্চিমা বিশ্বের তেলের অতিরঞ্জিত ব্যবহারই তেল ফুরিয়ে যাবার প্রধান কারণ।
১৯৯০ সালে বলকান অঞ্চলে পশ্চিমাদের অনুপ্রবেশ মুসলমানদের সাহায্য করবার জন্য হয়েছিল
একটি যুক্তিসঙ্গত শান্তি প্রস্তাবনার আওতায় বিশেষত কসোভোতে একটি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনায় যুগোস্লাভিয়ার একপেঁশে অস্বীকৃতি জানানোকে ১৯৯৩ সালে পশ্চিমারা ন্যাটো কর্তৃক যুগোস্লাভিয়া আক্রমণের পেছনে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। ন্যাটো কর্তৃক বলকান অঞ্চলে হস্তক্ষেপ এবং বোমাবর্ষনের মাধ্যমে মাধ্যমে পশ্চিমারা বর্তমান “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ” কে শুধুমাত্র ইসলামের বিরুদ্ধে একটি অভিযান বলতে নারাজ; বরং তারা বলতে চায়, পৃথিবীর যেখানে মানবতা আক্রান্ত হয় সেখানেই এ অভিযান অব্যাহত থাকবে-এমনকি মুসলিমদের রক্ষার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাবেক উপদেষ্টা ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র জেমস রুবিন ২০০৩ সালে এ ব্যাপারে সাফাই গাইতে গিয়ে বলেন, ‘ইরাক দখল, কসোভোতে মুসলিমদের গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা করা এবং বসনিয়ায় বিলম্বিত মার্কিন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আমেরিকা মানবাধিকার রক্ষায় তার দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটিয়েছে।’
বাস্তবে ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য অন্যরকম। ১৯৯০ সালে বলকান অঞ্চলে সংঘটিত অস্থিরতা ছিল অত্র অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্যকে বিচূর্ণ করে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, তার উপর ইউরোপ এর নির্ভরশীলতা বাড়ানো এবং ন্যাটোকে নতুন ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে ঠান্ডা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এর উপযোগিতা প্রমাণ করা।
পশ্চিমারা বিশেষত মার্কিন এবং বৃটিশরা যুগোস্লাভিয়াকে টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। যা যুগোস্লাভিয়ায় অবস্থিত মার্কিন দূত ওয়ারেন জিমারম্যানের কথায় ফুটে উঠে, ‘আমরা যুগোস্লাভিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছি।’ ১৯৯২ এর ১৮ মার্চ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন লিসবনে বসনিয়ান মুসলিম, ক্রোয়েট এবং সার্বিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সার্বিয়ান প্রজাতন্ত্রকে তিনটি জাতিভিত্তিক অঞ্চলে বিভক্ত করে কনফেডারেশনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করতে চায়। মার্কিনীরা এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে বসনিয়ান নেতা আলিজা ইজতবেগোভিচকে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়ে বলতে বলেন, “মার্চের ১ তারিখে অনুষ্ঠিত গনভোটের মাধ্যমে এর যৌক্তিকতা প্রমানিত হয়েছে”। পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেক্রেটারী জেনারেল জোসে কিউটিলেরো বলেন, “সত্যি কথা বলতে আসলে প্রেসিডেন্ট আলিয়া এজেদবেগোভিক এবং তার সহযোগিরা এই চুক্তিটি না মেনে একক বসনিয়ো রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পশ্চিমা মদ্ধস্ততাকারীদের কাছ থেকেই”। এভাবেই বসনিয়ান গৃহযুদ্ধের শুরু।
আজকে বসনিয়া, কসোভো ও মেসেডোনিয়ায় শান্তিরক্ষার জন্য ১১০০০ সৈন্য উপস্থিতি রয়েছে-যা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সংরক্ষণ করছে। নিউইয়র্ক টাইমসের সাথে প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান লি হ্যামিল্টন বলেন, ‘আমরা পুরোপুরি বলকান অঞ্চলের নিয়ন্ত্রন নিয়ে নিয়েছি। মার্কিন কর্মকর্তাগণ সাবেক যুগোস্লাভিয়ার সর্বত্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। আমরাই মুলত; দেশ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত।
ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ কারেন টালবোটের মতে, ‘যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো পুরো যুগোস্লাভিয়া বিশেষত কসোভোকে অফুরান প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য দখলে রাখতে চায়। রাশিয়ার পশ্চিমে পুরো ইউরোপের মধ্যে এককভাবে কসোভোতে সবচেয়ে দামী প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ রয়েছে।’
নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, ‘রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশাল ট্রেপকা মাইনিং কমপ্লেঙ্ হল বলকানদের সবচেয়ে মূল্যবান ভূ-সম্পত্তি। এর মূল্য কমপক্ষে ৫ বিলিয়ন ডলার, এতে উৎপাদিত হয় স্বর্ণ, রৌপ্য, বিশুদ্ধ শীশা, দস্তা, ক্যাডমিয়াম এবং প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার মুনাফা হয়। কসোভোর আরও আছে ১৭ বিলিয়ন টন কয়লা ভান্ডার এবং কসোভোর (সার্বিয়া এবং আলবেনিয়ার মত) তেল বন্দরও আছে’।
প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনতো একবার বলেই বসলেন, ‘পুরো পৃথিবীব্যাপী পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে আমরা যদি একটি শক্তিশালী অর্থনীতির দিকে যেতে চাই তাহলে ইউরোপকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে….আর এর জন্যই কসোভোকে দরকার।’
বোমাবর্ষণ শেষ হওয়ার পর মার্কিনীরা বলকান অঞ্চলে অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। কসোভোতে মার্কিনীরা একটি বড় সামরিক ঘাঁটি করে-যা ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর বিদেশে করা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। ন্যাটোতে মার্কিনীদের ব্যাপক প্রভাব মূলত: এ অঞ্চলে ন্যাটোর আড়ালে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যকেই মজবুত করেছে। ফাঁস হয়ে যাওয়া পেন্টাগণের ১৯৯৪-১৯৯৯ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা নির্দেশনা রিপোর্টে বলা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে, ‘ইউরোপীয়ানদের প্রাধান্য সৃষ্টির যে কোন পথ রুদ্ধ করতে হবে-যা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ন্যাটোকে চ্যালেঞ্জ করবে….একারণে পশ্চিমা নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রাথমিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার এবং ইউরোপের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর প্রভাব ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাটোকে রক্ষা করা মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।’
সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বলা যায় যে, রাশিয়ার প্রভাবকে ক্ষুন্ন করা, কাস্পিয়ান সাগরে তেল সম্পদ এবং ন্যাটোর মাধ্যমে মার্কিন আধিপত্যকে আরও বেশী পাকাপোক্ত করাই ছিল বলকান অঞ্চলে পশ্চিমা হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য। হাজারও নিষ্পাপ মানুষের জীবন এবং সেব্রেনিৎজায় অসংখ্য লাশ ছিল মার্কিনীদের এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার চরমমূল্য।
জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ততা প্রমাণ করে
ভবিষ্যতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নিষ্ঠুরতা ও গণহত্যার মত ভয়াবহ কিছু যাতে না ঘটে সেজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একটি বিশ্বসংস্থার ব্যাপারে ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠিত হয় প্রধানত ‘পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে যুদ্ধের উন্মাদনা থেকে রক্ষার জন্য’ এই উচ্চাভিলাষী চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে । সেসময় থেকে পুরো পৃথিবী প্রায় ২৫০ টি সংঘাতের মধ্য দিয়ে গেছে। সেকারণে এটা জোর দিয়ে বলা যায়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।
পশ্চিমা বিশ্ব এমনকি তৃতীয় বিশ্বের অনেক নীতিনির্ধারকেরা মনে করেন জাতিসংঘ হল ২০০টির মত সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটিনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা-যেটি আন্তর্জাতিকতাবাদ, বহুপক্ষীয় কর্মকান্ড, গণতন্ত্র, পরমতসহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সহনশীলতা, মানবাধিকার ও স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্ধুদ্ধ। এর থেকে বড় মিথ্যাচার কিছু হতে পারে না।
বাস্তবে জাতিসংঘ হল সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যসমূহের শোষণ ও নিপীড়নকে আইনগত বৈধতা দেবার জন্য গড়ে তোলা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।
১৯৯৪ সালে স্থায়ী সদস্যসমূহের সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হওয়ায় ১০ লক্ষ জনগণের গণহত্যার স্বীকার হয় রুয়ান্ডা। ফ্রান্স (নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য) তুতসীদের বিরুদ্ধে হুতো উপজাতীয়দের সমর্থন দিয়ে উপনিবেশকালীন সময়ের মত একটি গৃহযুদ্ধের অবতারণা করল। এ যুদ্ধকালীন সময়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীকে কেবলমাত্র রুয়ান্ডায় অবস্থিত বিদেশীদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু তুতসীদের সহায়তায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সেসময় বেলজিয়ান শান্তি রক্ষীরা ২০০০ উদ্বাস্তুসহ একটি টেকনিক্যাল স্কুল ছেড়ে চলে যায় যখন বাইরে হুতু জঙ্গীরা অপেক্ষমান ছিল। শান্তিরক্ষীদের প্রস্থানের পরই জঙ্গীরা স্কুলে প্রবেশ করে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তার শিকার হয় শত শত শিশু। এর চারদিন পরই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তার শান্তিরক্ষী কমিয়ে ২৬০ এ নামিয়ে নিয়ে আসার পক্ষে মতামত প্রদান করে।
এর এক বছর পর সেব্রেনিৎজার গণহত্যার সময় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। বৃটেন এবং আমেরিকা উভয়ই চাচ্ছিল এ অঞ্চল ভেঙে টুকরো টুকরো হোক। কিন্তু আমেরিকা ন্যাটোকে একটি কার্যকরী ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিল। জাতিসংঘ ৬০০ ডাচ শান্তিরক্ষী নিয়োগ করে সেব্রেনিৎজাকে উদ্বাস্তদের জন্য ‘নিরাপদ আশ্রয়’ ঘোষণা দেয়। পরবর্তীতে এই ডাচরা সেব্রেনিৎজার উদ্বাস্তুদের সার্ব বাহিনীর হাতে তুলে দেয় এবং তারা ইতিহাসের ন্যক্কারজনক গণহত্যা চালায়।
জাতিসংঘ গণতান্ত্রিক রিপাবলিক কঙ্গোতে দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধেও ভূমিকা পালনে আবারো ব্যর্থ হয়। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারীতে নিরাপত্তা পরিষদের ১২৯১ নং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হয়। এই শান্তিরক্ষা বাহিনীও গৃহযুদ্ধে ৫০ লক্ষ লোকের গণহত্যা ঠেকাতে পারেনি।
প্যালেস্টাইন-ইসরাইল ইস্যুতেও জাতিসংঘ সমানভাবে ব্যর্থ। ইসরাইলের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ আইনসম্মত উপায়ে নিরাপত্তা পরিষদে একটি নিন্দা প্রস্তাব প্রদানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছে।
জাতিসংঘ ভীষণভাবে অকার্যকরী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংস্থা হিসেবে পরিস্ফুট হয়ে উঠে দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধের সময়। সেসময় যুক্তরাষ্ট্র কোন রাখঢাকের দরকার মনে করেনি। জাতিসংঘে তাদের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জন বোল্টন জাতিসংঘের সম্পর্কে ২০০৪ সালে বলেন, ‘জাতিসংঘ বলতে কোন জিনিস আসলে অস্তিত্বহীন। যা আছে তা হল একমাত্র অবশিষ্ট সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।’
জাতিসংঘ মূলত নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণের (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স এবং চীন) পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের জন্য করা একটি বর্ধিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। সমস্যা হল আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপারে, যা বস্ততপক্ষে অস্তিত্বহীন। এখানে রয়েছে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্য কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন নয়। জাতীয়তাবাদমুক্ত একটি বিশ্বেই কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক আইন প্রতিপালন সম্ভব। যেহেতু এ ধরণের বিশ্ব এখন নেই, সেকারণে জাতি রাষ্ট্রসমূহ তার প্রয়োজনমত আইন প্রণয়ন করে তা আবার নিজেদের ইচ্ছেমত ভাঙ্গে- নব্য বাস্তববাদ (neo realism)(সি.এফ ওয়াল্টজ.কে.১৯৭৯. ‘এ থিওরি অব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স’)।
ঔপনিবেশিক শাসকরা আফ্রিকায় স্থিতিশীলতা নিয়ে এসেছিল এবং তাদের প্রস্থানই বর্তমান অস্থিতিশীলতার কারন
ঔপনিবেশিক দেশগুলো এ ধারণা পোষণ করে যে, তারা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই কল্যাণ নিয়ে এসেছে। ঔপনিবেশিক ধারণাপুষ্ট ঐতিহাসিকরা আফ্রিকার উন্নয়ন বিশেষত শিক্ষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য ঔপনিবেশিকদের আগমনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। কিন্তু তারা ঔপনিবেশিকদের দ্বারা সংঘটিত বর্ণবাদ, শোষণ এবং গণহত্যাকে উল্লেখ করেন না। এমনকি এইসব সাম্রাজ্যবাদীদের ধারণা শুধু আফ্রিকা নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মানুষও তাদের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না।
ব্যাপক সম্পদ ও খনিজ সম্পদের লোভে উপনিবেশবাদীরা আফ্রিকায় এসেছিল। ইউরোপীয়রা এ ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ দাস এবং ব্যাপক প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আফ্রিকায় ছুটে আসত। গণতন্ত্র ও পশ্চিমা মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা তখন খুব কমই ছিল।
ইউরোপীয়রা তাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পুরো আফ্রিকাকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করেছিল। বুরুন্ডির এক অংশ, রুয়ান্ডা, তানজানিয়া এবং নামিবিয়া জার্মানরা শাসন করত। ইটালী জবর দখল করেছিল ইরিত্রিয়ার কিছু অংশ ও সোমালিয়াকে। স্পেন আধিপত্য বিস্তার করেছিল পশ্চিম আফ্রিকায়। অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক এবং আরও ছোট ছোট অংশে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল পর্তুগীজরা। বেলজিয়াম নির্মমভাবে শোষণ করত কঙ্গোকে এবং ব্রিটেন পূর্ব আফ্রিকায় তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে সুদান, ঘানা, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে, মালাউই এবং নাইজেরিয়াতে। সেনেগাল, আইভরি কোস্ট চাদ, মাদাগাস্কার এবং কমোরোস প্রভৃতি পশ্চিম আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহের উপর ঔপনিবেশিক শাসন আরোপ করেছিল ফ্রান্স।
দশকের পর দশক ধরে আফ্রিকা পশ্চিমা পণ্যের জন্য মুক্ত বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আফ্রিকাকে বাধ্য করা হয়েছে ইউরোপীয়দের জন্য সস্তায় কাঁচামাল যেমন-তুলা, রাবার, চা, টিন এবং দাসব্যবসার মত সস্তা শ্রম সরবারহ করতে। এসবই সম্ভব হয়েছে খ্রীস্টান মিশনারীর আঁড়ালে উপনিবেশবাদীদের উপস্থিতির মাধ্যমে। মহাদেশটি ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের মধ্যকার লুটপাটের প্রতিদ্বন্দ্বীতার কারণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। এ কারণে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে একনায়কের সৃষ্টি হয়, সামরিক অভ্যুত্থান হয় অহরহ। এসব অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বীতার কারণে এ মহাদেশের ঋণের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৩৭০ বিলিয়ন ডলার, যা কিনা মহাদেশটির জাতীয় আয়ের ৬৫ ভাগ। শুধু তাই নয় এই মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এতবেশী পরিমাণ ভূমি মাইন (৩০ মিলিয়নেরও বেশী) বসানো আছে যে – তা কিনা পুরো বিশ্বের ভূমি মাইনের শতকরা ২৫ ভাগ হবে।
ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তাদের স্ব-স্ব শোষণের অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করবার জন্য নিজেদের ইচ্ছেমত মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কৃত্রিম সীমানা টেনে দেয়। এভাবে কৃত্রিমভাবে সীমানা টেনে দেয়ায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রসমূহের মধ্যে কোন বাফার অঞ্চল না থাকায় তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কৃত্রিম বিভেদরেখা টেনে দেয়ার আগে কঙ্গো নদী ছিল আফ্রিকার প্রাকৃতিক ভৌগলিক সীমানা। নদীর উভয়পাশে বসবাসরত গোত্রসমূহ একই ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করত। বেলজিয়ান এবং ফরাসি দখলদারদের ভূমি বিভাজনের কারণে এই গোত্রসমূহ আলাদা হয়ে পড়ে। যারা সাহারা ও সাব সাহারান অঞ্চলে বসবাস করত এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মহাদেশীয় বাণিজ্য চালু রেখেছিল। তাদেরকে এখন ঐ ইউরোপীয়দের তৈরি করা মানচিত্রের কারণে কৃত্রিম সীমান্ত পাড়ি দিতে হয়। মিশনারীদের সহায়তা ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য বজায় রাখার মাধ্যমে একটির পর একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে থাকে। যে সব জায়গায় ব্যাপক পরিমাণে ইউরোপীয় স্থাপনা ছিল যেমন রোডেশিয়া (বর্তমান জিম্বাবুয়ে) এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গদের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইউরোপীয়দের হাতে রাখা হয়েছিল। কঙ্গোতে সেখানাকার আদি অধিবাসীদের উপর চাপানো হয়েছিল বর্বর অত্যাচার এবং তাদেরকে দেয়া হয় দাসের মর্যাদা।
বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে বিস্তর বিভেদ তৈরির মাধ্যমে ইউরোপীয়রা আঞ্চলিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে জার্মানরা যখন আসে তখন বর্তমান রুয়ান্ডা এবং বুরুন্ডীতে হুতু ও তুতসী গোত্র এক সংস্কৃতির অন্তর্গত ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পারস্পরিক মিশ্রণ, বিবাহ এবং সংস্কৃতির অবাধ প্রবাহের কারণে কোন লক্ষ্যণীয় পার্থক্য দেখা যেত না। বেলজিয়ানরা এ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রন নেবার জন্য তাদের মাঝে বর্ণবাদের বীজ বপন করে। আর তখন বর্নবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতিসমূহকে বিভক্ত করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল ইউরোপীয় শাসনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। হুতু বলতে কৃষিনির্ভর বানটু ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা পশ্চিম থেকে বর্তমান বুরুন্ডী এবং রুয়ান্ডায় এসেছিল। অপরদিকে তুতসী বলতে উত্তর পূর্বদিকের গবাদি পশুপালন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে বুঝায়-যারা পরে এ অঞ্চলে এসেছিল। তুতসী বলতে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণীকে বুঝায়-যাদের প্রত্যেকের দশটিরও বেশী গবাদি পশু আছে। হুতুরা সংখ্যায় ছিল কম। বেলজিয়ানরা সেখানে গিয়ে বর্ণবাদী নিয়মকানুন চালু করল। গায়ের রঙের দিক থেকে কিছুটা ফর্সা, উচ্চতায় অপেক্ষাকৃত লম্বা, উন্নত ও সরু নাক – যারা প্রকৃতই হেমিটিক এবং যারা উত্তরাধিকারসূত্রে তুতসীদের কাছাকাছি-তাদেরকে বেলজিয়ানদের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা দেয়া হল। যদিও প্রশাসনে কিছু কিছু দেশীয় লোককে উচ্চ পদস্থ চাকুরীতে নিয়োগ দেয়া হল, কিন্তু ইউরোপীয়ানদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট করা। আফ্রিকান উন্নয়নে ইউরোপীয়দের ভূমিকা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ভিনসেন্ট খাপোয়া তার বইতে বলেন, ‘বেলজিয়ান ঔপনিবেশিক শাসনের সময় জায়ার (বেলজিয়ান কঙ্গো) থেকে ব্যাপক সম্পদ বেলজিয়ামে স্থানান্তরিত হয়। এসময় আফ্রিকানরা সামান্য শিক্ষা পেত-যা তাদের বাইবেল পড়া, মিশনারীয়দের হুকুম তামিল করা ও তা নির্বাহ করা এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে কেরানীর কাজ করতে কাজে লাগত।
খাপোয়া আফ্রিকার উন্নয়নে ইউরোপের অবদানের মিথ্যা কল্পকাহিনী সম্পর্কে আরও বলেন, ‘সব ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ সেসময়কার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মনোনিবেশ করেছিল। এর মধ্যে আছে ভূমি অধিগ্রহণ, খাদ্যশস্যের বদলে অর্থকরী ফসলের চাষ, প্রাক ঔপনিবেশিক সময়কার আন্তআফ্রিকান বাণিজ্য বন্ধ করা, ভারত থেকে শ্রমিক সংগ্রহ ইত্যাদি এবং আফ্রিকাকে ইউরোপীয় শিল্পের কাঁচামালের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা- কাজেই আফ্রিকাতে শিল্প স্থাপনের কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না।
ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের কারণে এখনও আফ্রিকায় রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ঊনিশ শতকে বৃটিশরা ছিল এ ব্যাপারে প্রতাপশালী এবং একুশ শতকে মার্কিনীরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে প্রত্যক্ষ উপনিবেশ সরে গেলেও একনায়ক, অস্ত্র্, ঋণ এবং অর্থনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে পরোক্ষ উপনিবেশবাদ বজায় আছে। সুতরাং ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি চলে যাওয়ার কারণে আফ্রিকা অস্থিতিশীল হয়নি বরং এই অপশক্তিসমূহের আফ্রিকার সম্পদকে কুক্ষিগত করবার হীন বাসনা থেকে এ অঞ্চলে নগ্ন হস্ত ক্ষেপের কারণেই গত ২০০ বছর ধরে সেখানে রক্তপাত হচ্ছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অজেয়
একুশ শতকের শুরুর দিকে আমেরিকা হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীব্যাপী পুরোদস্তুর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি। মার্কসবাদ ও বাজার ব্যবস্থার মধ্যে আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিরোধ দেখা যায়নি। মনে হচ্ছিল পশ্চিমা উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাই যেন ‘সরকার ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবয়ব’। এই বাস্তবতা নব্য রক্ষণশীলতার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিকাশকে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। এই পরিবেশ অনেকের মাঝে আমেরিকাকে আধিপত্য ও অজেয়তার অনিবার্য প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু ক্ষমতার বিশ্বব্যাপী ভারসাম্য ও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বর্তমান বুদ্ধিদীপ্ত পর্যবেক্ষণ আমেরিকার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকেই রেখাপাত করে।
ইরাক এবং আফগানিস্তানে মুমূর্ষু মার্কিনীদের যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে – তা তাদের মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যাবে। ইতোমধ্যেই দু’টি যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চেয়ে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার দিক দিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে উন্নত মার্কিন সেনাবাহিনী কিছু অপ্রশিক্ষিত ও ১৯৬০ এর দশকের অস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধাদের সাথে পেরে উঠছে না। বিব্রত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আঞ্চলিক শক্তিসমূহের উপর তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। মার্কিনীরা স্থিতিশীলতা বজায় রাখবার জন্য ইরান ও সিরিয়ার সাথে পেছনের দরজা দিয়ে সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। দক্ষিণ ইরাকে স্থিতিশীলতার জন্য সে ইরানের দুই আয়াতুল্লাহর উপর নির্ভর করছে। এরা হলেন সুপ্রিম কাউন্সিল অব ইসলামিক রেভ্যুলেশনের দুই নেতা – আয়াতুল্লাহ সিসতানি এবং আবদুল আজিজ আল হাকিম। এদের মধ্যে আবদুল আজিজ আল হাকিম ১০০০০ সৈন্য নিয়ে ইরাকের দক্ষিণে অবস্থিত ৯ টি প্রদেশ নিয়ে ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার শিয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ধারণা যেন ইরাককে তিন টুকরা করার মার্কিন পরিকল্পনার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। বাকের-হ্যামিলন্টন রিপোর্টে ইরান এবং সিরিয়াকে সংশ্লিষ্ট করার আহবান জানানোর এটাই প্রধান কারণ কেননা বিশেষ করে ইরান দক্ষিন ইরাকীদের আনুগত্য ভোগ করে থাকে।
ইরান উত্তর এবং পশ্চিম আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা বজায় রাখবার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে আসছে। কেননা একদিক দিয়ে ইরানের রয়েছে আফগানিস্তানের সাথে সীমান্ত। এ অঞ্চল দিয়ে পশতুন বিদ্রোহীরা যাতে মার্কিনীদের ক্ষতি করতে না পারে সে ব্যাপারে ইরান বাধা দেয়। ইরান আফগানিস্তানের ভেতর অনেক অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে যা ন্যাটোকে আরও ক্ষুদ্র একটি প্রতিরোধ যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। তালেবানদের উৎখাতের ব্যাপারে ইরান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং তারা আফগানিস্তানের ভেতর রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন এবং সীমান্ত স্টেশন তৈরিসহ আরও অবকাঠামোগত কাজের সাথে যুক্ত আছে। লন্ডনে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের ডিফেন্স এনালাইসিস ডিপার্টমেন্টের প্রধান কর্ণেল ক্রিস্টোফার লেংটনের মতে, “কেবলমাত্র অতীতে তালেবানদের বিরুদ্ধে তাদের ভূমিকার কারনেই নয়, সেখানকার হাযারা জনগোষ্ঠির (যারা ইরানীদের মতই শিয়া মুসলিম) উপর ইরানীদের প্রভাবের কারনেও তাদেরকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে। আর উন্নয়ন খাতে ইতিমধ্যেই অনেক প্রকল্প আছে যাতে ইরান সম্পর্কিত, যেমন- পারস্য উপসাগরের বন্দর আব্বাস থেকে আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত সড়কপথ নির্মান। এটি আফগানিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ন প্রকল্প। ইরান এবং আফগানিস্তান সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং নিরাপত্তা ইস্যু বিদ্যমান“।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাধর থিংকট্যাঙ্কের একজন রিচার্ড হাস এ সম্পর্কে বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যের দিন ফুরিয়ে এসেছে এবং এ অঞ্চলে আধুনিক ইতিহাসের এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এই রঙ্গমঞ্চে নতুন কুশিলবগন ও শক্তিসমূহ প্রভাব বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য আবির্ভূত হবে। সেসময় ওয়াশিংটনকে সামরিক শক্তির চেয়ে কূটনীতির উপর বেশী নির্ভর করতে হবে।‘
মার্কিনীরা এক দশক আগেও যেখানে নিরঙ্কুশভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছে সেখানে তারা এখন অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীণ হচ্ছে। সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য এখন আগের মত বিভক্ত নয়, অনেক বেশী এককেন্দ্রিক। সেকারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এখন আগের মত অঞ্চলভিত্তিক সমঝোতার প্রচেষ্টা বাদ রেখে এককেন্দ্রিক আধিপত্য বিস্তারের দিকেই মনোনিবেশ করতে হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ব্যাপারে চীন এবং রাশিয়ার সাথে মার্কিনীদের এখন প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। এ অঞ্চলের কাল সোনার জন্য তারা ভারত, জাপানসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছে। সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের নামে ব্রিটেনও অনেক জায়গায় নিজের হিস্যা বুঝে নিচ্ছে। জাতীয় স্বার্থ নিয়ে লিখবার সময় ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিলের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান গ্রাহাম ফুলার উল্লেখ করেন, ‘অনেকগুলো দেশ হাজারো ক্ষত তৈরির মাধ্যমে বুস এজেন্ডাকে দুর্বল, পথভ্রষ্ট, জটিল, সীমিত, ব্যহত, বিলম্বিত করে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য অনেক কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করছে। ‘
টনি ব্লেয়ারের সময় সিয়েরালিওনের প্রেসিডেন্ট কাব্বাকে সরিয়ে দেয়ার মার্কিন পরিকল্পনার ব্যাপারে ব্রিটেন আমেরিকাকে হতাশ করে এবং ৯/১১ এর পর নব্যরক্ষণশীল মার্কিনীদের কর্তৃক লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফীর সরকারকে উৎখাত করার পরিকল্পনায় গাদ্দাফীর পক্ষে ব্রিটেন অবস্থান গ্রহণ করে। দক্ষিণ সুদানকে মূল ভূ-খন্ড থেকে পৃথক করার মার্কিন পরিকল্পনাও দারফুরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সম্পৃক্ততার কারণে সম্ভব হয়ে উঠেনি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে মার্কিন প্রভাব বলয় থেকে বাইরে রাখতে এবং প্রতিবেশী আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যবহার করবার ক্ষেত্রে টনি ব্লেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাছাড়া তেলের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করবার জন্য আফ্রিকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রায় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ১০০ টিরও বেশী চুক্তি করে চীনকে সুবিধা দিতে আমেরিকা বাধ্য হয়েছে।
২০০৪ সালে প্রো-ব্রিটিশ দল কংগ্রেসের বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মার্কিন আধিপত্য হ্রাস পায়। ভারতীয় জনতা পার্টির পরাজয় ছিল মার্কিন স্বার্থের উপর বড় ধরণের আঘাত। পাকিস্তানেও ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় পারভেজ মোশারফের বিরুদ্ধে জনরোষ ঠেকানোর জন্য আমেরিকাকে ব্রিটেনের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি করতে হয়েছে।
পশ্চিমা উদারপন্থী গণতন্ত্রকে পেছনে ফেলে রাশিয়া ও চীন দারুণভাবে উঠে আসছে। অনেকক্ষেত্রে রাশিয়া শুধু পশ্চিমাদের নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খোলামেলা চ্যালেঞ্জ করে আসছে। সেটা সমুদ্রবক্ষে আর্কটিক আইসকেপের নীচে পতাকা ওড়ানো দিয়ে হোক কিংবা ব্যাপক বিধ্বংসী এয়ার ব্লাস্ট বোমার পরীক্ষা চালিয়ে হোক কিংবা পূর্ব ইউরোপে মার্কিন ্তুক্ষেপনাস্ত্র বিধ্বংসী প্রতিরক্ষ্থা বিরোধী বক্তব্য দিয়েই হোক না কেন। আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে রাশিয়া পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করছে। কারণ ইতোমধ্যে কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তানকে মার্কিন আধিপত্য থেকে উদ্ধার করে নিজেদের আওতার মধ্যে নিয়ে এসেছে এবং মধ্য এশিয়াকে সাম্প্রতিককালে সেখানে সংঘটিত তিনটি বিপ্লবের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। পৃথিবীর সর্বাধিক তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ দেশগুলোর অন্যতম একটি দেশের (রাশিয়া) কাছে ২০ বছর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।
১৮২৩ সালে মনেরো ডিক্লারেশনের পর থেকে নিজের বাড়ির উঠোন মনে করা ল্যাটিন আমেরিকার উপরও আমেরিকা এখন তার কর্তৃত্ব হারাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিন আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে কোন ধরণের হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়নি। আর এ কারণে ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে দূরে ছিল।
ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, চিলি প্রভৃতি দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে বামপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছে। সেকারণে এসব স্বাধীন দেশ ওয়াশিংটনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর-যা ইতিহাসে প্রথমবারের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, বলিভিয়ার মত রাষ্ট্রসমূহ গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহকে ইতোমধ্যে জাতীয়করণ করেছে এবং আই এম এফ, বিশ্বব্যাংকের প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের মধ্যে ব্যাংক অব দ্য সাউথের মত অর্থনৈতিক বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। প্রায় দুইশত বছর পর আমেরিকা মহাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বের দ্বারা মার্কিনীরা সরাসরি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রবেশের পর থেকে গড়ে তোলা অর্থনৈতিক আধিপত্য থেকেও যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বের অর্থনীতির পাওয়ার হাউস হিসেবে পরিচিত মার্কিন অর্থনীতি এখন উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তির পেছনে পড়ে যাচ্ছে। চীন ও ভারতের পর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিক দিয়ে মার্কিনীরা এখন তৃতীয়স্থানে রয়েছে। এ সমস্যা আরও জটিল হয়েছে তাদের ব্যাপক তেলের চাহিদার কারণে।
অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্কিনীরা চীনের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ কারণে তাদের মধ্যকার সম্পর্কে জটিলতর হচ্ছে। মার্কিন কোম্পানীগুলো চীনের ১.৫বিলিয়ন জনসংখ্যার বাজারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও চীনের ৭০ ভাগ উৎপাদিত পণ্য আমেরিকার বন্দরে পৌঁছে যায়। চীন-মার্কিন বাণিজ্য সমঝোতা থেকে প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার রিজার্ভ নিয়ে চীন সবসময় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব শিল্পকারখানাগুলো চীনের মত স্বল্প খরচে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ব্যর্থ হওয়ায় দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি এখন প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর দায় মেটায় ট্রেজারি বন্ডের মাধ্যমে। ৫০২ বিলিয়ন ডলার নিয়ে জাপানের পর চীন এ বন্ড কেনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে আছে-যা কিনা মার্কিনীদের মোট বিদেশী ঋণের শতকরা ২০ ভাগ। অন্যদিকে আমেরিকা চীনের ক্রমবর্ধমান তেলের চাহিদা থেকে লাভবান হচ্ছে। সুতরাং এ দু’দেশের পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবসময় কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থায় থাকে না।
ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধে ব্যর্থতা পুরো পৃথিবীজুড়ে মার্কিন প্রতাপ ও ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রকে এক্ষেত্রে অপরাজেয় মনে না করে সবাই পরনির্ভরশীল ভাবতে শুরু করেছে। আর তার সাথে যোগ হয়েছে অভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক সংকট। ২০০৫ সালে এফ.বি.আই এর সরবরাহকৃত উপাত্ত অনুসারে আমেরিকায় প্রতি ২২ সেকেন্ডে একটি করে অপরাধ, ৩১ মিনিটে একটি করে হত্যা এবং প্রতি ৫ মিনিটে একটি করে ধর্ষণ ও প্রতি ১ মিনিটে একটি করে ডাকাতি সংঘটিত হচ্ছে।
আমেরিকা অজেয় হওয়ার বাস্তবতা থেকে এখন অনেক দূরে। ক্ষয়িষ্ণু মার্কিনীরা সময়ের অতল গহবরে বিলীন হওয়ার প্রহর গুণছে মাত্র।
ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করে
পৃথিবীর অনেক লোক ইসরাইলের দিকে অত্যন্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা ছিল নির্যাতিত একটি জাতি। মাত্র ৬০ বছর বয়সে ইসরাইল প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে যে তার রয়েছে পৃথিবীর সর্বাধুনিক সেনাবাহিনী। এর জনসংখ্যা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রের সমান হলেও শুরু থেকে পর পর চারটি পাতানো যুদ্ধে সে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে পরাজিত করে এমন একটি ধারণার জন্ম দেয় যে, সে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিই নয় বরং পুরো পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রন করছে। কিন্তু এটা খুঁজে বের করা দরকার কে কাকে নিয়ন্ত্রন করছে এবং তা কী পরিমাণে?
বিগত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সম্পর্ক মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। কংগ্রেসে কোনরূপ প্রশ্ন ছাড়াই প্রতিবছর প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারের সামরিক ও আর্থিক সাহায্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইসরাইলে পৌঁছানোর অনুমোদন দেয়। এ ব্যাপারে উদারমনারা – যারা বিভিন্ন সময় মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেন এবং রক্ষণশীলরা-যারা বিদেশীদের সাহায্যের ব্যাপারে অনাগ্রহী সকলেই বিনা প্রশ্ন ব্যায়ে সম্মতি দিয়ে থাকেন। বস্তুত সকল পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ ইসরাইলের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি মার্কিনীদের অকুন্ঠ সমর্থনকে প্রশংসার চোখে দেখে। জাতিসংঘসহ অন্যান্য ফোরামে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ যখন ইসরাইলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের দায়ে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করে তখন প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্র একা তাদের পক্ষে অবস্থান নেয়।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্য অঞ্চলের তেলের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে। আর এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে হলে আমেরিকা একা পেরে উঠবে না-এটা সে ভালই বুঝতে পেরেছিল। ১৯৪৫ সালে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে বলে যে, ‘এটি কৌশলগত শক্তির একটি বিশ্বয়কর ভান্ডার এবং বিশ্বের ইতিহাসে সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার।’ মার্কিনীরা বুঝতে পারে যে, পুরো পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রনে আনতে হলে এ অঞ্চলের তেলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী পরিকল্পনাবিদ জর্জ কেনান বলেন, ‘যদি আমেরিকা তেলের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যত প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানী ও জাপানের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর ভেটো ক্ষমতা বজায় রাখতে পারবে।’ মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরে এ কারণে আমেরিকা এ অঞ্চলকে ঘিরে অসংখ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে।
১৯০৬ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হেনরী বেনারম্যান একটি ইহুদী জন্মভূমির পরিকল্পনার কথা বলেন, ‘মুসলিমরা পুরো পৃথিবীজুড়ে এরকম অনেক অঞ্চল দখল করে আছে যেগুলো প্রচুর দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান প্রাচূর্যে ভরপুর। পৃথিবীর সংযোগস্থলসমূহে তারা আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। তাদের ভূমিসমূহ ধর্ম ও মানবসভ্যতার পীঠস্থান। তাদের এক বিশ্বাস, এক ভাষা, এক ইতিহাস এবং অভিন্ন লক্ষ্য। কোন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা তাদের মাঝে বাধা হয়ে দাড়াঁতে পারে না.. যদি কোন কারণে এই দেশসমূহ এক হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর ভাগ্য তাদের হাতে চলে যাবে এবং তারা পুরো বিশ্ব থেকে ইউরোপকে আলাদা করে ফেলবে। সেকারণে আরবের হৃদয়ের মাঝখানে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা আরব বিশ্বের একীভূত হওয়াকে প্রতিহত করবে এবং অবিনাশী যুদ্ধের মধ্যে তাদেরকে সবসময় বেধে রাখবে। এ রাষ্ট্র পশ্চিমাদের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে।’
ইসরাইলের জন্মই হয়েছিল আরবে মুসলিম বিশ্বের মাঝখানে ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণ করবার জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৃটেনের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় আমেরিকা এ অঞ্চলে এ পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বৃহত্তর ইসরাইলের স্বপ্ন নিয়ে গঠিত হলেও আমেরিকা ইসরাইলকে একটি সুনির্দিষ্ট সীমান্তের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল। এটা ছিল ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার প্রথম মতপার্থক্য। ইসরাইলের অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট। একেবারে শুরু থেকে তারা তাদের সীমানা নির্ধারণে মোটেও রাজী ছিল না। এ ব্যাপারটি এটাই প্রমাণ করে যে, ইসরাইল কখনওই মার্কিন উপনিবেশ ছিল না এবং তাদের দু’জনের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে।
জায়নবাদী আন্দোলনের শুরু থেকেই ইহুদীরা এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। আমেরিকা ইউরোপীয়দের আধিপত্যের স্থলে ইসরাইলীদের আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনাকে প্রত্যাখান করেছে এবং সে তার স্বার্থকে অন্য কারও সাথে ভাগাভাগি করতেও রাজী নয়। আমেরিকা ইসরাইলের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং ইহুদীদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করবার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারপরেও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলি সম্প্রসারণ ও প্রভাব বৃদ্ধিকে ঠেকানোর জন্য মার্কিনীরা মধ্যপ্রাচ্য ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরাইলকে একঘরে করে ফেলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা হল আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে বর্তমান ইসরাইল ও অন্যান্য আরব দেশ যেমন জর্ডান, সিরিয়া, মিশর ও ভবিষ্যত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের মাঝে সীমান্তকে সুরক্ষিত করবার জন্য ব্যাপক বহুজাতিক সৈন্য সমাবেশ ঘটানোর মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। আমেরিকা জেরুজালেমের আন্তর্জাতিকীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। কেননা জেরুজালেম অনেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্পর্শকাতর স্থান- বিশেষত খ্রীস্টানরা এতে বেশ সন্তুষ্ট হবে এবং এর মাধ্যমে জাতিসংঘের নামে মার্কিন আধিপত্য সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
ইসরাইল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান যে অবস্থান রয়েছে তার নেপথ্যে রয়েছে বেশ কিছু কারণ:
১. অনেক আমেরিকান ইসরাইলীদের প্রতি একধরণের আবেগিক সম্পর্ক অনুভব করে বিশেষত যারা উদারমনা সরকারী নেতৃবৃন্দ এবং প্রচারমাধ্যম। অধিকাংশই ইসরাইলের ঐতিহাসিক সংগ্রাম, শতাব্দীর পর শতাব্দী সংখ্যালঘু একটি জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার নিবিড় প্রচেষ্টা প্রভৃতিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখে।
২. আমেরিকান খ্রীস্টানদের ডানপন্থীরা ঐতিহাসিকভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন রিপাবলিকান সমর্থকদের নিয়ে সবসময় মিডিয়া ও রাজনৈতিকভাবে ইসরাইলকে ও ডানপন্থী ইসরাইলী নেতাদের সমর্থন দিয়ে আসছে। ধর্মতত্ত্ব অনুসারে পবিত্র ভূমিতে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন দ্বিতীয়বার যীশু খ্রীস্ট আসবার পূর্বশর্ত মনে করা হয় এবং বলা হয় ইসরাইলী ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যকার এ সংঘাত এটাই প্রমাণ করে যে ইসরাইল ঈশ্বরের ইচ্ছায় কেবলমাত্র ইহুদীদের।
৩. মূলধারার ইহুদী এবং রক্ষণশীল ইহুদী সংগঠনসমূহ তদবির করা, তহবিল সংগ্রহ, প্রচারমাধ্যমসমূহে ইসরাইলী সরকারের পক্ষে নাগরিক চাপ প্রয়োগ প্রভৃতির জন্য শক্তিশালী সিন্ডিকেট তৈরী করেছে। ইহুদী সমর্থকগোষ্ঠীর কাজ হচ্ছে ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে একটি পরিবেশ তৈরী করা এবং উদারমনা ও প্রগতিশীল ইহুদীদের ভেতর ইসরাইলবিরোধী চেতনার বিপক্ষে চাপ সৃষ্টি করা।
৪. এ.আই.পি.এ.সি (আমেরিকান ইসরাইল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি) এবং অন্যান্য ইহুদীবাদী সংগঠনগুলোর চেয়ে অস্ত্র প্রস্তুতকারী কোম্পানীগুলো পাঁচগুণ বেশী অর্থ ব্যয় করে কংগ্রেসনাল প্রচার ও লবির জন্য। এসব কোম্পানী ইসরাইল ও মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান মিত্রদের কাছে ব্যাপক পরিমাণ অস্ত্র বিক্রয় করে থাকে। সেকারণে নিজ এলাকায় অবস্থিত অস্ত্র বিক্রেতা কোম্পানীগুলোর স্বার্থের দিকে তাকালে বিভিন্ন কংগ্রেসম্যানদের ইসরাইলের পক্ষ অবলম্বন করা ছাড়া আর কিছুই করবার থাকে না। ইসরাইলে ২ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির এক প্রস্তাবের কাছে ইন্দোনেশিয়ায় ৬০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব তাই ধোপে টেকে না।
ইসরাইল খুব সফলভাবে একটি রাষ্ট্র গঠন করেছে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিবিধ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তার সম্পদকে কাজে লাগিয়েছে। অবশ্যই পশ্চিমাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া আজকের ইসরাইলের অবস্থান সম্ভব হত না। তবে ইহুদীদের ভাষায় তারা স্থায়ী সীমানাবিশিষ্ট সেই রাষ্ট্রটি এখন পর্যন্ত কায়েম করতে পারেনি যার ভূখন্ডগুলোর ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এর একটিই কারণ। আর তা হল মার্কিনীদের পরিকল্পনার ভেতর এটা নেই।
যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন একটি ইহুদী রাষ্ট্রের কথা রয়েছে যার পাশে রয়েছে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র। ইসরাইলের ইতিহাসে যে দলটি সবচেয়ে বেশী সময় ধরে ক্ষমতায় ছিল তা হল লিকুদ পার্টি-যা ইসরাইলের সীমানা নির্ধারণের জন্য মুসলিমদের হটিয়ে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করে আসছে। কিন্তু যে কোন ধরণের চূড়ান্ত স্থাপনার জন্য আমেরিকার সমর্থন ইসরাইলের দরকার। সেকারণে মার্কিন ও বিশ্ব প্রচারমাধ্যম ও বিভিন্ন লবির মাধ্যমে ইহুদীরা তাদের চূড়ান্ত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে আসছে। বৃহত্তর ইসরাইলের ধারণা বেশ জটিল। কেননা লেবার পার্টি মনে করে প্রয়োজনে কিছু ভূমি ছাড় দিয়ে হলেও ইসরাইলের সীমানাকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। আর এই ছাড় দেয়া ভূমি প্রয়োজন বৃহত্তর ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য।
সুতরাং ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রন করে না বরং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে মাত্র। আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যকে সংগঠিত করছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল একই নীতি গ্রহণ করে থাকে কিন্তু ইসরাইলের কারণে আমেরিকা তার নীতি থেকে সরে আসে না। ইসরাইলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন তার অন্যান্য মিত্রদের প্রতি সমর্থনের মতই। কোন ধরণের নৈতিক দায়বদ্ধতা এখানে কাজ করে না। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি সর্বদাই তার কৌশলগত স্বার্থকে চরিতার্থ করবার জন্যই প্রণীত হয়।
চারটি যুদ্ধে ইতোমধ্যে ইসরাইল নিজেকে অপরাজেয় প্রমাণ করেছে; মুসলিম উম্মাহ্’র উচিৎ এর অস্তিত্ব মেনে নেয়া
১৯৪৮ সালে ইসরাইল সৃষ্টির পর থেকে এর সামরিক শক্তিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অপরাজেয় হিসেবে তুলে ধরবার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। মজার ব্যাপার হল এ ধরণের আষাঢ়ের গল্প ইসরাইল নিজে স্বপ্রণোদিত হয়ে যতটা না প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে তার চেয়ে বেশী কাজ করেছে বিশ্বাসঘাতক মুসলিম শাসকগুলো।
১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ এর যুদ্ধগুলোতে পারদর্শিতা সামরিক ক্ষেত্রে ইসরাইলের পরিষ্কার প্রাধান্যকে প্রমাণ করে। এ পরিষ্কার প্রাধান্য ও মুসলিম ভূমির জবরদখল আরব রাষ্ট্রসমূহকে এই ধারণা দেয় যে, সামরিক নয় বরং কূটনৈতিক সমঝোতাই একমাত্র বাস্তবসম্মত বিকল্প। সেকারণে শান্তি প্রক্রিয়ার নামে বিভিন্ন পরিকল্পনায় ইসরাইলের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।
ইসরাইলের এই সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে কোন স্বার্থে এ ধরণের আষাঢ়ে গল্পের প্রচলন করা হয়েছে?
১৯৪৮ সালের যুদ্ধ-ইসরাইলের সৃষ্টি
১৯৪৮ সাল ছিল ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টির বছর। বাহ্যিকভাবে এটা বুঝা যাচ্ছে না কিভাবে ৪০ মিলিয়ন আরব মাত্র ৬০০০০০ ইহুদীর সাথে যুদ্ধে পেরে উঠল না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমুহের বর্তমান ও অতীত ভূমিকা ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।
ট্রান্সজর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ, মিশরের বাদশাহ ফারুক, প্যালেস্টাইনের মুফতিগণ সকলেই বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত দূর্বল শাসক ছিলেন – যারা প্রাথমিকভাবে ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধি ছিল। বাদশাহ আবদুল্লাহ নিজেকে ফিলিস্তিনীদের রক্ষাকবচ হিসেবে দাবী করাটা ছিল ছলনা মাত্র। শোনা যায় তিনি এবং ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন একসাথে ইস্তাম্বুলে পড়াশোনা করতেন এবং একটি গোপন বৈঠকে আবদুল্লাহকে আরব জনঅধ্যুষিত অঞ্চল ফিলিস্তিনের উপর জর্ডানের নিয়ন্ত্রনের বিনিময়ে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাকে গ্রহণ করে নেবার প্রস্তাব করা হয়।
বাদশাহ আবদুল্লাহর বিদায়ের সময় আরব জনগণের মধ্যে ইংরেজ জেনারেল জন গ্লাবের নেতৃত্বে ৪৫০০ লোকের একটি সুপ্রশিক্ষিত ইউনিটও ছিল। গ্লাব তার স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন যে, বৃটেনের পক্ষ থেকে তাকে কড়া নির্দেশ দেয়া ছিল যাতে তিনি ইহুদী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে প্রবেশ না করেন। মিশর ইসরাইলের উপর আক্রমনের ধার কমিয়ে দেয় এবং তখন প্রধানমন্ত্রী নাকরাশি পাশা নিয়মিত সেনাবাহিনীকে আক্রমনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে মাত্র সেবছরের জানুয়ারীতে গঠিত হওয়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রেরণ করে। জর্ডান তার অঞ্চল দিয়ে যাবার সময় ইরাকী সেনাবাহিনীর যাত্রাকে প্রলম্বিত করে ইসরাইলে হামলার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। একারনে জর্ডানের সেনাবাহিনীর মনোবল জাগিয়ে তুলবার জন্য নিয়োগ পাওয়া একজন অন্ধ ইমাম যুদ্ধে অপ্রস্তত বাদশাহ আবদুল্লাহকে এই বলে অপমানিত করেছিলেন যে, “হে সেনাবাহিনী যদি তোমরা আমাদের হতে” (আরব অঞ্চল ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধিনস্ত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে)।
৪০০০০ মুসলিম সৈন্যের মধ্যে মাত্র ১০০০০ ছিল প্রশিক্ষিত। ইহুদীদের ৩০০০০ সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল, ১০০০০ স্থানীয় নিরাপত্তায় নিয়োজিত এবং অন্য ২৫০০০ ছিল আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য। এছাড়াও ৩০০০ এর মত ইরগুন ও ষ্টার্ণ গ্যাং সন্ত্রাসী ছিল। সরবরাহ করা হয় সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র এবং ব্রিটেন এবং আমেরিকার জায়নবাদী সংগঠনগুলো তাদের অর্থায়ন করে। ইহুদীদের প্রস্তুতি ছাড়াও মুসলিম শাসকদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ফিলিস্তিনে জায়নবাদীদের আখড়া গড়তে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।
১৯৫৬ সালের সুয়েজ খাল সংকট
এ যুদ্ধটি কোনক্রমেই ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার জন্য ছিল না, বরং এটি ছিল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সুয়েজ খালকে নিয়ন্ত্রনের জন্য আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যকার একটি সংঘাত।
মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রতিপত্তিকে সুসংহত করবার জন্য মিশরকে তারা গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে দেখেছিল। সি.আই.এ-র সহায়তা নিয়ে ১৯৫২ সালে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৃটিশ অনুগত বাদশাহ ফারুককে অপসারণ করে জামাল আব্দুল নাসেরের নেতৃত্বে ফ্রি অফিসার্স-কে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হয়। “একজন মুসলিম বিলি গ্রাহাম- এর খোঁজে (The Search for a Moslem Billy Graham)” নামে ১৯৫১ সালে সি.আই.এ একটি প্রজেক্ট পরিচালনা করে। সি.আই.এ কর্মকর্তা মাইক কোপল্যান্ড ১৯৮৯ সালে ‘দি গেম প্লেয়ার’ নামক স্মারকগ্রন্থে উল্লেখ করেন কিভাবে তাদের প্রত্যক্ষ মদদে বৃটিশ পুতুল শাসক বাদশাহ ফারুককে ক্যু এর মাধ্যমে অপসারণ করা হয়। এই প্রজেক্টের দায়িত্বে থাকা কোপল্যান্ড বর্ণণা করেন যে, ’অত্র অঞ্চলে আমেরিকাবিরোধী প্রচারণাকে রুখবার জন্য সি.আই.এ এর একজন অতি জনপ্রিয় তুখোড় নেতার দরকার হয়ে পড়েছিল।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সি.আই.এ এবং নাসেরের মধ্যে ইসরাইলের ব্যাপারে একটি চুক্তি হয়। যদিও নাসেরের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা করা ছিল নিতান্তই অযৌক্তিক। আলোচনার বিষয় ছিল সুয়েজ খালের উপর বৃটিশ কর্তৃত্বকে খাটো করা। কেননা ব্রিটেন ছিল নাসেরের শত্রু।
১৯৫৬ সালে নাসের আমেরিকার দাবি মোতাবেক সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করে। ব্রিটেনের প্রচেষ্টা ছিল এর সাথে ফ্রান্স এবং ইসরাইলকে সংযুক্ত করা। ঐতিহাসিক করেলি বার্নেট তার “দি কলাপ্স অব ব্রিটিশ পাওয়ার (ব্রিটিশ কর্তৃত্বের পতন)” গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ‘ফ্রান্স নাসেরের প্রতি বিরুপ ছিল কারণ মিশর আলজেরিও বিদ্রোহের সাহায্য করছিল এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ফ্রান্স এই খালের সাথে সম্পর্কিত ছিল কেননা একজন ফরাসী এটি খনন করেছিলেন। ফিলিস্তিনের ফিদেইন হামলা এবং মিশর কর্তৃক তিরান প্রনালীর অবরোধের কারনে ইসরাইল যেকোন উপায়ে নাসেরের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর অপেক্ষায় ছিল। সেকারণে স্যার অ্যান্থনী এডেন (ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) ফ্রান্স এবং ইসরাইলের সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় কূট পরিকল্পনা হাতে নেন’। তিনি আরও বলেন, “সিনাই উপদ্বীপ এলাকা দিয়ে ইসরাইল মিশরকে দখল করে নেবে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স তখন বিবাদমান পক্ষগুলোকে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য একটি সময়সীমা বেধে দেবে অথবা খালটিকে ‘রক্ষার’ জন্য হস্তক্ষেপ করবে”।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সরে যাবার জন্য ব্রিটেনের উপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে। রাশিয়া লন্ডন এবং প্যারিসকে পারমাণবিক হামলার হুমকি দেয়। ব্যাপক আন্তর্জাতিক চাপের কারণে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স মিশর থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। আইজেনহাওয়ার এর নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের মাধ্যমে ইসরাইলকে অধিকৃত মিশরের ভূমি থেকে সরে আসবার জন্য চাপ দিতে থাকে যদিও ইসরাইলের জন্য তখন এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিল অসুবিধাজনক। আর এরপরই মার্কিনীরা মধ্যপ্রাচ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।
১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধ
এ যুদ্ধটিও ছিল এ অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যের দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি হিসেবে ১১ বছর আগে ভূমিকা খর্ব হলেও জর্ডান, সিরিয়া ও ইসরাইলে ব্রিটেনের প্রতি অনুগত শাসকগণ তখনও ছিল। নাসেরকে দুর্বল করবার লক্ষ্যে ভবিষ্যত শান্তি প্রক্রিয়ায় দর কষাকষির উপকরণ হিসেবে মিশরের কিছু ভূমি দখল করে নেবার জন্য ব্রিটেন ইসরাইলকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। ১৯৬৭ সালের ৫ জুন তারিখে ইসরাইল আক্রমণ করে মিশরের শতকরা ৬০ ভাগ ভূমিতে অবস্থানরত বিমানবাহিনী এবং সিরিয়া ও জর্ডানের শতকরা ৬৬ ভাগ যুদ্ধরত বিমানবাহিনী ধ্বসিয়ে দেয়। জর্ডান নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম ইসরাইল দখল করে নেয়। যুদ্ধের আগে বাদশাহ হোসেন তার সেনাবাহিনীকে মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দুরে সরিয়ে রাখে। মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পশ্চিম তীরের গুরুত্বপূর্ণ শহরসমূহ ইসরাইল দখল করে নেয়। যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনের মাথায় তারা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ গোলান মালভূমি দখল করে নেয়। গোলান মালভূমিতে অবস্থানরত সিরীয় সেনাবাহিনী তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বেতারের মাধ্যমে জানতে পারে ইসরাইল গোলান মালভূমি দখল করে নিয়েছে যদিও তখনও গোলান মালভূমি সিরিয়ার অধিকারেই ছিল। তিরানে যাবার জলপথ শার্ম-আল-শেখ দখল করে নেবার মাধ্যমে ইসরাইল মার্কিনপন্থী নাসেরকে ভয়াবহ ধাক্কা দেয়। নাসেরের ক্ষমতাকে খর্ব করার লক্ষ্য অর্জিত হয় এবং অত্র অঞ্চলে ব্রিটিশ আধিপত্য পাকাপোক্ত হয়। ইসরাইলের আরও ভূমি দখল করে নেবার সক্ষমতা ছিল এবং ১৯৪৮ সালের মত দখলের খাতিরে দখলের জন্য নয় বরং এটাকে এখন পর্যন্ত শান্তি প্রক্রিয়ায় দর কষাকষির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ বিভাজন পরিকল্পনার (UN Partition plan) আওতায় ইসরাইলকে শতকরা ৫৭ ভাগ ভূমি ও ফিলিস্তিনীদের শতকরা ৪২ ভাগ ভূমি প্রদান করে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের মাধ্যমে ইসরাইল এটাকে বাড়িয়ে ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের ৭৮ ভাগ দখল করে নেয়।
১৯৭৩ সালের যুদ্ধ
মিশর এবং সিরিয়া কর্তৃক ইসরাইলের বিরুদ্ধে চালানো ১৯৭৩ সালের যুদ্ধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-এর লক্ষ্য ছিল সীমিত এবং কখনওই এটা ফিলিস্তিনীদের মুক্ত করবার জন্য পরিচালিত হয়নি। এমনকি গোলান মালভূমিকে (যা ছিল সিরিয়া ও ইসরাইলের মধ্যকার শান্তিচুক্তির বিষয়) মুক্ত করবার জন্যও এ যুদ্ধ পরিচালিত হয়নি। এ যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল অনেকটা সেনাঅভ্যূত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা অপেক্ষাকৃত নতুন রাষ্ট্রনায়ক আনোয়ার সাদাত ও হাফিয আল আসাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করবার জন্য। সাদাতের অবস্থান এক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল। কেননা তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় নাসেরের স্থলাভিসিক্ত হয়েছিলেন।
যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও ১৯৫৭-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আল আহরামের সম্পাদক মুহম্মদ হেকেল তার বই ‘দি রোড টু রামাদান’ এ এই যুদ্ধে আনোয়ার সাদাতের লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি সাদাতের একজন জেনারেল মুহম্মদ ফাউজীর বরাত দিয়ে বলেন, সংঘটিত যুদ্ধকে তুলনার জন্য একটি সামুরাই চিত্র যেখানে একটি লম্বা তলোয়ার ও খাটো তলোয়ার রয়েছে সেটি উপস্থাপন করা হয়। জেনারেল ফাউজী ছোট তলোয়ারটিকে দেখিয়ে বলেন, এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সীমিত।
ইসরাইলের সাথে একটি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবার কোন অভিলাষ আনোয়ার সাদাতের ছিল না। সেকারণে যুদ্ধ জয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা সত্ত্বেও ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি করা হয়। প্রথম ২৪ ঘন্টার যুদ্ধে মিশর মাত্র ৬৮ জনের প্রাণের বিনিময়ে সুয়েজ খালের পূর্বদিকে অবস্থিত বার-লেভ প্রাচীরগুলো গুড়িয়ে দেয়। ২ টি সিরীয় ডিভিশন ও ৫০০ ট্যাঙ্ক গোলান মালভূমির দিকে অগ্রসর হয়ে ১৯৬৭ সালে অধিকৃত কিছু অংশ পূর্ণদখল করে নেয়। মাত্র দু’দিনের যুদ্ধে ইসরাইল ৪৯ টি এয়ারক্রাফট ও ৫০০ টি ট্যাঙ্ক হারায়। এর মধ্যে আনোয়ার সাদাত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারকে পাঠানো একটি খবরে যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেন,‘মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং কোন আংশিক সমঝোতা নয়’। এই খবরের অর্থ দাড়ায় যে, যদি ইসরাইল দখলকৃত ভূমি ছেড়ে চলে যায় তাহলে মিশর জাতিসংঘ কিংবা অন্য কোন নিরপেক্ষ কারও মধ্যস্থতায় শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে প্রস্তত।
কৌশলগত দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও আনোয়ার সাদাত শান্তি চুক্তিতে প্রস্তত ছিল। আনোয়ার সাদাতের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ছাড় দেবার কারণে ইসরাইল মার্কিনীদের সমর্থন নিয়ে অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে খুব সহজে সটকে পড়ে। আর এতে করে ১৯৭৪ সালের ২৫ অক্টোবর তারিখে যুদ্ধের অবসান ঘটে।
ইসরাইলের সাথে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধে মুসলিম প্রতারক শাসকগন ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করবার জন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আন্তরিকতার সাথে লড়েনি। উপরের যুদ্ধের ঘটনাসমূহ সঠিকভাবে না জানা থাকার কারণে ইসরাইলের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ব্যাপক বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। বিশ্বাসঘাতক মুসলিম শাসকগন এ ধরণের বিভ্রান্তি সৃষ্টির পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। ইসরাইলের আধিপত্যকে তারা লালন করেছে, উস্কে দিয়েছে এবং বহাল তবিয়তে বলবৎ রেখেছে। আরব বিশ্ব কখনই ইসরাইলকে উৎখাতের জন্য এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে কাজ করেনি। প্রতিটি যুদ্ধের পেছনে ইসরাইলের সমূল উৎপাটন কিংবা ফিলিস্তিন মুক্ত করবার বদলে অন্য উদ্দেশ্যগুলো কাজ করেছে। সম্মিলিতভাবে ব্যাপক শক্তিশালী আরব দেশসমূহ ইসরাইলের সামরিক সক্ষমতা ও বৈধতাকে কখনই আন্তরিকতার সাথে চ্যালেঞ্জ করেনি।
খাদ্যের অপ্রতুলতাই তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র্যের কারণ
বিশ্বব্যাপী পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, সম্পদের অপ্রতুলতা এবং গণতন্ত্রের অভাব দারিদ্র্যের সাধারণ কারণসমূহের মধ্যে প্রধান। সমাজবিজ্ঞানী ও অন্যান্য থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মধ্যে যদিও এ ব্যাপারে কোন ঐক্যমত্য নেই। এ ব্যাপারে খুব প্রাধান্য বিস্তারকারী ধারণা হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে পুঁজিবাদের বিকাশই হল এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। কিন্তু খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, খাদ্যের অপ্রতুলতা নয়, বরং অন্যান্য কিছু বাস্তবতা শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্ব নয় পুরো তৃতীয় বিশ্বে দরিদ্রতার জন্য দায়ী।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংক এবং এদের কাঠামোগত পরিবর্তন নীতি (Structural Adjustment Policy) মিশর, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশের বিবিধ অর্থনৈতিক সংকট তৈরির পেছনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। দরিদ্রতা মুক্তির উপর তাদের নিজস্ব প্রেসক্রিপশন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাছে বিক্রয় করে থাকে। এসব সংস্থা প্রদত্ত নীতিসমূহের মধ্যে রয়েছে শস্যের মজুদ না রাখা বা কমিয়ে আনা, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত খাবারের উপর কর হ্রাস, সারসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের উপর থেকে ভর্তুকি উঠিয়ে নেয়া প্রভৃতি। অন্যান্য দরিদ্র দেশসমূহ থেকে আমদানির বদলে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে তারা। বাজার অর্থনীতি ও ব্যক্তিখাতের বিকাশের মাধ্যমে অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করা ও একে দারিদ্রতা বিমোচনের পথ হিসেবে দেখানো হয়।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য পাকিস্তানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অবকাঠামো খাতে ব্যাপক উন্নয়ন দরকার। এসময় বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল পাকিস্তানকে এসব খাতে সরকারী বিনিয়োগ কমিয়ে বরং রপ্তানীর দিকে আগে মনোযোগী হতে পরামর্শ দিয়েছে। তারা এমন সব খাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় যেতে বলে যেগুলোতে পাকিস্তান অনগ্রসর। আর এভাবে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে।
দারিদ্র্যের অপর কারণগুলোর মধ্যে একটি হল ঋণ। আফ্রিকাকে ঔপনিবেশিক সময়ের ঋণ পরিশোধ করবার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। এ ধরণের দেনার কারণ হচ্ছে অসদুপায়ে উচ্চ সুদে ঔপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহের ঋণ গ্রহণ। আবার অনেক সময় দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরশাসকদের বিলাসিতায় অপচয়ের জন্য ধনী দেশসমূহ ঋণ দিয়েছে যা ‘ঘৃন্য ঋন’ হিসাবে পরিচিত। উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ২৮ বিলিয়ন ডলারের (যা বর্তমানে ৪৬ বিলিয়ন) “বর্নবাদ জনিত ঋন” এ জর্জরিত। বর্নবাদ পরবর্তি আফ্রিকার উপর বর্নবাদ শাসনামলের ঋন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৯৯৮ সালে এ.সি.টি.এস.এ (এ.সি.টি.এস.এ: অ্যাকশন ফর সাউদার্ন আফ্রিকা) হিসেব করে দেখেছে যে, বর্নবাদ বজায় রাখবার জন্য ১১ বিলিয়ন ডলার (যা বর্তমানে ১৮ বিলিয়ন ডলার) ধার করেছে। আর প্রতিবেশী দেশসমুহও এ জন্য ১৭ বিলিয়ন ডলার (যা বর্তমানে ২৮ বিলিয়ন) ঋণ গ্রহণ করেছে। শতকরা ৭৪ ভাগের উপরে আফ্রিকান ঋণে জর্জরিত থাকায় পুরো মহাদেশ জুড়ে অস্থিতিশীলতা ও সংঘাত বজায় আছে।
ঔপনিবেশিকতা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতার অন্যতম কারণ। উপনিবেশবাদ পশ্চিমাদের প্রতি নির্ভরশীলতাকে প্রলম্বিত করেছে। এ কারণে খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অংশের উপর পশ্চিমা আধিপত্য ও হস্তক্ষেপ বজায় ছিল। ঔপনিবেশিক আমল থেকে আফ্রিকার শ্রম পশ্চিমাদের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং সেদেশের জনগণকে পশ্চিমে উৎপাদিত পণ্য সাধ্যের অতীত মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য করা হচ্ছে।
বর্তমান বৈশ্বিক কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক সময়ের মত কেবলমাত্র কৃষকের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিচালিত হয় না। ১৯৬০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহ এ ধরণের ব্যবস্থা এবং সরকারকে খাদ্য সরবরাহের উপর হস্তক্ষেপের সুযোগ থেকে বের হয়ে আসবার জন্য কৌশল প্রণয়ন করেছে। লাভের অঙ্কটাকে বাড়িয়ে নেবার জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলো এ সুযোগে এগিয়ে এসেছে। পণ্যদ্রব্যের মূল্যের ব্যাপক হ্রাসবৃদ্ধিতে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ এখন আর নেই। সেকারণে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের জনগণ কে আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজার কর্তৃক বেধে দেয়া মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে হয়। বিশ্ব মন্দা চলাকালীন সময়ে কিংবা তার আগে অনুমাননির্ভর আর্থিক ব্যবস্থাপনা খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। শুরু থেকেই বিলাসজাত পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি ছিল বৈশ্বিক ব্যবসা। কিন্তু ১৯৬০ সাল থেকে খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন আঞ্চলিক পরিমন্ডল থেকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে রূপান্তরিত হয়।
কেবলমাত্র নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য যারা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে তাদের চেয়ে যারা রপ্তানীর জন্য উৎপাদন করে তাদেরকে বিশ্ব বাণিজ্যিক নীতিসমূহ উৎসাহিত করে। যদিও গ্রীষ্মকালে বৃটিশ কলম্বিয়া এবং ক্যালিফোর্ণিয়া উভয় অঞ্চলের কৃষকেরা টমেটো উৎপাদন করে, তারপরও তাদের জন্য লাভজনক হচ্ছে এগুলো নিজ এলাকায় বিক্রয়ের চেয়ে রপ্তানী করা। অথচ ক্রমবর্ধমান পরিবহন ব্যয় পণ্যসমূহের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ কারণে এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের কিছু কিছু অংশে প্রান্তিক চাষীদের দেখা যায় না বললেই চলে। মনোক্রপিং, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার মাধ্যমে কৃষির ব্যাপক শিল্পায়নের কারণে প্রান্তিক চাষীরা সফল হতে পারছে না। জেনেটিক রূপান্তরের জন্য গড়ে উঠা মনসান্তো, আরচার ড্যানিয়েলস,মিডল্যান্ড এবং কারগিল এর মত কোম্পানিসমূহ বিশাল অঙ্কের মুনাফা করছে।
উন্নত বিশ্ব দাবী করছে যে, অধিক জনসংখ্যার কারণে খাদ্যে অপ্রতুলতার দরুণ খাদ্য সংকট তীব্রতর হচ্ছে। খাদ্যের অপ্রতুলতার দোহাই দিয়ে খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমুল্যের পক্ষে সাফাই গাওয়া হয়। তবে এরকম উচ্চফলনশীল ও দক্ষ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও কেন প্রায় এক বিলিয়ন লোক ক্ষুধার্ত থাকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সমস্যা আসলে আন্তর্জাতিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যেই: বিশ্বব্যাপী কৃষিপণ্য বন্টন ব্যবস্থা এবং বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার একচেটিয়া কর্তৃত্বেও (মনোপলি) মধ্যে।
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দরিদ্র দেশসমূহে ধনী দেশ ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর অশুভ পদচারণার মাধ্যমে উপার্জনের ক্ষেত্রস্থল বানানোয় সেসব দেশের কৃষির উপর কুপ্রভাব পড়েছে। অসম বানিজ্য চুক্তি; প্রধান ফসলসমূহের উৎপাদনের উপর অতি খবরদারি; বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতি সংস্থার নিয়ন্ত্রন ও আধিপত্য দরিদ্র দেশসমূহের কৃষির মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে।
কাঠামোগত পরিবর্তনের (Structural Adjustment) মত নীতির মাধ্যমে বিশ্বসংস্থাসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে দরিদ্র মানুষের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থই শুধু নয়, বরং কৃষিখাতে বরাদ্দকৃত অর্থও সংকোচনে বাধ্য করে। দেশজ শিল্পের জন্য বিদেশী পণ্যের উপর বাণিজ্য বাধা দুরীকরণসহ অন্যান্য গৃহীত সুবিধার বিলোপসাধন ও বিদেশী কোম্পানীগুলোকে সহজে ব্যবসা করবার মত পরিবেশ তৈরির ব্যবস্থা করতেও বাধ্য করে (যদিও ধনী দেশসমূহ সে তুলনায় বিদেশী পণ্যের প্রবেশের পথ সুগম করে না)। এছাড়াও দরিদ্র দেশসমুহকে ঋণের ব্যয়ভার বহনের জন্য খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে ডলার উপার্জনের দিকে উৎসাহিত করা হয়। সেকারণে একই ধরণের ফসল বছরের পর বছর উৎপাদনের জন্য ফসলের বৈচিত্র ব্যাহত হয় এবং ফলে ইকোসিস্টেমে ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বিনষ্ট হয় ও রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা ক্রমশ বাড়তে থাকে।
ক্রমবর্ধমান দরিদ্রতা ও অসমতা দরিদ্র দেশসমূহে দুর্নীতিকে বাড়িয়ে দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও প্রতিকূল করছে। দরিদ্রদেশকে ধনীদেশের খাদ্য সহায়তা প্রদানের নামে অতিরিক্ত খাদ্য বিক্রি করা; উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের কৃষিতে ব্যাপক ভর্তুকি প্রদান, প্রভৃতি তৃতীয় বিশ্বের খাদ্য সংকট ও দরিদ্রতাকে ঘনীভূত করছে।
পশ্চিমাদের নীতির কারণেই তৃতীয় বিশ্ব দরিদ্র এবং খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা নয় বরং উন্নত বিশ্বের অপব্যয়ের কারণেই সৃষ্ট খাদ্যসংকটের ফলে তারা দরিদ্রই থাকবে:
– বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর মোট কৃষি উৎপাদনের ৮০ ভাগ পশ্চিমারা ভোগ করে
– মোট পণ্যদ্রব্যের শতকরা ৮৬ ভাগ ভোগ করে
– মোট দুধের ৭৫ ভাগ ভোগ করে
– মোট কাঠের ৭০ ভাগ ভোগ করে
– মোট পানির ৬২ ভাগ ভোগ করে
– মোট জ্বালানীর ৪৮ ভাগ ভোগ করে
– মোট মাছ এবং মাংসের ৪৫ ভাগ ভোগ করে
পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য রয়েছে; পশ্চিমারাই যার সিংহভাগ ভোগ করছে।
তৃতীয় বিশ্বকে তাদের উন্নয়নের জন্যই অর্থনীতিকে আরও উদার করতে হবে
বিগত তিন দশক ধরে পুরো বিশ্ব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নে পুঁজিবাদের আধিপত্য দেখেছে। এটা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে করায়ত্ব করেছে এবং পুরো পৃথিবীতে তার অর্থনৈতিক দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এশীয় বাঘ হিসেবে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং হংকং উদার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে সাফল্য লাভ করেছে এবং এগিয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্ব ব্যাংকের মতে শিল্পায়ন এবং উদার অর্থনৈতিক চিন্তা গতানুগতিক সমাজ ও অর্থনীতিতে একধরণের রূপান্তর ঘটায়। এর প্রভাব দরিদ্র দেশসমূহকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যায়-যে পথে পশ্চিমা শিল্পোন্নত বিশ্ব শিল্প বিপ্লবের সময় গিয়েছে।
বর্তমানে দরিদ্রতা পৃথিবীর অধিকাংশ জনগণের বাস্তবতা। প্রায় ৩ বিলিয়ন লোক প্রতিদিন ২ ডলারের কম আয় করে। অন্য ১.৩ বিলিয়ন লোক দিনে এক ডলারেরও কম আয় করে। ৩ বিলিয়ন লোকের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই এবং ২ বিলিয়ন লোক বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত। উদার নীতি গ্রহণের কারণে পুরো পৃথিবী জুড়েই সম্পদের আকাশসম অসম বন্টন এবং দারিদ্র্য সুনিশ্চিত হয়েছে। উদার নীতি পশ্চিমা বিশ্বকে সমৃদ্ধ করে বাকী বিশ্বকে দারিদ্র্য উপহার দিয়েছে। উদার অর্থনীতি কোনভাবেই দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক নয়। সেকারণে তৃতীয় বিশ্বে এ নীতির প্রয়োগের কারণে দারিদ্র্য আরও ঘনীতূত হয়েছে।
উদার নীতি পশ্চিমেও ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি করেছে-যার উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে প্রবল। উদাহরণ হিসেবে যদি যুক্তরাজ্যের কথা বলি তাহলে দেখা যাবে যে, ২০০৫ সালে তাদের মোট বার্ষিক উৎপাদিত সম্পদ ও সেবার পরিমাণ প্রায় ২.২ ট্রিলিয়ন পাউন্ড-যা বিগত বছরের তুলনায় বেশী ছিল। অনেকে একে উদার নীতি গ্রহণের কারণে মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির পরিচায়ক হিসেবে তুলে ধরতে চাইবেন। অর্থাৎ জনগণ এখন খুশী – কারণ তাদের খরচ করবার মত সম্পদ বেড়েছে। কিন্তু আমরা যদি লক্ষ্য করি কিভাবে বৃটেনের ৬০ মিলিয়ন জনগণ এ সম্পদকে গ্রহণ করেছিল। ২০০৫ সালে প্রকাশিত এইচ.এম রেভিনিউ এন্ড কাসটম্স -এর উপাত্ত অনুযায়ী সর্বোচ্চ ধনী শতকরা ১০ ভাগের কাছে রয়েছে জাতীয় সম্পদের শতকরা ৫০ ভাগ এবং শতকরা ৪০ ভাগ বৃটিশ জনগণ এ সম্পদের মাত্র ৫ ভাগ ভোগ দখল করে। সেকারণে বৃটেনের অধিকাংশ জনগণকে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য ধার করতে হয়। এ কারণে যুক্তরাজ্যে ভোক্তা ঋণের পরিমাণ প্রায় ১.৩ ট্রিলিয়ন পাউন্ড-যা তাদের মোট অর্থনীতির চেয়ে বড়। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা আরও ভয়াবহ। তারা হয়ত বছরে ১৩ ট্রিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ সম্পদ তৈরি করে কিন্তু জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৮.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ মার্কিন জনগণ ঋণের মাধ্যমে তাদের ব্যয় নির্বাহ করছে, যতই তারা সম্পদ ও সেবা তৈরি করুক না কেন। ২০০৫ সালে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির এক রিপোর্টে বলা হয়, শতকরা ১০ ভাগ জনগণ ৭০ ভাগ সম্পদ ভোগ করে এবং শীর্ষ ১ ভাগ ৪০ ভাগ সম্পদকে নিয়ন্ত্রন করে। অপরদিকে নীচের দিকের ৪০ ভাগ জনগণ শতকরা মাত্র ১ ভাগ সম্পদ ভোগ করে।
সুতরাং উদার নীতি পশ্চিমা বিশ্বেও সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে-যারা প্রায় শতাব্দীকাল ধরে এ নীতির আওতায় রয়েছে।
পশ্চিমা বিশ্ব আজকে আমাদের যেসব নীতিমালার কথা বলছে, তারা উন্নয়ন করেছে এর বিপরীত সব নীতিমালার ভিত্তিতে। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হা জনু চেঙ ২০০৩ সালে তার অবিস্মরণীয় কাজ ‘কিকিং অ্যাওয়ে দি ল্যাডার’-এ উল্লেখ করেন, প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রক্ষণশীল নীতিমালা গ্রহণ করেছে। উন্নয়নের ধারা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ থেকে সুবিধা আদায় নয় বরং বাজারকে রক্ষা করার মাধ্যমে উচ্চ উপযোগ সৃষ্টিকারী পণ্যের উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে বাজারকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াটি ঔপনিবেশিক এবং দাসপ্রথাতান্ত্রিক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে বাজার প্রভাবিত হয় কৃষি ও ইস্পাত খাতে ভর্তুকির মাধ্যমে। সরকার ব্যাপক খরচ কওে জীবপ্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা খাতে-যা ও একধরণের ভর্তুকি।
সেকারণে উদার নীতি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য সহায়ক নয় বরং একধরণের প্রতিবন্ধকতা। দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ কারণ হল উদার নীতি গ্রহণ।
বিশ্বায়ন হল মুক্তবাণিজ্যের শীর্ষ পর্যায় এবং একুশ শতকের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য
১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি আমেরিকান বড় বড় কোম্পানিগুলোর কার্যক্রমকে বুঝানোর জন্য সর্বপ্রথম বিশ্বায়ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির কারণে যুক্তরাষ্ট্র একধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয় করা অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচ হওয়ায় উচ্চ উৎপাদন খরচের কারণে মার্কিন পণ্য রপ্তানি করা দুরূহ হয়ে পড়ে। নিজ গৃহে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সেসব পণ্য মার্কিনীরা বিদেশে প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করতে পারছিল না।
সেকারণে সস্তা বিদেশী বাজার দরকার হয়ে পড়েছিল। সস্তা শ্রম, শ্রম আইনের যথেচ্ছ অবমাননা এবং শোষণের মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে উৎপাদন সুবিধার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার নামই হল বিশ্বায়ন।
সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর বিশ্বায়নের শিক্ষা যে রাষ্ট্রটিকে প্রথম দেয়া হয়, সেটি হল রাশিয়া। ১৯৯০ সালে সমাজতন্ত্রের পতনের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর এককেন্দ্রিক বাজারনির্ভর অর্থনীতির অনুপস্থিতিতে পুঁজিবাদী সংস্থাগুলো রাশিয়ায় ঢুকে পড়ে। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রায় ১২৯ বিলিয়ন ডলার নিয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করে। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য রাশিয়ার অর্থনীতিকে মুক্ত করে দেয়া হয়। শিল্পকারখানাগুলোকে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয় এবং অর্থনীতিকে বৈশ্বিক দরের উঠানামার কাছে স্পর্শকাতর করে তোলা হয়। ১৯৯৭ সালে বিনিয়োগকারীরা রাশিয়ার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলায় সেখান থেকে অর্থ উঠিয়ে নিতে থাকে। আর উদারনীতি গ্রহণের কারণে রাশিয়ার তখন অসহায়ের মত পরিস্থিতি অবলোকন করা ছাড়া কিছুই করবার ছিল না। দরিদ্রতা ৩০০০ ভাগ বেড়ে ২মিলিয়ন থেকে ৬০ মিলিয়নের পৌঁছায়। ইউনিসেফ পর্যবেক্ষণ করে যে এর কারণে প্রতিবছর ৫০০০০০ অতিরিক্ত মৃত্যু হয়। রাশিয়া হল বিশ্বায়নের কারণে সর্বনাশের চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি।
বিশ্বায়ন প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে পরাশক্তিসমূহ বিভিন্ন নীতিমালা চাপিয়ে দেয়ার অপর নাম-যা ইতিহাসে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার একটি অংশমাত্র। ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন থেকে আলাদা হলেও মার্কিনীরা উত্তরাধিকার সূত্রে উপনিবেশিক বৃটিশ নোংরামী ও অসততা বহন করে। সেকারণে বৃটিশরা একসময় অন্যদের সাথে যা করত মার্কিনীরা এখন তাই করে। ১৮১২ সালে বৃটিশ বাণিজ্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের অল্পকিছুদিন পর মার্কিন রাজনীতিজ্ঞ হেনরী ক্লে একজন বৃটিশ নেতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আমাদের মত বিভিন্ন জাতিসমূহ জানে ‘মুক্ত বাণিজ্য’ এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা ব্যাপক সুবিধা ভোগ করি এবং তাদের বাজারে আমাদের উৎপাদনকারীরা মনোপলি ব্যবসা করে এবং তাদের উৎপাদনকারী জাতিতে পরিণত হবার স্বপ্নকে এভাবে চিরতরে বিনষ্ট করা হয়।
রিগান এবং থেচারের সময় বিশেষভাবে দেখা যায়, বিশ্বায়নের নামে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কীভাবে মুক্ত বাণিজ্যের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যে কোন কিছুই ধ্বসিয়ে দিয়ে গণখাতের সব কিছুকে প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে ঢালাওভাবে ব্যক্তিমালিকানাধীন করা হয়। ধনী দেশের বড় বড় কোম্পানীগুলো যাতে সস্তায় দরিদ্র দেশের বিভিন্ন সম্পদের মালিক বনে যেতে পারে সে কারণে অবকাঠামোগত সমন্বয় নীতি গ্রহণ করা হয়।
বিশ্বায়নের ব্যর্থতার অনেক উদাহরণ আছে। এ পর্যন্ত দরিদ্রতা নিয়ে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা স্কোরকার্ড অন গ্লোবালাইজেশন ১৯৮০-২০০০ এ দি সেন্টার ফর ইকোনোমিক এন্ড পলিসি রিসার্চ এর গবেষক মার্ক ওয়েসব্রট, ডীন বেকার সহ প্রমুখ গবেষকগণ উল্লেখ করেন যে, ১৯৬০-১৯৮০ তুলনায় ১৯৮০-২০০০ এর বিশ্বায়নের সময়ে গড় আয়ু, শিশু মৃত্যুহার, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার হার অনেক কমে গেছে। ১৯৬০-১৯৮০ সাল সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তাদের দেশীয় শিল্পকারখানাকে পুষ্ট ও প্রতিযোগিতামূলক করবার জন্য এবং অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক বাজারের হাত থেকে রক্ষার জন্য রক্ষণশীল নীতিমালা গ্রহণ করত। এই ঠিক একই প্রক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বেড়ে উঠে।
পশ্চিমাদের বৈদেশিক সাহায্যই উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে ভুমিকা রাখছে
দশকের পর দশক ধরে বৈদেশিক সাহায্যকে উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ পর্যন্ত উন্নয়নশীর দেশগুলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রায় ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এসব সাহায্য দেয়ার পেছনে কি কোন দুরভিসন্ধি কাজ করে?
কখনও কখনও কেবলমাত্র মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সাহায্য করা হয়। অনেক সময় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সহযোগীকে অনুদান দেয়া হয়। আবার কখনও কখনও গ্রহণকারী রাষ্ট্রের রাজনীতিকে প্রভাবিত করবার জন্যও সাহায্য দেয়া হয়। বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র এবং পু্ঁজিবাদের দ্বন্দ্বের সময়, এইসব আদর্শের পুরোধা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করা কিংবা দুর্বল সহযোগীকে সাহায্য করবার জন্য আর্থিক অনুদানকে ব্যবহার করেছে। মার্কিনীরা সবসময় ইউরোপকে সমাজতন্ত্রের হাত থেকে বাঁচিয়ে পুঁজিবাদের দিকে নিয়ে আসবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অনুন্নত দেশে সাহায্য সবসময় প্রদানকারী দেশের অনুকূলে যায়। এখানে আনুকূল্য বলতে সামরিক সুবিধা, বাজার সম্প্রসারণ, বিদেশী বিনিয়োগ, মিশনারী কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার বুঝায়। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাহায্য প্রদানের পেছনে প্রাথমিকভাবে বড় বড় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের নতুন বাজার তৈরির হীন উদ্দেশ্য কাজ করে – যদিও এর পেছনে সাহায্য গ্রহণকারী রাষ্ট্রের জনগণের সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয় ।
| বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক সাহায্যর পরিমান ২০০৭ (বিলিয়ন ডলারে) | |
| যুক্তরাষ্ট্র | ২১ বিলিয়ন |
| জার্মানি | ১১ বিলিয়ন |
| ফ্রান্স | ৮.৯ বিলিয়ন |
| যুক্তরাজ্য | ৮.৮ বিলিয়ন |
| জাপান | ৭.৮ বিলিয়ন |
| হল্যান্ড | ৫.৬ বিলিয়ন |
| স্পেন | ৫.১ বিলিয়ন |
| সুইডেন | ৩.৮ বিলিয়ন |
| কানাডা | ৩.৫ বিলিয়ন |
| যুক্তরাষ্ট্র | ২১ বিলিয়ন |
| জার্মানি | ১১ বিলিয়ন |
| সুত্র: ও.ই.সি.ডি | |
বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক উইলিয়াম ইস্টারলি উন্নয়ন ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর প্রচলিত ধারার সমালোচনা করে বলেন, দাতাগোষ্ঠীর অনুদান লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। তার মতে, ‘এটা পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টের বিষয় যে, বিগত পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমারা অনুদান হিসেবে ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার দেবার পরও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত শিশুদের অর্ধেককেও মাত্র বার সেন্টের ওষুধ দেয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমারা ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেললেও দরিদ্র পরিবারগুলোতে ৪ ডলার দামের মশারির ব্যবস্থা করা যায়নি। ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হবার পরও ৫ মিলিয়ন শিশুর মৃত্যুকে ঠেকানোর জন্য তাদের মায়েদের হাতে ৩ ডলার তুলে দেয়া সম্ভব হয়নি। এটা খুবই হৃদয়বিদারক যে, বিশ্বসমাজ ধনী , বয়ঃবৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য বিনোদনের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, কিন্তু দরিদ্র মৃত শিশুদের জন্য মাত্র ১২ সেন্ট যোগানো সম্ভব হচ্ছে না।’
বৈদেশিক সাহায্যের সব দিক নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এটি কোনভাবে প্রশ্নাতীত নয়। যুক্তরাষ্ট্র ও দাতাগোষ্ঠী তাদের ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য সিদ্ধি করবার জন্য এই অনুদানকে ব্যবহার করছে। যেমন:
১. মার্কিনীরা সেসব জায়গায় সাহায্য দেয় যেখান থেকে তাদের জাতীয় নিরাপত্তার উপর হুমকি আসতে পারে, যেমন: মধ্যপ্রাচ্য এবং ঠান্ডা যুদ্ধকালীন সময়ে মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারেবিয়ান দেশসমূহ।
২. সুইডেনের লক্ষ্য হল তথাকথিত “প্রগতিশীল সমাজ”।
৩. ফ্রান্স তাদের সংস্কৃতি, ভাষা এবং প্রভাব বিস্তার করবার জন্য বিশেষত পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহকে সহায়তা দিয়ে থাকে। আবার যাদের সাথে ফরাসীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে তাদেরকে অনানুপাতিক হারে অনুদান দেয়।
৪. জাপান তাদের পণ্য ক্রয়ের শর্তে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে সহায়তা প্রদান করে।
ঔপনিবেশিকতার অবসানের পর বিশেষ করে আফ্রিকাকে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আশ্বস্ত করা হয়। জি-৮ সম্মেলন থেকে অসংখ্যবার অনুদান ও ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে বলা হয়, ‘এটা অনস্বীকার্য যে ব্যাপক হারে অপশাসন, দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনার স্বীকার হয়েছে আফ্রিকা। এ্যাকশন ফর সাউদার্ন অফ্রিকা সম্মেলনে বলা হয় : ‘এটা অনস্বীকার্য যে, আফ্রিকায় সুশাসনের অভাব, দূর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনা রয়েছে। তবে উপনিবেশবাদের কুপ্রভাব, ঠান্ডাযুদ্ধকালীন সময়ে অবহেলিত অঞ্চলসমূহে জি ৮ এর মাধ্যমে প্রদত্ত সহায়তা, ঋণের ফাঁদ সৃষ্টি, বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচীর (স্ট্রাকচারাল এ্যডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম) ব্যাপক ব্যর্থতা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অযথার্থ নীতিমালা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। আফ্রিকার সংকট সৃষ্টিতে জি ৮ এর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না। সেকারণে এ সংস্থাকে সংস্কার করতে হবে এবং আফ্রিকার উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী অন্যায় নীতিসমূহের প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।’
আজকের বিশ্বে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। সুশাসন নামক এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রন ও বাজারকে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করে। উন্নত দেশের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহের কৃষি ও বস্ত্রখাতে পর্যন্ত বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা ও ভর্তুকির সম্মুখীন করে।
বিগত দুই শতাব্দী ধরে বিশ্ব যে উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেখেছে তা ইতিহাসে বিরল এবং তা পুজিঁবাদের আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ
বিগত দুই শতাব্দী ধরে বিশ্ব যে উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেখেছে তা ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং এটা কি পুজিঁবাদের আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ?
২০০৭ সাল ছিল ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছর পুরো বিশ্ব ইতিহাসে রেকর্ড ৫৪ ট্রিলিয়ন ডলারের মত সম্পদ উৎপাদন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব অর্থনীতির আকার ছিল ১ ট্রিলিয়ন ডলার। পুঁজিবাদ গ্রহণের পর ইউরোপে শিল্প বিপ্লব হয় এবং এর মধ্য দিয়ে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও অগ্রগতি সুচিত হয়-যা সত্যি ইতিহাসে বিরল।
পুঁজিবাদের নিজস্ব অগ্রগতি বাদ দিলেও এর বিশেষজ্ঞরা সমাজতন্ত্রের পতনের পর পুঁজিবাদ এখনও বলবৎ থাকাকে এ ব্যবস্থার শক্তিশালী দিক মনে করেন। কিছু কিছু পুঁজিবাদী ব্যক্তি বর্ণবাদের দোষে দুষ্ট হয়ে নিজেদেরকে সভ্যতাকেন্দ্রিকভাবেই অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে অগ্রগামী বলে মনে করেন। ৯/১১ এর ঘটনার পর ইটালিয়ান প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লোসকনি অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে বলেন, ‘আমরা অবশ্যই আমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সচেতন থাকব-যা আমাদের ভালভাবে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দিয়েছে, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে শিখিয়েছে-যা ইসলামী দেশগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়-শিখিয়েছে সম্মান করতে মানুষের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকারকে। এটা এমন এক ব্যবস্থা যা পরমতসহিষ্ণু ও বৈচিত্র্যপূর্ণ..পশ্চিমারা মানুষকে জয় করবে যেমনিভাবে এটা সমাজতন্ত্রকে জয় করেছে-যদিও এর অন্যান্য সভ্যতা-যেমন ইসলামের সাথে বিরোধ রয়েছে-যা ১৪০০ বছর আগের ব্যবস্থায় আটকে আছে।’
বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও ধ্বসের সময়েও পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা মোহাচ্ছন্নের মত বলেছেন, ‘অর্থনীতি আয়তনে বেড়ে যাওয়া, ধ্বস নামা এ সবই পশ্চিমা অর্থব্যবস্থার মাধূর্য্য, এবং এর পরেও এটাই যোগ্যতর।’
পশ্চিমাদের জন্য পুঁজিবাদ হল অগ্রগতির অপর নাম। আর এ ধরণের দাম্ভিক উচ্চারণের জন্য ভিত্তি হিসেবে তারা ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে যদিও বাকী সবকিছু একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের এবং এগুলোর সংস্কার প্রয়োজন। আসলে এ ধরণের দর্প সেখান থেকেই শুরু হয় যেখানে সংকট নিহিত রয়েছে।
পুঁজিবাদে উন্নয়নের প্রধান সূচক হল কী পরিমাণ সম্পদ বিশ্ব উৎপাদন বা অর্জন করতে সমর্থ্য হয়েছে – যাকে তারা জি.ডি.পি (জি.ডি.পি: গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) বলে থাকে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সবই উৎপাদনের হাতিয়ার এবং সুদক্ষ শিল্পায়ন অতি সামান্য থেকে ব্যাপক উৎপাদন সুনিশ্চিত করবে। যাই হোক, প্রশ্ন হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে চালিত করে কে? এর মাধ্যমে একটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কারণসমূহের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি কীভাবে এ ধরণের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়। বৃটেনকে মনে করা হয় বিশ্বের প্রথম শিল্পোন্নত দেশ এবং এটা করা হয়েছিল পুরো বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনের মনবাসনা নিয়ে। সমুদ্র ব্যবহারের আলাদা সুবিধা থাকার কারণে সেখানে বিশেষ কর্মপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বৃটেন উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজের দেশে ব্যাপক সম্পদরাজি গড়ে তোলে।
প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও যুগান্তকারী আবিষ্কারের অধিকাংশই হয়েছে যুদ্ধের সময় বিশেষত বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল ওয়ারের সময় সাবমেরিন আবিষ্কার করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জয়ের প্রয়োজনে রেলগাড়ির উন্নয়ন করা হয়। যদিও যুদ্ধের আগে রেলগাড়ি ছিল কিন্তু যুদ্ধের সময় অস্ত্র পরিবহনের জন্য এর উৎকর্ষতা বিধান করা হয়। অপারেশন পেপারক্লিপ-যা ছিল মূলত নাৎসী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি অপহরনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকেট নিয়ে গবেষণা করার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। রকেটবিজ্ঞানের উন্নয়নের কারণে মহাকাশবিজ্ঞান, ব্যালেস্টিক মিসাইল, কৃত্রিম উপগ্রহ ও প্রাথমিক কম্পিউটার উদ্ভাবন ও উৎকর্ষতা অর্জনের পথ সুগম হয়। এ ধরণের আবিষ্কার থেকে সাধারণ ভোক্তা পণ্য এবং গৃহস্থালীর কাজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের গতি সঞ্চারের জন্য অটোমোবাইল ও উড়োজাহাজে দহন ইজ্ঞিন ব্যবহার করা হয়। ককপিটের স্ক্রীণে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত দর্শনীয় করবার জন্য এবং জেটপাইলটদের যোগাযোগের সুবিধার জন্য টেলিভিশন, আধুনিক রেডিও প্রভৃতির উন্নয়ন সাধিত হয়। হাতে গোনা সামান্য কিছু আবিষ্কার পাওয়া যাবে যেগুলো যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে আবিস্কৃত হয়নি।
ইতিহাসে পুঁজিবাদী পশ্চিমাদের প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অগ্রগামী হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু সম্পদের সন্ধান, উপনিবেশবাদ এবং যুদ্ধ পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।
পুঁজিবাদ সম্পদ উৎপাদনের জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশী মরিয়া। কিন্তু তার এখনও আরও অনেক কিছু করার অবকাশ আছে। উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত বিশ্ব অনেক সম্পদ উৎপাদন করছে, কিন্তু পৃথিবীর অর্ধেক লোক মাত্র ২ ডলারের চেয়ে কম আয় করে বলে তারা খেতে পায় না এবং ৯৫ ভাগ জনগণ দিনে ১০ ডলারেরও কম আয় করে। পুরো বিশ্বে পুঁজিবাদের কারণে দরিদ্রতা ত্বরান্বিত হচ্ছে। অতীতে ইউরোপীয়ানরা সম্পদের জন্য পুরো বিশ্ব চষে বেড়াত-যা এখন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। উনিশ শতকে যে পরিবর্তন হয়েছে তা হল বন্দুক প্রতিস্থাপিত হয়েছে শিল্প দ্বারা, দাসপ্রথা প্রতিস্থাপিত হয়েছে ভোগের মনোবৃত্তি দিয়ে, সেনাবাহিনী প্রতিস্থাপিত হয়েছে মিডিয়া দিয়ে, কৃষি প্রতিস্থাপিত হয়েছে শেয়ার মার্কেট দিয়ে।
পুজিঁবাদের পরবর্তী সাফল্য হল বিশ্বের ইতিহাসে সম্পদের পতনের সর্বনিম্ন রেখাকে স্পর্শ করা। যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তার ভরণপোষনের জন্য মাত্র কয়েক ডলার উপার্জন করতে পারে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যক বিলিওনিয়ার। একারণে পৃথিবীর অর্থনীতি ভারসাম্যহীন। ২০০৬ সালে ওয়ার্ল্ড ইন্সষ্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট ইকোনোমিঙ্ রিসার্চ অব দি ইউ.এন পৃথিবীর অর্থনীতি সম্পর্কে সর্বসাম্প্রতিক সমীক্ষা তুলে ধরে। যার প্রাপ্তিগুলো ছিল সত্যিই অদ্ভুত। পৃথিবীর সব দেশের গবেষণা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে যে, বিশ্বের শতকরা ১ ভাগ জনগণ গোটা দুনিয়ার ৪০ ভাগ সম্পদ ভোগ করে এবং মাত্র শতকরা ১০ ভাগ জনগণ ৮৫ ভাগ সম্পদের মালিক। রিচার্ড রবিন তার পুরষ্কারপ্রাপ্ত বই ‘গ্লোবাল প্রবলেম্স এন্ড দি কালচার অব ক্যাপিটালিসম’-এ উল্লেখ করেন : পুঁজিবাদের উত্থান এমন এক সংস্কৃতির জন্ম দেয় যেখানে বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে একসাথে কিছু ব্যক্তিকে চূড়ান্ত আরাম ও আভিজাত্যের সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে সবচাইতে সফল। কিন্তু প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটি মোটেও সফল নয় এবং এ ক্ষেত্রে এর ব্যর্থতাই এর একটি বড় সমস্যা।
পুঁজিবাদ স্মরণাতীতকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ঋণগ্রস্ত করেছে- যেখানে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি উভয়েরই আয়ের চেয়ে বেশী দেনা রয়েছে। পৃথিবী উৎপাদন করে ৫৪ ট্রিলিয়ন ডলার-একথা তখনই অন্তসারশূন্য হয়ে যায় যখন বুঝা যায়- এর অধিকাংশ অংশই আসে ধারদেনা থেকে। পশ্চিমা বিশ্ব ভোগে আসক্ত। তারা সবসময় যা আয় করে তার চেয়ে বেশী ভোগ করে। আর এই ভোগের যোগান আসে ঋণ থেকে। কারণ সত্যিকারের সম্পদ অর্জন করে খুব সামান্য কয়েকজন। বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অর্থনীতি – তার পতন ও সাম্প্রতিক মন্দা ঋণনির্ভর অর্থনীতির গর্বকে খর্ব করে এবং পুঁজিবাদের করুণ পরিণতির কথা আমাদের সামনে নিয়ে আসে। ২০০৭ সালে মার্কিনীরা সম্পদ উৎপাদন করে ১৪ ট্রিলিয়ন ডলার। কিন্তু তাদের জাতীয়ভাবে ঋণের পরিমাণ- যা কেন্দ্রীয় সরকার মার্কিন জনগণ ও বিশ্বের কাছ থেকে বন্ডের মাধ্যমে ৯.৭ ট্রিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ব্যাপক পরিমাণে আমদানি পণ্য ভোগ করে ও ফ্ল্যাট ক্রয় করে। একারণে ভোক্তা ঋণের পরিমাণ প্রায় ১১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। মার্কিন কোম্পানিগুলোর দেনার পরিমাণ ১৮.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। এভাবে মার্কিনীদের দেনার পরিমাণ প্রায় ৪০ ট্রিলিয়ন ডলার – যা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ। ৩৭ মিলিয়ন মার্কিনী দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। পুঁজিবাদের সার্বজনীন অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিন্তা নিতান্তই অসার।
পুঁজিবাদ নামকরণের পেছনে রয়েছে এর প্রধান দিক পুঁজির ব্যাপারটি। এটা বস্তগত সম্পদকে জীবনের একমাত্র চাওয়া পাওয়ার বিষয় হিসেবে দাঁড় করায় যেন এটা ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন। একারণে অভিজাত শ্রেণী এ ব্যবস্থার শাসকদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে করে শাসকগোষ্ঠী সর্বদা পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। পরবর্তীতে অভিজাততন্ত্র বড় বড় কোম্পানী ও তাদের প্রধানদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যেমন তেলক্ষেত্রে জন রকফেলার, অটোমোবাইলে হেনরী ফোর্ড, রেলরোডে জে গোল্ড, জে. পিয়ারপন্ট মরগান ব্যংকিং-এ এবং এন্ড্রু কার্নেগী ইস্পাতশিল্পে। পশ্চিমা সরকারগুলো উপনিবেশের মাধ্যমে যে পরিমাণ সম্পদ আহরণ করতে পারেনি-এসব বড় বড় কোম্পানীগুলো তার চেয়ে বেশী সম্পদ লুট করছে। প্রাথমিকভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখবার জন্য, সম্পদের বৈষম্যকে কমানোর জন্য ও ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য সম্পদ সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কেননা তাদের জনগনের কাছে ব্যয় করবার জন্য সম্পদ যতসামান্যই ছিল। এ চিন্তা থেকেই ভোগবাদেও উদ্ভব হয়-যেখানে ব্যয়, নতুন আবিষ্কারের স্বাদ আস্বাদন এবং নতুন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায় জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এভাবে অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়।
পুঁজিবাদ সব সময় সম্পদ সৃষ্টি করবে। এ ধারণার ভিত্তিতেই এ ব্যবস্থা পরিচালিত-যা কখনওই বন্টনের দিকে মনোযোগী নয়। যদি তাদের এ সম্পদ সৃষ্টি করতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে পুরো একটি মহাদেশকে দরিদ্র বানাতে হয় তাহলে তারা তাই করবে কিংবা বর্তমানে উপনিবেশবাদের নতুন সংস্করণ মুক্ত বাণিজ্য বা বিশ্বায়ন বাস্তবায়ন করবে। পুঁজিবাদ কখনওই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না বরং এটা একটি দুর্যোগ।
মুসলিম বিশ্ব ইসলাম চায় না এবং তারা এর জন্য প্রস্তুতও নয়
বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমারা বলে আসছে যে, মুসলিমরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা চায়; কিন্তু তারা ইসলাম চায় না। তারা বলে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কিছু সংখ্যালঘু মুসলিম ইসলাম চায়। বাকীরা পশ্চিমা ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে এবং পুঁজিবাদ দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করতে চায়। তথাকথিত কিছু আধুনিক মুসলিমরাও আজকাল বলে বসেন যে, মুসলিমরা ইসলাম চায় না এবং তারা এর জন্য প্রস্তুতও নয়। যদিও পশ্চিমা বিশ্ব ঠিকই বুঝতে পেরেছে যে, মুসলিম বিশ্ব ইসলাম চায় এবং ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের উত্থান তাদের জন্য হুমকি।
ইউ.এস ন্যাশনাল ইন্টিলিজেন্স কাউন্সিল তাদের ‘গ্লোবাল ২০২০’ প্রজেক্টের আওতায় ‘ম্যাপিং দি গ্লোবাল ফিউচার’ শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশ করে। দি ন্যাশনাল ইন্টিলিজেন্স কাউন্সিল (এন.আই.সি) হল আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কেন্দ্র। এই রিপোর্টের মাধ্যমে ২০২০ সাল নাগাদ পুরো পৃথিবীর একটি প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। রিপোর্টের উপসংহারে বলা হয়, মুসলিমরা আবার ইসলামের মূল ভিত্তিভূমির দিকে ফেরত যাচ্ছে – যখন ইসলামী সভ্যতা খিলাফতের মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। রিপোর্টে একটি কাল্পনিক দৃশ্যের অবতারণা করে বলা হয়, ‘কিভাবে একটি কট্টরপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠী কর্তৃক প্রণোদিত বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের উত্থান সম্ভব।’ এছাড়াও বলা হয়, খিলাফতের উত্থানের দিকে দৃষ্টি রেখেই মার্কিন সব পরিকল্পনা, প্রস্তুতি নেয়া উচিত। মার্কিন অন্যান্য নীতি নির্ধারক ও থিঙ্কট্যাঙ্কদের রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয় পুরো পৃথিবীব্যাপী একটি বৃহৎ আদর্শিক আন্দোলন খিলাফতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য কাজ করে আসছে। সি.আই.এ ইতোমধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধকালীন সময়ের মত আরেকবার সাফল্য পাবার জন্য ইসলামিক মিডিয়া, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে গোপন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করবার জন্য ক্রমবর্ধমান হারে অর্থ, জনবল ও সম্পদের সরবরাহ পাচ্ছে।
একই সময়ে বিভিন্ন গবেষণা, উপাত্ত ও নীতিনির্ধারকদের রিপোর্ট এটা মেনে নিয়েছে যে, পুরো পৃথিবীব্যাপী মুসলিমরা পশ্চিমা মূল্যবোধকে প্রত্যাখান করেছে। পশ্চিমারা যখন তাদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে না, তখন এটা সত্যিই অপমানজনক এক পরাজয়। তার অর্থ মন এবং মগজের যুদ্ধে পশ্চিমারা ইতোমধ্যে পরাজিত। সেকারণে ভিন্ন একধরণের সরকার ব্যবস্থার উত্থানের পথকে রুদ্ধ করবার জন্য সরাসরি দখলদারিত্ব সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
পশ্চিমাদের কর্মকান্ড দেখলে মনে হয় উম্মাহ্’র চাহিদা সম্পর্কে তারা অনেক মুসলমানের চেয়ে বেশী বিশ্বাসী। এসব কর্মকান্ড এটাও প্রমাণ করে যে, মুসলিমরা শুধুমাত্র ইসলাম চায়ই না; বরং তারা এর কাছাকাছি পৌছেও গেছে।
২০০৭ সালে ম্যারিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি একটি ভোটের ব্যবস্থা করে, যার ফলাফল ইউনিভার্সিটি অব জর্ডানের চালানো পূর্বেকার পরিসংখ্যানের সাথে মিলে যায়। চারটি বৃহৎ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে (মিশর, পাকিস্তান, মরক্কো এবং ইন্দোনেশিয়া) চালানো গবেষণায় বিস্ময়করভাবে খিলাফতের পক্ষে শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী ভোট পড়ে। এ জাতিসমূহ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে শরীয়াহ্’র বাস্তবায়ন দেখতে চায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঐক্যের ভিত্তিতে সংগঠিত ইসলামী রাষ্ট্র – খিলাফত চায়-যা অবস্থান নেবে মুসলিম ভূমিসমূহে পশ্চিমাদের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে, মুসলিম ভূমিতে পশ্চিমা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এবং নিরপরাধ সাধারণ জনগণের উপর আরোপিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।
Worldpublicopinion.org কর্তৃক পরিচালিত আর একটি ব্যাপক ভোটে পুরো পৃথিবীব্যাপি মুসলিমরা শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী সমর্থন দেয় শারী’আহ্ আইন ও খিলাফতের পক্ষে।
মুসলিম উম্মাহ্ একটি দীর্ঘ সময় ধরে পতনের পর এখন তারা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে সমাধান হিসেবে গ্রহণ করতে চাচ্ছে। কোন ধরণের ব্যবস্থার ভেতর না থাকায় মুসলিম উম্মাহ্’র ভেতর যে দুর্নীতি বাসা বেধেছে তা থেকে বের হয়ে আসবার জন্যই আজকে মুসলিম বিশ্বে বিশৃংখলা হচ্ছে। এর মানে এই নয় উম্মাহ্ ইসলামের জন্য প্রস্তুত নয়; বরং এই বিশৃংখলার ভেতর দিয়েই সাধারণত পরিবর্তন আসে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে উদার গণতন্ত্রের উত্থানের সময় এ অবস্থা দেখা দিয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উত্থানের সময় কিংবা চীনের বর্তমান উত্থানের সময়। মুসলিম উম্মাহের এ উচ্চাকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় যখন ইসলাম কোনভাবে আক্রান্ত হলে তারা একত্রে প্রতিবাদে ঝাপিয়ে পড়ে তখন; যেমন: ফ্রান্সে হিজাব নিষিদ্ধ করার পর কিংবা রাসূলুল্লাহ (সা) এর ব্যঙ্গ কার্টুন অঙ্কন করবার পর। মুসলিম উম্মাহ্ ইসলামের জন্য অনেক বেশী প্রস্তুত। এখন তাদের দরকার কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্র।
ইসলাম সেকেলে
বিগত দুই শতক ধরে পুরো বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অচিন্ত্যনীয় সাফল্য অর্জন করেছে- রেলপথের উন্নয়ন, উড়োজাহাজ, পারমাণবিক প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, আই ভি এফ, জেনেটিক উপায়ে রূপান্তরিত খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। এসব উন্নয়নের সাথে সাথে যুগপৎভাবে পশ্চিমারাও এগিয়েছে এবং ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের একপেশে উন্নয়ন আমাদের এ ধরণের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে যে, উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল উদার মূল্যবোধ।
অনেক চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের মতে বর্তমান বিশ্বে ইসলামের কোন অবস্থান নেই। মুসলিম দেশ সমূহ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতায় কোন ভূমিকা না রাখায় এ ধরণের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। পশ্চিমারা দাবী করে জ্ঞান বিজ্ঞানে তখনই তারা অগ্রগতি অর্জন করেছিল যখন তারা গীর্জা নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে ধারণ করেছে। গীর্জা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য অন্তরায়, কেননা ধর্ম কিছু অলীক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের উপর নির্ভরশীল। ধর্ম থেকে শাসনব্যবস্থার পৃথকীকরণের কারণেই শিল্প বিপ্লব সম্ভবপর হয়েছিল এবং তারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদারপন্থীদের কারণেই আজকের জ্ঞান এবং বিজ্ঞান। তাদের দাবী, জ্ঞানের ভিত্তিমূল তারাই রচনা করেছিল এবং এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখাও তাদেরই সৃষ্টি।
পশ্চিমারা তাদের ইতিহাসকে পৃথিবীর ইতিহাস বলে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পশ্চিমাদের ইতিহাস বর্ণনায় কখনওই মুসলিম সভ্যতার কাছ থেকে গৃহীত জ্ঞানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করা হয় না। ঐতিহাসিকভাবে সকল সভ্যতারই কিছু না কিছু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ইতিহাস রয়েছে। পশ্চিমারা গ্রীক সভ্যতা থেকে গৃহীত জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করেছে এবং ইসলামী সভ্যতাও ৮ম-১০ম শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক কাজসমূহকে আরবীতে অনুবাদ করেছিল।
বিজ্ঞান হল বিশ্বব্রক্ষান্ড সম্পর্কে গবেষণা, নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত বিশেষ জ্ঞান।
প্রাথমিকভাবে দহন ইজ্ঞিনের উন্নতরূপই হল আজকের অটোমোবাইল। যেখানে দাহ্য জ্বালানী ইজ্ঞিনের পিস্টনের উপর চাপ প্রয়োগ করে এবং অটোমোবাইলকে চালনা করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যে তৎকালীন সময়ে পিস্টন চালনা এবং যন্ত্রের মধ্যে ঘূর্ণন গতি সৃষ্টির জন্য প্রথমে বাষ্প এবং পরবর্তীতে কয়লাকে ব্যবহার করা হত। এ ধরণের উন্নয়ন সম্ভবপর ছিল ১২ শতকে আল জাজারির ক্রাঙ্কশ্যাফট আবিষ্কারের মাধ্যমে যেখানে তিনি রড এবং সিলিন্ডারের মাধ্যমে ঘূর্ণন গতি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম যন্ত্রে এটি ব্যবহার করেন।
ড্র্যাগ (Drag) ফোর্সকে ব্যবহার করে বাতাসের মধ্যে একটি বস্তুর গতিকে ধীর করবার প্রক্রিয়ায় প্যারাসুট কাজ করে। পূর্বের নিরীক্ষালদ্ধ ফলাফল থেকে বর্তমানে প্যারাসুট ডিজাইন করা হয়েছে। ৯ম শতাব্দীতে ইবনে ফিরনাস প্যারাসুটের প্রাথমিক নকশা করেন। তিনি কর্ডোভার ম্যাজকুইটা মসজিদ থেকে বিশাল ডানা সম্বলিত আলখেল্লা পরে লাফ দিয়েছিলেন এবং সামান্য আহত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। কাঠের কাঠামোর উপর লিনেন কাপড় জুড়ে দিয়ে এর চেয়েও ভাল নকশা সম্বলিত প্যারাসুট নির্মিত হয়। পরবর্তীতে শক্তিমত্তা ও কম ওজনের কারণে মোড়ানো সিল্ক ব্যবহার করা হয়।
এসব উদাহরণ এটাই প্রমাণ করে যে, কোন সভ্যতা বিজ্ঞানে তাদের অবদানকে নিরঙ্কুশ বলতে পারে না। বরং সার্বজনীন এ বিশাল জ্ঞান সমুদ্রের অন্যতম অংশীদার হতে পারে। যেমন অণু পরমাণু সমূহ বিশ্বব্রক্ষ্ণাণ্ডের নিয়ম অনুসারে চলে। এই নিয়মকানুনসমূহ কোন মুসলিম, হিন্দু বা খ্রিস্টান যেই আবিষ্কার করুক না কেন তা ব্যক্তিনিরপেক্ষ। এটা সার্বজনীন এবং কারো বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত নয়। সত্যিকারের বিতর্কের বিষয় হল কোন সভ্যতা জ্ঞান বিজ্ঞানে কতটুকু অবদান রেখেছে এবং কেন তারা এক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনে তৎপর ছিলো।
৮ম থেকে ১৩শ শতাব্দীকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এসময়ে ইসলামী বিশ্বের প্রকৌশলী, পন্ডিত এবং ব্যবসায়ীরা কলা, কৃষি, অর্থনীতি, শিল্পকারখানা, আইন, সাহিত্য, নৌবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্বের জ্ঞান সংরক্ষণ ও নতুন জ্ঞান অন্বেষণে বড় ভূমিকা পালন করে। মধ্যযুগের ইতিহাসের উপর বিশেষজ্ঞ একজন ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড টার্নার তার বই ‘সায়েন্স ইন ম্যাডিভেল ইসলাম’ এ উল্লেখ করেন, ‘মুসলিম শিল্পী এবং বিজ্ঞানী, রাজপুত্রগন এবং শ্রমিকরা একত্রে এমন এক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন যে, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল মহাদেশের সমাজকে প্রভাবিত করেছিল।’ ইসলামের ভেতরেই এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞানে অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতে উদ্ধুদ্ধ করেছিল।
আল্লাহ্’কে উপাসনা করা এমন একটি ব্যাপার যে তা আবিষ্কারে উদ্ধুদ্ধ করে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, কিবলা ঠিক করা, রমযান শুরু এবং শেষ করা প্রভৃতি বিষয়ের জন্য চাঁদ এবং নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান জানা অত্যাবশ্যকীয়। আর একারণেই মুসলমানরা দূরবীক্ষণ এবং নৌবিক্ষণ বিষয়ে গবেষণা শুরু করে। একারণে অধিকাংশ নৌবীক্ষণিক নক্ষত্রের নাম আরবীতে, যেমন: একামার, বাহাম, বাতেন কাইতোস, ক্যাফ, যাবিহ, ফুরুয, ইযার, লিসাস, মিরাক, নাশিরা, র্তাফ এবং ভেগা ইত্যাদি।
মুসলিমরা মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অবদান রেখেছে এবং পরবর্তীতে তারা অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল ঘড়ি উদ্ভাবন করেছে। ১০ম শতাব্দীতে আবু রায়হান আল বিরুণী গিয়ার হুইল সমৃদ্ধ যান্ত্রিক সৌর-চন্দ্র বর্ষপঞ্জিকা তৈরি করেন। ১৫শ শতাব্দীতে এই নকশার উপর ভিত্তি করে তাকী আল দীন যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কার করেন। কিবলা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা থেকেই কম্পাস আবিষ্কৃত হয় যা মুসলিম জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কারলব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছিল। মুসলিমরা কমপাস রোজ আবিষ্কার করে- যার মাধ্যমে মানচিত্রে এবং নটিক্যাল ম্যাপে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিন প্রদর্শন করা হয়।
আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:
‘তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন যেন জল-স্থলের অন্ধকারে পথের দিশা পাও‘ (সূরা আন’আম: ৯৭)
এ আয়াত মুসলমানদেরকে ভাল দূরবীক্ষণ ও নৌবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের ব্যাপারে উদ্ধুদ্ধ করে। এ যন্ত্রপাতি পৃথিবী অভিযানে ব্যবহৃত হয়। অনেক মুসলিম ভূ-বিজ্ঞানী এগুলোকে ম্যানুয়াল হিসেবে সংগ্রহ করেন। কুরআনের আয়াত তাদের এ ব্যাপারে উৎসাহী করেছে যেখানে আল্লাহ বলেন,
‘আর আমি যমিনে পর্বত সৃষ্টি করলাম, যেন জমিন টলতে না পারে, এবং আমি তথায় তাদের চলবার জন্য প্রশস্ত পথ নির্মান করে রেখেছি।‘ (সূরা আম্বিয়া:৩১)
আগের মুসলিমরা বুঝতে সমর্থ হয়েছিল যে, ইসলাম সকল বস্তগত উন্নয়ন- যেমন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পায়ন প্রভূতিকে গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধ করে। কেননা এতে মানুষের অবস্থা ও জীবনমানকে উন্নত করবার জন্য বস্তুর রূপান্তর ও উন্নয়ন করার জ্ঞান শেখানো হয়। যেহেতু অনেক অঞ্চল ধীরে ধীরে মুসলিম সভ্যতার আওতায় আসে সেহেতু এসব অঞ্চলে নগরায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন শুরু হয়। আরবের অনেক মরু অঞ্চল পানির মাধ্যমে বসবাসের উপযোগী করা হয়। মুসলিম প্রকৌশলীরা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী থেকে অসংখ্য খাল খনন করে পানির ব্যবস্থা করেন। বাগদাদের চারিদিকের নীচু জায়গায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে শহরকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করা হয়। মুসলিম প্রকৌশলীরা পানির চাকাকে (ওয়াটার হুইল) অধিকতর উপযোগী করে গড়ে তুলেন এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির ধারাগুলোকে বিস্তৃত করেন যাকে কানাতস্ বলা হয়। একারণে উন্নত গার্হস্থ্য পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠে। যার মধ্যে ছিল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, গণগোসলখানা, পান উপযোগী ঝর্ণা, পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং বহুলব্যবহৃত ব্যক্তিমালিকানাধীন অথবা গণশৌচাগার ও গোসলখানা।
মুসলিম চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী এবং বিশেষজ্ঞগণ বিজ্ঞানসহ অন্যান্য শাখায় ব্যাপক অবদান রাখেন। এসব অবদান আজকাল পশ্চিমারা ব্যবহার করছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারাও এগুলোর উন্নয়ন বিধান করেছে। কেননা একক কোন সভ্যতা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার কৃতিত্ব নিতে পারে না। প্রত্যেক সভ্যতাই তার আবিষ্কারসমূহকে লিপিবদ্ধ করেছে যা পরবর্তীতে একই বিষয়ের উপর চালিত গবেষণার জন্য সহায়ক (রেফারেন্স) হিসেবে কাজ করে। ইসলামের উত্থানের আগে আরব বিশ্ব বিজ্ঞানে কোন অবদান রাখেনি। এই একই জনগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন তারা আবিষ্কার করতে শুরু করল-যা পরবর্তী প্রজন্ম সদ্ব্যবহার করেছিল। এমনকি এসব আজও আমাদের কাজে আসে। ইসলাম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা তো নয়ই বরং এক্ষেত্রে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।
বিভিন্ন উপদল ও দেশে বিভক্ত হওয়ার কারনে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য নিতান্তই অসম্ভব
অনেকে শিয়া সুন্নীর বিভক্তিকে সামনে এনে এটা প্রতিষ্ঠিত করতে চান যে আধুনিক বিশ্বে এক মুসলিম উম্মাহ্’র ধারণা আর বাস্তবসম্মত নয়। যদিও মুসলিমদের ইতিহাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্তির পরও ঐক্যের ইতিহাস। আজকাল নতুন নতুন সীমানার মধ্যেই মুসলিমদের ঐক্য গড়ে উঠেছে। মুসলিম উম্মাহর ইসলামী ধারনাটি বহু শতাব্দির পুরোনো একটি ধারনা হিসেবে বিবেচিত হয়। শতাব্দীকাল আগে ইসলামী ধারণার মত মুসলিম বিশ্বে ঐক্য ছিল। বর্তমান বিভক্তির কারণে অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিভেদ নিরসনের একমাত্র উপায় বলে মনে করছেন এবং খিলাফতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্’র ঐক্যের ধারণাকে তাত্ত্বিক একটি বিষয় বলে জ্ঞান করছেন।
এখন আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইসলাম কিভাবে বিভক্তিকে দেখে? কিভাবে এত দল, উপদল, জাতিতে বিভক্ত পৃথিবীতে একটি বৈশ্বিক ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা সম্ভব হতে পারে?
এটি বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে যে, মুসলিম জাতিই একমাত্র জাতি নয় যাদের মধ্যে এমন ভিন্নতা রয়েছে। ১৮৬১ সালে আমেরিকার United States of America এবং Confederate States of America মধ্যে জাতিগত বিভক্তির কারণে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ হয়। ১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিংকন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর এগারটি দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্র ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়ে যেতে চায়। ২০১৩ সালের মধ্যে ব্রিটেন থেকে স্কটল্যান্ড এর পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আলোচিত দু’টি সংকটের সময়ই কেউ ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। গৃহযুদ্ধকে মার্কিন স্কুল সমূহের পাঠ্যবইয়ে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পড়ানো হয়।
বিভিন্ন মানুষ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা, চিন্তার কাছে ইসলাম অপরিচিত কিছু নয়। যখন ইসলামিক শাসন বিস্তৃতি লাভ করছিল তখন বিভিন্ন চিন্তা ও মূল্যবোধের লোকেরা ইসলামিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেই পরিগণিত হচ্ছিল। আব্বাসীয় খিলাফতের শাসনামলে ইসলাম এমন সব ভূমিতে পৌঁছে যায় যেখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে ইসলামী চিন্তাবিদ ও পন্ডিত ব্যক্তিদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আর এই দ্বন্দ্বের কারণেই ইসলামিক আক্বীদার উপর পড়াশোনা করতে গিয়ে যৌক্তিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। ইসলামী বিশ্বাসসমূহকে সাধারণ চিন্তা ও প্রমাণের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এ শাখার গোড়াপত্তন হয়। এ বিষয়টি পড়ে আরও অনেক উপশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। নতুন নতুন ভূমি জয় করবার পর এ বিষয়টি আরও সমৃদ্ধ হতে থাকে। সেকারণে অনেক মুসলমান এ বিষয়ে গবেষণা, শিক্ষালাভ, বিজ্ঞানচর্চায় নিজেদেরকে উজাড় করে দিতে থাকে। রাষ্ট্রের ভেতর একটি বহুমুখী ইসলামিক সংস্কৃতির উদ্ভদ ঘটে। বিধায় মুসলিমরা খিলাফতকে শক্তিশালী করবার জন্য এ ব্যাপারে জ্ঞানলাভে আগ্রহী হয়ে উঠে। প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী – তিনি যে সংস্কৃতির উপরই পারদর্শীতা লাভ করুক না কেন; প্রত্যেক লেখক – যে সাহিত্য ধারায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন না কেন; প্রত্যেক গণিতবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী এ সংঘাতের কারণেই সব সময় ইসলামী বিষয় নিয়ে বিতর্ক করেছেন ও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।
এ কারণে মতামতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের দল, উপদল ও ভিন্নতা দেখা দেয়-যাদের মধ্যে হাতেগোনা সামান্য কয়েকটি ইসলামিক পরিসরের বাইরে চলে যায়। যদিও চিন্তার এ ভিন্নতার কারণে মুসলিম উম্মাহ্ কখনওই বিভক্ত ছিল না। বরং আব্বাসীয় খিলাফতকালে বাগদাদ ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈপ্লবিক চিন্তার পীঠস্থান। বিভিন্ন চিন্তা ও দর্শনের ব্যক্তিদের বিতর্ককে স্বাগত জানানো হত। এভাবে ইসলাম সম্পর্কে একটি স্ফটিকস্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠে। কেননা ইসলাম বিভিন্ন চিন্তার বিপরীতে নিজের অবস্থানে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারে। সেকারণে চিন্তার ভিত্তিতে বিভিন্ন দল, উপদলের উপস্থিতি সমস্যা সৃষ্টির বদলে ইসলামকে আরও ভালভাবে বুঝার পথকে সুগম করেছে।
মুসলিম বিশ্বে বর্তমান বিভক্তি দুটি ইস্যুর কারণে জন্ম নিয়েছে। প্রথমটি হল ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞানতা এবং দ্বিতীয়টি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ডেভিড ফ্রমকিন তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন অধিকাংশক্ষেত্রেই মুসলিমরা ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার মতে, ‘সাবেক ওসমানিয়া খিলাফতের অধিকাংশ সম্পদই এখন বিজয়ীদের দখলে। কিন্তু এটা সবার মনে রাখা উচিত মুসলিমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খ্রীস্টান অধ্যুষিত ইউরোপকে পদানত করতে চেয়েছে। আর বর্তমানে বিজয়ী পশ্চিমা শক্তি সবসময় চেয়েছে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মুসলিম উম্মাহ যাতে আর কখনওই ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। শতকের পর শতকের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার আলোকে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ক্ষুদ্র, অস্থিতিশীল রাষ্ট্র জন্ম দিয়েছে যাদের শাসকেরা ক্ষমতায় থাকবার জন্য পশ্চিমাদের উপর নির্ভরশীল। ঐসব দেশের উন্নয়ন এবং বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রন করা হয়েছে এবং তারা কখনওই পশ্চিমাদের জন্য হুমকি হতে পারবে না। এই বহিঃশক্তিসমূহ পুতুল শাসকগুলোর সাথে আরবের সম্পদসমূহ সস্তায় ক্রয় করবার জন্য চুক্তি করেছে। অধিকাংশ জনগণ কে দরিদ্রতার অতল গহবরে নিক্ষেপ করে শাসকগোষ্ঠীকে ব্যাপক সম্পদশালী করা হয়েছে।’
ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা ক্ষুদ্র, অস্থিতিশীল রাষ্ট্র তৈরির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা সচেতনভাবেই করেছে-যাতে করে তারা পুনরায় একত্রিত হতে না পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে। কাগজের মানচিত্রের উপরে তারা পেন্সিল দিয়ে সীমানা এঁকে জর্ডান, সিরিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক এবং ইরানকে তৈরি করেছে। শত শত বছর ধরে একত্রে বসবাস করে আসা জনগণকে বিভক্ত করে পাকিস্তান, ভারত ও আফগানিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ঊপনিবেশিক নীতি বর্তমানে অসংখ্য সমস্যার জন্ম দিয়েছে। প্রত্যেক জাতির জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতি অনুগত শাসক নিযুক্ত করা হয়। হিজাজ অঞ্চলের নেতৃত্ব পাবার তাগিদে সৌদ পরিবার ওসমানিয়া খিলাফতকে ধ্বংসের জন্য বৃটিশদের সাথে একত্রে কাজ করে। মুসলমানেরা বর্তমানে পৃথিবীকে এইসব কৃত্রিম সীমারেখাগুলোকে দিয়ে দেখে। ঊপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করে দিয়ে বাহ্যিকভাবে বিভক্ত করে ফেলে। তারপর জাতীয় পতাকা, জাতীয় স্বাধীনতা দিবস এবং জাতীয় পতাকার ভিত্তিতে মুসলিমরা যাতে আর কখনওই একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতে না পারে সে ব্যবস্থা করে।
পূর্বে উম্মাহ্ একত্রিত হয়েছিল ইসলামের ভিত্তিতেই-যা মুসলিম ভূমিসমূহে সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মান করেছিল। সেকারণে ইসলামের অনুপস্থিতি ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের ষড়যন্ত্রের কারণেই একসময়কার ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্ আজ ৫০ টি ক্ষুদ্র অকার্যকর রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।
ইসলামের কারণে এ বিভক্তি তৈরি হয়নি বরং ইসলাম না থাকার কারণেই আজকের অনৈক্যের সৃষ্টি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল পশ্চিমা বিশ্ব সুন্নী এবং শিয়া সমস্যা নিরসনের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমাধান হিসেবে নিয়ে এসেছে। বিরোধপূর্ণ দুটি দলের মধ্যে এ ধরণের সমাধানের প্রস্তাব নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতার সমাধান সমস্যাটিকে সামষ্টিকভাবে সমাধানের বদলে ব্যক্তিপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। মহানবী মুহম্মদ (সা) এর উম্মতের যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামের প্রামাণ্য দলিলের কাছে আমাদেরকে আসতে হবে। মুহম্মদ (সা) এর পরিবারে বিপক্ষে কিছু মুসলমানের অবস্থান কিংবা মুয়াবিয়া (রা) কিছু কর্মকান্ড কখনই ইসলামিক সমাধান কিংবা বিচারব্যবস্থার প্রামান্য দলিল হতে পারে না। এখানে সূত্র হচ্ছে কোরআন এবং হাদীস। আর এর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য থাকতে পারে-যা যে কোন রায়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদিও ব্যাখ্যা দেবার কিছু সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে।
বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আসা সমাধানের ক্ষেত্রে যে কোন আদর্শের মধ্যেই মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশসমূহে ব্যাখ্যার ভিন্নতার দরূন চিন্তার অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানরা রয়েছে। যুক্তরাজ্যে রয়েছে লেবার, লিবারেল ডেমোক্রেট এবং কনজারভেটিভরা। পশ্চিমা বিশ্বে আরও রয়েছে নিউকনজারভেটিভ, লির্বাটেরিয়ানস, ফেবিয়ানস, ইনভারোমেন্টালিস্ট এবং খ্রীস্টান ডেমোক্রেটস। তারা সকলেই পুঁজিবাদের আক্বীদা ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে কতটুকু উদার হবে এই বিতর্কে মতানৈক্য পোষণ করে। মনেটারিস্টদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ক্যানসিয়ান স্কুল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপের স্বপক্ষে অবস্থান নেয়। যারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের উপর অটুট রয়েছে তাদেরও অনেকগুলো শাখা রয়েছে। সমাজতন্ত্রের পক্ষ শক্তি পুঁজিবাদের ‘মালিকানার স্বাধীনতা’ ধারণার ফলে সৃষ্ট সম্পদের ব্যাপক বৈষম্যকে সকল সমস্যার মূল বলে চিহ্নিত করে এর সমাধান করতে হবে বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একটি চিন্তার অনুসারীদের (কমিউনিস্ট চিন্তাধারার) মতে, ব্যক্তিপর্যায়ের মালিকানা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে সবক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত সাম্যতা নিশ্চিতই সবচেয়ে যুগপত সমাধান। অন্য চিন্তার অনুসারীদের (এগ্রেরিয়ান স্যোসালিস্টদের) মতে, কেবলমাত্র কৃষিজমির জন্য ব্যক্তিপর্যায়ের মালিকানা নিষিদ্ধ করতে হবে। তখন তৃতীয় একটি চিন্তার উন্মেষ ঘটে যাকে বলা হয় স্টেট্ স্যোসালিজম-যার মূল কথা হল ব্যক্তিমালিকানা থেকে জনস্বার্থে গণমালিকানা সর্বক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করতে হবে।
পশ্চিমে অনেক পন্ডিত ও গবেষকগণ শিয়া সুন্নী বিভক্তির বিষয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, এক উম্মাহ্’র ধারণাকে হেয় করবার জন্য এ সমস্যার উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তবে এ ধরণের কর্মকান্ড মুসলিম উম্মাহ্’র ভেতরে এক ধরনের পরিবর্তনের সূচনা করেছে -যা মুসলিম বিশ্বে একটি শক্তিশালী দাবী হিসেবে ত্বরান্বিত হচ্ছে।
আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি পুরো বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ একত্রে পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করছে। এমনকি প্যালেস্টাইনের মুসলিমরা দীর্ঘদিন অবৈধ দখলদারিত্বের অধীনের থাকবার পরও ইরাক, আফগানিস্তানের মুসলমানদের প্রতি একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশের জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে। উম্মাহ একটি দেহের মত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে যখন ‘মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মহানবী (সা) এর ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন (নায়ুজুবিল্লাহ্) ইউরোপে প্রকাশ করা হয়।
উম্মাহ পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে, দালাল শাসকগুলো কোনভাবেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে না। প্রসারিত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এখন উম্মাহ এবং শাসকদের মাঝামাঝি রয়েছে। দীর্ঘদিন অধঃপতিত থাকায় এখন উম্মাহ্ একসময়কার ঐক্যের কথা ভাবতে পারছে না।
আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা একটি সরকারের অন্তর্গত সমাজ সবসময় ঐক্য সৃষ্টি করে এবং নিশ্চিত করে। সাহাবীরা খারিজিদের সাথে খুব কঠোর আচরণ করেছিলেন যখন তারা ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু আমদানি করবার মাধ্যমে অনৈক্য সৃষ্টির পাঁয়তারা করে। খিলাফতের প্রত্যাবর্তন এখন অতি নিকটে এবং এ ব্যাপারে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও সি.আই. এ’র মত জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। একটি রাষ্ট্র ছাড়া ঐক্য নিতান্তই অসম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ছাড়া উত্তর আমেরিকায় আমরা দু’টি রাষ্ট্র দেখতে পেতাম। সরকারী কাঠামো না থাকলে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের মধ্যে ঐক্য থাকত না। রাষ্ট্র জনগনের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করে। এটা ছাড়া ঐক্য একেবারেই অসম্ভব। ইসলামী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, এ ব্যবস্থায় ঐক্য সৃষ্টির জন্য বিশদ প্রক্রিয়া রয়েছে এবং বিভিন্ন পরিচয় থেকে আসা লোকদের মাঝে সফলভাবে ঐক্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। বর্তমানে যে অনৈক্য দেখি তা পশ্চিমাদের সৃষ্টি এবং ক্রমাগতভাবে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
ইসলামে কোনো শাসনব্যাবস্থা নেই
দীর্ঘ প্রায় চৌদ্দশত বছর ধরে এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক ছিল না যে, ইসলামে কোন শাসনব্যবস্থা নেই। ১৯২৪ সালে যখন খিলাফত শাসনব্যবস্থা ধ্বংসের সম্মুখীন তখন এ প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছিল। এটা সে সময়ের কথা যখন অনেক ব্যক্তিই পশ্চিমা সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পন করছিল এবং ইসলামে কোন শাসনব্যবস্থা থাকাকে অস্বীকার করছিল। ১৯২৫ সালে খিলাফত ধ্বংসের এক বছর পর আলী আবদুর রাজিক ‘আল ইসলাম ওয়া উসুলুল হুকুম’ বইয়ের মাধ্যমে উল্লেখ করেন, ইসলামে কোন ধরণেরই শাসন বা সরকারব্যবস্থা নেই। স্যার থমাস আরনল্ডের মত ওরিয়েন্টালিস্টও ইসলামী অনেক তথ্য প্রমাণ দ্বারা ব্যাপক সাহিত্য রচনা করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে, ইসলামে কোন শাসনব্যবস্থা নেই।
দূর্ভাগ্যজনকভাবে আজকাল অনেক মুসলিমও ইসলামকে আধুনিকীকরণের নামে প্রমাণ করবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যে, ইসলামের নিজস্ব কোন সরকার ব্যবস্থা নেই। তাদের যুক্তি হচ্ছে মুসলমানরা যে কোন সমাজে বসবাস করতে পারে এবং এর মধ্যে সবচেয়ে ভালটি গ্রহণ করতে পারে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ইংল্যান্ডে ২০০৭ সালে “ইসলাম এন্ড মুসলিমস ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড টুডে” শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে। মিশরের প্রধান মুফতি আলী গোমাসহ অন্যান্য ‘মধ্যমপন্থি’ (মডারেট) মুসলিমের তকমা লাগানো ব্যক্তিবর্গ আলোচনা করেন কীভাবে ইসলামকে পশ্চিমাদের প্রয়োজনে পরিবর্তন করা উচিত। ইসলামে কোন শাসনব্যবস্থা নেই – এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য আলী গোমা বলেন,
‘অনেকে মনে করেন ইসলামী শাসনব্যবস্থা মানেই খিলাফত- যেখানে খলীফা একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতির মাধ্যমে শাসন করবেন। ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে এর কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। খিলাফত এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা মুসলিমরা একটি বিশেষ সময়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনে গ্রহণ করেছিল। তার মানে এই নয় যখনই সরকার ব্যবস্থার প্রসঙ্গ আসবে তখনই খিলাফতের কথা ভাবতে হবে। মিশর এ ব্যাপারে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে তা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। এ ব্যাপারে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন মুহম্মদ আলী পাশা। যার ধারবাহিকতায় খেদিব ইসমাইল একটি আধুনিক মিশর গড়বার প্রয়াস পায়। এর মানে হল ইসলামী আইনের সংস্কার। এ প্রক্রিয়ায় ইসলামিক চিন্তাবিদদের সমর্থন নিয়েই মিশর গণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে একটি উদার রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হয়। মুসলমানরা তাদের প্রয়োজনমাফিক ইচ্ছেমত যে কোন ধরণের শাসনব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রাখে।’
ইতোমধ্যে বিভিন্ন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীবর্গ একটি সম্ভাব্য ইসলামী শাসনব্যবস্থার উত্থানের ব্যাপারে সর্তক করে দিয়েছেন। এর মানে হল ইসলামে একটি শাসনব্যবস্থা রয়েছে এটা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেয়া। মুসলিমদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ট একটি মহল মনে করে যে ইসলামে কোন শাসনব্যবস্থা নেই। তাদের যুক্তি হল ইতিহাসে যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা দেখতে পাই তা মূলত: একটি সাময়িক ব্যাপারমাত্র – যা বর্তমান সময়ে একেবারেই অপ্রযোজ্য। পূর্বে ইসলামে যে শাসন আমরা দেখেছি তা বস্তুত কিছু রীতিনীতির অধীন ছিল। এ ব্যাপারটি বুঝতে হলে আমাদের ইসলামী প্রামাণ্য দলিলসমূহ খুব সুক্ষ্ণভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।
কুর’আন আল্লাহ্’র আইন দ্বারা শাসিত হবার ব্যাপারে বিভিন্ন আয়াতে বেশ জোর দিয়েছেন। যেমন:
‘এবং যারা আল্লাহ্’র দেয়া বিধান ছাড়া অন্য বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করে তারাই কাফের (অবিশ্বাসী)..জালেম (অত্যাচারী)..ফাসেক (মিথ্যাবাদী)।’ (সূরা মায়েদা:৪৪-৪৭)
আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আরও বলেন,
‘সুতরাং তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন ও যে সত্য আপনার কাছে এসেছে তা দিয়ে এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।’ (সূরা মায়েদা: ৪৮)
তিনি আরও বলেন,
‘আর আপনি আল্লাহ্’র নির্দেশ অনুযায়ী ফায়সালা করুন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, সাবধান থাকুন, যাতে তারা বিভ্রান্ত করতে না পারে।’ (সূরা মায়েদা: ৪৯)
এছাড়াও দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং শারী’আহ্ দ্বারা শাসিত হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এর এটা কখনওই সম্ভবপর হবে না যদি একজন শাসক না থাকেন -যিনি এই শারী’আহ্ বাস্তবায়ন করবেন। এভাবে অসংখ্য প্রমাণ পেশ করা যাবে যেসবের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, একজন শাসক নিয়োগ করা ফরয দায়িত্ব।
একজন খলীফা নিয়োগ করবার বাধ্যবাধকতা আমরা রাসূলের সুন্নাহ ও ইজমায়ে সাহাবা থেকে পেয়ে থাকি। নাফিয়া বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, ‘যে ব্যক্তি (খলীফার) আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিল, সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার পক্ষে কোন প্রমাণ থাকবে না এবং যে তার কাঁধে খলীফার বাই’য়াত না থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।’ (মুসলিম)
সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) সব মুসলিমের কাঁধে বাই’য়াত থাকবার প্রয়োজনীয়তা ফরয করে দিয়েছেন। তিনি বাই’য়াতহীন মৃত্যুকে জাহেলিয়াতের সময়ের মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন। ‘কাঁধে বাই’য়াত থাকা’ এর অর্থ হল একজন খলীফা থাকা। খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতিও রাসূলুল্লাহ (সা) বিবৃত করেছেন। আবু হাজিম বলেন যে, তিনি আবু হুরাইরার সাথে পাঁচ বছর অতিবাহিত করাকালীন সময়ে শুনতে পান যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ‘বনী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ। একজন মারা গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। এরপর আসবেন অসংখ্য খলীফা। তখন সাহাবা (রা) প্রশ্ন করলেন এ ব্যাপারে আপনি আমাদের কী করতে উপদেশ দেন? তিনি (সা) বলেন, তোমরা প্রথম একজনের পর অপর প্রথম (খলীফা)-এর প্রতি বাই’য়াত পূর্ণ করবে এবং তাদের জন্য রক্ষিত অধিকার প্রদান করবে। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।’
নবী করীম (সা) ইসলামী সরকারের রূপরেখা প্রদান করেন, এর নিয়মকানুন বাতলে দেন এবং বিস্তারিত ব্যাখা দেন। তিনি যখন মদীনাতে সপ্তম শতাব্দীতে খিলাফত রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন তখন সেটা ছিল বিবাদমান বিভিন্ন গোত্র অধ্যুষিত একটি শহরকেন্দ্রিক রাষ্ট্র। কুরাইশরা নতুন গড়া সমাজকে সমূলে উৎপাটন করার অপচেষ্টা চালায়। রাসূল (সা) অতিদ্রুত এমন এক রাষ্ট্র কায়েম করেন যা ছিল প্রতিরক্ষায় সক্ষম এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কুরাইশদের ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং ব্যবসায়িক পথকে সুগম রাখবার জন্য বাণিজ্য চুক্তি ও বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।
মদীনায় পা ফেলার মুহূর্ত থেকেই মুসলিম ও অমুসলিমদের সমস্যাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে তিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন শাসক হয়ে উঠেছিলেন। ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুহাম্মদ (সা) একটি কল্যাণমূলক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। একজন যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি ইহুদী, বানু দামরাহ ও বানু মাদলাজের সাথে চুক্তি করেন। তিনি তারপর চুক্তি স্বাক্ষর করেন কুরাইশ, আয়লাহ, আল জারবাহ এবং উজরাহের সাথে। সেনাপ্রধান হিসেবে তিনি অনেক যুদ্ধের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন। তিনি প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে ওয়ালী (গভর্ণর) এবং প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করে আমীল (মেয়র) নিযুক্ত করেন। যেমন: তিনি উতায়েব ইবনে উসাইদকে মক্কা বিজয়ের পর ওয়ালী এবং বাধান ইবনে সাসানকে ইয়েমেনের ইসলাম গ্রহণের পর ইয়ামেনের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। মুয়াজ ইবনে জাবাল আল খাজরাজীকে তিনি আল জানাদের ওয়ালী এবং খালিদ ইবনে সাইদ ইবনে আল আসকে সানার আমীল নিযুক্ত করেন।
রাসুলুল্লাহ (সা) লোকদের বিবাদ নিরসনের জন্য বিচারক নিয়োগ করেন। তিনি (সা) আলী (রা) কে ইয়েমেনে কাজী নিয়োগ করেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে নওফেলকে মদীনার বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। রাসুল (সা) তাদের জিজ্ঞেস করতেন, “তোমরা কি দিয়ে শাসন করবে?” তখন তারা প্রত্যুত্তরে বলতেন, “কোন রায়ের জন্য সমাধান যদি আমরা কুর’আনে না পাই, তাহলে তা সুন্নাহ্’র মধ্যে খুঁজব। যদি সেখানেও না পাই তাহলে আমরা কিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব।” তিনি (সা) এ প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন। রাসুল (সা) কখনও কখনও বিচারকদের এবং উলাহ্’দের বিষয়ে ট্রাইব্যুনালও গঠন করেছেন। তিনি ট্রাইব্যুনাল আসার পূর্বে বিবাদমান বিষয়সমুহ তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ করা ও বিচারব্যবস্থার ব্যাপারে রশীদ ইবনে আবদুল্লাহকে আমীর নিযুক্ত করেন।
মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা) রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান হিসেবে কয়েকজন রেজিস্ট্রার নিয়োগ করেন।
– আলী ইবনে আবু তালিবকে চুক্তিপত্রের লেখক হিসেবে
– মুয়াকেব ইবনে আবু ফাতিমাকে রাজস্ব বিভাগের সচিব হিসেবে
– হুজায়ফা ইবনে আল ইয়ামানকে হিজাজ অঞ্চলের ফসল ও ফলমুলের হিসেবের দায়িত্ব
– জুবায়ের ইবনে আল আওয়ামকে সাদকার সচিব
– আল মুগীরাহ ইবনে শু’বাহকে সকল ঋণ ও চুক্তিনামা লিপিবদ্ধের দায়িত্ব
– শারহাবিল ইবনে হাসানাকে বিভিন্ন বাদশাহের কাছে প্রেরিত চিঠি লিখবার দায়িত্ব
এভাবে মুহম্মদ (সা) বিভিন্ন বিভাগে সচিব অথবা পরিচালকের পদে বিভিন্ন সাহাবীদের নিয়োগ দেন। এ ব্যাপারে তিনি (সা) সাহাবীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন-যারা এসব বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও চিন্তার অধিকারী ছিলেন।
রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম- অমুসলিমদের সম্পদ বিশেষত ভূমি, ফসল ও ফলমুলের উপর কর ধার্য করেন। এগুলোর মধ্যে ছিল যাকাত, ওশর, গণীমতের মাল, খারাজ বা ভূমিকর এবং অমুসলিমদের কাছে প্রাপ্ত জিজিয়া। আনফাল এবং গণীমতের মাল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা থাকত। কুর’আনে বর্ণিত আটটি খাতেই জাকাতের অর্থ বন্টন করা হত।
মহানবী (সা) তাঁর জীবদ্দশাতেই এসব ব্যবস্থাদি বাস্তবায়ন করেন। তিনি (সা) রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী ছিলেন আর তাঁকে সহায়তা করবার জন্য ছিল বিভিন্ন সহযোগী, গভর্ণর, বিচারক, সেনাবাহিনী, সচিবগণ এবং পরামর্শ সভা। এ ধরণের কাঠামোকে বলা হয় খিলাফত এবং এটাই ইসলামের শাসনব্যবস্থা। ইসলামী রাষ্ট্রের এসব কাঠামো বিস্তারিতভাবে তাওয়াতুর বর্ণনার মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাতে পৌঁছবার দিন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। আবু বকর ও ওমর (রা) তাঁর দু’জন সহযোগী ছিলেন। সাহাবীগণ রাসূল (সা) এর মৃত্যুর পর ঐক্যমত্যে (ইজমা) পৌঁছেছিলেন যে, ইসলামী খিলাফতের প্রধান নির্বাহী হিসেবে একজন শাসক অর্থাৎ খলীফা নিয়োগ করা প্রয়োজন। অবশ্যই এই ব্যক্তি কোন নবী বা বার্তাবহনকারী হবেন না, কারণ মুহম্মদ (সা) ছিলেন শেষ নবী। একটি শাসনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা মহানবী (সা.) তার জীবনকালেই প্রদর্শন করে গেছেন। সেকারণে তাঁর প্রদর্শিত শাসনব্যবস্থা আমাদের জন্য এখনও অণুকরণীয়।
সাহাবীগণ এ মর্মে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছিলেন যে, রাসুলূল্লাহ (সা) এর মৃত্যুর পর একজন উত্তরসুরী নিয়োগ করা প্রয়োজন। তারা সেকারণে আবু বকর (রা) এর মৃত্যুর পর একই ধারাবাহিকতায় উত্তরসুরী হিসেবে ওমর (রা) কে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। এভাবে উসমান ও আলী (রা) খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। একজন খলিফা নিযুক্ত করবার আবশ্যকতা আমরা সাহাবী (রা) ঐক্যমত্য থেকে পাই যে, রাসুলুল্লাহ (সা) এর ওফাতের পর শীঘ্রই মৃতদেহ সৎকারের বাধ্যবাধকতার চেয়ে তাঁরা খলীফা নিয়োগ করার বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মৃতের দাফন কাফনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য দাফন কাফন শেষ করবার আগে অন্য কোন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা এক অর্থে হারাম। এরপরও কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসুলুল্লাহ (সা) এর দাফনের চেয়ে খলীফা নিয়োগ করা নিয়ে তখন ব্যস্ত ছিলেন। অন্য সাহাবীরা এই ব্যাপারে নীরব ছিলেন যদিও তাঁরা রাসূল (সা) এর দাফন সম্পূর্ণ করতে দুই রাত অপেক্ষা নাও করতে পারতেন।
অর্থাৎ তাঁর (সা) মৃত্যুর পর উম্মাহর ঐকমত্য নিয়ে সাহাবীগনের মধ্য হতে একজন খলীফা নিয়োগ করা হয়েছিল। যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করছিল তখন বিভিন্ন জায়গায় ওয়ালী নিয়োগ করা হয়েছিল এবং এভাবে ইসলাম সুসংহত হয়েছিল। প্রত্যেক সাহাবীই পুরো জীবনভর একজন খলীফা নিয়োগ করবার ব্যাপারে একমত ছিলেন। কে খলীফা হবেন- এ ব্যাপারে মত পার্থক্য থাকলেও খলীফা নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কারও ভেতর কোনরূপ দ্বিধা ছিল না। এটা রাসূল (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মৃত্যুর পর উত্তরসুরী খলীফা নিয়োগের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে। একইভাবে সাহাবীদের ঐকমত্য (ইজমায়ে সাহাবা) এই যে, মুসলমানদের একজন খলীফা থাকতেই হবে।
কখনও কখনও অপপ্রয়োগ ঘটলেও রাসূলের সময় থেকে ইস্তাম্বুলে ১৯২৪ সালে ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খিলাফত ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা) খিলাফতের যে বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত রূপরেখা প্রদর্শন করে গেছেন তাতে এ কথা বলার কোন সুযোগ নেই যে, এটা কেবলমাত্র একটি ঐতিহ্যগত বিষয় ছিল। আর এটা সর্বকালের জন্য সত্য কথা যে, অবশ্যই রাজতান্ত্রিক কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সুতরাং খিলাফত ইসলাম দ্বারা পরিচালিত একটি অনন্য শাসন ব্যবস্থা। খিলাফত ইসলামকে বাস্তবায়ন করে এবং সব অঞ্চলে ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়।
ইতিহাসে খিলাফতের শাসনব্যবস্থা ছিল সর্বজনগ্রাহ্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
ওরিয়েন্টালিস্ট বার্ণার্ড লুইস তার বই ‘What went wrong?’ এ বলেন:
‘পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছিল ইসলাম..এটা ছিল অর্থনৈতিক সুপারপাওয়ার..অর্জন করেছিল মানব ইতিহাসে বিজ্ঞান ও কলায় সর্বোচ্চ উৎকর্ষমন্ডিত সভ্যতা-যা ছিল বহুজাতিক, আন্তর্জাতিক -অন্যকথায় আন্তমহাদেশীয়।’
পশ্চিমাদের কাছে জীবিত কিংবদন্তীতুল্য বুদ্ধিজীবি ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা-যিনি বিশ্বাস করেন বর্তমান পৃথিবীতে পুঁজিবাদের বিপরীতে ইসলামই একমাত্র চ্যালেঞ্জ-তাঁর মতে, ‘আদর্শের জগতে বর্তমানে গণতন্ত্রের একমাত্র যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বী হল রাজনৈতিক ইসলাম। পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়াবহ রাষ্ট্র হল ইরান-যা কট্টরপন্থী শিয়া মোল্লাদের দ্বারা পরিচালিত। সুন্নী কট্টরপন্থীরা তার সমর্থকদের কাছে সঠিকভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করতে না পারায় এখনও একটি জাতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না।’
শিল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের কারণ মুক্তবাজার ও মুক্ত বাণিজ্য
বৃটেনকে লাইসেজ ফেয়ার (laissez-faire) মতবাদ গ্রহণকারী রাষ্ট্র হিসেবে এবং তারাই একমাত্র মুক্তবাণিজ্য চর্চা করে থাকে বলে মনে করা হয় । বৃটেন সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়া অথবা খুব সামান্য হস্তক্ষেপের কারণে উন্নত একটি দেশ। তবে একথা বললে মিথ্যাবলা হবে না যে, এ রাষ্ট্রটিই সর্বপ্রথম নতুন গড়ে উঠা শিল্প সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষার জন্যই এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।
১৯০৭ সালে একজন ইতিহাসবেত্তা অর্থনীতিবিদ ব্রিসকো বাণিজ্য আইনের ১৭২১ সালের সংস্কারের সারমর্ম এভাবে তুলে ধরেন,‘দেশীয় উৎপাদনকারীদেরকে বিদেশী পন্য থেকে রক্ষা করতে হবে, উৎপাদিত পন্যের অবাধ রপ্তানী নিশ্চিত করতে হবে এবং যেখানে সম্ভব আর্থিক সুবিধা ও ভাতা দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে’-এর ফলে কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেয়া হয় এবং বিদেশে উৎপাদিত পণ্যের উপর অধিক হারে করারোপ করা হয়। বিশেষত বৃটেন নিজস্ব শিল্পকে রক্ষার জন্য তার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল মানের পণ্য আমদানিকে নিষিদ্ধ করে।
১৮৪৬ সালে শস্য আইন বাতিলের মাধ্যমে বড় ধরণের পরিবর্তন আনা হয়। এই আইনটি ছিল বৃটিশ কৃষক ও ভূ-স্বামীদের রক্ষার জন্য কমদামে বিদেশী শস্য ক্রয় রোধকল্পে করারোপ সর্ম্পকিত। কিন্তু এটা করা হয়েছিল মহাদেশে শিল্পায়নকে ঠেকাবার লক্ষ্যে এবং বৃটিশ কৃষির রপ্তানী বাজারকে সম্প্রসারণ করবার জন্য। বৃটেনের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা মুক্ত বাণিজ্যের দ্বারকে উন্মোচিত করে এবং এর বিকাশ লাভ হয়েছিল দীর্ঘমেয়াদী করারোপের মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি করে। বৃটিশ অর্থনীতির উদারীকরণ একটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সুচিন্তিত পদক্ষেপ ছিল এবং এটি লাইসেজ ফেয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত বিষয় নয়।
শিল্পবান্ধব কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে বৃটেন ১৮০০ সালে যখন শিল্পায়নের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায় তখন সমুদ্র অভিযানের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সম্পদের খোঁজে নেমে পড়ে। আগ্রাসী উপনিবেশবাদের এই প্রক্রিয়া বিশ্বে বৃটেনের অবস্থানকে সুসংহত করে এবং ভূমি দখল নয় বরং উপকূলবর্তী বাজার দখলের জন্য যুদ্ধের নতুন ধারণার জন্ম হয়। ঔপনিবেশিক বিস্তৃতির জন্যই বৃটেনে তখন ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আবিষ্কার, শ্রমিক সংগ্রহের নতুন ধারণা এবং সামরিক কৌশলের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। পুরো বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের পরই বৃটেন ‘উন্নয়নের জন্য উদার মূল্যবোধ’ নীতি গ্রহণ করে। প্রচন্ড প্রতাপে পুরো বিশ্বে যখন বৃটেন দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন অন্য দেশের বাজার দখলের জন্য মুক্ত বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করে। উন্নত হবার পরই মূলত মুক্তবাজার ধারণা এসেছে। কিন্তু এটা কখনই বৃটিশ সাম্রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করেনি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নও এভাবেই হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যুক্তরাষ্ট্র তার বাণিজ্যকে উদার করেনি। কেম্ব্রিজের ইতিহাসবেত্তা অর্থনীতিবিদ ড. জুন চেঙ এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ‘ যখন শিল্পক্ষেত্রে প্রাধান্যের দিক থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল তখনই বাণিজ্যকে উদার করল এবং মুক্ত বাণিজ্যকে ছড়িয়ে দিতে লাগল’।
রক্ষণশীল নীতির মাধ্যমে পশ্চিমা দেশসমূহ যখন শিল্পক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সমর্থ হয় তখন মুক্তবাজারের পক্ষে তারা সাফাই গাইতে শুরু করে যাতে অন্যরা এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে না পারে এবং তাদের আধিপত্য বজায় থাকে। ঊনিশশতকের মাঝামাঝি সময়ে বৃটেনসহ পুরো ইউরোপ এ উদারনীতিমালা গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার একশত বছর পর ঠিক একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে।
ঐতিহাসিকভাবে জাপানের উন্নয়ন এবং চীনের উন্নয়ন বিশ্বায়নের ফসল
কথা বলা হয় যে, ঐতিহাসিকভাবে জাপান হল উদার অর্থনৈতিক আন্দোলনের সাফল্যগাঁথা-যারা মুক্তবাজার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ও অর্ধশতাব্দীরও কম সময়কালের মধ্যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অর্থনীতিতে পরিণত হয়। চীনের বর্তমান অগ্রগতির পেছনেও একই ধরণের কথা প্রচলিত আছে। যদিও সত্যিকারের ঘটনা যা বলা হচ্ছে মোটেও তা নয়।
যেসব কৌশল গ্রহণ করার কারণে জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে তা উদারনীতি ও বিশ্বায়নের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। জাপান সরকার তার দেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় খাতসমূহকে বিকাশের জন্য বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত রেখেছে। বৈদেশিক মুদ্রা বন্টনের দায়িত্ব জাপানি সরকার স্বীয় অধিকারে রাখে-যার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রনে রাখা, জাপানি কোম্পানিগুলোর বিদেশী প্রযুক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বিভিন্ন উপাদানকে নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভবপর হয়। সরকার নির্দিষ্ট শিল্পসমূহেঅর্থপ্রবাহ সুনিশ্চিত করার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দ্যা এক্্রপোর্ট ব্যাংক অব জাপান এবং জাপান ডেভেলোপমেন্ট ব্যংক স্থাপন করে।
মিনিস্ট্র অব ইন্টাঃ ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এম আই টি আই) নামক মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ জাপানের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিভাগটি উৎপাদন, সেবা এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রসারতাকে নিয়ন্ত্রন করে। জাপানি শিল্প কাঠামোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন, জাতীয় অর্থনীতিতে পণ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত এবং কাঁচামাল ও শক্তির নির্ভরযোগ্য উৎস পর্যবেক্ষণ করা ছিল এ বিভাগের দায়িত্ব। সুতরাং জাপানের অর্থনীতি ছিল কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত; কোনক্রমেই মুক্তবাজার ব্যবস্থার অধীন ছিল না।
বৈশ্বিক ব্যপারে চীন তার কয়েক দশকের পুরনো,সংকীর্ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা থেকে বের হয়ে এসেছে। চীন তার ১৫০ বছরের লজ্জা ও অপমানের দীর্ঘ লালিত ভিক্টিম (victim) মানসিকতাকে ঝেড়ে ফেলে বৃহত্তর শক্তির মানসিকতা গ্রহন করেছে (ডাগুয়া জিনতাই)। এর অবধারিত ফলাফল হল বৈশ্বিক বিষয়াবলিতে চীনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা। ভিক্টিম মানসিকতা থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর শক্তির মানসিকতা ধারণের কারণে চীন এখন নিজেকে বিশ্বশক্তিসমূহের কাছাকাছি এক সত্ত্বা হিসেবে খুঁজে পাচ্ছে। ১৯৯০ এর দশক থেকে চীনের এ পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়ে উঠে। চীন এখন তার বৈশ্বিক দায়দায়িত্বের ব্যাপারে খোলামেলা কথা বলে থাকে এবং সেদেশের নীতিনির্ধারকেরা এ চশমা দিয়েই চীন পৃথিবীকে দেখে।
গতানুগতিক ধারার অর্থনীতিবিদ ও যারা বিশ্বাস করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে উদার মূল্যবোধ গ্রহণ-তাদের জন্য চীন এক বিস্ময়। পশ্চিমা উন্নয়নের ধারণা-যেখানে গণতন্ত্র, মুক্ত বাজার এবং উদার মূল্যবোধ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে- চীন প্রথমেই সেগুলোকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে পুরো পৃথিবী এ ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞ রয়েছে।
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা বিশ্বায়নে অংশগ্রহণ না করেও চীনে ব্যাপক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্পায়ন হয়েছে- যা ছিল সম্পূর্ণ কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত এবং উদার নীতিমালার সাথে দূরতম সম্পর্ক বিবর্জিত। চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিন তাও ২০০৪ সালে বলেন, ‘আমরা কখনই অন্ধভাবে অন্য দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অনুকরণ করবো না। ইতিহাস প্রমাণ করে যে নির্বিচারে পশ্চিমা রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকরণ চীনের জন্য এক তিমিরাচ্ছন্ন পথ হবে’। সুতরাং একথা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, চীন অদুর ভবিষ্যতে উদার নীতিমালা গ্রহণ করবে না এবং উন্নয়নের পশ্চিমা ধারণা ছাড়াই তাদের উন্নয়ন সুনিশ্চিত হয়েছে।
জাপান এবং জার্মানীর মত চীনও কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত অর্থনীতি নিয়ে এগিয়ে গেছে। বাজারের সব ক্ষেত্রে রয়েছে চীনা সরকারের হস্তক্ষেপ। কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে চীন তার সম্পদকে একদিকে পরিচালিত করেছে এবং এটা তাকে আঞ্চলিক নেতৃত্ব বিধান করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে সবচেয়ে বড় অর্থনীতি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে সমাজতান্ত্রিক ঘরানার হওয়ার কারণে চীন পশ্চিমাদের সহায়তা একেবারেই পায়নি। তবে তারা দেখিয়ে দিয়েছে যে একটি স্বাধীন, আগে দেশের স্বার্থ এবং কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত নীতিমালা অর্থনৈতিক সাফল্য এনে দেয়।
মুক্তবাজারের কারনে এশিয়ান টাইগারদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে
১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং এরং তাইওয়ানের ব্যাপক ও দ্রুত শিল্পায়নকে বুঝানোর জন্য ‘টাইগার’ অর্থনীতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এই চার টাইগার অন্যান্য এশীয় অর্থনীতি-চীন এবং জাপানের সাথে অনেকক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ। যারা এশীয় ধাচের রপ্তানীমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথিকৃৎ। এই দেশসমূহ পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোকে লক্ষ্য করে পণ্য উৎপাদন শুরু করে এবং সরকারী নীতি গ্রহণের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে।
এ জাতিগুলোর দিকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাদের উন্নয়ন ছিল সম্পূর্ণ কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত, সরকারী ভতুর্কি এবং রক্ষণশীল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
১৯৬৫ সালে স্বাধীনতা লাভের পর সিঙ্গাপুর ছোট আভ্যন্তরীণ বাজার ও সম্পদের অপ্রতুলতা অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালে সিঙ্গাপুর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করে। এর দায়িত্ব ছিল সিঙ্গাপুরের উৎপাদিত পণ্যকে উৎসাহিত করবার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। সিঙ্গাপুরের প্রশাসন বেকারত্বকে কমিয়ে নিয়ে আসে, জীবনমান উন্নয়নের জন্য গণগৃহায়ন প্রকল্প চালু করে। সাথে সাথে ব্যবসাবান্ধব, বিদেশী বিনিয়োগ নির্ভর, রপ্তানীমুখী ব্যবসায়ী নীতি প্রণয়ন ও জাতীয় করপোরেশনগুলোতে সরাসরি সরকারী বিনিয়োগ করা হয়। সরকারী হস্তক্ষেপের কারণে সিঙ্গাপুরের অর্থনীতি অনেক উন্নত হয়, বিশেষত: ইলেকট্রনিক্স, কেমিক্যাল এবং সেবাশিল্পে। সিঙ্গাপুর সরকার তার অর্থনীতিকে তেমাসে-লিংকড্ কোম্পানীর (টি.এল.সি) দিকে পরিচালিত করতে থাকে। এই কোম্পানীসমূহের রয়েছে সার্বভৌম সম্পদের তহবিল। টি.এল.সি গুলো বিশেষত উৎপাদনখাতে কাজ করে এবং এরা বাণিজ্যিক সত্ত্বা হিসেবে পরিগণিত হয়। জিডিপির শতকরা ৬০ ভাগের অবদান ছিল এ কোম্পানীসমূহের।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাইওয়ানের প্রথম নেতা কমিটঙের শাসনামলে ক্ষুদ্র দ্বীপ দেশটির উন্নয়ন শুরু হয়। তখন কিছু অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। নতুন মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা প্রচুর অর্থনৈতিক সাহায্য উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে। সরকার প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। কৃষিখাতের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদকে কাজে লাগানো হত শিল্পখাতে। শিল্পখাতকে উন্নয়ন করবার জন্য শস্য রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করা হত কলকারখানার মেশিনারী ক্রয়ের জন্য। সরকার আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দেয়, বিদেশের সাথে ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রন করে এবং দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য আমদানিকে নিরুৎসাহিত করে। ১৯৬০ এর মধ্যে তাইওয়ানের শিল্পসমূহ অনুধাবন করতে পারল ইতোমধ্যে আভ্যন্তরীণ বাজার সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। তখন দেশটি অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে রপ্তানি বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করে। চিয়াং চিং কুয়ু’র ১০ টি প্রধান অবকাঠামোগত প্রকল্প এবং বিশ্বের সর্বপ্রথম রপ্তানী প্রক্রিয়াকরন অঞ্চলের মাধ্যমে তাইওয়ানে ব্যাপক শিল্পায়নের ভিত্তি রচিত হয়।
দক্ষিণ কোরিয়াও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একইভাবে এগিয়ে যায়। ১৯৬১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে অনেকগুলো পঞ্চবার্ষিকী নীতির প্রথমটি প্রণীত হয়। আর এর মাধ্যমে অতি স্বল্প সময়ে যে উন্নয়ন হয়েছে তা মুক্তবাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে করা নিতান্তই অসম্ভব ছিল। অর্থনীতিতে আধিপত্য করত কিছু ব্যক্তিমালিকানাধীন বহুজাতিক কোম্পানী যেগুলো চায়েবল নামে পরিচিত ছিল। এছাড়াও লৌহ, ইস্পাত, শক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সার, কেমিক্যাল এবং অন্যান্য ভারী শিল্পের কিছু সরকারী কোম্পানী ছিল। সরকার ঋণের সুবিধা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তিখাতের শিল্পসমূহকে রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিত, পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করত এবং গতানুগতিক মুদ্রানীতি ও আর্থিক কৌশল প্রণয়ন করত।
১৯৬৫ সালে সরকার ব্যাংকসমূহকে জাতীয়করণের মাধ্যমে আরও নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে এবং কৃষিভিত্তিক সমবায়কে কৃষি ব্যাংকের সাথে সমন্বিত করে ফেলে। সকল ঋণপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের উপর নিয়ন্ত্রন আরোপের মাধ্যমে অন্যান্য ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের উপরও সরকার কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। ১৯৬১ সালে একজন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ইকোনমিক প্ল্যানিং বোর্ড গঠিত হয়-যা সম্পদ বন্টন, ঋণের প্রবাহকে সুনিশ্চিতকরণ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সব ধরণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।
এশিয়ান টাইগারদের উন্নয়ন ব্যাপকভাবে সরকারী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। আর এটাই ছিল তাদের উন্নয়নের মেরুদন্ড। তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে। আর তাদের বর্তমান অবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় বা সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে-এর জন্য কোনক্রমেই গতানুগতিক ধারার পুঁজিবাদী মুক্তবাজার ব্যবস্থা অনুসৃত হয়নি। এই টাইগারদের অর্থনীতি মূলত ভোক্তাদের অর্থনীতি যেখানে রপ্তানী হল মূল চালিকাশক্তি।
মুসলিম বিশ্বের জন্য দুবাই এখন নতুন অর্থনৈতিক মডেল
দুবাইকে মুসলিম বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় নতুন অর্থনৈতিক সফলতা হিসেবে তুলে ধরা হয়। অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে দুবাইয়ের ৪৬ বিলিয়ন ডলারের সৃজনশীল রিয়েল এস্টেট এবং খেলাধুলা আয়োজনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা অর্থনীতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। অনেক অর্থনীতিবিদ জোর দিয়ে বলেছেন, তেল থেকে আলাদা এ অর্থনীতি অত্র অঞ্চলের জন্য উন্নয়নের নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করেছে এবং এটা ইসলামিক ধারার অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
উপসাগরীয় যুদ্ধের পর দুবাইকে তেল থেকে উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে মুক্ত বাণিজ্য ও পর্যটনের দিকে উৎসাহিত করা হয়। যাবিল আলী ফ্রি জোনের সাফল্যকে সামনে রেখে দুবাই ইন্টারনেট সিটি, দুবাই মিডিয়া সিটি এবং দুবাই মেরিটাইম সিটির মত অসংখ্য ফ্রি জোন গড়ে তোলা হয়। বুরজ্ আল আরবের মত বিশ্বের উচ্চতম ফ্রি স্ট্যান্ডিং হোটেল সহ অন্যান্য আবাসিক স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে পর্যটনের বড় বাজার হিসেবে দুবাইকে তুলে ধরা হয়। ২০০২ সাল থেকে দ্যা পাম আইল্যান্ডস, দ্যা ওয়ার্ল্ড আইল্যান্ডস এবং বুরজ্ দুবাইয়ের মত ব্যক্তিখাতের গৃহায়ন শিল্পে বিনিয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে দুবাইয়ের উন্নয়ন বলতে সুরম্য আকাশচুম্বী অট্টালিকা আর বৃহৎ আকারের শপিং মল ছাড়া আর কিছুই নয়।
বিগত বিশ বছর ধরে দুবাইয়ে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন হবার কারণে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে এটি একটি অনন্য অবস্থান করে নিয়েছে। প্রাচুর্যেও প্রদর্শনী, যেমন- সুরম্য অট্টালিকা ও অনন্য উন্নয়নের কারণে দুবাই এখন একটি আধুনিক শহর। এটা এমন একটি শহর যেখানে শুধুমাত্র ইসলামিক দেশগুলো থেকে মুসলিমরাই আসে না বরং পৃথিবীর সব দেশ থেকে সব শ্রেণীর লোকজনই আসে। দুবাই সবার জন্য প্রাচ্যের স্বাদে পশ্চিমা জীবনধারা উপহার দেয়। স্বদেশীয় লোক সেখানে সংখ্যালঘু। জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগণ বিদেশী। দুবাইয়ের ছোট্ট দ্বীপ- পৃথিবীবাসীর জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় হওয়ায় অনেকের কাছে এটা সাফল্যগাঁথা হলেও এর পেছনে রয়েছে অন্যরকম অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপকগল্প।
দুবাইয়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে তেলসম্পদ। একসময়কার মৎসজীবিদের ছোট্ট গ্রামটি আধুনিক শহরে পরিণত হয়েছে তেল বিক্রির আয় থেকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পর্যটন ও সেবাখাতে অর্থনীতিকে পরিচালিত করা হচ্ছে। একারণে দুবাই এখন শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্য নয় পুরো বিশ্বের জন্য আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। লন্ডন এবং নিউইয়র্কের মত ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র হওয়ার উচ্চাকাংখাও দুবাইয়ের রয়েছে।
দুবাইয়ের সমস্যা এই যে, এই উন্নয়ন অন্যরা অনুসরণ করতে পারবে না বরং এর উন্নয়ন অনন্য স্বতন্ত্র্য। এর উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে এটি একটি প্রসারমান অর্থনৈতিক বেলুন। দুবাইয়ের প্রবৃদ্ধির পেছনে এর তেল সম্পদের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। আর রয়েছে সেসব কোম্পানী- যেগুলো চলে বিদেশী শ্রমিকদের দিয়ে। ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে এর অবস্থানও সম্পদ সৃষ্টির পেছনে ভূমিকা রেখেছে। সমস্যা হল তেল সম্পদ অসীম নয় এবং ইতোমধ্যে এটি শেষ হওয়া শুরু করেছে। সেবাখাতের শ্রমিকগণ যারা সেদেশের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে তারা অধিকাংশই বিদেশী। মোট জনসংখ্যার খুব সামান্যই স্বদেশীয় আরব।
উপরোক্ত বাস্তবতাসমূহ প্রমাণ করে যে, দুবাইয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনভাবেই সত্যিকারের নয়। সে তার সীমিত সম্পদকে ব্যবহার করেছে এবং অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখবার জন্য স্বল্পশিক্ষিত ও দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশী বিশেষজ্ঞ আমদানি করেছে। এছাড়া দুবাই তার শহরের লোকজন ক্রয় করতে পারে এমন কোন পণ্য উৎপাদন করে না। তার ভোগ্যপণ্যসমূহকে উৎপাদনের জন্য দেশটির কোন প্রাকৃতিক সম্পদ বা অবকাঠামো নেই বলে জাতি হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী নয়। বিদেশী নাগরিক ও কোম্পানিসমূহের জন্য করমুক্ত অঞ্চল হওয়ায় এর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। এ কোম্পানিসমূহ যখন কাউকে নিয়োগ দেয় তখন কোন ধরনের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সরবরাহ করে না। এর গৃহণির্মাণ শিল্পগুলোর দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে এই আশায় যে, এগুলোর দাম ভবিষ্যতে আরও বাড়বে এবং বিক্রয় করে প্রচুর লাভ করা যাবে।
সেবাভিত্তিক অর্থনীতি হিসেবে দুবাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সরকার বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর পরিচালনার জন্য অবকাঠামো, যোগাযোগ, এ্যাপার্টমেন্ট, পার্ক, দোকান এবং পর্যটনের মত সেবাসমূহ প্রদান করে আসছে। এ ধরণের উন্নয়নের ভয়াবহ দিক হচ্ছে কোম্পানিগুলো এক জায়গায় স্থির থেকে নয় বরং প্রয়োজনে স্থান পরিবর্তন করে পরিচালিত হতে পারে। আর যে কোন ধরনের অস্থিতিশীলতা এ ধরণের পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। পৃথিবীর সবচেয়ে অস্থিতিশীল অঞ্চল হওয়ায় যে কোন ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলেই এসব কোম্পানী যে কোন সময় দুবাই ত্যাগ করতে পারে।
এসব কারণেই দুবাই মরুভূমিতে একটি মরিচীকা ছাড়া আর কিছুই নয়।
উন্নয়ন ও অস্তিত্ত্ব রক্ষার জন্য বিদেশী মেধা এবং প্রযুক্তি নির্ভর দুবাইয়ের অর্থনীতি। এর ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করবার জন্য পর্যটনসহ ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাতে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করে। এসব খাত অধিকাংশ সময়েই সুনাম ও বিদেশীদের আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। আর দুবাইয়ের অর্থনীতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর অবস্থায় রয়েছে-কারণ যে কোন সময়েই এসব বিদেশীরা চলে যেতে পারে। এ অবস্থা অনেক কারণেই ঘটতে পারে। একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ সেখানকার শ্রমিকদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলতে পারে। হাউজিং ব্যবসার দাম পড়ে যেতে পারে এবং এ ব্যবসায় লগ্নীকৃত সকল অর্থ সরিয়ে নেয়া হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান রাজনৈতিক হাল থেকে বুঝা যায় যে, এই সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এমনকি দুবাই তার অগ্রগতি সুনিশ্চিত করবার জন্য পশ্চিমা শ্রমশক্তিকে লক্ষ্য করে মদ এবং অন্যান্য অপকর্মকে বৈধতা দানের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধকে বিকিয়ে দেয়া হয়েছে।
যদি কেউ দুবাইকে অনুসরণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রধান সীমাবদ্ধতা হল যে, পর্যটন এবং অর্থায়নের জন্য সেখানে একটি মাত্র ক্ষেত্র আছে। অর্থাৎ সংজ্ঞা অনুসারে একাধিক কেন্দ্র বা ক্ষেত্র এক জায়গায় থাকতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে দুটি আঞ্চলিক এয়ারলাইনের কথাই বিবেচনা করা যাক। এমিরেটস এমন একটি এয়ারলাইন যা দুবাইয়ের বাইরে গমন করে যখন ইতিহাদ যাত্রা করে আবু দাবী থেকে। এমিরেটস ইতোমধ্যে নিজেকে একটি ব্রান্ড হিসেবে পরিচিত করে ফেলেছে এবং এ অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। অন্যদিকে যাত্রী পাবার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণে ইতিহাদ সব সময় খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে।
শিল্পায়ন উত্তর বিশ্বে সেবাখাতের বিকাশকে একুশ শতকের অর্থনীতির পূর্বশর্ত ধরে নেয়া হয়। আমেরিকা এবং ব্রিটেনের অর্থনীতির শতকরা ৭০ ভাগের উপরে হল এই সেবাখাতের অবদান। তবে দুবাই এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব কখনই শিল্পায়নের ভেতর দিয়ে যায়নি। সেকারণে সেবাখাতভিত্তিক অর্থনৈতিক মডেলের যৌক্তিকতা এখানে নেই। পশ্চিমা বিশ্ব যে পথ পাড়ি দিয়ে স্বাধীন অর্থনীতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে- যে কারণে তাদের উৎপাদনের একটি ভিত্তি রয়েছে, রয়েছে বৃহৎ সামরিক শক্তি এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত কৃষিখাত- তার সাথে দুবাইয়ের উন্নয়নের ধারণা পুরোপুরি দ্বান্দ্বিক। সাম্প্রতিক ‘ক্রেডিট ক্রাঞ্চ’ এর মত দুবাইয়ের অর্থনীতিও বিস্ফোরণ উন্মুখ ফেঁপে উঠা একটি বেলুন।
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান দ্বন্দ্ব কি আসল?
পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ব্যাপক সম্পদরাজি, ভূ-রাজনৈতিক গুরত্ব ও অপরিশোধিত তেলের সর্ববৃহৎ উৎসের কারণে গত একশত বছর ধরে বিভিন্ন শক্তির সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আর এখানে ইরান অবশ্যই একটি গুরত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে পরিগণিত। একারণে যে শক্তি ইরানকে নিয়ন্ত্রণ করবে এই অঞ্চলের আধিপত্য তারই।
যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাক দখলের পর থেকেই বিভিন্ন উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তাদের সমালোচনার শিকার হয়েছে ইরান এবং প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের যুদ্ধের হুমকির মুখে পড়েছে। ২০০২ সালে বুশের স্টেট অব ইউনিয়ন ভাষণে শয়তানের অক্ষশক্তি ঘোষণার পর থেকে জর্জ বুশ ইরানের সাথে যে কোন সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। ইরাকে জঙ্গীবাদ উস্কে দেয়া, হিজবুল্লাহকে সমর্থন প্রদান ও পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টার জন্য ইরানকে দায়ী করা হচ্ছে। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। তাদের লক্ষ্য ভিন্ন হওয়ায় এ অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থের জন্য ইরান বড় হুমকি। সেকারণে ইরানকে নিরস্ত্র করা দরকার, বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধকরণ এবং এর ইসলামিক ভাবমূর্তিকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।
১৯৭৯ সালে তথাকথিত ‘ইসলামিক বিপ্লব’-এর পর আসা ধারাবাহিক সরকারগুলোর মধ্যে রাফসানজানি ও খাতামির শাসনামল থেকে ইউরোপ ও ইরানের সাথে সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে ইরানের কট্টর রক্ষণশীল ভাবমূর্তি থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ কারণে বেশ কিছু জায়গায় ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে মার্কিনীদের কাছ থেকে অস্ত্র ক্রয়ের মাধ্যমে ইরানের আসল চেহারা বের হয়ে আসে। আমেরিকা তার স্বঘোষিত শত্রুদেরকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অর্থায়ন করতে থাকে, যেমন: নিকারাগুয়ায় একটি কমিউনিষ্ট- বিরোধী দলকে তারা সহায়তা দেয়। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের মাধ্যমে ইরানের কাছে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মিসাইল ও ভূমি থেকে শূন্যে নিক্ষেপনযোগ্য মিসাইল বিক্রয় করে।
মার্কিন কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে ইরানের বিষোদগার করলেও ইরানী সরকারে অবস্থানরত সংস্কারপন্থীরা ইরান, আফগানিস্তান ও ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে সংরক্ষণ করে আসছে। ইরাকে এস সি আই আর নেতা আয়াতুল্লাহ হাকিম ও বদর ব্রিগেডের প্রতি তেহরান সমর্থন অব্যাহত রেখেছে-যারা দক্ষিণ ইরাকে মার্কিন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান সূত্র হিসেবে কাজ করছে। আফগানিস্তানে কাবুল, হেরাত ও কান্দাহারে ইরান ব্যাপকহারে পূনর্গঠন ও প্রশিক্ষণ কাজে অংশ নিচ্ছে। উত্তর আফগানিস্তানে পশতুন প্রতিরোধ ঠেকানোর জন্য ইরান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাকের-হ্যামিল্টনের রিপোর্টে এ ধরণের সম্পৃক্ততার কথা পাওয়া যায়, “…ইরাক ও অন্যান্য আঞ্চলিক ইস্যুতে ইতিবাচক নীতির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষভাবে ইরান ও সিরিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। ইরান ও সিরিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হবার সময় ইতিবাচক ফলাফলের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড় দেয়া ও ছাড় না দেয়ার বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে বিশেষ করে মাকির্ন-ইরান সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইরানকে সম্পৃক্ত করা সমস্যাপূর্ণ। এখন আফগানিস্তানে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের সহযোগী এবং উভয় পক্ষকেই চিন্তা করে দেখতে হবে ইরাকেও একই ধরণের সহযোগিতার মডেল অনুসরণ করা যায় কিনা?“
অপরদিকে পারমাণবিক শক্তিধর হওয়ার প্রচেষ্টাকে মার্কিনীরা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করে সবসময়ই ইরানকে চাপের মধ্যে রাখার কৌশল গ্রহণ করেছে। ইসরাইল একমাত্র দেশ যারা মনে করে মাসখানেকের মধ্যে ইরান পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করতে যাচ্ছে। ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলভান সেলম নিউইয়র্কে ইহুদী নেতাদের এক বৈঠকে বলেন, “আমাদের জনবল, নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মতে তারা পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর খুব, খুব কাছাকাছি চলে এসেছে- হয়ত বা মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তারা এ ব্যাপারে পুরো জ্ঞান লাভ করবে।“
২০০৫ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিতব্য ইন্টারন্যাশনাল এটোমিক এনার্জি এজেন্সি (আই.এ.ই.এ) এর বৈঠকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনী নিউক্লিয়ার অস্ত্র সংরক্ষণ, উৎপাদন এবং ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি ফতোয়া জারি করেন। এই সর্বোচ্চ নেতা ২০০৩ সালে ইসরাইলের সাথে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দেন।
অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময়কাল ধরে বিভিন্নক্ষেত্রে ইরান ও মার্কিন সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে আমরা ওয়াশিংটনের কাছ থেকে একধরণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি। যখন কোথাও কোথাও আমরা দুটি দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক দেখতে পাই। আবার অন্যদিকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি ও ইসলামিক ভাবমূর্তির জন্য প্রকাশ্যে ইরানকে তারা তিরষ্কার করে থাকে।
ইসলামিক বিপ্লবের পেছনে মার্কিন সহযোগিতা ইরানকে আমেরিকার ক্রীড়ানক হিসেবে ব্যবহারের পথকে সুগম করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সচেতনভাবে উদ্দেশ্য হাসিল হবার পর ইসলামিক বিপ্লবকে থামিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে যেরকমভাবে পাকিস্তানে জিহাদীদেরকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্বের ব্যাপারে উস্কে দিয়ে পরে থামানোর চেষ্টা করেছে।
১৯৭৯ সালে বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে যাওয়া শাহকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা। সেক্ষেত্রে আমেরিকার কৌশলগত প্রাধান্য ছিল ইরানী জনগণের কাছে জনপ্রিয় বিকল্পকে দিয়ে শাহকে সরিয়ে দেয়া। সুদানি নেতা সাদেক আল মেহেদীর মধ্যস্ততায় বিপ্লবকে কার্যকরী করবার জন্য খোমেনী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও এখানে প্রাক্তন অ্যাটর্নী জেনারেল রামসে ক্লার্ক ১৯৭৯ সালে খোমেনীর সাথে এ ব্যাপারে সরাসরি কথা বলেন। খোমেনীর নেতৃত্বাধীন বিপ্লবের মাধ্যমে রক্ষণশীলেরা কার্যকরভাবে সামরিকবাহিনী, বিচারব্যবস্থা, গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। মার্কিন বিরোধী সকল প্রচারণার পরও ইরান কখনওই আমেরিকাকে তেল সরবরাহ করা বন্ধ করেনি কিংবা এ সম্পর্কিত কোন চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। কট্টরপন্থীদের অবস্থানের কারণে যুক্তরাষ্ট্র বিপ্লবকে বিপরীত খাতে প্রবাহিত করতে সমর্থ্য হয়নি। এই কট্টরপন্থীরাই তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করবার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র বানাতে চায় এবং স্পর্শকাতর অস্ত্র সংগ্রহ করতে চায়।
ইরানের জনগনের ৭০ ভাগেরই বয়স ৩০ এর নীচে। তার মানে সেদেশের জনগনের অধিকাংশই ইসলামী বিপ্লবের সময় জন্মই নেয়নি। এই তরুণ জনগনের বিপ্লব সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। আর তারা এমন একটি অংশ দ্বারা শাসিত হচ্ছে যারা বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। মার্কিনীরা সরাসরি ইরানী সরকারের সংস্কারপন্থী অংশ এবং ছাত্রদের সাথে সম্পৃক্ত এবং তাদেরকে এই ধারণা প্রদান করে যে, আমেরিকার স্বার্থ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে তারা সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে।
যুক্তরাষ্ট্র এব্যাপারে নিশ্চিত নয়, কিভাবে তারা ইরানের বিরুদ্ধে লক্ষ্য অর্জন করবে- কূটনৈতিকভাবে নাকি সামরিকভাবে? জর্জ বুশ দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে এ ব্যাপারটি বেশ তোলপাড় তুলে এবং ওয়াশিংটন মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে।
ইরানের ব্যাপারে সঠিক সমাধান কি হবে এ ব্যাপারে দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে বাস্তববাদী (realists) এবং নব্য রক্ষণশীলদের (neoconservatives) মতবাদ। আমেরিকান সরকারের সকল অংশ এবং বিভিন্ন সংস্থা, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, পেন্টাগণ এবং সিআইএ যুদ্ধের ব্যাপারে একমত পোষণ করে। কিন্তু মতানৈক্য দেখা দেয় ২০০৪ সালে যখন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের জাতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ড জিবিংনিউ ব্রেজিনস্কির তত্ত্বাবধানে কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন্স (সি.এফ.আর) সংস্থাটি ‘ইরানঃ টাইম ফর অ্যা নিউ এপ্রোচ’-নামক রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ রিপোর্ট দাবী করে যে, ইরানের বর্তমান শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের উপযুক্ত সময় সম্পর্কে নব্য রক্ষণশীলদের বর্তমান ধারণা মোটেও সঠিক নয়। রিপোর্টের মতে, “রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি ও অসন্তোষ সত্ত্বেও ইরান আরেকটি বিপ্লবের সম্মুখীন নয়। যারা বর্তমান ব্যবস্থার পুরোধা তারা পুরো পরিস্থিতি এখনও ভালভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছে।” রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয় সকল সমস্যা সমাধানের জন্য তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার তুমুল বিতর্ক অবাস্তব; বরং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও নিউক্লিয়ার শক্তি হবার উচ্চাকাংখা থেকে ইরানকে বিরত রাখার জন্য প্রধান বিষয়গুলো নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডের নিকটবর্তী নব্য রক্ষণশীলেরা এই রিপোর্টের মতামতকে মুহূর্তের মধ্যে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন। নব্য রক্ষণশীল মাইকেল লেডেন, ন্যাশনাল রিভিউ অনলাইন-এ লিখেন যে, তেহরান হল ইসলামিক সন্ত্রাসীদের রাজধানী এবং সি এফ আর সুপারিশকে অপমানজনক ও আপোষকামী বলে উল্লেখ করেন।
বুশের দ্বিতীয়বারের শাসনামলে নব্য রক্ষণশীলদের প্রভাব ব্যাপকভাবে কমতে থাকে। নব্য রক্ষণশীলদের মধ্যে পল উলফোভিচ, জন বোল্টন প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিশ্ব ব্যাংক ও জাতিসংঘের নীতি বাস্তবায়নের কাজে নিযুক্ত করা হয়। অন্যদের মধ্যে ডগলাস ফেইথকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। নব্য রক্ষণশীলদের বিদায়ের মাধ্যমে বুশ প্রশাসনে বাস্তববাদীরা (realists) সুযোগ পায়। পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক ব্যাপারগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও পেন্টাগনের ভেতর সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। অন্যান্য সহযোগী দেশকে সম্পৃক্ত করে পূর্ববতী মার্কিন প্রশাসন যৌথভাবে সুদান, লেবানন, উত্তর কোরিয়া এবং ইরানের ব্যাপারে বিতর্কিত বিষয়গুলো সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে বাস্তবাদীদের উপস্থিতি ইরানের ব্যাপারে নব্য রক্ষণশীলদের ভূমিকাকে পুরোপুরি স্তদ্ধ করতে পারেনি। নব্য রক্ষণশীলতাবাদের কট্টর সমর্থক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ইরানের তেল ও গ্যাসের উপর মার্কিন আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সেদেশের উপর প্রচন্ড চাপ প্রয়োগের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।
পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, ইরান এবং মার্কিনীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সত্যিকার অর্থেই রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেসব দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে গিয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। বুশ প্রশাসনের বাস্তবাদীরা এখন এগিয়ে আছে এবং তাদের নীতি হল একক প্রচেষ্টা বা সামরিক হস্তক্ষেপকে আপাত পরিহার করে বহুজাতিক সহযোগিতা ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইরানের সাথে বিতর্কিত নিউক্লিয়ার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়া। তবে ইরানে সামরিক হামলা চালানোর ব্যাপারে যারা চাপ প্রয়োগ করছিল তাদের দমানোর ব্যাপারে বুশ প্রশাসনের ব্যর্থতা বিশ্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিবে।